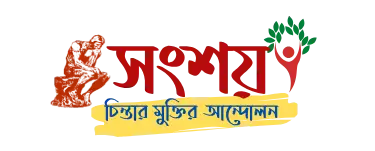ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism): রাষ্ট্র, ধর্ম আর ব্যক্তির স্বাধীনতার এক গোলকধাঁধা
Table of Contents
- 1 ভূমিকা
- 2 ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে কী? শব্দের জট এবং ধারণার মুক্তি
- 3 ইতিহাসের ধুলোপথ ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম
- 4 একই বৃন্তে নানা ফুল – ধর্মনিরপেক্ষতার রকমফের
- 4.1 ১. ফরাসি মডেল: কঠোর বিচ্ছেদের ‘লাইসিতে’ (Laïcité)
- 4.2 ২. আমেরিকান মডেল: বন্ধুসুলভ বিচ্ছেদের প্রাচীর (Friendly Wall of Separation)
- 4.3 ৩. ভারতীয় মডেল: নীতিগত দূরত্বের ‘সর্বধর্ম সমভাব’ (Principled Distance)
- 4.4 ৪. তুর্কি মডেল: রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বা আক্রমণাত্মক ধর্মনিরপেক্ষতা (Assertive Secularism)
- 4.5 ৫. ব্রিটিশ মডেল: প্রতিষ্ঠা সহ ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism with an Established Church)
- 5 ধর্মনিরপেক্ষতা কেন দরকার? আধুনিক রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ
- 6 সমালোচনার আয়নায় ধর্মনিরপেক্ষতা – চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা
- 7 বাংলাদেশ ও ধর্মনিরপেক্ষতা – এক জটিল ও অমীমাংসিত অধ্যায়
- 8 ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ: নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
- 9 আদর্শের স্থপতিগণ – যেসব চিন্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ধর্মনিরপেক্ষতা
- 9.1 ১. জন লক (John Locke): সহিষ্ণুতার প্রথম প্রবক্তা
- 9.2 ২. ভলতেয়ার (Voltaire): যুক্তির শাণিত তরবারি
- 9.3 ৩. কার্ল মার্ক্স (Karl Marx): ধর্মনিরপেক্ষতার র্যাডিকাল সমালোচনা
- 9.4 ৪. এমিল ডুর্খাইম (Émile Durkheim): ধর্মের সামাজিক ভূমিকা এবং ‘সিভিল রিলিজিয়ন’
- 9.5 ৫. জন রলস (John Rawls): পাবলিক রিজন এবং ওভারল্যাপিং কনসেনসাস
- 9.6 ৬. তালাল আসাদ (Talal Asad): ধর্মনিরপেক্ষতার উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচনা
- 9.7 ৭. রাজীব ভার্গব (Rajeev Bhargava): নীতিগত দূরত্বের ধারণা
- 10 উপসংহার
- 11 তথ্যসূত্র
ভূমিকা
শুরু করার আগে চলুন একটা ছোট্ট দৃশ্য কল্পনা করা যাক। ধরুন, একটা বড় রাস্তার মোড়ে বিশাল এক জটলা। গাড়ি, রিকশা, বাস, মানুষ – সব মিলেমিশে একাকার। ট্রাফিক পুলিশ তাঁর সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন জট ছাড়ানোর। তিনি কি কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের গাড়িকে আগে যেতে দিচ্ছেন? বা কোনো বিশেষ রঙের পোশাক পরা মানুষকে রাস্তা পার হতে বিশেষ সুবিধা দিচ্ছেন? না। তাঁর কাছে সবাই সমান। তাঁর একমাত্র কাজ হলো নিয়মটা সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা, যাতে পুরো ব্যবস্থাটা সচল থাকে, যাতে কেউ কারো ওপর চড়াও না হয়, যাতে সবাই নিজের গন্তব্যে শান্তিমতো পৌঁছাতে পারে। রাষ্ট্র আর ধর্মের সম্পর্কের বিষয়টা অনেকটা এই ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকার মতো। আর এই ভূমিকাটি পালন করার যে দর্শন, তার সবচেয়ে কাছাকাছি শব্দ সম্ভবত ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ (Secularism)।
শব্দটা শুনলেই আমাদের মনে নানা রকম ছবি ভেসে ওঠে। কারো মনে হয় এটা ধর্মহীনতার নামান্তর, আধুনিকতার নামে শিকড় কেটে ফেলার এক নির্মম কুঠার। কেউ ভাবেন, এটা বুঝি ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবন থেকে মুছে ফেলার কোনো পশ্চিমা ষড়যন্ত্র, যা আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে দেবে। আবার কারো কাছে এটা আধুনিক রাষ্ট্রের একটা অপরিহার্য গুণ, যা ছাড়া বহু জাতি, বহু ভাষা আর বহু বিশ্বাসের একটা দেশ এক হয়ে থাকতেই পারে না। তাঁদের কাছে এটা এক রক্ষাকবচ, যা ভিন্নমতের মানুষকে সংখ্যাগরিষ্ঠের আগ্রাসন থেকে বাঁচায়, যা রাষ্ট্রকে সবার করে তোলে। সত্যিটা কী? ধর্মনিরপেক্ষতা কি বন্ধু, নাকি শত্রু? এটা কি নিছকই একটা রাজনৈতিক বুলি, নাকি এর কোনো গভীর দার্শনিক ভিত্তি আছে? এটা কি সব রোগের মহৌষধ, নাকি নিজেই এক নতুন রোগের কারণ?
এই যে এত প্রশ্ন, এত ধোঁয়াশা, এর কারণ হলো আমরা প্রায়ই শব্দটার গভীরে না গিয়ে এর উপরের খোলসটা নিয়েই বেশি আলোচনা করি। এই লেখায় আমরা সেই খোলসটা ছাড়িয়ে একেবারে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করব। আমরা দেখব, এই ধারণাটার জন্ম কেন হলো, কীভাবে হলো। ইতিহাসে এর পথচলা কেমন ছিল? আমেরিকা থেকে ফ্রান্স, তুরস্ক থেকে ভারত – একেক দেশে এর চেহারা একেক রকম কেন? এর আসল দরকারটাই বা কী? আর এর সীমাবদ্ধতাগুলোই বা কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের নিজেদের রাষ্ট্র, সমাজ আর ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রভাব ঠিক কতখানি?
আমরা কোনো জটিল সংজ্ঞার মারপ্যাঁচে যাব না। বরং গল্পে গল্পে, ইতিহাসের অলিগলিতে ঘুরতে ঘুরতে আর বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার এই গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার একটা পথ খোঁজার চেষ্টা করব। এই যাত্রাটা কেবল একটা শব্দের অর্থ খোঁজা নয়, বরং আধুনিক মানুষ হিসেবে আমাদের নিজেদের পরিচয়, আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝারও একটা প্রচেষ্টা। আমরা দেখব, কীভাবে ধর্মের নামে হওয়া যুদ্ধ আর রক্তপাত থেকে বাঁচার তাগিদে এই ধারণার জন্ম হয়েছিল। আমরা বোঝার চেষ্টা করব, কেন গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা আর আধুনিক বিজ্ঞান – এই সবকিছুর বিকাশের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার একটা গভীর যোগসূত্র আছে।
একইসাথে, আমরা এর অন্ধকার দিকগুলোকেও এড়িয়ে যাব না। আমরা দেখব, কীভাবে এই আদর্শকে ব্যবহার করে মানুষের ওপর নতুন ধরনের নিপীড়ন চালানো হয়েছে, কীভাবে ‘নিরপেক্ষতা’-র মুখোশের আড়ালে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতিকেই সবার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রশ্ন করব, রাষ্ট্র কি আদৌ পুরোপুরি নিরপেক্ষ হতে পারে? নাকি এটা একটা অসম্ভব কল্পনা?
এটা কোনো রায় দেওয়ার চেষ্টা নয়, বরং একটা দীর্ঘ অনুসন্ধানী যাত্রা। এই যাত্রায় আমরা অনেক চেনা ধারণাকে নতুন করে প্রশ্ন করব, অনেক কঠিন সত্যের মুখোমুখি হব, আর শেষ পর্যন্ত হয়তো আবিষ্কার করব যে, বিষয়টা যতটা সহজ আমরা ভাবি, ততটা সহজ নয়; আবার যতটা জটিল বলে ভয় পাই, ততটাও হয়তো জটিল নয়। চলুন, তাহলে শুরু করা যাক সেই গোলকধাঁধার পথে হাঁটা।
ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে কী? শব্দের জট এবং ধারণার মুক্তি
‘সেক্যুলারিজম’ বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা শোনার সাথে সাথেই আমাদের মনে যে ধারণাটা আসে, তা হলো রাষ্ট্র আর ধর্মকে আলাদা রাখা। কথাটা ভুল নয়, তবে এটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। জলের নিচে লুকিয়ে থাকা বিশাল বরফখণ্ডের মতো এর গভীরে রয়েছে জটিল দার্শনিক বিতর্ক, রক্তাক্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আর আধুনিক সমাজের পরিচয় নির্মাণের এক নিরন্তর সংগ্রাম। ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল একটি নীতি নয়, এটি একটি বহুমাত্রিক ধারণা যার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং দার্শনিক দিক রয়েছে। এর লাতিন উৎস ‘saeculum’ শব্দটির অর্থ ছিল ‘একটি প্রজন্ম’ বা ‘একটি যুগ’, যা ধীরে ধীরে পারলৌকিক বা অনন্ত জগতের (religious sphere) বিপরীতে এই জাগতিক জগৎকে (temporal sphere) বোঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এই জাগতিকতার দিকে মনোযোগ দেওয়াই এর মূল স্পিরিট। একে ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা কয়েকটি মূল স্তম্ভ, কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা এবং এর সাথে সম্পর্কিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে আলাদাভাবে এবং বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব।
মূল ধারণা: তিনটি প্রধান স্তম্ভ
যেকোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণাকে মোটামুটি তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো বলে ধরে নেওয়া যায়। এই তিনটি স্তম্ভ একে অপরের সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত যে একটিকে ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ বা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এরা একটি মজবুত ত্রিপদের মতো, যার যেকোনো একটি পা সরিয়ে নিলে পুরো কাঠামোটিই ভেঙে পড়বে।
১. রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পৃথকীকরণ (Separation of State and Religious Institutions)
এটাই ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে পরিচিত এবং মৌলিক ভিত্তি। এর সরল অর্থ হলো, রাষ্ট্র পরিচালনার যন্ত্র (government machinery) এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম (organized religion) একে অপরের কার্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না। রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে তার অফিসিয়াল ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না বা কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। রাষ্ট্রের কোনো গির্জা, মন্দির বা মসজিদ থাকবে না। একইভাবে, কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না বা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে কোনো বিশেষ সুবিধা পাবে না। রাষ্ট্রের আইনকানুন তৈরি হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সার্বজনীন যুক্তির ভিত্তিতে, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে নয়। এর মানে হলো, রাষ্ট্রীয় পদে বসার জন্য কোনো ধর্মীয় যোগ্যতা বা অযোগ্যতা থাকবে না, এবং রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে না।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা থমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) এই ধারণাটিকে একটি শক্তিশালী রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন, যাকে তিনি বলেন ‘গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর’ (a wall of separation between church and state) (Jefferson, 1802)। এই প্রাচীরের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ: একদিকে এটি রাষ্ট্রকে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাতের প্রভাব থেকে রক্ষা করে, অন্যদিকে এটি ধর্মকেও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং দুর্নীতির প্রভাব থেকে রক্ষা করে। একটু ভেবে দেখুন, রাষ্ট্র যখন কোনো ধর্মকে নিজের কাঁধে তুলে নেয়, তখন কি ধর্মটির উপকার হয়, নাকি অপকার? ইতিহাস বলে, দ্বিতীয়টিই বেশি সত্যি। ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকলে ধর্মের আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা প্রায়ই হারিয়ে যায়। সেটি তখন আর মানুষের মুক্তির পথ দেখায় না, বরং শাসকের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ারে পরিণত হয়। আমেরিকার প্রথম দিকের চিন্তাবিদ রজার উইলিয়ামসের (Roger Williams) মতো মানুষেরা ঠিক এই কারণেই রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা রাখতে চেয়েছিলেন – শুধু রাষ্ট্রকে নয়, খোদ ধর্মকে বাঁচানোর জন্যই (Williams, 1644)। তাই এই পৃথকীকরণ ধর্ম এবং রাষ্ট্র উভয়ের জন্যই স্বাস্থ্যকর। রাষ্ট্রের কাজ জাগতিক বিষয় নিয়ে – যেমন রাস্তাঘাট বানানো, অর্থনীতি সামলানো, নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা ইত্যাদি। আর ধর্মের কাজ হলো মানুষের আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক চাহিদা মেটানো। দুটো আলাদা জগৎ, দুটোর কার্যক্ষেত্র আলাদা। এই পৃথকীকরণ রাষ্ট্রকে একটি নিরপেক্ষ মঞ্চে পরিণত করে, যেখানে সব ধর্মের মানুষ নিজেদের সমান নাগরিক হিসেবে ভাবতে পারে।
২. সকল নাগরিকের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা (Freedom of Religion for all Citizens)
ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করেই ক্ষান্ত হয় না, এটি ব্যক্তিকে তার নিজের বিশ্বাস বেছে নেওয়ার এবং পালন করার সর্বোচ্চ স্বাধীনতাও দেয়। এই স্বাধীনতা দুটি অংশে বিভক্ত: ‘বিশ্বাস করার স্বাধীনতা’ (freedom of conscience) এবং ‘ধর্ম পালনের স্বাধীনতা’ (freedom to practice religion)। এটি কেবল ‘ধর্মের স্বাধীনতা’ (freedom of religion) নয়, বরং ‘ধর্ম থেকে মুক্তি’র স্বাধীনতাও (freedom from religion) বটে।
যেকোনো নাগরিক তার পছন্দমতো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে, পালন করতে পারবে, ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবে, অথবা কোনো ধর্মই পালন না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। রাষ্ট্র তাকে কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাস গ্রহণ বা বর্জন করার জন্য কোনো ধরনের চাপ, প্রলোভন বা শাস্তি দিতে পারবে না। এটি ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান, যা জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের (UDHR) ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদেও স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, নিজের ধর্মকে ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে প্রচার করার অধিকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যতক্ষণ না তা অন্য কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বা ঘৃণার উদ্রেক করে। এর মধ্যে উপাসনালয় নির্মাণ, ধর্মীয় উৎসব পালন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান এবং ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলার অধিকারও পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নাস্তিক, আস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) – সবাইকে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপনের নিরাপত্তা দেয়। এই স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ একটি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থায় পরিণত হতে পারে, যেমনটা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে বা কামাল আতাতুর্কের (Kemal Atatürk) তুরস্কের প্রাথমিক পর্যায়ে, যেখানে রাষ্ট্র ধর্ম থেকে পৃথক তো ছিলই, কিন্তু নাগরিকদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতাও কেড়ে নিয়েছিল বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। সুতরাং, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে রাষ্ট্রের ধর্মহীনতা নয়, বরং রাষ্ট্রের এমন একটি চরিত্র যা সব ধরনের ধর্মীয় (এবং অধর্মীয়) বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে।
৩. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের প্রতি সমতা (Equality of all Citizens regardless of Religion)
এটি ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য। পৃথকীকরণ এবং স্বাধীনতা – এই দুটি স্তম্ভের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যই হলো এই তৃতীয় স্তম্ভটিকে প্রতিষ্ঠা করা। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সব নাগরিকের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় হবে ‘নাগরিক’, কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারী নয়। আইন সবার জন্য সমান হবে। ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা বিশ্বাসের কারণে কাউকে কোনো বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না, আবার কাউকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিতও করা হবে না।
এর মানে হলো, সরকারি চাকরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বণ্টন বা আইনি প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার থাকবে। রাষ্ট্র একজন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা নাস্তিককে ভিন্ন ভিন্ন চোখে দেখবে না; দেখবে শুধুই ‘নাগরিক’ হিসেবে। এই সমতার নীতিই রাষ্ট্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারে পরিণত হওয়া থেকে আটকায়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সদস্যরা যে অধিকার ভোগ করবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন সদস্যও ঠিক একই অধিকার ভোগ করবে। এই নীতি ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেমন, কোনো রাষ্ট্রে যদি ব্লাসফেমি বা ধর্ম অবমাননার আইন থাকে, তবে সেটি ধর্মনিরপেক্ষতার সমতার নীতিকে সরাসরি লঙ্ঘন করে। কারণ এই ধরনের আইন সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকেই রক্ষা করে এবং সংখ্যালঘু বা ভিন্নমতাবলম্বীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করে। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হলো এমন একটি আইনি কাঠামো যেখানে কোনো বিশ্বাসের প্রতিই আইনগতভাবে বিশেষ আনুকূল্য দেখানো হবে না।
সম্পর্কিত কিন্তু ভিন্ন ধারণা: কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য
ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনাকে আরও স্পষ্ট করার জন্য এর সাথে সম্পর্কিত কিন্তু ভিন্ন কিছু ধারণার পার্থক্য বোঝা জরুরি। এই ধারণাগুলোকে প্রায়ই একসাথে গুলিয়ে ফেলা হয়, যা মূল আলোচনাকে বিপথে চালিত করে।
- ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষকরণ (Secularism vs. Secularization): যেমনটা আগে বলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম হলো একটি রাজনৈতিক আদর্শ বা মতাদর্শ (ideology)। এটি একটি প্রেসক্রিপশনের মতো, যা বলে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। অন্যদিকে, ধর্মনিরপেক্ষকরণ বা সেকুলারাইজেশন হলো একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া (socio-historical process)। এটি বর্ণনা করে যে, আধুনিকতার বিকাশের সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র (যেমন – বিজ্ঞান, শিক্ষা, আইন, অর্থনীতি) থেকে ধর্মের প্রভাব কীভাবে ধীরে ধীরে কমে আসছে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার (Max Weber) এই প্রক্রিয়াকে ‘বিশ্বের মোহমুক্তি’ (disenchantment of the world) বলে আখ্যায়িত করেছেন (Weber, 1946)। এই বিষয়টিকে একবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে গভীরভাবে দেখেছেন কানাডিয়ান দার্শনিক চার্লস টেইলর (Charles Taylor)। তাঁর বিশাল গ্রন্থ A Secular Age (2007)-এ তিনি দেখিয়েছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষকরণ মানে এই নয় যে মানুষ আর ধর্মে বিশ্বাস করে না। বরং এর মানে হলো, আমাদের বিশ্বাসের শর্তগুলোই বদলে গেছে। ৫০০ বছর আগে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা ছিল প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, বিশ্বাস না করাটাই ছিল ব্যতিক্রম। আর আজ, বিশ্বাস করাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকগুলো বিকল্পের মধ্যে একটি মাত্র, যা প্রতিনিয়ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সেক্যুলারিজম একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, আর সেকুলারাইজেশন একটি সামাজিক বাস্তবতা।
- ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম সহিষ্ণুতা (Secularism vs. Toleration): সহিষ্ণুতা (Toleration) মানে হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ বা ক্ষমতাবান গোষ্ঠী ভিন্ন বিশ্বাসকে সহ্য করা বা মেনে নেওয়া। এর মধ্যে এক ধরনের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা লুকিয়ে থাকে। ‘আমি তোমাকে সহ্য করছি’ – এই কথার মধ্যেই নিহিত থাকে যে, আমার ক্ষমতা আছে তোমাকে সহ্য না করার। এটি এক ধরনের দয়া বা করুণা, অধিকার নয়। দার্শনিক মাইকেল ওয়ালজারের (Michael Walzer) মতে, সহিষ্ণুতা প্রায়ই একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা, যা পরিস্থিতি বদলালে ক্ষমতাবান গোষ্ঠী তুলেও নিতে পারে (Walzer, 1997)। অন্যদিকে, ধর্মনিরপেক্ষতা সহিষ্ণুতার ধারণা থেকে এক ধাপ এগিয়ে। এটি কোনো গোষ্ঠীর দয়া বা করুণার ওপর নির্ভর করে না। এটি সব নাগরিককে সমান অধিকার দেয়, যা সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত। রাষ্ট্র এখানে কোনো ধর্মকে ‘সহ্য’ করে না, বরং সব ধর্মকে সমান সম্মান ও অধিকারের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেয়।
- ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম বহুত্ববাদ (Secularism vs. Pluralism): বহুত্ববাদ (Pluralism) হলো একটি সমাজের বাস্তবতা, যেখানে নানা ধরনের ধর্ম, সংস্কৃতি ও মতাদর্শের মানুষ একসাথে বসবাস করে। হার্ভার্ডের অধ্যাপক ডায়ানা এক (Diana Eck) plurality (বৈচিত্র্যের বাস্তবতা) এবং pluralism (সেই বৈচিত্র্যের সাথে সক্রিয় বোঝাপড়া)-এর মধ্যে একটি সুন্দর পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, বহুত্ববাদ কেবল বৈচিত্র্যকে স্বীকার করাই নয়, বরং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, বোঝাপড়া এবং সংলাপ তৈরি করার একটি সক্রিয় প্রচেষ্টা (Eck, 2006)। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সেই বহুত্ববাদী সমাজকে পরিচালনা করার একটি রাজনৈতিক কাঠামো বা অপারেটিং সিস্টেম। একটি সমাজ বহুত্ববাদী হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ নাও হতে পারে (যেমন – অটোমান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা ‘ম তুলেইল্লেত’ পাশাপাশি বাস করত, কিন্তু তারা সমান নাগরিক ছিল না)। আবার, একটি রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি করলেও সমাজে বহুত্ববাদের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকতে পারে। আদর্শগতভাবে, ধর্মনিরপেক্ষতা বহুত্ববাদকে রক্ষা এবং বিকশিত করতে সাহায্য করে।
সবচেয়ে বড় কিছু ভুল ধারণা
ধারণাটা যতটা সরল মনে হচ্ছে, বাস্তবে এর প্রয়োগ ততটা সরল নয়। আর এই জটিলতার কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে অনেক ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে, যা প্রায়ই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়ানো হয়।
- ভুল ধারণা ১: ধর্মনিরপেক্ষতা মানে নাস্তিকতা (Secularism is Atheism): এটা সম্ভবত সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল ধারণা। ধর্মনিরপেক্ষতা আর নাস্তিকতা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। নাস্তিকতা হলো ঈশ্বর বা কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস। এটা একটা ব্যক্তিগত দার্শনিক অবস্থান। অন্যদিকে, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, এটা রাষ্ট্র পরিচালনার একটা নীতি। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নাস্তিক হতে বলে না। বরং, এটি এমন একটি খেলার মাঠ তৈরি করে যেখানে আস্তিক, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী সবাই নিজের নিজের নিয়ম অনুযায়ী খেলতে পারে, যতক্ষণ না তারা অন্যের খেলায় বাধা সৃষ্টি করছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজীব ভার্গব (Rajeev Bhargava) যেমনটা বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে নির্মূল করতে চায় না, বরং ধর্মের সবচেয়ে খারাপ প্রকাশ – অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা – থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষা করতে চায় (Bhargava, 2011)।
- ভুল ধারণা ২: ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্ম বিরোধিতা (Secularism is Anti-Religion): অনেকেই মনে করেন, সেকুলার হওয়া মানে ধর্মকে ঘৃণা করা বা জনজীবন থেকে ধর্মকে পুরোপুরি মুছে ফেলা। এটাও ঠিক নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পরিসর থেকে উচ্ছেদ করতে চায় না। এটি শুধু চায় যে, ‘রাষ্ট্রীয়’ পরিসরটা যেন ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত থাকে। আপনি আপনার ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে বাঁচবেন, উৎসব করবেন, উপাসনালয়ে যাবেন – এতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু তখনই, যখন আপনি আপনার ধর্মীয় বিশ্বাসকে রাষ্ট্রের আইন বানাতে চাইবেন বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার কেড়ে নিতে চাইবেন। বরং বলা যেতে পারে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে রাজনীতির দূষণ থেকে বাঁচায়। যখন ধর্ম রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন প্রায়শই তার আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক সারবত্তা হারিয়ে যায়।
- ভুল ধারণা ৩: ধর্মনিরপেক্ষতা একটি পশ্চিমা বা বিজাতীয় ধারণা (Secularism is a Western Concept): এটা সত্যি যে, ‘সেক্যুলারিজম’ শব্দটি এবং এর আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ (লিখিত সংবিধান, বিচার বিভাগ) পশ্চিমের মাটিতেই জন্মেছে। কিন্তু এর মূল ভাবনা – অর্থাৎ পরধর্মসহিষ্ণুতা, বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের একসাথে বসবাস এবং শাসকের নিরপেক্ষতা – পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতাতেই বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে। প্রাচীন পারস্যের সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেটের (Cyrus the Great) সিলিন্ডার, সম্রাট অশোকের (Ashoka) শিলালিপি, বা সম্রাট আকবরের (Akbar) ‘সুলহ-ই-কুল’ (সকলের জন্য শান্তি) নীতিও ছিল এক ধরনের পরধর্মসহিষ্ণুতার প্রচেষ্টা। ভারতীয় উপমহাদেশের ভক্তি এবং সুফি আন্দোলনগুলোও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে এক ধরনের মানবিক এবং সমন্বয়বাদী চেতনার জন্ম দিয়েছিল, যা ধর্মনিরপেক্ষতার মূল স্পিরিটের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই ধারণাটিকে পুরোপুরি ‘পশ্চিমা’ বলে দাগিয়ে দেওয়াটা এক ধরনের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা। আধুনিক বিশ্বে এর প্রয়োগ প্রতিটি দেশ তার নিজের ইতিহাস, সংস্কৃতি আর প্রয়োজন অনুযায়ী করেছে, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখব।
সুতরাং, ধর্মনিরপেক্ষতা হলো রাষ্ট্র পরিচালনার একটি কাঠামো এবং দর্শন, যা ধর্মকে তার যথাযথ সম্মান দিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিসরে রেখে, রাষ্ট্রীয় পরিসরকে একটি সার্বজনীন, নিরপেক্ষ এবং সমতার জায়গায় পরিণত করতে চায়, যেখানে সব নাগরিকের পরিচয় ও অধিকার সমান। এটি ধর্মহীনতা নয়, বরং বহু-ধর্মীয় সমাজে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার শর্ত।
ইতিহাসের ধুলোপথ ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম
কোনো ধারণাই শূন্য থেকে জন্মায় না। প্রতিটি বড় ধারণার পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের রক্ত, ঘাম আর চোখের জলের ইতিহাস। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটিও এর ব্যতিক্রম নয়। যে সুন্দর শব্দগুলো আমরা আজ সহজে ব্যবহার করি – স্বাধীনতা, সমতা, নিরপেক্ষতা – সেগুলো অর্জন করতে মানব সভ্যতাকে কয়েক শতাব্দী ধরে ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এই ধারণার শিকড় খুঁজতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেইসব সময়ে, যখন মানুষের বিশ্বাসই হয়ে উঠেছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু, যখন ঈশ্বরের নামে মানুষের রক্তে মাটি ভিজে যেত, আর রাষ্ট্র ছিল সেই রক্তপাতের প্রধান আয়োজক। এটি মূলত ইউরোপীয় ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া এক আলোর শিখা।
প্রাক-আধুনিক প্রেক্ষাপট: ক্ষমতা আর বিশ্বাসের জটিল গাঁটছড়া
আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার জন্মের অনেক আগে থেকেই রাষ্ট্র (বা রাজা) এবং ধর্মের (বা পুরোহিত) মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে এক দীর্ঘ ও জটিল টানাপোড়েন চলে আসছিল। আজকের দিনে আমরা রাষ্ট্র এবং ধর্মকে দুটি আলাদা সত্তা হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত, কিন্তু প্রাচীন জগতে এ দুয়ের মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিভাজন ছিল না। বরং, ক্ষমতা এবং বিশ্বাস ছিল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাসকের ক্ষমতাকে বৈধতা দিত ধর্ম, আর ধর্ম তার প্রসার এবং আধিপত্য বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের শক্তির ওপর নির্ভর করত।
প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার দিকে তাকালে আমরা দেখি, ফারাও কেবল একজন শাসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন হোরাসের (Horus) পার্থিব রূপ এবং মৃত্যুর পর ওসাইরিস (Osiris)। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন জীবন্ত দেবতা। তাঁর শাসন ছিল ঐশ্বরিক আদেশেরই প্রতিফলন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়া মানে ছিল দেবতাদের বিরুদ্ধেই যাওয়া। মেসোপটেমীয় সভ্যতাতেও রাজার ক্ষমতা আসত দেবতাদের কাছ থেকে, রাজা ছিলেন দেবতাদের প্রধান পুরোহিত। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে এই ধারণাটি আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সম্রাট অগাস্টাসের (Augustus) সময় থেকে সম্রাটকে প্রায়ই দেবতার আসনে বসানো হতো এবং সম্রাটের উপাসনা (Imperial Cult) করা ছিল রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রতীক। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল, যা বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় সাম্রাজ্যকে একটি সাধারণ আনুগত্যের সূত্রে বাঁধতে সাহায্য করত। যারা এই উপাসনা করতে অস্বীকার করত, যেমন প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানরা বা রক্ষণশীল ইহুদিরা, তাদের ওপর নেমে আসত নির্মম নিপীড়ন। তাদের দেখা হতো রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে, কারণ তাদের ধর্মীয় আনুগত্য ছিল জাগতিক সম্রাটের ঊর্ধ্বে এক স্বর্গীয় সত্তার প্রতি।
খ্রিস্টধর্ম যখন চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট কন্সট্যান্টাইনের (Constantine) হাত ধরে প্রথমে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য এবং পরে ৩৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াসের (Theodosius) সময়ে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হলো, তখন দৃশ্যপট নাটকীয়ভাবে বদলে গেল। যে ধর্ম একসময় রাষ্ট্রের হাতে নির্যাতিত ছিল, সেই ধর্মই এখন রাষ্ট্রের ক্ষমতার অংশীদার হয়ে উঠল। চার্চ এবং সাম্রাজ্য একে অপরের ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ল। রাষ্ট্র তার তরবারি দিয়ে চার্চের শত্রুদের – যাদের ‘ধর্মদ্রোহী’ (heretic) বা ‘পেগান’ (pagan) বলা হতো – দমন করত, আর চার্চ তার ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব দিয়ে রাজার শাসনকে বৈধতা দিত। এই ব্যবস্থাকে অনেক সময় ‘সিজারোপেপিজম’ (Caesaropapism) বলা হয়, যেখানে জাগতিক শাসকই (সিজার) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেরও প্রধান (পোপ)। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে এই মডেলটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল, যেখানে সম্রাট চার্চের কাউন্সিল আহ্বান করতেন এবং ধর্মীয় মতবাদ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।
কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে ক্ষমতার ভারসাম্য ছিল ভিন্ন এবং অনেক বেশি জটিল। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়, তা পূরণ করতে এগিয়ে আসে রোমের বিশপ বা পোপের নেতৃত্বে থাকা ক্যাথলিক চার্চ। বিভিন্ন বর্বর উপজাতিদের হানাহানিতে যখন জাগতিক শাসন ভেঙে পড়ছিল, তখন চার্চই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষা, আইন এবং সংগঠনের একটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল। এর ফলে পোপ নিজেকে কেবল আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবেই নয়, জাগতিক বিষয়েও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দাবি করতে শুরু করেন। পোপ অষ্টম গ্রেগরির (Pope Gregory VIII) মতো শক্তিশালী পোপেরা ‘দুই তরবারির তত্ত্ব’ (Doctrine of the Two Swords) প্রচার করেন, যেখানে বলা হয় যে, ঈশ্বর পোপকে আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক – উভয় তরবারিরই ক্ষমতা দিয়েছেন। পোপ জাগতিক তরবারিটি সম্রাট বা রাজাকে ব্যবহার করার জন্য দেন, কিন্তু তার চূড়ান্ত মালিকানা পোপেরই থাকে (Tierney, 1964)।
এর ফলে পোপ এবং বিভিন্ন দেশের রাজাদের মধ্যে কে বড়, তা নিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত চলেছিল, যা ‘ইনভেস্টিচার বিতর্ক’ (Investiture Controversy) নামে পরিচিত। এই বিতর্কের মূল বিষয় ছিল – বিশপ বা উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকদের নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা কার থাকবে, পোপের নাকি রাজার (Berman, 1983)? এটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিক বিতর্ক ছিল না, এটি ছিল ক্ষমতার লড়াই। কারণ বিশপরা কেবল ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসক। তাই তাঁদের ওপর যার নিয়ন্ত্রণ থাকবে, রাজ্যের ক্ষমতার একটি বড় অংশ তারই হাতে থাকবে। পবিত্র রোমান সম্রাট চতুর্থ হেনরি (Henry IV) এবং পোপ সপ্তম গ্রেগরির (Pope Gregory VII) মধ্যেকার বিখ্যাত সংঘাত, যেখানে সম্রাটকে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য খালি পায়ে বরফের মধ্যে তিন দিন কানোসার দুর্গের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, এই ক্ষমতার লড়াইয়েরই চরম মুহূর্ত।
এই সংঘাতগুলোই প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র ও ধর্মের ক্ষমতাকে আলাদা করার চিন্তাটি বহু পুরনো। এটি ছিল ক্ষমতার লড়াই, আদর্শের নয়। কিন্তু এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই ইউরোপে দুটি স্বতন্ত্র ক্ষমতার কেন্দ্র – একটি জাগতিক (রাষ্ট্র, যাকে regnum বলা হতো) এবং অন্যটি আধ্যাত্মিক (চার্চ, যাকে sacerdotium বলা হতো) – এর ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করে, যা বিশ্বের অন্য অনেক সভ্যতায় অনুপস্থিত ছিল। এই দ্বৈত কর্তৃত্বের কাঠামোই পরবর্তীকালে ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার বিকাশের জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল। কারণ যেখানেই দুটি ক্ষমতার কেন্দ্র থাকে, সেখানেই তাদের সীমানা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং সেই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নেয় পৃথকীকরণের ধারণা।
ইউরোপের অন্ধকার: ধর্মের নামে রক্তগঙ্গা
ধর্মনিরপেক্ষতার আধুনিক ধারণার জন্মভূমি মূলত ইউরোপ। আর এর জন্মের প্রেক্ষাপট ছিল ভয়ঙ্কর, রক্তাক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী। এটি কোনো দার্শনিকের আরামকেদারায় বসে তৈরি হওয়া তত্ত্ব নয়, বরং এটি ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষা থেকে উঠে আসা এক যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধি। মধ্যযুগের শেষ দিকে এবং আধুনিক যুগের শুরুতে ইউরোপজুড়ে ধর্মের নামে যে পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে, তা কল্পনা করাও কঠিন। তখন ক্যাথলিক চার্চ এবং রাষ্ট্র ছিল একে অপরের সাথে এমনভাবে জড়িত যে, একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। পোপের কথাই ছিল আইন, যা জাগতিক শাসকের মাধ্যমে কার্যকর করা হতো। রাজার ক্ষমতাকে বৈধতা দিত চার্চ, আর রাজা তার সামরিক শক্তি দিয়ে চার্চের আধিপত্য বজায় রাখত, ধর্মদ্রোহীদের দমন করত এবং চার্চের সম্পদ রক্ষা করত। এই আঁতাত একটি শক্তিশালী নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা তৈরি করেছিল, যার পরিণতি ছিল ভয়াবহ।
যারা চার্চের বা তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় মতের সামান্যতম বিরোধিতা করত, তাদের ‘ধর্মদ্রোহী’ (Heretic) আখ্যা দেওয়া হতো। এই ধর্মদ্রোহীদের খুঁজে বের করে বিচার করার জন্য তৈরি হয়েছিল ইনকুইজিশন (Inquisition) নামক কুখ্যাত বিচারব্যবস্থা। ইনকুইজিশনের বিচার ছিল নিষ্ঠুর এবং একপেশে। অভিযুক্তকে প্রায়ই অত্যাচারের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায়ে বাধ্য করা হতো এবং তারপর হয় পুড়িয়ে মারা হতো, নয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হতো। জর্দানো ব্রুনোকে (Giordano Bruno) পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, কারণ তিনি বলেছিলেন মহাবিশ্ব অনন্ত এবং তার কোনো কেন্দ্র নেই, যা তৎকালীন ধর্মীয় মতবাদের পরিপন্থী ছিল। গ্যালিলিওর (Galileo Galilei) মতো বিজ্ঞানীকে সত্য বলার জন্য – অর্থাৎ, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, এই কথা বলার জন্য – গৃহবন্দী হতে হয়েছিল এবং চার্চের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়েছিল (Finocchiaro, 1989)। শুধু ভিন্নমতাবলম্বী খ্রিস্টানরাই নয়, ইহুদি এবং মুসলিমদেরও এই ব্যবস্থা থেকে হয় ধর্মান্তরিত হতে, নয়তো দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যেমনটা ঘটেছিল স্পেনের কুখ্যাত ইনকুইজিশনের সময়।
কিন্তু আসল বিপর্যয় নেমে আসে ষোড়শ শতকে প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের (Protestant Reformation) পর। ১৫১৭ সালে জার্মান ধর্মযাজক মার্টিন লুথার (Martin Luther) যখন ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি, বিশেষ করে ‘ইনডালজেন্স’ (indulgence) বা পাপমোচনপত্র বিক্রির বিরুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত ‘পঁচানব্বই থিসিস’ (Ninety-five Theses) প্রকাশ করেন, তখন তিনি নিজেও হয়তো কল্পনা করতে পারেননি যে কী ভয়ঙ্কর এক দাবানলের সূচনা তিনি করছেন। লুথারের হাত ধরে খ্রিস্টধর্ম যখন ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট – এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ হয়ে গেল, তখন ইউরোপজুড়ে শুরু হলো শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ধর্মীয় যুদ্ধ (Wars of Religion)। এই যুদ্ধগুলো কেবল ধর্মতত্ত্বের লড়াই ছিল না, এর সাথে জড়িয়ে ছিল রাজাদের ক্ষমতা দখলের লড়াই, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং জাতীয়তাবাদের উত্থান।
জার্মানির ‘ত্রিশ বছরের যুদ্ধ’ (Thirty Years’ War, 1618-1648) এর সবচেয়ে কুখ্যাত উদাহরণ। যা শুরু হয়েছিল বোহেমিয়ার প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে পবিত্র রোমান সম্রাটের সংঘাত দিয়ে, তা ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করে ফেলে। ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টদের এই লড়াইয়ে কেবল সৈন্যরাই মরেনি, মারা গিয়েছিল সাধারণ মানুষ – অগণিত, অসহায়। ভাড়াটে সৈন্যরা গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত, ফসল লুট করত, নারীদের ওপর অত্যাচার করত। এর ফলে যে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী দেখা দেয়, তাতে জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল কোনো কোনো অঞ্চলে। জার্মানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ – প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ – মারা গিয়েছিল এই যুদ্ধে (Wilson, 2009)। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস – সবখানেই চলছিল একই রকম হত্যা আর ধ্বংসের খেলা। ফ্রান্সে সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসের গণহত্যায় (St. Bartholomew’s Day Massacre, 1572) ক্যাথলিকদের হাতে এক রাতেই প্যারিসে এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে পুরো ফ্রান্সে হাজার হাজার প্রোটেস্ট্যান্টকে (যাদের হুগেনো বলা হতো) নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মানুষ তখন তিক্তভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করল যে, রাষ্ট্র যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় পক্ষ নেয়, তাহলে শান্তি অসম্ভব। যখন শাসকের ধর্ম আর প্রজাদের একাংশের ধর্ম ভিন্ন হয়, তখন সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।
এই যুদ্ধগুলোর অবসান ঘটে ১৬৪৮ সালের ‘ওয়েস্টফালিয়ার শান্তিচুক্তি’ (Peace of Westphalia) দিয়ে। এই চুক্তিটি ছিল এক ধরনের ক্লান্তিকর ঐকমত্য। সবাই বুঝতে পারছিল যে, যুদ্ধ করে কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারবে না। তাই সহাবস্থানের একটি উপায় খুঁজে বের করা জরুরি। এই চুক্তিটি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম দিয়েছিল এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিল: Cuius regio, eius religio অর্থাৎ, ‘শাসকের ধর্মই হবে রাজ্যের ধর্ম’। এর মানে হলো, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ভেতরের শত শত রাজ্যের শাসকরা নিজেদের রাজ্যের জন্য ক্যাথলিক, লুথারান বা ক্যালভিনিজমের মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়ার অধিকার পেয়েছিল।
এটা ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না, কারণ এটি শাসকের ধর্মকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার দিয়েছিল এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার ছিল খুবই সীমিত – তারা হয় শাসক নির্ধারিত ধর্ম গ্রহণ করত, নয়তো দেশত্যাগ করত। কিন্তু এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ধাপ। কারণ এটি স্বীকার করে নিয়েছিল যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের তার নিজের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় বিষয় নির্ধারণ করার অধিকার আছে, অন্য কোনো রাষ্ট্র বা পোপ সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এটি ছিল রাষ্ট্রকে চার্চের সার্বভৌম কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ, যা আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম দেয়। এই চুক্তি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, ধর্মীয় ঐক্য আর সম্ভব নয় এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ধর্মীয় বহুত্ববাদকে (যদিও খুব সীমিত আকারে) মেনে নিতেই হবে। এই রক্তাক্ত অভিজ্ঞতাই পরবর্তী যুগের দার্শনিকদের শিখিয়েছিল যে, শান্তি চাইলে রাষ্ট্রকে ধর্মের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে হবে।
জ্ঞানদীপ্তির আলো: নতুন চিন্তার উন্মোচন
এই রক্ত আর ধ্বংসের মধ্য থেকেই জন্ম নিল নতুন চিন্তা। শত শত বছরের ধর্মীয় যুদ্ধ ইউরোপের মানুষকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত এবং মোহমুক্ত করে দিয়েছিল। তারা বুঝতে শুরু করেছিল যে, পারলৌকিক মুক্তির আশায় ইহলৌকিক জীবনকে নরকে পরিণত করাটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে এক নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের জন্ম হয়, যাকে বলা হয় ‘জ্ঞানদীপ্তির যুগ’ (The Age of Enlightenment)। ইমানুয়েল কান্টের (Immanuel Kant) ভাষায়, জ্ঞানদীপ্তি ছিল মানুষের ‘স্ব-আরোপিত অপরিণত অবস্থা থেকে মুক্তি’ (release from his self-incurred tutelage) (Kant, 1784)। ভলতেয়ার (Voltaire), জন লক (John Locke), রুশো (Jean-Jacques Rousseau), মঁতেস্কু (Montesquieu), দেনি দিদেরোর (Denis Diderot) মতো দার্শনিকরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করলেন সেইসব প্রথা, বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, যা হাজার বছর ধরে স্বতঃসিদ্ধ বলে মানা হতো। তাঁরা বললেন, মানুষের মুক্তি কোনো ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশে বা অন্ধ বিশ্বাসে নয়, মানুষের মুক্তি তার নিজের যুক্তির ব্যবহারে। আর তাঁদের এই যুক্তির শাণিত তরবারির প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ও ধর্মের সেই অশুভ আঁতাত, যা ইউরোপকে রক্তাক্ত করেছিল।
- জন লক (John Locke): ইংরেজ দার্শনিক জন লককে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম আদি প্রবক্তা বলা হয়। ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ এবং গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution)-এর সাক্ষী হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অপরিহার্য। তাঁর লেখা যুগান্তকারী গ্রন্থ ‘A Letter Concerning Toleration’ (1689)-এ তিনি রাষ্ট্র এবং চার্চের কার্যক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ আলাদা করার এক সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করান। লকের মূল যুক্তিটি ছিল বিস্ময়কর রকমের সরল এবং শক্তিশালী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের কাজ হলো মানুষের ‘নাগরিক স্বার্থ’ (civil interests) রক্ষা করা, যার মধ্যে পড়ে জীবন, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি (Locke, 1689)। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কাজ হলো এই পৃথিবীতে আমাদের জাগতিক জীবনকে নিরাপদ রাখা। অন্যদিকে, আত্মার মুক্তি বা পারলৌকিক কল্যাণ হলো ধর্মের বিষয়। এই দুটিকে মেলানো যাবে না। কারণ, প্রথমত, ঈশ্বর কোনো শাসককে অন্যের আত্মার যত্ন নেওয়ার ক্ষমতা দেননি। এটি ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বাস কোনো জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। একজন মানুষকে তরবারির ভয় দেখিয়ে গির্জায় পাঠানো যেতে পারে, কিন্তু তার মনের ভেতরে সত্যিকারের বিশ্বাস তৈরি করা যায় না। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ধর্মবিশ্বাস আসলে ভণ্ডামির জন্ম দেয়, ধার্মিকতার নয়। তাই লকের মতে, রাষ্ট্রের উচিত সব ধর্মকে ‘সহ্য’ করা (tolerate), যতক্ষণ না তারা রাষ্ট্রের আইন ভাঙে বা অন্য নাগরিকদের ক্ষতি করে। যদিও লকের সহিষ্ণুতার একটি সীমা ছিল, তবুও তাঁর এই চিন্তাই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রথম স্পষ্ট তাত্ত্বিক রূপরেখা।
- ভলতেয়ার (Voltaire): ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামির সবচেয়ে কঠোর, অক্লান্ত এবং লড়াকু সমালোচক। তিনি কোনো গভীর দার্শনিক তত্ত্ব দেননি, কিন্তু তাঁর শ্লেষ, বিদ্রূপ আর ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে ক্যাথলিক চার্চের গোঁড়ামি আর অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে একাই একটি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ক্যালভিনবাদী জ্যাঁ ক্যালাস (Jean Calas) নামক একজন প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যক্তিকে যখন তাঁর ছেলেকে ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধা দেওয়ার জন্য হত্যার মিথ্যা অভিযোগে নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়, তখন ভলতেয়ার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা শুরু করেন। তিনি বছরের পর বছর ধরে লিখে, বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে তদবির করে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেন যে, ক্যালাস নির্দোষ ছিলেন এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন (Voltaire, 1763)। এই একটি ঘটনাই ইউরোপের বিবেককে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। ভলতেয়ারের যুক্তি ছিল মূলত প্রায়োগিক। তিনি দেখিয়েছিলেন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা কেবল অনৈতিকই নয়, এটি সমাজের জন্যও ক্ষতিকর। এটি বাণিজ্য, শিল্প এবং সামাজিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, “Ecrasez l’infâme!” (“Crush the infamous thing!”) – যার লক্ষ্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ামি – জ্ঞানদীপ্তির যুগের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।
- বারুখ স্পিনোজা (Baruch Spinoza): ডাচ দার্শনিক স্পিনোজা ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা এক চিন্তাবিদ। ইহুদি সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত এবং খ্রিস্টানদের দ্বারা সমালোচিত এই নিঃসঙ্গ দার্শনিক আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর Theologico-Political Treatise (1670) গ্রন্থে যুক্তি দেন যে, একটি স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের জন্য চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের কাজ হলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়। যদি রাষ্ট্র মানুষের চিন্তা বা বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তবে তা কেবল বিদ্রোহেরই জন্ম দেবে। স্পিনোজার মতে, গণতন্ত্রই হলো সবচেয়ে স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা, কারণ এটি মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সাথে সবচেয়ে বেশি সংগতিপূর্ণ। তিনিই প্রথম আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম যিনি গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি অবিচ্ছেদ্য প্যাকেজ হিসেবে দেখেছিলেন (Spinoza, 1670)।
- মঁতেস্কু (Montesquieu) এবং দিদেরো (Diderot): মঁতেস্কু তাঁর The Spirit of the Laws (1748) গ্রন্থে ক্ষমতার পৃথকীকরণের (separation of powers) যে ধারণা দেন, তা পরোক্ষভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিকেও শক্তিশালী করে। কারণ রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণও এক ধরনের ক্ষমতার পৃথকীকরণ। অন্যদিকে, দেনি দিদেরো (Denis Diderot) এবং তাঁর সঙ্গীরা মিলে যে বিশাল Encyclopédie সম্পাদনা করেছিলেন, তা ছিল জ্ঞানদীপ্তির যুগের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। এটি ছিল মানব জ্ঞানের এক বিশাল সংকলন, যা কোনো ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর না করে কেবল যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এটি ছিল জ্ঞানকে চার্চের হাত থেকে মুক্ত করার এক বিপ্লবী পদক্ষেপ।
এই দার্শনিকদের চিন্তাভাবনাগুলো ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এক নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক আবহ তৈরি করে। তাঁরা মানুষকে শেখান যে, রাষ্ট্র কোনো ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি মানুষের নিজেদের প্রয়োজনে তৈরি করা একটি চুক্তি। আর সেই রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার রক্ষা করা, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করা নয়। এই বিপ্লবী চিন্তাভাবনাগুলোই পরবর্তী দুটি বড় বিপ্লবের – আমেরিকান বিপ্লব এবং ফরাসি বিপ্লব – আদর্শগত ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল, যা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে তত্ত্ব থেকে বাস্তবে রূপ দেবে।
দুটি বিপ্লব, দুই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা
জ্ঞানদীপ্তির দার্শনিকরা যে আদর্শের বীজ বপন করেছিলেন, তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুটি বিশাল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চারাগাছ থেকে মহীরুহে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়: আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৬) এবং ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)। এই দুটি বিপ্লবই রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকারের কথা বলেছিল, আর সেই অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা। কিন্তু তাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হওয়ার কারণে তারা ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি ভিন্ন মডেলের জন্ম দিয়েছিল, যা আজও বিশ্বজুড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বিতর্ককে প্রভাবিত করে।
১. আমেরিকান বিপ্লব: বহুত্ববাদ রক্ষার জন্য বিচ্ছেদ
আমেরিকার জন্মই হয়েছিল ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে পিউরিটান, কোয়েকার, ব্যাপ্টিস্টদের মতো নানা ধর্মীয় গোষ্ঠী পালিয়ে এসে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিল, কারণ তারা নিজেদের দেশে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে পারছিল না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই গোষ্ঠীগুলো নিজেরা ক্ষমতায় এসে প্রায়ই অন্যদের ওপর নিজেদের ধর্মীয় মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। যেমন, ম্যাসাচুসেটসের পিউরিটানরা তাদের নিজস্ব কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর অত্যাচার চালাত। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতারা (Founding Fathers) যেমন – থমাস জেফারসন (Thomas Jefferson), জেমস ম্যাডিসন (James Madison) – শিখেছিলেন যে, কোনো একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দেওয়াটা কতটা বিপজ্জনক।
তাঁরা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান তৈরি করেন, তখন খুব সচেতনভাবেই রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা রাখেন। জেমস ম্যাডিসন (James Madison) তাঁর বিখ্যাত Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments (1785)-এ যুক্তি দেখান যে, ধর্ম হলো ব্যক্তির বিবেক এবং ঈশ্বরের মধ্যকার একটি বিষয়, যেখানে রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। তিনি বলেন, রাষ্ট্র যখন কোনো ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে, তখন তা ধর্মকে ‘দুর্নীতিগ্রস্ত’ করে এবং নাগরিকদের অধিকার হরণ করে (Madison, 1785)।
এই চিন্তারই প্রতিফলন ঘটে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে (First Amendment, 1791), যা বিল অফ রাইটসের অংশ। এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা রয়েছে, যা ‘Establishment Clause’ এবং ‘Free Exercise Clause’ নামে পরিচিত।
- Establishment Clause বলে, “কংগ্রেস কোনো ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে কোনো আইন তৈরি করবে না।” এর মানে হলো, রাষ্ট্র কোনো চার্চকে আর্থিক সাহায্য দিতে পারবে না, কোনো ধর্মীয় মতবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না, বা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করতে পারবে না।
- Free Exercise Clause বলে, রাষ্ট্র “ধর্মের অবাধ অনুশীলনকে নিষিদ্ধ করবে না।” এর মানে হলো, নাগরিকরা তাদের পছন্দমতো ধর্ম পালন বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।
থমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) এই দুটি ধারাকে একসাথে ব্যাখ্যা করতে গিয়েই তাঁর বিখ্যাত ‘গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর’ (a wall of separation between church and state) রূপকটি ব্যবহার করেন (Jefferson, 1802)। আমেরিকার মডেলটা ছিল মূলত দ্বিমুখী রক্ষার একটি প্রচেষ্টা: একদিকে রাষ্ট্রকে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর আধিপত্য থেকে বাঁচানো, এবং অন্যদিকে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচানো। এর লক্ষ্য ছিল এমন একটি ‘মুক্ত বাজার’ (free marketplace of ideas) তৈরি করা, যেখানে সব ধর্ম (এবং অধর্ম) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র থাকবে একজন নিরপেক্ষ রেফারি। এটি ছিল মূলত বহুত্ববাদকে (pluralism) রক্ষা করার একটি উপায়।
২. ফরাসি বিপ্লব: প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য বিচ্ছেদ
ফ্রান্সের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমেরিকায় যেখানে নানা ধরনের ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল এবং কোনো একটিরই একক আধিপত্য ছিল না, সেখানে ফ্রান্সে ছিল ক্যাথলিক চার্চের একচ্ছত্র এবং অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য। চার্চ ছিল রাজতন্ত্রের (Ancien Régime) প্রধান স্তম্ভ এবং বিশাল ক্ষমতার অধিকারী। এটি ছিল দেশের সবচেয়ে বড় ভূস্বামী, জনগণকে ‘টাইদ’ (tithe) নামক ধর্মীয় কর দিতে বাধ্য করত, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত, এবং জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের নিবন্ধন রাখত। চার্চ এবং রাজতন্ত্র ছিল একে অপরের সহযোগী, যারা একসাথে সাধারণ মানুষকে শোষণ করত।
তাই বিপ্লবীরা যখন ‘স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী’ (Liberté, égalité, fraternité) স্লোগান দিয়ে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করল, তখন তাদের লড়াইটা ছিল অনিবার্যভাবে চার্চের বিরুদ্ধেও। তারা চার্চকে কেবল একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেনি, দেখেছে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে, যা বিপ্লবের আদর্শের পরিপন্থী। তাই তারা কেবল রাষ্ট্র থেকে চার্চকে আলাদা করেই সন্তুষ্ট থাকেনি, তারা চেয়েছিল জনজীবন (public sphere) থেকেও ধর্মের প্রভাব পুরোপুরি মুছে ফেলতে।
বিপ্লবের সময় চার্চের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়, যাজকদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে বাধ্য করা হয় এবং এমনকি একটি নতুন, যুক্তিনির্ভর ‘কাল্ট অফ দ্য সুপ্রিম বিয়িং’ (Cult of the Supreme Being) তৈরি করারও চেষ্টা করা হয়। এই দীর্ঘ লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯০৫ সালের একটি আইনে, যা ফ্রান্সে রাষ্ট্র ও চার্চের আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ ঘটায়। এই ধারণাটিই ‘লাইসিতে’ (Laïcité) নামে পরিচিত।
ফরাসি মডেলটি আমেরিকান মডেলের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর এবং আক্রমণাত্মক। আমেরিকার লক্ষ্য যেখানে ছিল ধর্মকে ‘রক্ষা’ করা, সেখানে ফ্রান্সের লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রভাব থেকে ‘মুক্ত’ করা। এটি ধর্মকে কঠোরভাবে একটি ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখে এবং পাবলিক পরিসরকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখতে চায়। এর পেছনের যুক্তি হলো, প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসেবে সবার পরিচয় এক এবং অভিন্ন। ধর্মীয় পরিচয় এই সার্বজনীন নাগরিক পরিচয়কে বিভক্ত করতে পারে, তাই পাবলিক পরিসরে (যেমন – স্কুল, সরকারি অফিস) এর কোনো স্থান নেই। এই কারণেই ফ্রান্সে হিজাব বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতীক নিয়ে এত বিতর্ক দেখা যায়।
সুতরাং, আমেরিকান বিপ্লব জন্ম দিয়েছিল এমন এক ধর্মনিরপেক্ষতার, যা বহুত্ববাদকে ধারণ করতে চায়। আর ফরাসি বিপ্লব জন্ম দিয়েছিল এমন এক ধর্মনিরপেক্ষতার, যা জাতীয় ঐক্য এবং প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে রক্ষা করতে চায়। এই দুটি মডেলই পরবর্তী ২০০ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বিভিন্ন রূপকে প্রভাবিত করেছে।
‘সেক্যুলারিজম’ শব্দের জন্ম এবং ধারণার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ
এতক্ষণ আমরা যে ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম – রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা – সেগুলো সবই ছিল, কিন্তু সেগুলোকে ডাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট নাম ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে সেই শূন্যস্থানটি পূরণ হলো। শিল্প বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি, ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোড়নের মধ্যে এই ধারণাটি একটি আনুষ্ঠানিক নাম পেল: সেক্যুলারিজম।
এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ব্রিটিশ লেখক, বক্তা এবং সমাজ সংস্কারক জর্জ জ্যাকব হোলিওক (George Jacob Holyoake)। হোলিওক নিজে ছিলেন একজন অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) এবং রবার্ট ওয়েনের (Robert Owen) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি দেখছিলেন, তৎকালীন ব্রিটিশ সমাজে ধর্ম, বিশেষ করে চার্চ অফ ইংল্যান্ড, রাজনীতি এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। যারা চার্চের শিক্ষায় বিশ্বাস করত না, যেমন নাস্তিক বা ভিন্নমতাবলম্বীরা, তাদের সামাজিকভাবে একঘরে করে রাখা হতো এবং আইনিভাবেও নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। যেমন, আদালতে শপথ নেওয়ার জন্য বাইবেলে হাত রাখতে অস্বীকার করলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো না।
হোলিওক এমন একটি নৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার কথা ভাবছিলেন যা কোনো ধর্ম বা অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হবে না। তিনি এমন একটি ইতিবাচক মতাদর্শের সন্ধান করছিলেন যা নাস্তিকতার (atheism) নেতিবাচক এবং আক্রমণাত্মক চিত্র থেকে মুক্ত থাকবে। ১৮৫১ সালে তিনি প্রথম ‘Secularism’ শব্দটি ব্যবহার করেন এই নতুন জীবনদর্শনকে বোঝানোর জন্য (Holyoake, 1896)।
হোলিওকের সেক্যুলারিজমের মূল কথাগুলো ছিল:
- ইহজাগতিকতার ওপর গুরুত্ব: মানুষের উচিত এই জীবনের (this-worldly) উন্নতি এবং মঙ্গলের দিকে মনোযোগ দেওয়া, পরকালের অনিশ্চিত পুরস্কার বা শাস্তির দিকে নয়।
- বিজ্ঞান ও যুক্তির ব্যবহার: মানবজাতির সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের উচিত বিজ্ঞান, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করা, কোনো ধর্মগ্রন্থ বা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের ওপর নয়।
- মানবকল্যাণই নৈতিকতার ভিত্তি: কোনো কাজ ভালো না মন্দ, তার বিচার হবে সেই কাজটি মানবকল্যাণে কতটুকু অবদান রাখছে তার ওপর ভিত্তি করে, কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে নয়।
মজার ব্যাপার হলো, হোলিওকের সেক্যুলারিজম প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো নীতি ছিল না, বরং এটি ছিল একটি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নৈতিকতার কাঠামো। তিনি ধর্মকে সরাসরি আক্রমণ করার বদলে একটি বিকল্প প্রস্তাব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ধারণাটি দ্রুতই একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করে। চার্লস ব্র্যাডলর (Charles Bradlaugh) মতো আরও র্যাডিকাল চিন্তাবিদরা সেক্যুলারিজমের ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান এবং এটিকে পার্লামেন্ট থেকে চার্চের প্রভাব দূর করা, রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মমুক্ত করা এবং মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সাথে যুক্ত করেন। ব্র্যাডল একজন ঘোষিত নাস্তিক হওয়ায় পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়ার পরও তাঁকে দীর্ঘ ৫ বছর ধরে শপথ নিতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, যা ব্রিটেনে রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে এক বিশাল বিতর্কের জন্ম দেয় (Royle, 1980)।
সুতরাং, ‘সেক্যুলারিজম’ শব্দটি যখন জন্ম নিল, তখন এর দুটি অর্থ ছিল: একটি সংকীর্ণ অর্থে একটি জীবনদর্শন, এবং একটি বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্র ও সমাজকে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। কিন্তু ধীরে ধীরে শব্দটি তার প্রথম অর্থ থেকে সরে এসে দ্বিতীয় অর্থেই, অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নীতি হিসেবেই, বিশ্বজুড়ে বেশি পরিচিতি লাভ করে।
ইতিহাসের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমাই আমাদের বলে দেয়, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো আকাশ থেকে পড়া ধারণা নয়। এটি কোনো একক ব্যক্তি বা একক ঘটনার ফল নয়। এটি মানব সভ্যতার এক তিক্ত অভিজ্ঞতার ফসল। ধর্মের নামে হওয়া অকথ্য অত্যাচার, যুদ্ধ আর বিভেদ থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে শিখিয়েছে যে, রাষ্ট্রকে যদি সবার হতে হয়, তবে তাকে যেকোনো একটি ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এটি ছিল শত শত বছরের সংঘাত, বিতর্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত এক উপলব্ধি। এটি ছিল শান্তি, স্বাধীনতা এবং যুক্তির পথে মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত অপরিহার্য অভিযাত্রা।
একই বৃন্তে নানা ফুল – ধর্মনিরপেক্ষতার রকমফের
আমরা প্রায়ই ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটা মাত্রিক ধারণা হিসেবে দেখি – হয় একটি দেশ ধর্মনিরপেক্ষ, অথবা নয়। কিন্তু বাস্তবতা এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং রঙিন। ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো তৈরি পোশাক নয় যে এক মাপেই সবার গায়ে লেগে যাবে। এটি বরং দর্জির বানানো স্যুটের মতো, প্রতিটি দেশের জন্য তার নিজের ইতিহাস, সামাজিক গঠন এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে আলাদাভাবে তৈরি করতে হয়। পৃথিবীর সব দেশ একভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চা করে না। একেক দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার মডেল একেক রকম, ঠিক যেমন একই বাগানের ভিন্ন ভিন্ন গাছের যত্ন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিতে হয়। চলুন, বিশ্বের কয়েকটি প্রধান মডেলের দিকে তাকানো যাক এবং তাদের শক্তি ও দুর্বলতাগুলো বোঝার চেষ্টা করি।
১. ফরাসি মডেল: কঠোর বিচ্ছেদের ‘লাইসিতে’ (Laïcité)
ফরাসি মডেলটি ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে কঠোর, আপসহীন এবং সম্ভবত সবচেয়ে বিতর্কিত রূপ। ফরাসি বিপ্লবের সময়কার চার্চ-বিরোধী মনোভাব থেকে এর জন্ম এবং ১৯০৫ সালের ‘রাষ্ট্র ও গির্জার পৃথকীকরণ আইন’ (Law on the Separation of the Churches and the State) দ্বারা এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ‘লাইসিতে’ (Laïcité)-র মূল কথা হলো, পাবলিক বা রাষ্ট্রীয় পরিসরকে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা, কেবল পৃথক রাখা নয়।
বৈশিষ্ট্য:
- ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়: ধর্মকে কঠোরভাবে ব্যক্তিগত জীবনের অংশ (private sphere) বলে মনে করা হয়। পাবলিক স্পেসে (public sphere) এর কোনো প্রকাশ কাম্য নয়। রাষ্ট্র কেবল ধর্ম থেকে নিজেকে দূরেই রাখে না, বরং সক্রিয়ভাবে পাবলিক স্পেসকে ধর্মমুক্ত রাখে, যাতে একটি সার্বজনীন ‘নাগরিক পরিসর’ (civic space) তৈরি করা যায়।
- রাষ্ট্রীয় কঠোর নিরপেক্ষতা: রাষ্ট্র কেবল কোনো ধর্মের পক্ষই নেয় না, বরং নিজেকে ধর্ম সম্পর্কিত সব ধরনের প্রতীক ও প্রকাশ থেকে দূরে রাখে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে সবাই শুধুই ফ্রান্সের নাগরিক, তাদের ধর্মীয় পরিচয় সেখানে অদৃশ্য থাকবে, যা জাতীয় ঐক্যকে (indivisibilité) শক্তিশালী করবে।
- পাবলিক প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় প্রতীক নিষিদ্ধ: ২০০৪ সালের আইন অনুযায়ী, সরকারি স্কুলে কোনো ধরনের স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান (conspicuous) ধর্মীয় প্রতীক (যেমন – বড় ক্রস, হিজাব, কিপ্পা, পাগড়ি) পরা নিষিদ্ধ। ২০১০ সালে জনসমক্ষে মুখ ঢাকা বোরকা বা নিকাব পরাও নিষিদ্ধ করা হয়। এর পেছনের যুক্তি হলো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সবাই শুধুই ফ্রান্সের নাগরিক হিসেবে আসবে, যা প্রজাতন্ত্রের সাম্যের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে।
সমালোচনা:
এই মডেলের সবচেয়ে বড় সমালোচনা হলো, এটি অনেক সময় ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতাকে খর্ব করে। হিজাব বা পাগড়ি নিষিদ্ধ করার আইনগুলোকে অনেকেই ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন। সমালোচকরা বলেন, রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকতে গিয়ে কার্যত ধর্ম পালনের অধিকারে বাধা সৃষ্টি করছে এবং এক ধরনের সাংস্কৃতিক একরূপতা (cultural homogeneity) চাপিয়ে দিচ্ছে। দার্শনিক তালাল আসাদের (Talal Asad) মতে, ফরাসি ‘লাইসিতে’ আসলে একটি নির্দিষ্ট (খ্রিস্টান-পরবর্তী) সেকুলার সংস্কৃতিকে সবার ওপর চাপিয়ে দেয় এবং অন্য সংস্কৃতির প্রকাশকে, বিশেষ করে ইসলামের প্রকাশ্য রূপগুলোকে, দমন করে (Asad, 2003)। দার্শনিক মার্থা নুসবাউম (Martha Nussbaum) এই মডেলকে ‘স্বাধীনতার প্রতি অসম্মান’ হিসেবে দেখেছেন, কারণ এটি মানুষের পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে প্রকাশ করতে বাধা দেয় (Nussbaum, 2012)।
২. আমেরিকান মডেল: বন্ধুসুলভ বিচ্ছেদের প্রাচীর (Friendly Wall of Separation)
আমেরিকান মডেলটিও রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, কিন্তু এর প্রয়োগ ফরাসি মডেলের মতো কঠোর নয়। বরং একে ‘বন্ধুত্বপূর্ণ বিচ্ছেদ’ বা ‘সহনশীল ধর্মনিরপেক্ষতা’ (accommodative secularism) বলা যেতে পারে। এখানে রাষ্ট্র ও ধর্মকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা হয় না, বরং দুটি আলাদা জগৎ হিসেবে দেখা হয় যারা প্রয়োজনে একে অপরের সাথে আলোচনা করতে পারে।
বৈশিষ্ট্য:
- কোনো রাষ্ট্রধর্ম নেই: ফরাসি মডেলের মতোই, এখানেও কোনো রাষ্ট্রধর্ম নেই এবং রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে না, যা সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ে (যেমন, Everson v. Board of Education, 1947) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ধর্মের অবাধ অনুশীলন: রাষ্ট্র মানুষের ধর্ম পালনের স্বাধীনতায় সাধারণত হস্তক্ষেপ করে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে সহায়তা করে। পাবলিক স্পেসে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে কোনো বাধা নেই। একজন শিখ ছাত্র স্কুলে পাগড়ি পরে যেতে পারে, একজন মুসলিম নারী সরকারি অফিসে হিজাব পরে কাজ করতে পারে। রাষ্ট্র অনেক সময় ধর্মীয় দাতব্য সংস্থাগুলোকে সামাজিক কাজের জন্য অর্থও দিয়ে থাকে।
- জনজীবনে ধর্মের শক্তিশালী উপস্থিতি: আমেরিকার রাজনীতি ও সমাজজীবনে ধর্মের উপস্থিতি বেশ প্রকট। প্রেসিডেন্টকে বাইবেল হাতে শপথ নিতে দেখা যায়, টাকার নোটে লেখা থাকে ‘In God We Trust’, এবং কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয় প্রার্থনা দিয়ে। এখানে এক ধরনের ‘নাগরিক ধর্ম’ (Civil Religion) প্রচলিত আছে, যেমনটা রবার্ট বেলা (Robert Bellah) দেখিয়েছেন, যেখানে দেশের প্রতি আনুগত্যের সাথে একটি সাধারণ ধর্মীয় চেতনার মিশ্রণ ঘটানো হয় (Bellah, 1967)।
সমালোচনা:
এই মডেলের সমালোচনা হলো, ‘বিচ্ছেদের প্রাচীর’ এখানে প্রায়ই নড়বড়ে হয়ে যায়। রাজনীতিতে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর (বিশেষ করে ইভানজেলিকাল খ্রিস্টানদের) প্রভাব অত্যন্ত বেশি। গর্ভপাত, সমকামী বিয়ে বা স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ানোর মতো বিষয়গুলো প্রায়ই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এছাড়া, সামাজিক জীবনে ধর্মের এত বেশি উপস্থিতির কারণে যারা অধার্মিক বা সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী, তারা অনেক সময় এক ধরনের সামাজিক চাপের মুখে পড়েন এবং নিজেদের ‘আউটসাইডার’ হিসেবে অনুভব করেন।
৩. ভারতীয় মডেল: নীতিগত দূরত্বের ‘সর্বধর্ম সমভাব’ (Principled Distance)
ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মডেলটি পশ্চিমা মডেলগুলো থেকে বেশ আলাদা এবং এই অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজীব ভার্গব (Rajeev Bhargava) এই মডেলটিকে ‘নীতিগত দূরত্ব’ (Principled Distance) বলে আখ্যা দিয়েছেন (Bhargava, 2011)।
বৈশিষ্ট্য:
- রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, কিন্তু কঠোর বিচ্ছিন্নতা নয়: ভারতীয় রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পক্ষ নেয় না, কিন্তু প্রয়োজনে যেকোনো ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এটি পশ্চিমা মডেলের ‘কঠোর বিচ্ছেদ’-এর ধারণা থেকে সরে আসে।
- ইতিবাচক ও নেতিবাচক হস্তক্ষেপ: রাষ্ট্র একদিকে যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য করতে পারে (ইতিবাচক হস্তক্ষেপ), তেমনি ধর্মের নামে চলা কোনো কুপ্রথা (যেমন – অস্পৃশ্যতা, তিন তালাক) বন্ধ করার জন্য আইনও পাস করতে পারে (নেতিবাচক হস্তক্ষেপ)। শাহ বানো মামলা বা মন্দিরে দলিতদের প্রবেশাধিকারের মতো ঘটনাগুলো এর উদাহরণ।
- লক্ষ্য: এর মূল লক্ষ্য শুধু বিভিন্ন ধর্মকে আলাদা রাখা নয়, বরং তাদের মধ্যে এবং তাদের ভেতরেও সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্র এখানে শুধু একজন নিরপেক্ষ রেফারি নয়, প্রয়োজনে সে একজন সক্রিয় কোচও বটে।
সমালোচনা:
এই মডেলের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো এর প্রয়োগ। ‘নীতিগত দূরত্ব’ কখন, কোথায় এবং কতটা হবে, তা প্রায়ই রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করে। এর ফলে কখনও কখনও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে ‘সংখ্যালঘু তোষণ’ (minority appeasement) বলে মনে করা হয়। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই ভারতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থান ঘটেছে, যা এই মডেলের অস্তিত্বকেই সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে।
৪. তুর্কি মডেল: রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বা আক্রমণাত্মক ধর্মনিরপেক্ষতা (Assertive Secularism)
তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতার মডেলটিও বেশ স্বকীয় এবং এটি ফরাসি মডেলের একটি চরম রূপ। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক (Mustafa Kemal Atatürk) যখন ১৯২৩ সালে আধুনিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি একটি কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করেন।
বৈশিষ্ট্য:
- টপ-ডাউন বা উপর থেকে চাপানো: এটি ছিল জনগণের ভেতর থেকে গড়ে ওঠা কোনো ব্যবস্থা নয়, বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভিজাত শ্রেণী দ্বারা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি আদর্শ।
- ধর্মের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ: রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। দিয়ানাত (Diyanet) বা ধর্ম বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে দেশের সমস্ত মসজিদের ইমামদের বেতন দেওয়া এবং তাদের খুৎবা নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়।
- প্রতীকী ও সামাজিক সংস্কার: আরবি হরফের বদলে ল্যাটিন হরফ চালু করা, হিজাব ও ফেজ টুপি জনসমক্ষে নিষিদ্ধ করা, পশ্চিমা পোশাক ও আইন গ্রহণ করা – এরকম নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাজকে জোর করে ‘আধুনিক’ করার চেষ্টা করা হয়।
সমালোচনা:
কামালিস্ট সেক্যুলারিজমকে অনেকেই স্বৈরাচারী এবং গণবিরোধী বলে মনে করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় তুরস্কে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান ঘটে এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের (Erdoğan) অধীনে তুরস্ক এই কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ মডেল থেকে অনেকটাই সরে এসেছে।
৫. ব্রিটিশ মডেল: প্রতিষ্ঠা সহ ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism with an Established Church)
এটি একটি প্যারাডক্সিক্যাল মডেল। ব্রিটেনে রাষ্ট্রপ্রধান (রাজা বা রানী) একই সাথে চার্চ অফ ইংল্যান্ডেরও প্রধান। লর্ড সভায় ২৬ জন বিশপের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। অর্থাৎ, এখানে রাষ্ট্র ও ধর্মের আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ নেই। তা সত্ত্বেও, ব্রিটেন বাস্তবে একটি বহুত্ববাদী ও কার্যকরী ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র হিসেবেই পরিচালিত হয়। আইন সবার জন্য সমান এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত। এটি দেখায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদই একমাত্র পথ নয়, বরং একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোও নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে।
এই বিভিন্ন মডেল থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার – ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো একক, সার্বভৌম (universal) সংজ্ঞা নেই। প্রতিটি সমাজ তার নিজের ঐতিহাসিক ক্ষত, সামাজিক বাস্তবতা এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এর রূপ নির্ধারণ করে।
ধর্মনিরপেক্ষতা কেন দরকার? আধুনিক রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ
একবিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীতেও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কেউ বলেন, এটি একটি সেকেলে পশ্চিমা ধারণা যা আমাদের সমাজের জন্য উপযুক্ত নয়। কেউ বলেন, ধর্মই যেখানে সমাজের নৈতিকতার মূল ভিত্তি, সেখানে রাষ্ট্র ধর্ম থেকে দূরে থাকবে কেন? এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেবল একটি ভালো আদর্শ হিসেবে না দেখে, এর প্রয়োজনীয়তাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যাক, যা প্রমাণ করে এটি কোনো রাজনৈতিক বিলাসিতা নয়, বরং একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক এবং বহুত্ববাদী সমাজের অপরিহার্য শর্ত এবং রক্ষাকবচ।
শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং বহুত্ববাদের সুরক্ষার জন্য
আধুনিক বিশ্বের প্রায় কোনো দেশই একটি মাত্র ধর্ম, সংস্কৃতি বা একটি মাত্র জাতির মানুষ নিয়ে গঠিত নয়। বিশ্বায়ন, অভিবাসন এবং ঐতিহাসিক নানা কারণে প্রায় প্রতিটি দেশেই বহু ধর্ম, বহু ভাষা এবং বহু সংস্কৃতির মানুষের বসবাস। এই বৈচিত্র্যই একটি দেশের সৌন্দর্য এবং শক্তি, কিন্তু একই সাথে এটি সংঘাতের একটি সম্ভাব্য উৎসও বটে। যখন রাষ্ট্র কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে বা তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়, তখন অন্য ধর্মাবলম্বীরা স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। তাদের মনে নিরাপত্তাহীনতা, বঞ্চনা এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়। এই অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং অবশেষে সংঘাত। ইতিহাস সাক্ষী, যেখানেই রাষ্ট্র কোনো একটি ধর্মের পক্ষ নিয়েছে, সেখানেই সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে এবং গৃহযুদ্ধ বা দাঙ্গা লেগেছে। মধ্যযুগের ইউরোপের ধর্মীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে যুগোস্লাভিয়ার ভাঙন, রুয়ান্ডার গণহত্যা, বা নিকট অতীতে মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন – এর প্রত্যেকটির পেছনেই ছিল রাষ্ট্রীয় মদতে চলা ধর্মীয় বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের রাজনীতি।
ধর্মনিরপেক্ষতা এই সংঘাত এড়ানোর একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক উপায়। যখন রাষ্ট্র ঘোষণা করে যে, সে সব ধর্মের থেকে সমান দূরত্বে থাকবে এবং সব নাগরিককে সমান চোখে দেখবে, তখন বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের আস্থা তৈরি হয়। তারা রাষ্ট্রকে নিজের প্রতিপক্ষ না ভেবে নিজেদের রক্ষাকর্তা হিসেবে ভাবতে শেখে। এটি একটি বহু-ধর্মীয় সমাজে আঠার মতো কাজ করে, যা সবাইকে একসাথে ধরে রাখে। এটি বহুত্ববাদকে (pluralism) কেবল সহ্যই করে না, তাকে উদযাপন করার একটি পরিবেশ তৈরি করে। ধর্মনিরপেক্ষতা বলে, দেশের প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য সবাইকে একই রকম বিশ্বাসী বা একই রকম সংস্কৃতির হতে হবে না। ভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা এক হতে পারি, কারণ আমাদের একতার ভিত্তি কোনো ধর্মীয় পরিচয় নয়, বরং একটি সাধারণ নাগরিক পরিচয়।
সংখ্যালঘু, ভিন্নমতাবলম্বী এবং অধার্মিকদের সুরক্ষার জন্য
যেকোনো সমাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বা সংস্কৃতির একটি স্বাভাবিক আধাপত্য থাকে। রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষ না হয়, তবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মই রাষ্ট্রের ধর্মে পরিণত হয় এবং তাদের বিশ্বাস, রীতিনীতি, উৎসবগুলোই রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এর ফলে সংখ্যালঘুরা শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবেই কোণঠাসা হয় না, সাংস্কৃতিকভাবেও অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করে।
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়। এটি নিশ্চিত করে যে, সংখ্যালঘুরা তাদের নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ভাষা চর্চা করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। রাষ্ট্র তাদের উপাসনালয় রক্ষা করবে, তাদের উৎসব পালনে সহায়তা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণকে আইনগতভাবে প্রতিহত করবে। শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘু নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী বা যারা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে না, তাদের অধিকারও রক্ষা করে। ধর্মরাষ্ট্রে প্রায় সবসময়ই ধর্মত্যাগ (apostasy) বা ধর্মদ্রোহিতাকে (blasphemy) ভয়ঙ্কর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর শাস্তি হয় কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মানুষের ‘বিশ্বাস না করার অধিকার’ (right to not believe) বা ‘ধর্ম পরিবর্তনের অধিকার’কে (right to convert) মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এটিই হলো প্রকৃত চিন্তার স্বাধীনতা, যা কেবল কী বিশ্বাস করতে হবে তা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাই দেয় না, বরং কী বিশ্বাস করতে হবে না, সেটাও বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়।
ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিসর প্রসারিত করার জন্য
ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে না, এটি রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ককেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। ধর্মরাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে – কী খাবে, কী পরবে, কার সাথে মিশবে, কীভাবে চিন্তা করবে – তার ওপর ধর্মীয় আইন চাপিয়ে দিতে চায়। সেখানে ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ, বিবেক বা যুক্তির কোনো স্থান থাকে না। ব্যক্তিকে সেখানে রাষ্ট্রের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ একটি সত্তা হিসেবে দেখা হয়।
ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তিকে এই ধর্মীয় অনুশাসনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দেয়। এটি বলে, তোমার আধ্যাত্মিক বা নৈতিক সিদ্ধান্ত তুমি নিজে নেবে। রাষ্ট্র তোমার অভিভাবক নয় যে সে তোমাকে পরকালের পথ বাতলে দেবে। রাষ্ট্রের কাজ তোমাকে ইহকালে একটি নিরাপদ, স্বাধীন এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ করে দেওয়া। দার্শনিক অমর্ত্য সেন (Amartya Sen) যেমনটা দেখিয়েছেন, মানুষের উন্নয়ন ও সক্ষমতা (capability) বিকাশের জন্য তার ‘বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা’ (freedom to choose) অত্যন্ত জরুরি (Sen, 1999)। ধর্মনিরপেক্ষতা সেই বেছে নেওয়ার পরিসরকে প্রসারিত করে। এটি ব্যক্তিকে তার নিজের জীবনের কর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং তাকে তার নিজস্ব ভালো-মন্দের ধারণা (conception of the good) অনুযায়ী জীবনযাপন করার সুযোগ দেয়, যতক্ষণ না তা অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে।
গণতন্ত্র এবং সার্বজনীন নাগরিকত্বের বিকাশের জন্য
গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো নাগরিকের ধারণা – যেখানে প্রতিটি মানুষের পরিচয় ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সমান। ধর্মরাষ্ট্র এই ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ সেখানে নাগরিকের অধিকার তার ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যেমন, একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম নাগরিক কখনওই রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন না, বা একজন ইহুদি রাষ্ট্রে একজন অ-ইহুদি পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা পান না। এটি গণতন্ত্রের মূলনীতি – সকলের সমানাধিকারকে লঙ্ঘন করে।
ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিকত্বের এই সার্বভৌম ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে। এখানে সবার অধিকার ও কর্তব্য সমান, কারণ সবাই প্রথমত এবং শেষ পর্যন্ত দেশের নাগরিক। এটি মানুষকে তার ধর্মীয় পরিচয়ের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বের করে একটি বৃহত্তর, জাতীয় পরিচয়ের অংশ হতে সাহায্য করে। দার্শনিক জন রলসের (John Rawls) ‘পাবলিক রিজন’ (Public Reason) তত্ত্বানুযায়ী, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে আইন ও নীতি এমন যুক্তির ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত যা সকল নাগরিক, তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস নির্বিশেষে, গ্রহণ করতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষতা এই পাবলিক রিজনের চর্চার জন্য অপরিহার্য (Rawls, 1997)। এটি নিশ্চিত করে যে, পাবলিক পলিসির বিতর্কগুলো সাধারণ যুক্তির ভিত্তিতে হবে, কোনো নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নয়।
বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং নৈতিক অগ্রগতির জন্য
ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, যখনই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সামাজিক সংস্কারের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, তখনই সমাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কোপার্নিকাস (Copernicus) বা গ্যালিলিওর (Galileo Galilei) ওপর চার্চের খড়্গহস্ত হওয়ার ঘটনা এর ক্লাসিক উদাহরণ। মধ্যযুগে ইসলামী বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে থাকলেও, পরবর্তীকালে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রসারের ফলে সেই অগ্রগতি থেমে যায়।
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র জ্ঞানচর্চা এবং আইন প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থকে না মেনে যুক্তি, বিজ্ঞান এবং মানবকল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে বিজ্ঞান গবেষণা, শিল্প-সাহিত্য এবং সামাজিক সংস্কারের পথ খুলে যায়। যেসব বিষয় – যেমন, নারী অধিকার, লিঙ্গ সমতা, এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায়ের অধিকার, চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার (যেমন, স্টেম সেল গবেষণা) – ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারত, সেগুলো একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোতে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। এটি সমাজকে সময়ের সাথে সাথে নিজেকে পরিবর্তন ও উন্নত করার সুযোগ করে দেয়। এটি সমাজকে শেখায় যে, নৈতিকতার উৎস কেবল ধর্ম নয়, মানবতাবাদ, যুক্তি এবং সহানুভূতিও হতে পারে।
সুতরাং, ধর্মনিরপেক্ষতা কেবল একটি রাজনৈতিক বিলাসিতা নয়, এটি একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক এবং বহুত্ববাদী (pluralistic) সমাজের অপরিহার্য শর্ত। এটি শান্তি, স্বাধীনতা এবং অগ্রগতির একটি অন্যতম প্রধান রক্ষাকবচ। এটি একটি প্রতিশ্রুতি, যা রাষ্ট্র তার সব নাগরিককে দেয়: তুমি যেই হও না কেন, যা-ই বিশ্বাস করো না কেন, এই দেশ তোমারও।
সমালোচনার আয়নায় ধর্মনিরপেক্ষতা – চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা
ধর্মনিরপেক্ষতা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ আদর্শ, কিন্তু এর পথচলা মোটেও মসৃণ নয়। পৃথিবীর কোনো দেশেই এটি নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। এর ধারণা এবং প্রয়োগ নিয়ে প্রচুর সমালোচনা ও বিতর্ক রয়েছে, যা কেবল এর বিরোধীদের কাছ থেকেই আসে না, এর সমর্থকদের মধ্য থেকেও আসে। একটি আদর্শের শক্তি বোঝা যায় তার সীমাবদ্ধতাগুলোকে বোঝার মাধ্যমেই। তাই একজন সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসু পাঠক হিসেবে আমাদের এই সমালোচনাগুলোকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।
- ‘রাষ্ট্র কি সত্যিই নিরপেক্ষ হতে পারে?’ – নিরপেক্ষতার মিথ: ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো রাষ্ট্রের সত্যিকারের নিরপেক্ষতা অর্জন করা। সমালোচকরা প্রশ্ন তোলেন, রাষ্ট্র কি আদৌ তার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারে? রাষ্ট্র কোনো শূন্যস্থানে কাজ করে না, এটি একটি নির্দিষ্ট ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যেই গড়ে ওঠে।উদাহরণস্বরূপ, প্রায় সব পশ্চিমা দেশেই রোববার সাপ্তাহিক ছুটি এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ক্যালেন্ডারে বড়দিন বা ইস্টারের মতো উৎসবগুলোই প্রধান ছুটি হিসেবে থাকে, যা খ্রিস্টান ধর্মের একটি ঐতিহ্য। একইভাবে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে শুক্রবারে ছুটি বা ঈদ প্রধান উৎসব হিসেবে পালিত হয়। এই বিষয়গুলো হয়তো ছোটখাটো মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলো প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র কাগজে-কলমে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও তার কাঠামো, প্রতীক এবং অভ্যাসের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের একটি প্রচ্ছন্ন, অলিখিত প্রভাব থেকেই যায়। নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ (Talal Asad) তাঁর যুগান্তকারী বই Formations of the Secular (2003)-এ দেখিয়েছেন যে, সেক্যুলারিজম নিজেও একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক (মূলত পশ্চিমা খ্রিস্টান) প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসেছে এবং এটি মোটেও কোনো নিরপেক্ষ বা সার্বভৌম ধারণা নয়। তাঁর মতে, সেক্যুলারিজম আসলে ধর্মকে ‘ব্যক্তিগত বিশ্বাস’ হিসেবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে এক নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থা তৈরি করে, যা মানুষের জীবনকে ভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা একটি মিথ বা ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।
- ‘ধর্মনিরপেক্ষতা কি ধর্মকে দুর্বল করে এবং নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়?’: অনেক রক্ষণশীল চিন্তাবিদরা মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে জনজীবন থেকে নির্বাসিত করে ব্যক্তিগত পরিসরে বন্দী করে ফেলে। এর ফলে ধর্মের সামাজিক এবং নৈতিক ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা যুক্তি দেখান যে, ধর্মকে যখন পাবলিক স্পেস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এর জায়গা নেয় লাগামছাড়া ভোগবাদ (consumerism) এবং বস্তুবাদ (materialism), যা সমাজের জন্য আরও বেশি ক্ষতিকর। জার্মান দার্শনিক ইয়ুর্গেন হাবেরমাস (Jürgen Habermas) তাঁর পরবর্তী জীবনে ‘পোস্ট-সেকুলার’ (post-secular) সমাজের ধারণা দিয়েছেন, যেখানে তিনি সেকুলার সমাজের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত নৈতিক অন্তর্দৃষ্টিগুলোকে পুরোপুরি বর্জন না করে পাবলিক ডিসকোর্সে অন্তর্ভুক্ত করার পথ খোঁজে (Habermas, 2006)।
- ‘সংখ্যালঘুদের তোষণের অভিযোগ’ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের বিচ্ছিন্নতাবোধ: বিশেষ করে ভারত বা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ হলো, এটি প্রায়ই ‘সংখ্যালঘু তোষণ’ (minority appeasement)-এ পরিণত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের আশায় সংখ্যালঘুদের বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ ও বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম হয়। এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার আদায়ের নামে সাম্প্রদায়িক ও রক্ষণশীল রাজনীতির উত্থান ঘটে, যা ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়।
- ‘পশ্চিমা মডেল কি সব দেশের জন্য প্রযোজ্য?’ – উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচনা (Post-colonial Critique): উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাবিদদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা একটি পশ্চিমা ধারণা যা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশগুলোতে চাপিয়ে দিয়েছিল। চিন্তাবিদ আশিস নন্দীর (Ashis Nandy) মতো সমালোচকরা যুক্তি দেখান যে, উপনিবেশ-পূর্ব ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহাবস্থানের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং পদ্ধতি ছিল। আধুনিক, পশ্চিমা ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেই ঐতিহ্যবাহী সহনশীলতাকে ধ্বংস করে দিয়ে ধর্মকে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করেছে (Nandy, 1998)।
- নারীবাদী সমালোচনা (Feminist Critique): ধর্মনিরপেক্ষতা কি সবসময় নারীর মুক্তি নিশ্চিত করে? উত্তরটি জটিল। অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো সামাজিক স্থিতিশীলতার নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পিতৃতান্ত্রিক নেতাদের সাথে আপস করে এবং তাদের ব্যক্তিগত আইন (personal law) টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে, যা নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক। যেমন, ভারতের শাহ বানো মামলা এর একটি ক্লাসিক উদাহরণ। শাহ বানো নামক একজন মুসলিম নারী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশ পাওয়ার জন্য আদালতে মামলা জেতেন। কিন্তু মুসলিম রক্ষণশীল নেতাদের চাপে পড়ে তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষ সরকার পার্লামেন্টে আইন পাস করে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বাতিল করে দেয় (Jeffery, 1988)। এটি দেখায়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রায়ই নারীর অধিকারের চেয়ে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নেতাদের সন্তুষ্ট রাখাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আবার, ফ্রান্সের মতো কঠোর ধর্মনিরপেক্ষ দেশে হিজাব নিষিদ্ধ করার আইনকে অনেক নারীবাদী মুসলিম নারীদের এজেন্সি বা আত্ম-সিদ্ধান্তের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র এখানে নারীর মুক্তির নামে আসলে তাদের পোশাকের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে, যা এক নতুন ধরনের পিতৃতন্ত্র।
- ‘ধর্মনিরপেক্ষতা কি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রুখতে পেরেছে?’ – প্রয়োগের ব্যর্থতা: সমালোচকরা প্রায়ই ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোতে ঘটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদাহরণ টেনে বলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। যেমন, ভারত সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ১৯৮৪ সালের শিখ-বিরোধী দাঙ্গা, ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার মতো ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর উত্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তারা বলেন, দাঙ্গাগুলো ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের কারণে হয় না, বরং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগুলোকে ঠিকভাবে প্রয়োগ না করার কারণে বা রাজনৈতিক স্বার্থে রাষ্ট্র নিজেই যখন সেগুলোকে লঙ্ঘন করে, তখন হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই তাত্ত্বিক পার্থক্য অনেক সময় পৌঁছায় না। তারা যখন দেখে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানোর পরও তাদের জীবন, সম্পত্তি বা উপাসনালয় নিরাপদ নয়, তখন তারা এই আদর্শের ওপর থেকেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।
সুতরাং, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো জাদুকরী সমাধান নয় যা প্রয়োগ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এটি একটি আদর্শ, যা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম, আলোচনা এবং আত্ম-সমালোচনার প্রয়োজন। এর চ্যালেঞ্জগুলো বাস্তব এবং সেগুলোকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বরং এই সীমাবদ্ধতাগুলোকে স্বীকার করে নিয়েই কীভাবে একটি অপেক্ষাকৃত ভালো এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করা যায়, সেটাই মূল প্রশ্ন।
বাংলাদেশ ও ধর্মনিরপেক্ষতা – এক জটিল ও অমীমাংসিত অধ্যায়
ধর্মনিরপেক্ষতার এই বৈশ্বিক আলোচনার পর এবার আমাদের নিজেদের দিকে তাকানোর পালা। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম, বিকাশ এবং বর্তমান পরিচয়ের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এই সম্পর্কটি কখনোই সরলরৈখিক ছিল না। এটি বারবার হোঁচট খেয়েছে, পথ পরিবর্তন করেছে এবং আজও একটি অমীমাংসিত বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে। এটি একটি স্বপ্নের জন্ম এবং সেই স্বপ্নভঙ্গের এক জটিল কাহিনী।
জন্মের প্রতিশ্রুতি: বাহাত্তরের অসাম্প্রদায়িক স্বপ্ন
১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে বাঙালিরা তিক্তভাবে উপলব্ধি করেছিল যে, ধর্মের মিল থাকা সত্ত্বেও জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা চলতে পারে। ‘ইসলাম বিপন্ন’ – এই স্লোগান ব্যবহার করে পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমন করেছে, ভাষার দাবিকে অস্বীকার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে এক ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়েছে।
এই অভিজ্ঞতার কারণেই নবগঠিত বাংলাদেশের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’-কে গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক এবং প্রত্যাশিত। এটি ছিল পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট আদর্শিক অবস্থান। ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন গণপরিষদে বলেছিলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এর মানে হলো রাষ্ট্রের চোখে সব ধর্ম সমান এবং রাজনীতিকে ধর্ম থেকে মুক্ত রাখা হবে।
সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনার কথা বলা হয়:
- সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বিলোপ করা হবে।
- রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দেবে না।
- রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার করা যাবে না।
- কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার ওপর নিপীড়ন করা যাবে না।
বাহাত্তরের সংবিধানের এই ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল মূলত রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে এবং রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করার একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা। এর লক্ষ্য ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে নাগরিকের একমাত্র পরিচয় হবে সে বাংলাদেশি এবং বাঙালি, হিন্দু বা মুসলিম নয়।
পথচ্যুতি: আদর্শের ওপর সংশোধনীর খড়্গ
কিন্তু এই আদর্শ বেশিদিন অক্ষত থাকেনি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে উল্টোযাত্রা শুরু হয়, তার প্রথম বড় আঘাতটি আসে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং সামরিক শাসনের আগমন বাংলাদেশের আদর্শিক গতিপথকে বদলে দেয়।
- পঞ্চম সংশোধনী (Fifth Amendment): ১৯৭৫ সালের পর সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে নিজের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার এবং ডানপন্থী ও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে কাছে টানার জন্য সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি কার্যত বাতিল করে দেন। সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি তুলে দিয়ে তার বদলে ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ স্থাপন করা হয়। এটি ছিল বাহাত্তরের সংবিধানের চেতনা থেকে একটি সুস্পষ্ট পশ্চাদপসরণ এবং রাষ্ট্রকে পুনরায় ধর্মীয় পরিচয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ।
- অষ্টম সংশোধনী (Eighth Amendment): আরেক সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময়ে ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে ‘রাষ্ট্রধর্ম’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবেই রাষ্ট্রকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত করে দেওয়া হলো, যা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই পদক্ষেপের পেছনেও ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য – ইসলামপন্থী দলগুলোকে সন্তুষ্ট রাখা এবং নিজের শাসনের পক্ষে একটি ধর্মীয় বৈধতা তৈরি করা।
ফিরে আসার চেষ্টা এবং এক অদ্ভুত সাংবিধানিক সমীকরণ
দীর্ঘ সময় পর, ২০১০ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত, সুপ্রিম কোর্ট, একটি ঐতিহাসিক রায়ে পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। এর ফলে বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিগুলো, যার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাও ছিল, পুনঃস্থাপিত হওয়ার একটি সুযোগ তৈরি হয়।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর (Fifteenth Amendment) মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আবার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু এখানে একটি অদ্ভুত এবং স্ববিরোধী কাজ করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাকে ফিরিয়ে আনা হলেও, সংবিধানে আগে থেকে যুক্ত হওয়া ‘বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম’ এবং ‘রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম’ – এ দুটি বিষয়কেও রেখে দেওয়া হয়। এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয় যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকলেও অন্যান্য ধর্মও সমান মর্যাদায় পালিত হবে।
এর ফলে বাংলাদেশের সংবিধানে এক ধরনের অদ্ভুত সমীকরণ তৈরি হয়েছে, যা বিশ্বের আর কোনো দেশের সংবিধানে হয়তো দেখা যায় না। একদিকে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, আবার অন্যদিকে রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ধর্মও আছে। এই স্ববিরোধিতা নিয়ে আজও আইনজ্ঞ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে বিতর্ক চলছে। সমালোচকরা বলেন, এটি একটি রাজনৈতিক আপসকামিতা, যা কোনো সুস্পষ্ট আদর্শিক অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি রাষ্ট্র একই সাথে ধর্মনিরপেক্ষ এবং কোনো একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি অনুগত হতে পারে না। এটি একটি আদর্শিক গোলকধাঁধা, যা রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে একটি স্থায়ী ধোঁয়াশা তৈরি করে রেখেছে। অধ্যাপক আলী রীয়াজ (Ali Riaz) এই পরিস্থিতিকে ‘এক ধরনের সাংবিধানিক জগাখিচুড়ি’ বলে অভিহিত করেছেন, যা রাষ্ট্রের দিকনির্দেশনাকে অস্পষ্ট করে তোলে (Riaz, 2013)।
বাস্তবতার জমিন: আদর্শ ও প্রয়োগের যোজন যোজন ফারাক
সংবিধানে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, একটি দেশের আসল চরিত্র বোঝা যায় তার সমাজ এবং রাজনীতির দিকে তাকালে। বাংলাদেশের বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থা কেমন?
- রাজনীতিতে ধর্মের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার: ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হলেও, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ হয়নি, বরং বেড়েছে। প্রায় সব বড় রাজনৈতিক দলই ভোটের জন্য ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সাথে আপস করা এবং তাদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। হেফাজতে ইসলামের মতো সংগঠনের উত্থান এবং তাদের দাবির মুখে পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা এর অন্যতম বড় উদাহরণ।
- সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতা: বাস্তবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য) প্রায়ই নানা ধরনের বৈষম্য, সহিংসতা এবং নিরাপত্তাহীনতার শিকার হন। তাদের জমি দখল, উপাসনালয়ে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর এবং নির্বাচনের পর সহিংসতার মতো ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দিতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। রামু, নাসিরনগর বা নড়াইলের ঘটনাগুলো এই বেদনাদায়ক বাস্তবতারই চিত্র।
- মত প্রকাশের স্বাধীনতার সংকোচন: ধর্মনিরপেক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মুক্তচিন্তা এবং ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা। কিন্তু বাংলাদেশে মুক্তচিন্তার চর্চা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। ব্লগার, লেখক, প্রকাশক এবং অ্যাক্টিভিস্টদের হত্যা বা তাদের ওপর হামলা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো আইনের মাধ্যমে ভিন্নমতকে দমনের চেষ্টা একটি অসহিষ্ণু পরিবেশ তৈরি করেছে, যা ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনার পরিপন্থী।
- শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকীকরণ: শিক্ষাব্যবস্থায়, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকে, প্রায়ই এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং অন্য ধর্মাবলম্বী বা অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষের জন্য সংবেদনশীল। এটি নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করছে।
সুতরাং, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার যাত্রা একটি জটিল এবং কাঁটাভরা পথের গল্প। এটি আদর্শের সাথে বাস্তবতার, প্রতিশ্রুতির সাথে প্রয়োগের এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে সীমাবদ্ধতার এক নিরন্তর দ্বন্দ্বের ইতিহাস। বাহাত্তরের সংবিধানে যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল, সেই স্বপ্ন আর বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে দূরত্বটা আজ অনেক বেশি, যা এক গভীর আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম দেয়।
ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ: নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
একবিংশ শতাব্দীতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি এক নতুন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে যেমন এটি বিশ্বজুড়ে বহু দেশের সাংবিধানিক আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত, তেমনি অন্যদিকে এটি নতুন এবং জটিল কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, যা এর ভবিষ্যৎ রূপ নির্ধারণ করে দেবে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর অনেকেই ভেবেছিলেন, উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং তার সঙ্গী হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে ভিন্ন। ধর্মনিরপেক্ষতা আজ ভেতর এবং বাহির – দুই দিক থেকেই আক্রান্ত। চলুন, এর কিছু প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখা যাক।
বিশ্বায়ন, অভিবাসন এবং বহু-সাংস্কৃতিকতার সংকট
বিশ্বায়নের ফলে মানুষ, পুঁজি এবং সংস্কৃতির চলাচল অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে। এর ফলে পশ্চিমা দেশগুলো, যারা নিজেদের ঐতিহাসিকভাবে এক-ধর্মীয় (খ্রিস্টান) এবং এক-সাংস্কৃতিক সমাজ হিসেবে দেখত, তারা এখন উল্লেখযোগ্য মুসলিম, হিন্দু বা বৌদ্ধ জনসংখ্যার আবাসস্থল। এই নতুন বাস্তবতা তাদের বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষতার মডেলগুলোকে এক কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলছে। ফ্রান্সের হিজাব বিতর্ক, জার্মানির মসজিদের মিনার নির্মাণের বিতর্ক, বা সুইজারল্যান্ডে গণভোটে বোরকা নিষিদ্ধ করার মতো ঘটনাগুলো এরই প্রতিফলন।
এই ঘটনাগুলো একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছে: ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কি সংখ্যাগরিষ্ঠের সাংস্কৃতিক মানদণ্ড সংখ্যালঘুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? ফরাসি ‘লাইসিতে’ যখন হিজাবকে পাবলিক স্কুল থেকে নিষিদ্ধ করে, তখন কি এটি সত্যিই নিরপেক্ষ থাকছে, নাকি এটি একটি নির্দিষ্ট, সেকুলার-খ্রিস্টান সাংস্কৃতিক বোধকে সার্বজনীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে? কানাডিয়ান দার্শনিক উইল কিমলিকার (Will Kymlicka) মতো বহু-সাংস্কৃতিকতাবাদের প্রবক্তারা যুক্তি দেখান যে, সত্যিকারের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয়কে ধারণ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (accommodation) গ্রহণ করতে হবে (Kymlicka, 1995)। প্রশ্ন উঠছে, একটি সত্যিকারের বহু-সাংস্কৃতিক ধর্মনিরপেক্ষতা কি সম্ভব, যা সব সংস্কৃতিকে সমান সম্মান দেবে এবং কোনো একটিকে আদর্শ হিসেবে দেখবে না? এই প্রশ্নের উত্তরই পশ্চিমা দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।
ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ও পপুলিজমের উত্থান
একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বজুড়ে ডানপন্থী, পপুলিস্ট এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থান। আর এই নতুন জাতীয়তাবাদের একটি বড় অংশই হলো ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ (Religious Nationalism)। ভারতের হিন্দুত্ববাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদ, তুরস্কের রাজনৈতিক ইসলাম, রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের সাথে রাষ্ট্রের গাঁটছড়া, বা মায়ানমারের বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ – এগুলো সবই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে সরাসরি আক্রমণ করছে।
এই মতাদর্শগুলো জাতীয় পরিচয়কে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সাথে এক করে দেখে এবং সংখ্যালঘু ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ‘অন্য’ বা ‘বহিরাগত’ হিসেবে চিত্রিত করে। এই পপুলিস্ট নেতারা গণতন্ত্রের কাঠামো ব্যবহার করেই ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে (যেমন – বিচার বিভাগ, গণমাধ্যম, শিক্ষা) ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছেন। তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় আসছেন এবং তারপর সংবিধান পরিবর্তন করে, আইন বদলে এবং ভিন্নমতকে দমন করে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। এটি ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি, কারণ এটি আদর্শটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে এবং তার জায়গায় একটি বিভেদকামী, অসহিষ্ণু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
ডিজিটাল যুগ এবং পরিচয়ের রাজনীতি
ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া একদিকে যেমন মুক্তচিন্তা এবং ভিন্নমত প্রকাশের নতুন দরজা খুলে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে এটি সাম্প্রদায়িক ঘৃণা এবং ভুয়া খবর ছড়ানোর এক শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। অনলাইন ইকো-চেম্বার এবং অ্যালগরিদম মানুষকে সমমনা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলছে, যা ভিন্নমত ও ভিন্ন পরিচয়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা বাড়াচ্ছে। পরিচয়ের রাজনীতি (identity politics) আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, এবং প্রায়শই সেই পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে ধর্ম।
এই ডিজিটাল যুগে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া, গুজব ছড়ানো এবং দাঙ্গা বাধানো অনেক সহজ হয়ে গেছে। একটি ভুয়া ফেসবুক পোস্ট বা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ থেকেই একটি পুরো এলাকা জ্বলে উঠতে পারে। রাষ্ট্র এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো প্রায়ই এই ডিজিটাল ঘৃণার স্রোতকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ – যেমন সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, এবং যুক্তিনির্ভর আলোচনা – বজায় রাখা আরও বেশি কঠিন এবং জটিল হয়ে পড়েছে।
পোস্ট-সেকুলার সমাজের ধারণা এবং সংলাপের সম্ভাবনা
এইসব চ্যালেঞ্জের বিপরীতে কিছু নতুন সম্ভাবনাও উঁকি দিচ্ছে। অনেক চিন্তাবিদ এখন মনে করছেন যে, ক্লাসিক্যাল সেকুলারাইজেশনের তত্ত্ব – অর্থাৎ, আধুনিকতার সাথে সাথে ধর্ম সমাজ থেকে হারিয়ে যাবে – ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ধর্ম হারিয়ে যায়নি, বরং এটি নতুন এবং শক্তিশালী রূপে জনজীবনে ফিরে এসেছে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েই জার্মান দার্শনিক ইয়ুর্গেন হাবেরমাসের (Jürgen Habermas) মতো চিন্তাবিদরা ‘পোস্ট-সেকুলার’ (post-secular) সমাজের ধারণার কথা বলছেন (Habermas, 2006)।
পোস্ট-সেকুলার সমাজের ধারণাটি স্বীকার করে যে, আধুনিক সমাজে ধার্মিক এবং অধার্মিক নাগরিকদের একসাথে বসবাস করতে এবং একে অপরের কাছ থেকে শিখতে হবে। তাই কঠোর বিচ্ছেদের বদলে সেকুলার এবং ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে একটি গঠনমূলক সংলাপের প্রয়োজন। এই মডেল অনুযায়ী, ধার্মিক নাগরিকরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উৎসারিত নৈতিক যুক্তি পাবলিক পরিসরে আনতে পারেন, তবে শর্ত হলো, সেই যুক্তিগুলোকে তাদের এমনভাবে ‘অনুবাদ’ করতে হবে যা অধার্মিক নাগরিকরাও বুঝতে এবং গ্রহণ করতে পারে। এটি ধর্মনিরপেক্ষতার একটি নমনীয়, সংলাপ-ভিত্তিক এবং পারস্পরিক শিক্ষণীয় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়, যা কঠোর বিচ্ছেদ বা ধর্ম-বিরোধিতার মডেল থেকে সরে আসে।
ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আমরা কীভাবে মোকাবেলা করব তার ওপর। এটি কোনো স্থির আদর্শ নয়, বরং একটি চলমান প্রকল্প যা প্রতিটি প্রজন্মকে নতুন করে বুঝে নিতে হয় এবং তার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। একদিকে যেমন ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বিপদ বাড়ছে, তেমনি অন্যদিকে বহু-সাংস্কৃতিকতা এবং পোস্ট-সেকুলার সংলাপের নতুন দিগন্তও উন্মোচিত হচ্ছে। এই দুই বিপরীত শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যেই নির্ধারিত হবে একবিংশ শতাব্দীতে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাগ্য।
আদর্শের স্থপতিগণ – যেসব চিন্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ধর্মনিরপেক্ষতা
আদর্শের দালান তো আর শূন্যে ঝুলে থাকে না, তার জন্য দরকার হয় স্থপতি। এমন কিছু মানুষ, যাঁরা ইট-পাথরের বদলে শব্দ, যুক্তি আর দর্শন দিয়ে সেই দালানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটিও এমনি এমনি জন্মায়নি। এর পেছনে রয়েছে বহু দার্শনিকের বছরের পর বছর ধরে চালানো চিন্তার লড়াই, সমাজের ক্ষতগুলোকে বোঝার চেষ্টা এবং একটি উন্নততর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার সাহস। এই অংশে আমরা সেইসব স্থপতিদের কয়েকজনের সাথে পরিচিত হব, যাঁদের চিন্তার ছাঁচে ঢলেই ধর্মনিরপেক্ষতার আজকের রূপটি তৈরি হয়েছে। এঁদের কেউ রাষ্ট্র আর ধর্মকে আলাদা করার প্রথম নকশা এঁকেছেন, কেউ সেই নকশাকে আরও মজবুত করেছেন, আবার কেউ বা সেই দালানের দুর্বলতাগুলোকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।
১. জন লক (John Locke): সহিষ্ণুতার প্রথম প্রবক্তা
ধর্মনিরপেক্ষতার আধুনিক ধারণার গোড়াপত্তন যদি কাউকে দিয়ে করতে হয়, তবে তিনি হলেন ইংরেজ দার্শনিক জন লক (John Locke)। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের ধর্মীয় সংঘাত আর রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে বাস করে তিনি তিক্তভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, রাষ্ট্র যদি মানুষের আত্মার মুক্তি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে, তবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন অসম্ভব। তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ ‘A Letter Concerning Toleration’ (1689)-এ তিনি রাষ্ট্র এবং চার্চের কার্যক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ আলাদা করার এক সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করান।
লকের মূল যুক্তিটি ছিল বিস্ময়কর রকমের সরল এবং শক্তিশালী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের কাজ হলো মানুষের ‘নাগরিক স্বার্থ’ (civil interests) রক্ষা করা। এই নাগরিক স্বার্থের মধ্যে পড়ে জীবন, স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য এবং সম্পত্তি (Locke, 1689)। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কাজ হলো এই পৃথিবীতে আমাদের জাগতিক জীবনকে নিরাপদ রাখা। অন্যদিকে, আত্মার মুক্তি বা পারলৌকিক কল্যাণ হলো ধর্মের বিষয়। এই দুটিকে মেলানো যাবে না। কারণ, প্রথমত, ঈশ্বর কোনো শাসককে অন্যের আত্মার যত্ন নেওয়ার ক্ষমতা দেননি। এটি ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্বাস কোনো জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। একজন মানুষকে তরবারির ভয় দেখিয়ে গির্জায় পাঠানো যেতে পারে, কিন্তু তার মনের ভেতরে সত্যিকারের বিশ্বাস তৈরি করা যায় না। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ধর্মবিশ্বাস আসলে ভণ্ডামির জন্ম দেয়, ধার্মিকতার নয়।
তাই লকের মতে, রাষ্ট্রের উচিত সব ধর্মকে ‘সহ্য’ করা (tolerate), যতক্ষণ না তারা রাষ্ট্রের আইন ভাঙে বা অন্য নাগরিকদের ক্ষতি করে। তবে লকের এই সহিষ্ণুতারও একটি সীমা ছিল। তিনি ক্যাথলিকদের এই সুবিধার বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর মতে তারা পোপের প্রতি অনুগত, তাই তারা রাষ্ট্রের প্রতি পুরোপুরি অনুগত হতে পারে না। আর নাস্তিকদেরও তিনি অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন, কারণ তাঁর মতে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাদের দিয়ে কোনো শপথ বা চুক্তি করানো যায় না, যা সমাজের ভিত্তি। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, লকের এই চিন্তাই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রথম স্পষ্ট তাত্ত্বিক রূপরেখা, যা পরবর্তীকালে আমেরিকান এবং ফরাসি বিপ্লবকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।
২. ভলতেয়ার (Voltaire): যুক্তির শাণিত তরবারি
ফ্রান্সের জ্ঞানদীপ্তির যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং লড়াকু কণ্ঠস্বর ছিলেন ভলতেয়ার (Voltaire)। তিনি কোনো গভীর দার্শনিক তত্ত্ব দেননি, কিন্তু তাঁর শ্লেষ, বিদ্রূপ আর ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে ক্যাথলিক চার্চের গোঁড়ামি আর অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে একাই একটি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর কাছে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু, যা যুক্তিকে হত্যা করে এবং মানুষকে অন্ধ বানিয়ে রাখে।
ভলতেয়ারের ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল তাঁর এক্টিভিজম বা সক্রিয়তাবাদ। জ্যাঁ ক্যালাস (Jean Calas) নামক একজন প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যক্তিকে যখন তাঁর ছেলেকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তখন ভলতেয়ার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা শুরু করেন। তিনি বছরের পর বছর ধরে লিখে, বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে তদবির করে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেন যে, ক্যালাস নির্দোষ ছিলেন এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন (Voltaire, 1763)। এই একটি ঘটনাই ইউরোপের বিবেককে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল।
ভলতেয়ারের যুক্তি ছিল মূলত প্রায়োগিক। তিনি দেখিয়েছিলেন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা কেবল অনৈতিকই নয়, এটি সমাজের জন্যও ক্ষতিকর। এটি বাণিজ্য, শিল্প এবং সামাজিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি ইংল্যান্ডের উদাহরণ দিয়ে বলতেন, সেখানে যেখানে শত শত ধর্মবিশ্বাস একসাথে শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, সেখানেই দেশের উন্নতি হচ্ছে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, “Ecrasez l’infâme!” (“Crush the infamous thing!”) – যার লক্ষ্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ামি – জ্ঞানদীপ্তির যুগের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।
৩. কার্ল মার্ক্স (Karl Marx): ধর্মনিরপেক্ষতার র্যাডিকাল সমালোচনা
ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখেছিলেন জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)। তাঁর কাছে রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোনো চূড়ান্ত সমাধান ছিল না, বরং এটি ছিল একটি অসম্পূর্ণ বিপ্লব। মার্ক্সের বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘On the Jewish Question’ (1844)-এ তিনি দেখান যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মানুষকে ‘রাজনৈতিকভাবে’ মুক্তি দেয়, কিন্তু ‘মানবিকভাবে’ মুক্তি দেয় না।
তাঁর যুক্তিটি ছিল এমন: একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একজন নাগরিক পাবলিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে একজন সমান নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু তার ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে সে তখনও ধর্ম, সম্পত্তি বা শ্রেণীর দ্বারা বিভক্ত এবং শোষিত থাকে। রাষ্ট্র তাকে রাজনৈতিকভাবে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে, কিন্তু সমাজ থেকে ধর্মের যে মূল কারণ – অর্থাৎ জাগতিক জীবনের দুঃখ, কষ্ট এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation) – তা দূর করে না। ধর্ম হলো এই দুঃখের প্রকাশ এবং একই সাথে তার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। মার্ক্সের সেই বিখ্যাত উক্তিটি এখানেই প্রাসঙ্গিক: “ধর্ম হলো নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়, এবং আত্মাহীন পরিস্থিতির আত্মা। এটি জনগণের আফিম।” (Marx, 1844)।
মার্ক্সের মতে, আফিম যেমন মানুষের কষ্টকে ভুলিয়ে রাখে কিন্তু কষ্টের কারণকে দূর করে না, ধর্মও তেমনি। তাই শুধু রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করলেই হবে না, সত্যিকারের মুক্তির জন্য এমন একটি সমাজ তৈরি করতে হবে যেখানে কোনো শোষণ থাকবে না, কোনো বিচ্ছিন্নতাবোধ থাকবে না, এবং যেখানে মানুষের আর ধর্মের মতো কোনো ‘আফিম’-এর প্রয়োজন হবে না। মার্ক্সের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল বুর্জোয়া সমাজের একটি ধাপ মাত্র, মানবমুক্তির শেষ কথা নয়।
৪. এমিল ডুর্খাইম (Émile Durkheim): ধর্মের সামাজিক ভূমিকা এবং ‘সিভিল রিলিজিয়ন’
ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খাইম (Émile Durkheim) ধর্মকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখেছিলেন। মার্ক্সের মতো তিনি ধর্মকে কেবল শোষণ বা আফিম হিসেবে দেখেননি। তাঁর মতে, ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সামাজিক সংহতি (social solidarity) তৈরি করা। তাঁর ক্লাসিক গ্রন্থ The Elementary Forms of the Religious Life (1912)-এ তিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের টোটেম প্রথার উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে এক ধরনের ‘সম্মিলিত উচ্ছ্বাস’ (collective effervescence) তৈরি হয়, এবং তারা একটি নৈতিক সম্প্রদায় (moral community) হিসেবে নিজেদের অনুভব করে। মানুষ আসলে ঈশ্বরের উপাসনা করে না, তারা আসলে নিজেদের সমাজেরই উপাসনা করে।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ধর্মনিরপেক্ষতার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো: ধর্ম যদি সমাজকে একসাথে বেঁধে রাখার আঠা হয়, তবে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে সেই কাজটি কে করবে? ডুর্খাইমের উত্তর ছিল, রাষ্ট্রকে নিজেই নতুন ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ বা ‘নাগরিক ধর্ম’ (Civil Religion) তৈরি করতে হবে। এই নাগরিক ধর্মে কোনো ঈশ্বর বা পরকাল থাকবে না, কিন্তু তার নিজস্ব পবিত্র প্রতীক (যেমন – জাতীয় পতাকা), পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান (যেমন – জাতীয় দিবস পালন) এবং নৈতিক অনুশাসন (যেমন – দেশের প্রতি আনুগত্য, নাগরিক কর্তব্য) থাকবে, যা বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষকে একটি একক জাতীয় পরিচয়ে বাঁধবে (Durkheim, 1912)। ফ্রান্সের ‘লাইসিতে’ মডেল, যেখানে পাবলিক স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা প্রজাতন্ত্রের মূল্যবোধ শেখানোর ওপর জোর দেওয়া হয়, তা ডুর্খাইমের এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি।
৫. জন রলস (John Rawls): পাবলিক রিজন এবং ওভারল্যাপিং কনসেনসাস
বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দার্শনিক জন রলস (John Rawls) ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে এক নতুন তাত্ত্বিক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তাঁর Political Liberalism (1993) গ্রন্থে তিনি প্রশ্ন তোলেন, একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে মানুষ নানা ধরনের পরস্পরবিরোধী ধর্মীয়, দার্শনিক এবং নৈতিক মতবাদে (যাকে তিনি ‘comprehensive doctrines’ বলেছেন) বিশ্বাস করে, সেখানে কীভাবে একটি স্থিতিশীল এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করা সম্ভব?
রলসের উত্তর হলো ‘পাবলিক রিজন’ (Public Reason) এবং ‘ওভারল্যাপিং কনসেনসাস’ (Overlapping Consensus)-এর ধারণা। তাঁর মতে, পাবলিক পরিসরে, বিশেষ করে যখন আমরা মৌলিক সাংবিধানিক বিষয় বা ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি, তখন আমাদের নিজেদের সংকীর্ণ ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে যুক্তি দেওয়া উচিত নয়। বরং আমাদের এমন যুক্তি ব্যবহার করা উচিত যা অন্য সব যুক্তিবাদী নাগরিক, তাদের বিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, গ্রহণ করতে পারে। এটাই হলো পাবলিক রিজন। যেমন, ‘চুরি করা অন্যায় কারণ আমার ধর্মগ্রন্থে এটা নিষিদ্ধ’ – এটি একটি ব্যক্তিগত যুক্তি। কিন্তু ‘চুরি করা অন্যায় কারণ এটি অন্যের সম্পত্তির অধিকার হরণ করে এবং সামাজিক আস্থাকে নষ্ট করে’ – এটি একটি পাবলিক রিজন, যা একজন আস্তিক, নাস্তিক সবাই বুঝতে পারে।
একটি ন্যায্য সমাজ তখনই সম্ভব যখন বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মানুষ তাদের নিজেদের কারণে (কেউ ধর্মীয় কারণে, কেউ দার্শনিক কারণে) রাষ্ট্রের মূল নীতিগুলোর প্রতি একমত হয়। এই বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যে সাধারণ সম্মতিটুকু তৈরি হয়, তাকেই রলস বলছেন ‘ওভারল্যাপিং কনসেনসাস’ (Overlapping Consensus) (Rawls, 1993)। রলসের এই তত্ত্ব আধুনিক বহু-সাংস্কৃতিক সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার একটি অত্যন্ত পরিশীলিত এবং সহনশীল রূপরেখা প্রদান করে, যা কঠোর বিচ্ছেদের মডেল বা ধর্ম-বিরোধী মডেল থেকে সরে এসে সংলাপ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর জোর দেয়।
৬. তালাল আসাদ (Talal Asad): ধর্মনিরপেক্ষতার উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচনা
সাম্প্রতিককালে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে সবচেয়ে গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ (Talal Asad)। তিনি তাঁর প্রভাবশালী গ্রন্থ Formations of the Secular (2003)-এ যুক্তি দেখান যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মোটেও কোনো নিরপেক্ষ বা সার্বভৌম ধারণা নয়, যেমনটা দাবি করা হয়। বরং এটি নিজেই একটি নির্দিষ্ট পশ্চিমা, খ্রিস্টীয় ইতিহাস থেকে উদ্ভূত একটি আধুনিক শাসন-প্রকল্প।
আসাদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে ধ্বংস করে না, বরং তাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ধর্মকে ‘বিশ্বাস’ (belief) নামক একটি ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরিণত করে এবং তার সামাজিক, আইনি বা রাজনৈতিক প্রকাশকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এই বিভাজনটি (পাবলিক বনাম প্রাইভেট, আইন বনাম নৈতিকতা, রাজনীতি বনাম ধর্ম) খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস থেকে এসেছে এবং এটি ইসলামী বা অন্যান্য ঐতিহ্যের জন্য স্বাভাবিক নয়, যেখানে ধর্ম একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা।
আসাদ দেখান যে, সেকুলার রাষ্ট্র নিরপেক্ষতার ভান করলেও আসলে এটি এক নতুন ধরনের নৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এটি নির্ধারণ করে দেয়, কোন ধরনের ধর্মীয় আচরণ ‘গ্রহণযোগ্য’ (যেমন – ব্যক্তিগত প্রার্থনা) এবং কোনটি ‘অগ্রহণযোগ্য’ বা ‘চরমপন্থী’ (যেমন – ধর্মীয় আইন প্রতিষ্ঠার দাবি)। তাই আসাদের কাছে, সেক্যুলারিজম হলো ধর্মের অনুপস্থিতি নয়, বরং এটি ক্ষমতা এবং জ্ঞানের এক নতুন বিন্যাস যা ধর্ম এবং ধার্মিকদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে (Asad, 2003)।
৭. রাজীব ভার্গব (Rajeev Bhargava): নীতিগত দূরত্বের ধারণা
ভারতীয় রাজনৈতিক দার্শনিক রাজীব ভার্গব (Rajeev Bhargava) পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতার মডেলগুলোর সীমাবদ্ধতা তুলে ধরে একটি বিকল্প মডেলের প্রস্তাব করেছেন, যা ভারতের মতো বহু-ধর্মীয় এবং গভীর সামাজিক বৈষম্যপূর্ণ দেশের জন্য বেশি উপযুক্ত। তিনি পশ্চিমা মডেল, বিশেষ করে আমেরিকান ‘বিচ্ছেদের প্রাচীর’-এর ধারণাকে একটি ‘যান্ত্রিক’ বা ‘এক-মাত্রিক’ ধারণা বলে মনে করেন।
এর বিপরীতে তিনি ‘নীতিগত দূরত্ব’ (Principled Distance)-এর ধারণার কথা বলেন (Bhargava, 2011)। এর মানে হলো, রাষ্ট্র ধর্ম থেকে একটি নমনীয় এবং আদর্শ-নির্ভর দূরত্ব বজায় রাখবে। রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি সমান সম্মান দেখাবে, কিন্তু প্রয়োজনে সে ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এই হস্তক্ষেপ হবে কিছু নীতির ওপর ভিত্তি করে, যেমন – স্বাধীনতা, সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। যেমন, রাষ্ট্র যদি দেখে যে, কোনো ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতার মতো অমানবিক প্রথা চলছে বা নারীদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে, তখন সে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। সে সেই ধর্মীয় গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে সংস্কার আনার চেষ্টা করবে। আবার, রাষ্ট্র যদি দেখে যে, কোনো সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বৈষম্যের শিকার, তখন সে তাদের রক্ষা করার জন্য বা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বিশেষ সাহায্যও করতে পারে।
ভার্গবের এই মডেলটি ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতার ধারণা থেকে বের করে এনে একটি সক্রিয়, ন্যায়বিচার-কেন্দ্রিক প্রকল্পে পরিণত করে, যা কেবল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তিই চায় না, বরং ধর্মের ভেতরের অন্যায়গুলোকেও দূর করতে চায়।
এই স্থপতিদের চিন্তাগুলো আমাদের দেখায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো একক বা স্থির ধারণা নয়। এটি একটি জীবন্ত, বিবর্তনশীল এবং বিতর্কিত ক্ষেত্র। লকের সহিষ্ণুতার ধারণা থেকে শুরু করে রলসের পাবলিক রিজন, এবং আসাদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত – এই দীর্ঘ পথচলার মধ্য দিয়েই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি আজকের রূপে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিভিন্ন চিন্তার আলোকেই আমরা আমাদের নিজেদের সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পথটি খুঁজে পেতে পারি।
উপসংহার
অনেক দীর্ঘ পথ আমরা একসাথে হেঁটে এলাম। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম, তার নানা রূপ, তার প্রয়োজনীয়তা, তার সমালোচনা এবং আমাদের নিজেদের দেশের সাথে তার জটিল সম্পর্ক – সবকিছুকেই আমরা ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন, এই যাত্রার শেষে এসে আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি? এই গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার কোনো সহজ পথ কি আমরা খুঁজে পেলাম?
হয়তো না। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো গন্তব্য নয়, এটি একটি নিরন্তর চলমান প্রক্রিয়া। এটি কোনো স্বর্গীয় সমাধান নয় যা সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। এটি বরং একটি আদর্শ, যাকে অর্জন করার জন্য একটি সমাজকে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, বিতর্ক করতে হয়, ভুল থেকে শিখতে হয়। এটি অনেকটা কম্পাসের কাঁটার মতো, যা সবসময় সঠিক উত্তর দিকে নির্দেশ করে, কিন্তু সেই উত্তর দিকে পৌঁছানোর পথটা আমাদের নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হয়। সেই পথ কখনও মসৃণ, কখনও বন্ধুর, কখনও বা কাঁটায় ভরা।
এই ধারণার জন্ম হয়েছিল বিভেদ এবং রক্তপাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি সমাজ তৈরি করা, যেখানে মানুষ তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কারণে নির্যাতিত হবে না, যেখানে রাষ্ট্র সবার অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে, কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে নয়। এই মূল উদ্দেশ্যটা আজও পৃথিবীর যেকোনো বহু-ধর্মীয় সমাজের জন্য আগের মতোই প্রাসঙ্গিক এবং জরুরি।
তবে এর সমালোচনাগুলোও অমূলক নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে রাজনীতি হয়েছে, ভোটের খেলা হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতিকে সবার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো আদর্শটির ব্যর্থতা নয়, বরং আমাদের – মানুষের – ব্যর্থতা। যেকোনো মহৎ আদর্শকেই মানুষ তার সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। আগুন দিয়ে যেমন রান্না করা যায়, তেমনি ঘরও জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। দোষটা আগুনের নয়, ব্যবহারকারীর।
শেষ পর্যন্ত, ধর্মনিরপেক্ষতা হলো একটি গোলকধাঁধা, যার কোনো সহজ প্রবেশ বা প্রস্থান পথ নেই। এর ভেতরে আছে নানা পথ, নানা বাঁক। প্রতিটি সমাজকে তার নিজের ইতিহাস, নিজের সংস্কৃতি আর নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে এই গোলকধাঁধার ভেতর থেকে নিজের পথটা খুঁজে বের করতে হয়। ফ্রান্স, আমেরিকা বা ভারত যে পথে হেঁটেছে, আমাদের পথটা ঠিক সেরকম নাও হতে পারে। আমাদের পথ আমাদের নিজেদেরই তৈরি করতে হবে।
এই পথ তৈরির জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার খোলা মনে আলোচনা, বিতর্ক এবং আত্মসমালোচনা। ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি গালি বা পশ্চিমা ষড়যন্ত্র হিসেবে দাগিয়ে না দিয়ে, অথবা একে সব সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে, এর শক্তি এবং দুর্বলতাগুলোকে আমাদের নির্মোহভাবে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, এটা কোনো ধর্মহীন সমাজ তৈরির প্রকল্প নয়, বরং এমন একটি সমাজ তৈরির প্রচেষ্টা যেখানে সব ধর্মের, সব বিশ্বাসের এবং সব অবিশ্বাসের মানুষও একসাথে শান্তিতে, মর্যাদায় এবং স্বাধীনতায় বাঁচতে পারে। এই প্রচেষ্টা হয়তো কঠিন, হয়তো দীর্ঘ, কিন্তু অসম্ভব নয়। আর এই কঠিন পথ পাড়ি দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টার মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে একটি উন্নততর, মানবিক এবং ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।
তথ্যসূত্র
- Asad, T. (2003). Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford University Press.
- Bellah, R. N. (1967). Civil Religion in America. Daedalus, 96(1), 1-21.
- Berman, H. J. (1983). Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Harvard University Press.
- Bhargava, R. (Ed.). (2011). Secularism and its Critics. Oxford University Press.
- Durkheim, É. (1912). The Elementary Forms of the Religious Life. (J. W. Swain, Trans.). George Allen & Unwin.
- Eck, D. L. (2006). From Diversity to Pluralism. The Pluralism Project, Harvard University. Retrieved from http://pluralism.org/
- Finocchiaro, M. A. (1989). The Galileo Affair: A Documentary History. University of California Press.
- Habermas, J. (2006). Religion in the Public Sphere. European Journal of Philosophy, 14(1), 1-25.
- Holyoake, G. J. (1896). The Origin and Nature of Secularism. Watts & Co.
- Jefferson, T. (1802). Letter to the Danbury Baptists. Library of Congress.
- Jeffery, P. (1988). The Shah Bano case. Oxford University Press.
- Kant, I. (1784). Answering the Question: What Is Enlightenment? (Königsbergische Gelehrte und Politische Zeitungen).
- Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford University Press.
- Locke, J. (1689). A Letter Concerning Toleration. (J. Tully, Ed.). Hackett Publishing Company.
- Madison, J. (1785). Memorial and Remonstrance Against Religious Assessments.
- Marx, K. (1844). On the Jewish Question. (Deutsch-Französische Jahrbücher).
- Nandy, A. (1998). The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Tolerance. In R. Bhargava (Ed.), Secularism and Its Critics (pp. 321-344). Oxford University Press.
- Nussbaum, M. C. (2012). The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Rawls, J. (1993). Political Liberalism. Columbia University Press.
- Rawls, J. (1997). The Idea of Public Reason Revisited. The University of Chicago Law Review, 64(3), 765-807.
- Riaz, A. (2013). Islam and Identity Politics Among British-Bangladeshis. Manchester University Press.
- Royle, E. (1980). Radicals, Secularists and Republicans: Popular Freethought in Britain, 1866-1915. Manchester University Press.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Spinoza, B. (1670). Theologico-Political Treatise. (S. Shirley, Trans.). Hackett Publishing Company.
- Taylor, C. (2007). A Secular Age. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Tierney, B. (1964). The Crisis of Church and State, 1050-1300. Prentice-Hall.
- Voltaire. (1763). Treatise on Tolerance. (S. Harvey, Trans.). Cambridge University Press.
- Walzer, M. (1997). On Toleration. Yale University Press.
- Weber, M. (1946). Science as a Vocation. In H. H. Gerth & C. W. Mills (Eds. & Trans.), From Max Weber: Essays in Sociology (pp. 129-156). Oxford University Press.
- Williams, R. (1644). The Bloudy Tenent of Persecution, for Cause of Conscience.
- Wilson, P. H. (2009). Europe’s Tragedy: A History of the Thirty Years’ War. Allen Lane.