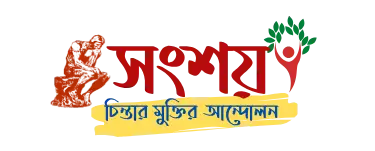ধর্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (Religion and International Relations): এক অদৃশ্য সুতার পাঠোদ্ধার
Table of Contents
- 1 ভূমিকা
- 2 চশমা বদলের গল্প – আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পুরোনো ধারণা ও তার সীমাবদ্ধতা
- 3 কেন ঘুম ভাঙল? ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তত্ত্বের সংকট ও ধর্মের প্রত্যাবর্তন
- 3.1 আধুনিকতার সংকট ও পরিচয়ের রাজনীতি (Crisis of Modernity and Identity Politics)
- 3.2 বিশ্বায়নের দ্বিমুখী প্রভাব (The Double-Edged Sword of Globalization)
- 3.3 রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা (Failure of Post-Colonial States and Ideologies)
- 3.4 উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি (The Role of Communication Technology)
- 4 ধর্ম কীভাবে কাজ করে? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নানান রূপ
- 4.1 পরিচয় ও বিভাজনের উৎস হিসেবে ধর্ম (Religion as a Source of Identity and Division)
- 4.2 রাষ্ট্রের বৈধতার উৎস হিসেবে ধর্ম (Religion as a Source of State Legitimacy)
- 4.3 আন্তর্জাতিক অভিনেতা হিসেবে ধর্মীয় সংগঠন (Transnational Religious Actors)
- 4.4 সংঘাত ও শান্তির দ্বিমুখী শক্তি হিসেবে ধর্ম (Religion as a a Double-Edged Sword: Conflict and Peacebuilding)
- 5 কয়েকটি অঞ্চলের চালচিত্র – তত্ত্ব থেকে বাস্তবে
- 6 তলোয়ারের পাশাপাশি জলপাই পাতা – ধর্ম, কূটনীতি ও শান্তি
- 7 মানচিত্র নির্মাতাদের কথা – তাত্ত্বিকদের দূরবীনে ধর্ম ও বিশ্ব
- 8 উপসংহার
- 9 তথ্যসূত্র
ভূমিকা
পৃথিবীর দিকে তাকালে কী দেখা যায়? একটা ম্যাপ। তাতে অনেকগুলো রঙ। প্রতিটি রঙ একেকটা দেশ। দেশগুলোকে আলাদা করেছে সরু, আঁকাবাঁকা সব রেখা। সীমানা। এই সীমানার একপাশে একদল লোক, অন্যপাশে আরেক দল। তাদের ভাষা আলাদা, পোশাক আলাদা, মুদ্রা আলাদা, পতাকা আলাদা। বড় বড় অট্টালিকায় বসে গম্ভীর চেহারার মানুষেরা ঠিক করেন এই দেশগুলো একে অপরের সাথে কীভাবে কথা বলবে, ব্যবসা করবে, নাকি যুদ্ধ করবে। এই পুরো ব্যাপারটাকে ভারী একটা নাম দেওয়া হয়েছে – আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International Relations)। দেখতে শুনতে বেশ গোছানো, ঝকঝকে একটা ছবি। সবকিছু যেন অঙ্ক কষে মেলানো যায়। রাষ্ট্রগুলো যেন দাবার বোর্ডের একেকটা ঘুঁটি, যারা কেবলই নিজেদের স্বার্থ (National Interest) বুঝে চলে। কে কতটা শক্তিশালী, কার অর্থনীতি কত বড়, কার কাছে কতগুলো পারমাণবিক বোমা আছে – এইসব কঠিন হিসাব-নিকাশের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব রাজনীতি।
কিন্তু মানুষের জগৎ কি এত সরল? এত গোছানো? ম্যাপের এই রঙিন দেশগুলোর ভেতরে কারা থাকে? মানুষ। কোটি কোটি মানুষ। তাদের মনে কী চলে? তাদের কিসে আনন্দ, কিসে ভয়? তারা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কী বিশ্বাস করে? রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে কার কাছে প্রার্থনা করে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ম্যাপে পাওয়া যায় না। অর্থনীতির গ্রাফে পাওয়া যায় না। পারমাণবিক বোমার হিসাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই উত্তরগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে পৃথিবীর আসল চালিকাশক্তির অনেকখানি। আর এই বিশ্বাসের জগতের সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে জটিল উপাদানটির নাম হলো ধর্ম।
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতরা বহুদিন এই ধর্মকে পাত্তাই দেননি। তারা ছিলেন সেই সব গণিতবিদের মতো, যারা অঙ্ক মেলানোর জন্য জটিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাগুলোকে সমীকরণের বাইরে রেখে দিতেন। তাদের কাছে রাষ্ট্র (State) ছিল মূল চরিত্র, আর রাষ্ট্র চলে যুক্তির ওপর। সেখানে আবেগ, বিশ্বাস বা ধর্মের মতো ‘অযৌক্তিক’ (Irrational) জিনিসের কোনো স্থান নেই। ধর্মকে তারা মনে করতেন মানুষের ব্যক্তিগত আলমারিতে তুলে রাখা এক পুরনো কাপড়ের মতো। বিশেষ দিনে হয়তো বের করা হয়, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তার কোনো প্রয়োজন নেই। আধুনিক, যুক্তিবাদী পৃথিবীতে রাষ্ট্র চলবে তার নিজের নিয়মে। ধর্ম থাকবে তার নিজের জায়গায় – মসজিদে, মন্দিরে, গির্জায়। রাজনীতির মাঠে তার প্রবেশ নিষেধ। এই ধারণাটি এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, একে একটি ‘ধর্মনিরপেক্ষ অনুমান’ (Secular Assumption) বলা যেতে পারে, যা পুরো শাস্ত্রটিকে কয়েক দশক ধরে শাসন করেছে।
কিন্তু আলমারিতে তুলে রাখা কাপড়টা যে আসলে জাদুর গালিচা হয়ে উড়তে পারে, সে খেয়াল কেউ করেনি। হঠাৎ করেই যেন সেই গালিচা উড়তে শুরু করল। ১৯৭৯ সালে ইরানে যখন আয়াতুল্লাহ খোমেনির (Ayatollah Khomeini) নেতৃত্বে ইসলামিক বিপ্লব হলো, তখন বড় বড় পণ্ডিতরা অবাক হয়ে দেখলেন, এটা তো তাদের জানা কোনো তত্ত্বের সাথে মিলছে না। এটা কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, নয় কোনো উদারনৈতিক আন্দোলন। এটা পুরোপুরি ধর্মের নামে, ধর্মের শক্তিতে ঘটানো এক পরিবর্তন, যা পুরো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রকে ওলটপালট করে দিল। আফগানিস্তানের পাহাড়ে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো এক পরাশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষেরা ‘জিহাদ’ ঘোষণা করল, তখন বিশ্ব দেখল বিশ্বাসের শক্তি আণবিক বোমার চেয়ে কম নয়। যুগোস্লাভিয়া যখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তখন দেখা গেল অর্থোডক্স, ক্যাথলিক আর মুসলিম – এই ধর্মীয় পরিচয়গুলো কমিউনিজমের ছাইচাপা আগুন থেকে বেরিয়ে এসে কী ভয়ঙ্কর দাবানল তৈরি করতে পারে।
দেখা গেল, যাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল, সে-ই আসলে বিশ্ব রাজনীতির এক নীরব পরিচালক। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই নীরব পরিচালক যেন সরব হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, বিশ্বায়নের (Globalization) উদ্দাম স্রোত, আর নানা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ডামাডোলে ধর্ম এক নতুন পরিচয়ে, নতুন শক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল মঞ্চে ফিরে এসেছে। যেটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হচ্ছিল, সেটাই এখন খবরের কাগজের শিরোনাম হচ্ছে।
এই দীর্ঘ লেখাটির উদ্দেশ্য হলো সেই ফিরে আসা পরিচালকের চরিত্র বিশ্লেষণ করা। ধর্ম কীভাবে দুটো দেশের মধ্যে হাজার বছরের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে দেয়, আবার কীভাবে এক উঠোনে থাকা দুটো ভাইকে চিরশত্রু বানিয়ে দেয় – সেই রহস্য খোঁজা। ধর্ম কি শুধুই সংঘাতের বারুদ, নাকি শান্তির পায়রাও হতে পারে? রাষ্ট্রগুলো কীভাবে পরম মমতায় ধর্মকে নিজেদের রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে? আবার ধর্মই বা কীভাবে মাঝে মাঝে রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে, সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে নিজের এক আলাদা জগৎ তৈরি করে?
আমরা এখানে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের গুণগান বা সমালোচনা করতে বসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য কোনো বিচারকের নয়, বরং একজন পর্যবেক্ষকের। একজন মনোবিজ্ঞানীর মতো করে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, মানুষের বিশ্বাস নামক এই জটিল অনুভূতিটি কীভাবে কাজ করে। কীভাবে এটি কোটি কোটি মানুষকে এক সুতোয় বাঁধে, আবার সেই সুতো দিয়েই গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয়। এই যাত্রায় আমরা তত্ত্বের শুষ্ক জগৎ থেকে বাস্তবের উত্তপ্ত ভূমিতে যাব, ইতিহাসের ধূসর পাতা থেকে বর্তমানের জ্বলজ্বল স্ক্রিনে চোখ রাখব, আর বোঝার চেষ্টা করব – মানুষের বিশ্বাস কীভাবে এই পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত গড়ে, আবার ভাঙে। চলুন, এই অদৃশ্য কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী সুতোর জট খোলার এই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর কিন্তু চিত্তাকর্ষক অভিযানে নামা যাক।
চশমা বদলের গল্প – আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পুরোনো ধারণা ও তার সীমাবদ্ধতা
যেকোনো বিষয়কে ভালোভাবে বুঝতে হলে তার শিকড় ধরে টান দিতে হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নামক জ্ঞানকাণ্ডের জন্ম হয়েছিল ইউরোপের এক রক্তাক্ত ইতিহাসের গর্ভ থেকে। ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে ইউরোপ এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, যা ইতিহাসে ‘ত্রিশ বছরের যুদ্ধ’ (Thirty Years’ War) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধটি নিছক কোনো রাজ্যের সাথে রাজ্যের লড়াই ছিল না; এটি ছিল বিশ্বাসের লড়াই, পরিচয়ের লড়াই। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট – খ্রিস্টধর্মের এই দুই ধারার অনুসারীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এমন এক দাবানলের জন্ম দিয়েছিল যা পুরো মহাদেশকে এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছিল। জার্মান ভূখণ্ডের কোনো কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এই অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞের পর যখন বিবদমান পক্ষগুলো ক্লান্ত, অবসন্ন এবং সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তখন তারা একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত হয়। ১৬৪৮ সালের সেই চুক্তিকে বলা হয় ‘ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তিচুক্তি’ (Peace of Westphalia)।
এই চুক্তিটি শুধু একটি যুদ্ধের অবসান ঘটায়নি, এটি এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল দুটি বৈপ্লবিক ধারণা, যা আজও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হয়ে আছে:
- সার্বভৌমত্ব (Sovereignty): প্রথমবারের মতো নীতিগতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হলো যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসক তার নিজের ভূখণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি। তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে, অন্য কোনো রাষ্ট্র বা বহিরাগত শক্তি, যেমন রোমের পোপ, হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ল্যাটিন ভাষায় একটি নীতি প্রতিষ্ঠিত হলো – Cuius regio, eius religio – অর্থাৎ, ‘যার রাজ্য, তার ধর্ম’। এর মানে হলো, শাসকের ধর্মই হবে রাজ্যের জনগণের ধর্ম। এটি ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল না, বরং এটি ছিল পোপের সার্বজনীন কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে রাজার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ (Philpott, 2001)।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (State System): আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল এবং একমাত্র বৈধ খেলোয়াড় হিসেবে রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। এর আগে ইউরোপের রাজনীতি ছিল এক জটিল জাল, যেখানে পোপ, পবিত্র রোমান সম্রাট, রাজা, ডিউক এবং বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের ক্ষমতা একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকত। ওয়েস্টফেলিয়া এই জট খুলে দিয়ে রাষ্ট্রকে ক্ষমতার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল।
এই চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় শাসকরা ধর্মকে রাজনীতির কেন্দ্রীয় মঞ্চ থেকে সচেতনভাবে সরিয়ে দিলেন। তাদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা বলছিল, ধর্ম যখন রাজনীতির সাথে মিশে যায়, তখন তা আপসহীন ও সর্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্ম দেয়। তাই একে যদি রাজনীতির বাইরে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসন দেওয়া যায়, তাহলেই কেবল শান্তি ও স্থিতিশীলতা সম্ভব। ধর্মকে বানানো হলো ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়, আর রাষ্ট্রকে বানানো হলো যুক্তিনির্ভর, স্বার্থকেন্দ্রিক এক প্রতিষ্ঠান। এই ওয়েস্টফেলিয়ান মডেলের ওপর ভিত্তি করেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাবশালী তত্ত্বগুলো (Theories of International Relations) গড়ে উঠেছিল। এই তত্ত্বগুলো ছিল সেই চশমার মতো, যা দিয়ে কয়েক প্রজন্ম ধরে পণ্ডিত ও নীতিনির্ধারকরা বিশ্বকে দেখেছেন।
বাস্তববাদ (Realism): জঙ্গলের আইন
বাস্তববাদের মূল কথা হলো, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাটা একটা নৈরাজ্যকর (Anarchic) জায়গা। এখানে কোনো বিশ্ব পুলিশ বা বিশ্ব সরকার নেই যে সবাইকে সুরক্ষা দেবে। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রকে নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই নিশ্চিত করতে হয়। এই তত্ত্বের শিকড় পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক থুসিডাইডিসের (Thucydides) ‘মেলিয়ান ডায়লগ’-এর মধ্যে, যেখানে শক্তিশালী এথেন্স দুর্বল মেলোসকে বলছে: “শক্তিশালীরা যা পারে তাই করে, আর দুর্বলরা যা পারে তাই মেনে নেয়।” আধুনিক কালে হ্যান্স মরগেনথাউ (Hans Morgenthau) পর্যন্ত বাস্তববাদীরা মনে করেন, মানব প্রকৃতি মৌলিকভাবে ক্ষমতার জন্য লোভী এবং স্বার্থপর। এই স্বার্থপর মানুষেরা যখন রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তখন রাষ্ট্রও স্বার্থপর আচরণ করে। অনেকটা জঙ্গলের মতো, যেখানে প্রতিটি প্রাণীকেই টিকে থাকার জন্য লড়াই করতে হয়। এই জঙ্গলে নৈতিকতা, আদর্শ, বন্ধুত্ব বা ধর্মের মতো নরম কথার কোনো দাম নেই। এখানে একটাই ভাষা চলে – শক্তির ভাষা। রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য হলো টিকে থাকা (Survival) এবং ক্ষমতা (Power) বাড়ানো (Morgenthau, 1948)।
বাস্তববাদী তত্ত্বের দুটি প্রধান ধারা রয়েছে। ক্লাসিক্যাল বাস্তববাদীরা (Classical Realists) যেমন মরগেনথাউ, মনে করেন, এই ক্ষমতার লড়াইয়ের উৎস হলো মানুষের প্রকৃতি। অন্যদিকে, নব্য-বাস্তববাদীরা (Neo-realists) বা কাঠামোগত বাস্তববাদীরা (Structural Realists), যেমন কেনেথ ওয়াল্টজ (Kenneth Waltz), মনে করেন যে সমস্যাটা মানুষের প্রকৃতিতে নয়, বরং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নৈরাজ্যকর কাঠামোতে। এই কাঠামোই রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষমতা বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করে, কারণ কে কখন আক্রমণ করে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই (Waltz, 1979)। জন মেয়ারশাইমারের (John Mearsheimer) মতো আক্রমণাত্মক বাস্তববাদীরা (Offensive Realists) আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্রগুলো কেবল নিজেদের অবস্থান রক্ষা করতেই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং সুযোগ পেলেই তারা প্রতিবেশীর বিনিময়ে নিজেদের ক্ষমতা সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করে (Mearsheimer, 2001)।
উভয় ধারার বাস্তববাদীদের কাছেই রাষ্ট্র হলো একটি ‘ব্ল্যাক বক্স’। রাষ্ট্রের ভেতরে কী হচ্ছে – তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা কী, সংস্কৃতি কেমন, মানুষ কোন ধর্মে বিশ্বাস করে – তা অপ্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রের আচরণ নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার চাপ দ্বারা, তার অভ্যন্তরীণ চরিত্র দ্বারা নয়। তাদের চোখে, সৌদি আরব যদি ইরানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তার কারণ তারা সুন্নি বা শিয়া নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যে (Balance of Power) একে অপরকে হুমকি হিসেবে দেখছে। একজন বাস্তববাদী বিশ্লেষক তাদের সামরিক বাজেট, অর্থনৈতিক শক্তি, ভৌগোলিক অবস্থান এবং মিত্রদের তালিকা দেখবেন; কিন্তু তেহরান বা রিয়াদের মসজিদে কী খুতবা দেওয়া হচ্ছে, তা তার কাছে গুরুত্বহীন। এই চশমা দিয়ে দেখলে, ধর্ম হলো নিছকই একটি উপরিকাঠামো বা ‘এপিফেনোমেনন’ (Epiphenomenon), যা রাষ্ট্র তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে ব্যবহার করে, কিন্তু এটি কখনোই রাষ্ট্রের আচরণের মূল চালিকাশক্তি নয়। ধর্ম হলো জাতীয় পতাকার মতোই একটি প্রতীক, যা দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যায়, কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয় শীতল, কঠিন স্বার্থের হিসাবে।
উদারতাবাদ (Liberalism): সহযোগিতার স্বপ্ন
উদারতাবাদীরা বাস্তববাদীদের মতো এতটা হতাশাবাদী নন। তারা মনে করেন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাটা শুধু ক্ষমতার লড়াইয়ের মঞ্চ নয়, এখানে সহযোগিতারও সুযোগ আছে। রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক আইন, সংস্থা (যেমন: জাতিসংঘ) এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার (Economic Interdependence) মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) তার ‘পারপেচুয়াল পিস’ (Perpetual Peace) প্রবন্ধে, যেখানে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক ফেডারেশন এবং বিশ্বনাগরিকত্বের আইনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।
আধুনিক উদারতাবাদীরা এই ধারণাগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। উদারতাবাদের একটি প্রভাবশালী উপ-তত্ত্ব হলো ‘গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব’ (Democratic Peace Theory)। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো একে অপরের সাথে যুদ্ধ করে না। কারণ গণতান্ত্রিক দেশের নেতারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন, এবং সাধারণ মানুষ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কারণে যুদ্ধ চায় না (Doyle, 1986)। উদারতাবাদীরা বিশ্বাস করেন, মুক্ত বাণিজ্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তৈরি করে, ফলে যুদ্ধ করাটা উভয় পক্ষের জন্যই ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে নরম্যান অ্যাঞ্জেল (Norman Angell) তার বিখ্যাত বই ‘দ্য গ্রেট ইলিউশন’ (The Great Illusion)-এ এই যুক্তিই দিয়েছিলেন যে, ইউরোপের দেশগুলোর অর্থনীতি এতটাই পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল যে, তাদের মধ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ হওয়াটা অযৌক্তিক এবং অসম্ভব (Angell, 1910)। যদিও ইতিহাস তার ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করেছে, কিন্তু অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার এই ধারণাটি উদারতাবাদের একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হয়ে আছে।
কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, উদারতাবাদীদের তত্ত্বেও ধর্ম প্রায় অনুপস্থিত। এর কারণ, তারা ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের (Enlightenment) ভাবধারায় গভীরভাবে বিশ্বাসী। এনলাইটেনমেন্টের মূল কথাই ছিল যুক্তি (Reason) দিয়ে কুসংস্কার, ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রতিস্থাপন করা। উদারতাবাদীরা মনে করতেন, আধুনিকতা, শিক্ষা এবং যুক্তির প্রসারের সাথে সাথে মানুষ তার সংকীর্ণ ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠবে। মানুষ নিজেকে ক্যাথলিক বা মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়ার আগে একজন ফরাসি বা জার্মান নাগরিক হিসেবে পরিচয় দেবে। তাদের কাছে, ধর্মীয় আবেগ হলো প্রাক-আধুনিক যুগের অবশেষ, যা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) হবে এবং নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। তাই তাদের বিশ্বশান্তির ফর্মুলাতেও ধর্মের জন্য কোনো ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকা রাখা হয়নি। ধর্মকে দেখা হয়েছে ব্যক্তিগত বিবেকের বিষয় হিসেবে, যা সর্বজনীন ক্ষেত্রে আলোচনার যোগ্য নয়।
মার্ক্সবাদ এবং বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব (Marxism and World-System Theory): আফিমের ঘোর
কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) অনুসারী তাত্ত্বিকরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখেন। তাদের মতে, বাস্তববাদীরা যাকে ‘ক্ষমতার লড়াই’ বা উদারতাবাদীরা যাকে ‘সহযোগিতা’ বলেন, তার সবই উপরিকাঠামো। আসল চালিকাশক্তি হলো অর্থনীতি এবং শ্রেণী সংগ্রাম। বিশ্বব্যবস্থা ধনী পুঁজিবাদী কেন্দ্র (Core) এবং শোষিত দরিদ্র পরিধি (Periphery) – এই দুই ভাগে বিভক্ত। আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো এই শ্রেণী সংগ্রামেরই প্রতিফলন। ধনী দেশগুলো গরিব দেশগুলোকে শোষণ করে নিজেদের সমৃদ্ধি বজায় রাখে। ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের (Immanuel Wallerstein) বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব এই কাঠামোকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে।
মার্ক্সীয় তত্ত্বে ধর্মকে দেখা হয়েছে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে। মার্ক্স বিখ্যাতভাবে ধর্মকে ‘জনগণের আফিম’ (Opium of the people) বলে অভিহিত করেছিলেন। তাদের মতে, ধর্ম হলো শাসক শ্রেণীর তৈরি করা একটি হাতিয়ার, যা দিয়ে শোষিত শ্রেণীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। ধর্ম মানুষকে পরকালের সুখের লোভ দেখিয়ে ইহকালের শোষণ-বঞ্চনা মেনে নিতে শেখায়, এবং এভাবে এটি বৈপ্লবিক চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধর্ম যদি কোনো ভূমিকা পালন করেও থাকে, তবে তা হলো পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার একটি কৌশল মাত্র। যেমন, উপনিবেশী শক্তিগুলো প্রায়শই খ্রিস্টান মিশনারিদের ব্যবহার করত স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে নিজেদের শাসনকে সহজ করার জন্য। তারা নিজেদের আগ্রাসনকে একটি ‘সভ্য করার মিশন’ (Civilizing Mission) হিসেবে উপস্থাপন করত। স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার মিত্র দেশগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে দমন করার নীতি গ্রহণ করেছিল, কারণ তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী ধর্ম ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে একটি বড় বাধা।
সীমাবদ্ধতা ও নতুন তত্ত্বের আগমন: কনস্ট্রাকটিভিজম (Constructivism)
এই প্রধান তত্ত্বগুলো, অর্থাৎ বাস্তববাদ, উদারতাবাদ এবং মার্ক্সবাদ, সম্মিলিতভাবে একটি ‘ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যমত্য’ (Secular Consensus) তৈরি করেছিল। তারা সবাই, ভিন্ন ভিন্ন কারণে, একমত হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে ধর্ম একটি অপ্রাসঙ্গিক চলক (Variable)।
কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে এই তত্ত্বগুলো দিয়ে অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। তখন এক নতুন তত্ত্বের আগমন ঘটে, যার নাম ‘কনস্ট্রাকটিভিজম’ বা ‘নির্মাণবাদ’ (Constructivism)। এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তাদের একজন হলেন আলেকজান্ডার ওয়েন্ডট (Alexander Wendt)। কনস্ট্রাকটিভিস্টরা বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগৎটা শুধু বস্তুগত শক্তি (যেমন: সেনাবাহিনী, অর্থনীতি) দিয়ে তৈরি নয়। এটি সামাজিক ধারণা, বিশ্বাস, পরিচয় এবং নিয়মকানুন (Norms) দিয়েও তৈরি। ওয়েন্ডটের বিখ্যাত উক্তি হলো, “নৈরাজ্য তাই, রাষ্ট্র যা তা থেকে তৈরি করে” (Anarchy is what states make of it) (Wendt, 1992)। এর মানে হলো, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নিজে থেকে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা তৈরি করে না। রাষ্ট্রগুলো একে অপরকে কীভাবে দেখে, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক কেমন হবে – তা নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক পরিচয় এবং বিশ্বাসের ওপর। যেমন, ব্রিটেনের ৫০০টি পারমাণবিক বোমা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভয়ের কারণ নয়, কিন্তু উত্তর কোরিয়ার ৫টি বোমা ভয়ের কারণ। এর কারণ বস্তুগত শক্তি নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যেকার বন্ধুত্ব এবং যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যেকার শত্রুতার সামাজিকভাবে নির্মিত ধারণা।
কনস্ট্রাকটিভিজম ধর্মের আলোচনার জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল। কারণ ধর্ম হলো পরিচয়, বিশ্বাস এবং নিয়মকানুন তৈরির অন্যতম প্রধান উৎস। যদি রাষ্ট্রের পরিচয় তার আচরণকে প্রভাবিত করে, তাহলে একটি ‘ইসলামিক প্রজাতন্ত্র’ ইরানের আচরণ একটি ‘ইহুদি রাষ্ট্র’ ইসরায়েলের থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। যদি নিয়মকানুন (Norms) গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে মানবাধিকারের সার্বজনীন ধারণা এবং শরিয়া আইনের মধ্যেকার বিতর্ক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। মার্থা ফিনেমোরের (Martha Finnemore) মতো কনস্ট্রাকটিভিস্টরা দেখিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তনের পেছনে মানবিক উদ্দেশ্য (যেমন দাসপ্রথা বিলোপ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (Finnemore, 1996)। ধর্মও তেমনই এক মানবিক ও নৈতিক প্রেরণার উৎস হতে পারে।
এই তত্ত্বগত পরিবর্তনের ফলেই পণ্ডিতরা ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করলেন, তাদের পুরনো চশমায় গুরুতর সমস্যা আছে। যেটাকে তারা মৃত বা অপ্রাসঙ্গিক বলে ধরে নিয়েছিলেন, সেই ধর্ম আসলে মরেনি। বরং এক দীর্ঘ ঘুম শেষে সে নতুন শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে। একে উপেক্ষা করে আর একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকে বোঝা সম্ভব নয়। বাস্তববাদ, উদারতাবাদ বা মার্ক্সবাদের চশমা দিয়ে বিশ্বকে দেখলে অনেক কিছুই ঝাপসা বা অদৃশ্য মনে হবে। পরিষ্কারভাবে দেখার জন্য চশমাটা বদলানোর সময় এসে গেছে।
কেন ঘুম ভাঙল? ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তত্ত্বের সংকট ও ধর্মের প্রত্যাবর্তন
একটা ধারণা একসময় পণ্ডিত মহলে প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো গৃহীত হয়েছিল। ধারণাটির নাম ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তত্ত্ব’ (Secularization Thesis)। এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তারা ছিলেন সমাজবিজ্ঞানের দিকপালেরা – ম্যাক্স ভেবার (Max Weber), এমিল ডুর্খাইম (Emile Durkheim) থেকে শুরু করে আধুনিক কালের পিটার বার্জার (Peter Berger) পর্যন্ত। তত্ত্বটা শুনতে খুব সরল, যৌক্তিক এবং আকর্ষণীয়। এর মূল বক্তব্য হলো, সমাজ যত আধুনিক হবে – অর্থাৎ যত বেশি শিল্পায়ন (Industrialization), নগরায়ন (Urbanization), বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার ঘটবে – মানুষ তত বেশি ‘যুক্তিবাদী’ (Rational) হয়ে উঠবে এবং বিশ্বকে আর ঐশ্বরিক বা অলৌকিক শক্তির লীলাক্ষেত্র হিসেবে দেখবে না। ম্যাক্স ভেবার এই প্রক্রিয়াকে বলেছিলেন পৃথিবীর ‘জাদু-মুক্তি’ (Disenchantment of the world)। মানুষ ধীরে ধীরে গির্জা বা পুরোহিতের নির্দেশনার বদলে নিজের যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর নির্ভর করবে। ফলে ধর্মের প্রভাব সমাজ ও রাজনীতি থেকে ততই কমে যাবে। ধর্ম টিকে থাকবে, কিন্তু তা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার (Private Affair) হয়ে। জনজীবনে (Public life), অর্থাৎ রাজনীতি, আইন, অর্থনীতিতে এর কোনো ভূমিকা থাকবে না। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পিটার বার্জার (Peter Berger) তার প্রথম দিকের লেখায় এই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ধার্মিক মানুষরা ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হবে (Berger, 1967)।
এই তত্ত্বের ভিত্তি ছিল মূলত পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা। ইউরোপে রেনেসাঁ, রিফর্মেশন এবং বিশেষ করে এনলাইটেনমেন্টের (Enlightenment) হাত ধরে গির্জার জ্ঞানতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে। রাষ্ট্র গির্জার প্রভাবমুক্ত হয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতরা, যারা মূলত এই পশ্চিমা জগতেই প্রশিক্ষিত, তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, এই ইউরোপীয় মডেলটাই হলো ইতিহাসের অমোঘ গতিপথ। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোও উন্নয়নের এই পথ ধরেই হাঁটবে এবং একসময় তারাও ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে ফেলবে।
কিন্তু বাস্তবে ঘটল এক নাটকীয় উল্টো ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে দেখা গেল, বিশ্বের প্রায় সব জায়গায় – ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিম ইউরোপ এবং বুদ্ধিজীবীদের একটি ছোট অংশ – ধর্মের প্রভাব কমার বদলে উল্টো বাড়ছে। গির্জা, মসজিদ, মন্দিরগুলো আবার লোকে লোকারণ্য হতে শুরু করল। ধর্মীয় আন্দোলনগুলো রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো। এই ঘটনাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়: ‘ধর্মের পুনরাবির্ভাব’ (Resurgence of Religion), ‘পবিত্রের প্রত্যাবর্তন’ (Return of the Sacred), বা হোসে কাসানোভার (José Casanova) ভাষায় ‘ধর্মের অপবিত্রায়ন’ (Deprivatization of Religion)। এর অর্থ হলো, ধর্ম যা ব্যক্তিগত চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছিল, তা আবার সদর্পে পাবলিক বা জনজীবনে ফিরে আসছে এবং সমাজ ও রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে (Casanova, 1994)।
কিন্তু কেন এমন হলো? কেন আধুনিকতার অমোঘ নিয়ম বলে প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তত্ত্বটি এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ল? এর পেছনে একটি নয়, বরং একাধিক জটিল ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কারণ রয়েছে।
আধুনিকতার সংকট ও পরিচয়ের রাজনীতি (Crisis of Modernity and Identity Politics)
আধুনিকতা মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে – বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উন্নত জীবনমান, ব্যক্তিস্বাধীনতা। কিন্তু এর একটি অন্ধকার দিকও ছিল, যা সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই চিহ্নিত করেছিলেন। কার্ল মার্ক্স যাকে ‘বিচ্ছিন্নতা’ (Alienation) বলেছেন, এমিল ডুর্খাইম যাকে ‘অ্যানোমি’ (Anomie) বা আদর্শহীনতা বলেছেন – সেটাই আধুনিক মানুষের এক গভীর সংকট। আধুনিকতা মানুষের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক বাঁধনগুলোকে আলগা করে দিয়েছে। যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার তৈরি হয়েছে, গ্রামের সম্প্রদায়ভিত্তিক জীবন নগরের বিচ্ছিন্ন ও নাম-পরিচয়হীন জীবনে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে মানুষ তার স্থানীয় পরিচয়, তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় মানুষের মনে এক গভীর শূন্যতা, এক অস্তিত্বের সংকট (Existential Crisis) তৈরি হয়। সে কে? তার জীবনের অর্থ কী? সে কোন বৃহত্তর গোষ্ঠীর অংশ?
এই পরিচয় সংকটের মুহূর্তে ধর্ম এক শক্তিশালী ও সহজলভ্য আশ্রয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। ধর্ম মানুষকে একটি ইতিহাস দেয়, একটি ঐতিহ্য দেয়, একটি ‘কাল্পনিক সম্প্রদায়’ (Imagined Community) দেয়, যা রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়েও বিস্তৃত হতে পারে (Anderson, 1983)। এটি জীবনের সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুকে একটি অর্থপূর্ণ কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে এবং কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, তার একটা সুস্পষ্ট নৈতিক দিকনির্দেশনা দেয়। জাতীয়তাবাদ বা সমাজতন্ত্রের মতো ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শগুলো অনেক সময় মানুষের এই গভীর অস্তিত্বের সংকট মেটাতে পারেনি। তারা মানুষকে নাগরিক বা কমরেড হিসেবে পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণ করতে পারেনি। ফলে মানুষ পরিচয়ের জন্য, জীবনের অর্থের জন্য, এবং নৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ধর্মের দিকে ফিরে গেছে।
বিশ্বায়নের দ্বিমুখী প্রভাব (The Double-Edged Sword of Globalization)
বিশ্বায়ন একদিকে যেমন সারা পৃথিবীকে একটি ‘গ্লোবাল ভিলেজ’ (Global Village) বা বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করেছে, তেমনই অন্যদিকে এটি মানুষের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক বিভেদকেও প্রকট করে তুলেছে। স্যাটেলাইট টিভি, ইন্টারনেট এবং বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতি, ভোক্তাবাদ (Consumerism) এবং জীবনযাত্রা বিশ্বের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক অ-পশ্চিমা সমাজে এটিকে ‘সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ’ (Cultural Imperialism) বা ‘সাংস্কৃতিক আগ্রাসন’ হিসেবে দেখা হয়েছে। তাদের মনে হয়েছে, এই বিশ্বায়ন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন বার্বার (Benjamin Barber) এই পরিস্থিতিকে ‘জিহাদ বনাম ম্যাকওয়ার্ল্ড’ (Jihad vs. McWorld) বলে বর্ণনা করেছেন। ‘ম্যাকওয়ার্ল্ড’ হলো বিশ্বায়নের সমরূপী, ভোগবাদী সংস্কৃতি, যা ম্যাকডোনাল্ডস, এমটিভি এবং অ্যাপলের মাধ্যমে বিশ্বকে একাকার করে ফেলতে চায়। আর ‘জিহাদ’ হলো এর বিরুদ্ধে সংকীর্ণ, গোষ্ঠীভিত্তিক, প্রায়শই ধর্মীয় পরিচয়ের সহিংস প্রতিক্রিয়া (Barber, 1995)।
এর প্রতিক্রিয়ায়, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও পরিচয় রক্ষার জন্য তারা আরও বেশি করে নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বিশ্বায়ন একদিকে যেমন মানুষকে বিশ্ব-নাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে, তেমনই নিজের ঘরকে, নিজের পরিচয়কে আঁকড়ে ধরার তাগিদও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে সমাজবিজ্ঞানী রোল্যান্ড রবার্টসন (Roland Robertson) বলেছেন ‘গ্লোকালাইজেশন’ (Glocalization) – অর্থাৎ বৈশ্বিক প্রভাব স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মিশে এক নতুন রূপ নিচ্ছে, যা প্রায়শই ধর্মীয় চরিত্রের হয় (Robertson, 1995)। বিশ্বায়ন এক ধরনের ‘সাংস্কৃতিক নিরাপত্তাহীনতা’ (Cultural Insecurity) তৈরি করেছে, যার প্রতিকার হিসেবে মানুষ ধর্মের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেছে।
রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা (Failure of Post-Colonial States and Ideologies)
উপনিবেশবাদ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ পশ্চিমা মডেলের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ (Secular Nationalism) বা সমাজতন্ত্র (Socialism) গ্রহণ করেছিল। গামাল আবদেল নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদ, বা ভারতের নেহেরুভিয়ান ধর্মনিরপেক্ষতার মতো মতাদর্শগুলো জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, এই মতাদর্শগুলো তাদের দারিদ্র্য, দুর্নীতি এবং সামাজিক অবিচার থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু কয়েক দশক পরেও যখন দেখা গেল যে এই রাষ্ট্রগুলো জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ, তখন প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। রাষ্ট্র প্রায়শই দুর্নীতিগ্রস্ত, অদক্ষ এবং নিপীড়ক একটি যন্ত্রে পরিণত হয়।
এই রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নেয় ধর্মীয় দল ও আন্দোলনগুলো। তারা প্রায়শই তৃণমূল পর্যায়ে এমন সব সামাজিক সেবা (Social Services) প্রদান করে, যা রাষ্ট্র করতে ব্যর্থ হয়। তারা স্কুল, হাসপাতাল, দাতব্য সংস্থা, এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সেবা করে এবং তাদের আস্থা অর্জন করে। তারা দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মনিরপেক্ষ এলিটদের বিকল্প হিসেবে নিজেদেরকে সৎ, নিষ্ঠাবান এবং ঈশ্বরের প্রতি দায়বদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করে। মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড, তুরস্কের জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (AKP), আলজেরিয়ার ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (FIS), বা ভারতের ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) উত্থানের পেছনে এই রাজনৈতিক ব্যর্থতা একটি বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে (Kepel, 2002)। তারা দেখিয়েছে যে, ধর্ম শুধু পারলৌকিক মুক্তির কথাই বলে না, ইহলৌকিক সমস্যা সমাধানেরও পথ দেখাতে পারে।
উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি (The Role of Communication Technology)
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তত্ত্বের প্রবক্তারা ভেবেছিলেন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষ করে গণমাধ্যম, মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ঘটাবে। কিন্তু বাস্তবে প্রযুক্তি ধর্মীয় ধারণা ও আন্দোলনের প্রসারে এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে যখন আয়াতুল্লাহ খোমেনি ফ্রান্সে নির্বাসিত ছিলেন, তখন তার জ্বালাময়ী ভাষণের অডিও ক্যাসেট লক্ষ লক্ষ কপি হয়ে ইরানের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিল। পরবর্তীকালে, স্যাটেলাইট টেলিভিশন বিভিন্ন ধর্মীয় প্রচারকদের (যেমন, খ্রিস্টান টেলি-ইভানজেলিস্ট বা মুসলিম দাঈ) বিশ্বব্যাপী তারকা বানিয়ে দিয়েছে। আর আজকের যুগে ইন্টারনেট, ইউটিউব এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো বিদ্যুৎ গতিতে তাদের বার্তা প্রচার করছে, সদস্য সংগ্রহ করছে এবং এমনকি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্যও লোক ভর্তি বা রিক্রুট করছে। প্রযুক্তি ধর্মকে দুর্বল করার বদলে তাকে সীমানা অতিক্রম করার (Transnational) ক্ষমতা দিয়েছে। এটি ‘দূরবর্তী ধর্মসভা’ (Long-distance congregations) তৈরি করেছে, যেখানে মানুষ ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন থেকেও একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অংশ হতে পারে।
এই সম্মিলিত কারণগুলোর ফলে, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে ধর্ম জনজীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। বরং এটি নতুন রূপে, নতুন শক্তিতে বিশ্ব রাজনীতিতে ফিরে এসেছে। পিটার বার্জার (Peter Berger), যিনি একসময় ধর্মনিরপেক্ষতা তত্ত্বের কট্টর সমর্থক ছিলেন, তিনিও পরবর্তীকালে তার ভুল স্বীকার করে বলেন, “আমার মূল বক্তব্য ছিল যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আধুনিকতা হাত ধরাধরি করে চলে। এই বক্তব্যটি মূলত ভুল ছিল।” তিনি তার নতুন অবস্থানকে ব্যাখ্যা করে বলেন, “পৃথিবী যতটা আশা করা হয়েছিল ততটা ধর্মনিরপেক্ষ হয়নি, বরং অনেক জায়গাতেই প্রচণ্ডভাবে ধার্মিক রয়ে গেছে” (Berger, 1999)। এই প্রত্যাবর্তন বা ‘পুনরাবির্ভাব’ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পুরো খেলার মাঠটাকেই বদলে দিয়েছে এবং পুরনো তত্ত্বগুলোকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে।
ধর্ম কীভাবে কাজ করে? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নানান রূপ
আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ধর্ম কোনো একক বা সরল ভূমিকা পালন করে না। এটি একটি বহুরূপী শক্তি, যা পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়। এটি একই সাথে সংঘাতের বিষ এবং শান্তির অমৃত হতে পারে। এর কার্যকারিতাকে বুঝতে হলে এর বিভিন্ন রূপকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ধর্ম কখনো স্বাধীন চলক (Independent Variable) হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ নিজেই ঘটনার কারণ হয়; আবার কখনো মধ্যবর্তী চলক (Intervening Variable) হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংঘাতকে আরও তীব্র করে তোলে।
পরিচয় ও বিভাজনের উৎস হিসেবে ধর্ম (Religion as a Source of Identity and Division)
মানুষের পরিচয়ের অনেকগুলো স্তর থাকে। সে একটি পরিবারের সদস্য, একটি গ্রামের বাসিন্দা, একটি ভাষা গোষ্ঠীর অংশ, একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। এই সব পরিচয়ের মধ্যে ধর্ম প্রায়শই সবচেয়ে গভীর এবং আবেগপূর্ণ পরিচয় হিসেবে কাজ করে। কারণ ধর্ম শুধু জাগতিক পরিচয় দেয় না, এটি মানুষের অস্তিত্ব, উদ্দেশ্য এবং পরকালের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়। এটি মানুষকে একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয়: “আমি কে?” এবং “কারা আমার দলের লোক?”। ধর্ম মানুষকে ‘আমরা’ (Us) এবং ‘ওরা’ (Them) এই দুই ভাগে ভাগ করার একটি শক্তিশালী মানদণ্ড তৈরি করে দেয়। যখন এই ‘আমরা’ বনাম ‘ওরা’র বিভাজনটি দুটি দেশের মধ্যে বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে, তখন তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সরাসরি প্রভাব ফেলে।
প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন (Samuel P. Huntington) তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বহুল বিতর্কিত ‘সভ্যতার সংঘাত’ (The Clash of Civilizations) তত্ত্বে এই বিষয়টিকেই সামনে এনেছিলেন। তার মূল বক্তব্য ছিল, স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিশ্ব রাজনীতিতে সংঘাতের প্রধান উৎস আর মতাদর্শ (পুঁজিবাদ বনাম কমিউনিজম) থাকবে না। বরং সংঘাত হবে বিভিন্ন ‘সভ্যতা’র (Civilizations) মধ্যেকার সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নিয়ে। আর এই সভ্যতাগুলোর মূল ভিত্তি হলো ধর্ম (যেমন: পাশ্চাত্য খ্রিস্টান সভ্যতা, ইসলামী সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, অর্থোডক্স সভ্যতা ইত্যাদি) (Huntington, 1993)। হান্টিংটনের মতে, বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন সভ্যতার মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ছে, যা তাদের মধ্যকার মিলের চেয়ে অমিলগুলোকেই বেশি করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।
হান্টিংটনের তত্ত্বটি সরলীকরণের দায়ে এবং ইসলাম-বিদ্বেষ উস্কে দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। এডওয়ার্ড সাঈদ (Edward Said) এর মতো সমালোচকরা বলেছেন, হান্টিংটন সভ্যতাগুলোকে একেকটি একাট্টা ও অপরিবর্তনশীল সত্তা হিসেবে দেখেছেন, যা বাস্তবতার প্রতিফলন নয়। প্রতিটি সভ্যতার ভেতরেই প্রচুর বৈচিত্র্য ও সংঘাত রয়েছে (Said, 2001)। অমর্ত্য সেন (Amartya Sen) দেখিয়েছেন যে, মানুষের বহুবিধ পরিচয় থাকে এবং শুধু ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর জোর দেওয়াটা বিপজ্জনক ও ভ্রান্ত (Sen, 2006)।
এত সমালোচনা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ধর্মীয় পরিচয় প্রায়শই আন্তর্জাতিক সংঘাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ:
- ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক: এই দুটি দেশের জন্মই হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক মূলত হিন্দু-সংখ্যাগুরু ভারত এবং মুসলিম-সংখ্যাগুরু পাকিস্তানের মধ্যকার অবিশ্বাস ও শত্রুতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। কাশ্মীর সমস্যা এই ধর্মীয় পরিচয়ের রাজনীতির সবচেয়ে রক্তাক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী উদাহরণ।
- ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত: এটি নিছক দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জমি দখলের লড়াই নয়। এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ইহুদি ও মুসলিমদের ধর্মীয় আবেগ এবং পবিত্র স্থানের ওপর অধিকারের প্রশ্ন। জেরুজালেম শহর, যা তিনটি আব্রাহামিক ধর্মের কাছেই পবিত্র, তা এই সংঘাতকে একটি রাজনৈতিক সমস্যা থেকে এক প্রায়-সমাধান-অযোগ্য ধর্মীয় সংঘাতে রূপান্তরিত করেছে।
- বলকান যুদ্ধ (Balkan Wars): নব্বইয়ের দশকে সাবেক যুগোস্লাভিয়া ভেঙে যাওয়ার পর যে ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ ও জাতিগত নিধনযজ্ঞ (Ethnic Cleansing) চলেছিল, তার পেছনেও ছিল ধর্মীয় পরিচয়ের বিভাজন। অর্থোডক্স খ্রিস্টান সার্ব, ক্যাথলিক খ্রিস্টান ক্রোয়াট এবং মুসলিম বসনিয়াক – এই তিনটি গোষ্ঠী, যারা একই ভাষায় কথা বলত এবং দেখতে প্রায় একই রকম ছিল, তারা নিজেদের আলাদা ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।
রাষ্ট্রের বৈধতার উৎস হিসেবে ধর্ম (Religion as a Source of State Legitimacy)
অনেক রাষ্ট্র তার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য ধর্মকে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। শাসকরা নিজেদেরকে ধর্মের রক্ষক বা ধারক হিসেবে উপস্থাপন করে জনগণের সমর্থন আদায় করেন এবং নিজেদের শাসনকে একটি নৈতিক ও ঐশ্বরিক বৈধতা (Legitimacy) দেওয়ার চেষ্টা করেন।
- সৌদি আরব: সৌদি রাজতন্ত্রের ক্ষমতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো ইসলাম, বিশেষ করে এর রক্ষণশীল ওয়াহাবি (Wahhabi) ধারা। অষ্টাদশ শতকে শাসক আল সৌদ পরিবার এবং ধর্মীয় নেতা মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল-ওয়াহাবের মধ্যেকার চুক্তির ওপর এই রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত। সৌদি বাদশাহ নিজেকে ‘দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষক’ (Custodian of the Two Holy Mosques) হিসেবে পরিচয় দেন। এই উপাধিটি তাকে শুধু দেশের ভেতরেই নয়, সারা বিশ্বের কোটি কোটি সুন্নি মুসলিমের কাছে একটি বিশেষ মর্যাদা ও প্রভাবের অধিকারী করে। মক্কা ও মদিনার ওপর নিয়ন্ত্রণ সৌদি আরবকে ইসলামী বিশ্বে এক অনন্য স্থান দিয়েছে, যা তারা তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে কাজে লাগায়।
- ইরান: ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর ইরান একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়, যার শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হলো আয়াতুল্লাহ খোমেনির ‘বেলায়াতে ফকিহ’ (Velayat-e Faqih) বা ‘ইসলামী আইনবিদের অভিভাবকত্ব’ তত্ত্ব। এর ফলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা একজন ধর্মীয় নেতার (Supreme Leader) হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ইরানের পররাষ্ট্রনীতি অনেকটাই শিয়া ইসলামের প্রচার এবং বিশ্বের শিয়া মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরবের সাথে ইরানের দ্বন্দ্বকে প্রায়শই সুন্নি ও শিয়া প্রভাব বিস্তারের ভূ-রাজনৈতিক লড়াই হিসেবে দেখা হয়।
- রাশিয়া: সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাশিয়া তার জাতীয় পরিচয় পুনঃনির্মাণের জন্য অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। রুশ অর্থোডক্স চার্চ এবং ক্রেমলিনের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ মিথোজীবী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন নিজেকে ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং পশ্চিমা উদারনৈতিকতাকে আক্রমণ করেন। এই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে তিনি দেশের ভেতরে জনসমর্থন ধরে রাখেন এবং বহির্বিশ্বে, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের অর্থোডক্স জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।
আন্তর্জাতিক অভিনেতা হিসেবে ধর্মীয় সংগঠন (Transnational Religious Actors)
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মানেই শুধু রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক নয়। এমন অনেক অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠন (Non-State Actor) আছে, যারা রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বজুড়ে কাজ করে এবং আন্তর্জাতিক নীতিকে প্রভাবিত করে। এদের মধ্যে ধর্মীয় সংগঠনগুলো অত্যন্ত প্রাচীন, প্রভাবশালী এবং সুসংগঠিত।
- ভ্যাটিকান ও ক্যাথলিক চার্চ: ভ্যাটিকান সিটি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সার্বভৌম রাষ্ট্র হলেও এর ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিশাল। পোপ হলেন সারা বিশ্বের প্রায় ১৩০ কোটি ক্যাথলিক খ্রিস্টানের আধ্যাত্মিক নেতা। তাঁর একটি নৈতিক কর্তৃত্ব (Moral Authority) রয়েছে, যা অনেক রাষ্ট্রপ্রধানেরও নেই। পোপের একটি বক্তব্য বা একটি কূটনৈতিক সফর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড় ধরনের আলোড়ন তুলতে পারে। যেমন, কিউবা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে পর্দার আড়ালে পোপ ফ্রান্সিসের (Pope Francis) ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। স্নায়ুযুদ্ধের সময় পোল্যান্ডে কমিউনিজমের পতনের পেছনে পোপ দ্বিতীয় জন পলের (Pope John Paul II) ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক।
- ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (Organisation of Islamic Cooperation – OIC): ৫৭টি মুসলিম-সংখ্যাগুরু দেশের এই জোটটি জাতিসংঘে মুসলিম বিশ্বের একটি সম্মিলিত কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করে। ফিলিস্তিন সমস্যা, ইসলামোফোবিয়া বা মুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকারের মতো বিষয়গুলোতে তারা একটি সাধারণ অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও অভ্যন্তরীণ বিভাজনের কারণে এর কার্যকারিতা প্রায়শই সীমিত, তবুও এটি মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।
- আন্তর্জাতিক ধর্মীয় এনজিও (Faith-Based NGOs): World Vision, Catholic Relief Services, Islamic Relief Worldwide, Aga Khan Foundation-এর মতো অসংখ্য ধর্মীয় এনজিও বিশ্বজুড়ে মানবিক সাহায্য, উন্নয়ন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বা দুর্যোগকবলিত এলাকায় তাদের নেটওয়ার্ক এবং কার্যক্রম প্রায়শই রাষ্ট্র বা জাতিসংঘের চেয়েও বেশি কার্যকর হয়। তারা সীমানা পেরিয়ে কোটি কোটি ডলারের সাহায্য ও সেবা পৌঁছে দেয়, যা তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব বা অ্যাক্টরে পরিণত করেছে।
- সহিংস অ-রাষ্ট্রীয় অভিনেতা (Violent Non-State Actors): ধর্মের এই আন্তর্জাতিক চরিত্রের একটি অন্ধকার দিকও রয়েছে। আল-কায়েদা বা আইসিসের (ISIS) মতো সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোও আন্তর্জাতিক ধর্মীয় অভিনেতা। তারা ধর্মের এক উগ্র ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্বজুড়ে এক খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহিংসতা চালায়। তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশ থেকে সদস্য সংগ্রহ করে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়। এই গোষ্ঠীগুলো দেখিয়েছে যে, ধর্মীয় ধারণা রাষ্ট্রের সীমানা মানে না এবং এটি বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য এক বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে।
সংঘাত ও শান্তির দ্বিমুখী শক্তি হিসেবে ধর্ম (Religion as a a Double-Edged Sword: Conflict and Peacebuilding)
ধর্মের সবচেয়ে জটিল ও পরস্পরবিরোধী রূপটি এখানেই দেখা যায়। একই ধর্মগ্রন্থ, একই প্রতীক, একই ঐতিহ্য একদিকে যেমন চরম সংঘাত ও সহিংসতার জন্ম দিতে পারে, তেমনই আবার শান্তি, ক্ষমা এবং সম্প্রীতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে। স্কট অ্যাপলবাই (R. Scott Appleby) এই দ্বৈত চরিত্রকে ‘পবিত্রের দ্ব্যর্থকতা’ (The Ambivalence of the Sacred) বলে অভিহিত করেছেন (Appleby, 2000)।
সংঘাতের জ্বালানি হিসেবে ধর্ম: ধর্ম যখন উগ্রপন্থী বা চরমপন্থী (Extremist) গোষ্ঠীর হাতে পড়ে, তখন এটি ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। তারা কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করে:
- শত্রুকে বিমানবিকীকরণ (Dehumanization): প্রতিপক্ষকে ‘কাফের’, ‘অবিশ্বাসী’ (Infidel) বা ‘শয়তানের অনুসারী’ হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এর ফলে তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের সহিংসতাকে বৈধ এবং এমনকি পুণ্যকাজ হিসেবে দেখানো সহজ হয়।
- মহাজাগতিক যুদ্ধ (Cosmic War): মার্ক জুর্গেনসমেয়ার (Mark Juergensmeyer) দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় সন্ত্রাসীরা তাদের লড়াইকে নিছক কোনো রাজনৈতিক বা জাগতিক লড়াই হিসেবে দেখে না। তারা মনে করে, এটি ভালো এবং মন্দের মধ্যে, ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে এক মহাজাগতিক যুদ্ধ। এই ধরনের যুদ্ধে কোনো আপস বা পরাজয় সম্ভব নয়, কেবল বিজয় বা শাহাদাত (Juergensmeyer, 2003)।
- ঐশ্বরিক বৈধতা (Divine Sanction): তারা তাদের সহিংসতার জন্য ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে খণ্ডিত অংশ উদ্ধৃত করে বা সেগুলোর চরমপন্থী ব্যাখ্যা দিয়ে ঐশ্বরিক অনুমোদন দাবি করে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নির্যাতন, শ্রীলঙ্কায় তামিলদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, বা ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার পেছনেও উগ্র বৌদ্ধ, সিংহলী বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভূমিকা রয়েছে।
শান্তির দূত হিসেবে ধর্ম: অন্যদিকে, সব ধর্মেই শান্তি, ক্ষমা, দয়া এবং ভালোবাসার শক্তিশালী বাণী রয়েছে। এই বাণীকে ভিত্তি করে অনেক ধর্মীয় নেতা ও সংগঠন সংঘাত নিরসনে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় (Peacebuilding) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- মধ্যস্থতা ও সম্প্রীতি (Mediation and Reconciliation): দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী (Apartheid) শাসনের অবসানের পর সত্য ও পুনর্মিলন কমিশন (Truth and Reconciliation Commission) গঠন করা হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু (Desmond Tutu)। তিনি খ্রিস্টীয় ক্ষমা ও সম্প্রীতির (Reconciliation) আদর্শকে সামনে এনেছিলেন, যা দেশটিকে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করেছিল।
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (Interfaith Dialogue): বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে, যেমন – নাইজেরিয়া, বসনিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যে, বিভিন্ন ধর্মের নেতারা একসাথে বসে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি এবং সংঘাত নিরসনের উপায় খোঁজেন। এটি হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বড় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না, কিন্তু এটি তৃণমূল পর্যায়ে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ কমাতে সাহায্য করে।
- শান্তির দর্শন (Theology of Peace): অনেক ধর্মতাত্ত্বিক ও অ্যাক্টিভিিস্ট তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে অহিংসা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শান্তির উপাদানগুলো খুঁজে বের করে একটি বিকল্প বয়ান বা ন্যারেটিভ তৈরি করেন, যা সহিংসতার বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করে। মহাত্মা গান্ধীর (Mahatma Gandhi) অহিংস আন্দোলন, যা হিন্দুধর্মের ‘অহিংসা’ ধারণা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল, এর একটি ক্লাসিক উদাহরণ।
এই দ্বিমুখী চরিত্রই ধর্মকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ধর্মকে কেবল ‘সমস্যা’ বা ‘সমাধান’ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পদ, যা ভালো বা মন্দ – উভয় কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন পরিস্থিতিতে এটি কোন রূপ নেবে, তা নির্ভর করে এর ব্যবহারকারী এবং পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর।
কয়েকটি অঞ্চলের চালচিত্র – তত্ত্ব থেকে বাস্তবে
এতক্ষণ আমরা তত্ত্ব নিয়ে অনেক কথা বললাম। এবার চলুন বিশ্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করে দেখি, সেখানে ধর্ম আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই জটিল খেলাটা বাস্তবে কীভাবে চলছে। প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতা রয়েছে, যা ধর্মকে এক অনন্য রূপ দিয়েছে। তত্ত্বের শুষ্ক কাঠামোর বাইরে বাস্তবের উত্তপ্ত ভূমিতে ধর্ম আরও জটিল, আরও আবেগপূর্ণ এবং আরও অপ্রত্যাশিতভাবে কাজ করে।
মধ্যপ্রাচ্য: বিশ্বাসের যুদ্ধক্ষেত্র
মধ্যপ্রাচ্যকে প্রায়শই ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণের এক আদর্শ পরীক্ষাগার (Laboratory) হিসেবে দেখা হয়। এখানে রাষ্ট্র, সীমানা এবং রাজনীতির প্রায় প্রতিটি দিকই ধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এই অঞ্চলের কোনো রাজনৈতিক সমীকরণই ধর্মকে ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।
- সুন্নি-শিয়া বিভাজন ও ছায়াযুদ্ধ: ইসলামের এই দুই প্রধান শাখার মধ্যকার ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক বিভাজন আজকের মধ্যপ্রাচ্যে প্রধান ভূ-রাজনৈতিক (Geopolitical) সংঘাতে পরিণত হয়েছে। একদিকে রয়েছে সুন্নি-প্রধান সৌদি আরব, যে নিজেকে সুন্নি বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অন্যদিকে রয়েছে শিয়া-প্রধান ইরান, যে ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে শিয়া ইসলামের এক বিপ্লবী ধারাকে ধারণ করে এবং অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রহী। এই দুই দেশের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুরো অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে। ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ, সিরিয়ার সংঘাত, ইরাকের রাজনৈতিক বিভাজন এবং লেবাননের ভঙ্গুর ক্ষমতার ভারসাম্য – এই সবকিছুতেই তেহরান ও রিয়াদের ছায়াযুদ্ধের (Proxy War) প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে ধর্ম শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়, এটি ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং কৌশলগত আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ের একটি শক্তিশালী আবরণ।
- ইসরায়েল, ফিলিস্তিন ও আব্রাহামিক ধর্মের সংঘাত: ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতকে বিশ্বের সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি শুধু জমি, সম্পদ বা সার্বভৌমত্বের লড়াই নয়। এর মূলে রয়েছে ধর্মীয় পরিচয়, ঐতিহাসিক বয়ান এবং পবিত্র স্থানের ওপর অধিকারের প্রশ্ন। ইহুদিদের জন্য এটি তাদের ‘প্রতিশ্রুত ভূমি’ (Promised Land) এবং তাদের হাজার বছরের নির্বাসন শেষে ফিরে আসার চূড়ান্ত পরিণতি। অন্যদিকে মুসলিমদের জন্য জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। খ্রিস্টানদের জন্যও জেরুজালেম এবং বেথলেহেম অত্যন্ত পবিত্র। এই ‘পবিত্র ভূমি’র ওপর কার একচ্ছত্র অধিকার থাকবে, এই প্রশ্নটি সংঘাতকে একটি রাজনৈতিক সমস্যা থেকে এক আবেগপূর্ণ, প্রায়-সমাধান-অযোগ্য ধর্মীয় সংঘাতে রূপান্তরিত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বহিরাগত শক্তিগুলোর নীতিও প্রায়শই অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় গোষ্ঠী (যেমন: ইভানজেলিকাল খ্রিস্টান, যারা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সমর্থন জানায়) দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে।
- রাজনৈতিক ইসলাম ও গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ: মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ে যে ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী বা রাজতান্ত্রিক সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছিল, তারা প্রায়শই স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই রাজনৈতিক শূন্যতায় ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ (Political Islam) বা ইসলামপন্থা (Islamism) এক শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে। মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে শুরু করে হামাস, হিজবুল্লাহ এবং এমনকি আইসিসের মতো বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী ইসলামের নামে এক বিকল্প রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কথা বলে। তাদের লক্ষ্য হলো আধুনিক রাষ্ট্রকে ইসলামের নীতি বা শরিয়া আইনের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা। গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং নারী অধিকারের মতো বিষয়গুলোতে তাদের অবস্থান পশ্চিমা উদারনৈতিক ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক, যা পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ককে সংঘাতময় করে তুলেছে।
দক্ষিণ এশিয়া: পরিচয়ের টানাপোড়েন ও প্রতিবেশ
দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এবং ধর্মীয়ভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি অঞ্চল। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বসবাস এখানে। এই অঞ্চলে ধর্ম, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়া অত্যন্ত প্রকট এবং প্রায়শই রক্তক্ষয়ী।
- ভারত ও হিন্দুত্ববাদের পররাষ্ট্রনীতি: ভারত সাংবিধানিকভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও সাম্প্রতিক দশকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী (Hindu Nationalism) বা ‘হিন্দুত্ব’ (Hindutva) মতাদর্শের উত্থান দেশটির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায় এবং তারা মনে করে, ভারতের জাতীয় পরিচয় ও সংস্কৃতি হিন্দুধর্মের ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। এই মতাদর্শের উত্থান ভারতের মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছে। এর প্রভাব ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতেও পড়ছে। বিশেষ করে মুসলিম-সংখ্যাগুরু প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী পরিচয় একটি বড় ভূমিকা রাখছে। নাগরিকত্ব আইন সংশোধন (CAA), বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও রামমন্দির নির্মাণ, বা কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের মতো ঘটনাগুলো শুধু ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় থাকছে না, বরং তা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কে উত্তেজনা তৈরি করছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে।
- পাকিস্তান: ইসলাম, রাষ্ট্র ও কৌশলগত গভীরতা: পাকিস্তানের জন্মই হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতের মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে। ফলে দেশটির পরিচয় ও রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইসলাম। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের ভূমিকা কী হবে – এই প্রশ্ন নিয়ে দেশটিতে শুরু থেকেই তীব্র বিতর্ক ও সংঘাত বিদ্যমান। একদিকে যেমন উদারপন্থী ও সুফি ইসলামের ধারা রয়েছে, তেমনই রয়েছে দেওবন্দি বা ওয়াহাবি ধারার উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাব। দেশটির শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ISI) প্রায়শই নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে, বিশেষ করে ভারতের বিরুদ্ধে ‘কৌশলগত গভীরতা’ (Strategic Depth) অর্জনের জন্য, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন ও ব্যবহার করার জন্য অভিযুক্ত হয় (Fair, 2014)। এটি ভারতের সাথে তার সম্পর্ককে এক চিরস্থায়ী অবিশ্বাস ও শত্রুতার বৃত্তে আটকে রেখেছে।
- শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমার: বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ ও সংখ্যালঘু নির্যাতন: বৌদ্ধধর্মকে সাধারণত একটি শান্তিবাদী ধর্ম হিসেবে দেখা হলেও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর এক উগ্র জাতীয়তাবাদী রূপ দেখা যায়। শ্রীলঙ্কায় সিংহলী-বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ তামিল সংখ্যালঘুদের (যারা মূলত হিন্দু) বিরুদ্ধে দশকের পর দশক ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল। সম্প্রতি মুসলিমদের বিরুদ্ধেও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা ও সহিংসতা দেখা গেছে। মিয়ানমারে এই বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। সেখানে ‘মা বা থা’ (Ma Ba Tha)-এর মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী ভিক্ষুদের সংগঠনগুলো প্রচার করে যে, রোহিঙ্গা মুসলিমরা বৌদ্ধ ধর্ম এবং মিয়ানমারের জাতীয় পরিচয়ের জন্য এক অস্তিত্বের সংকট বা হুমকি। এই ধর্মীয় বিদ্বেষকে ব্যবহার করে সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার, গণহত্যা ও জাতিগত নিধন (Ethnic Cleansing) চালিয়েছে, যা এক বিশাল শরণার্থী সংকট তৈরি করেছে এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশের ওপর প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেছে।
ইউরোপ ও আমেরিকা: ধর্মনিরপেক্ষতার দুর্গে ধর্মের পদধ্বনি
ইউরোপ ও আমেরিকাকে সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষতার কেন্দ্রবিন্দু এবং আধুনিকতার প্রতিভূ বলে মনে করা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এখানেও ধর্ম এক নতুন এবং অপ্রত্যাশিত উপায়ে রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ফিরে এসেছে, যা বহু পুরনো ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে।
- অভিবাসন, ইসলাম ও ইউরোপীয় পরিচয়ের সংকট: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক দশকে, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকে মুসলিম অভিবাসী ও শরণার্থীদের আগমন ইউরোপে এক বড় ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এর ফলে ইউরোপের অনেক দেশে ডানপন্থী, অভিবাসন-বিরোধী এবং ইসলাম-বিদ্বেষী (Islamophobic) রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। তারা প্রচার করে যে, মুসলিম অভিবাসীরা ইউরোপের ঐতিহ্যবাহী ‘খ্রিস্টীয়’ বা ‘জুডিও-খ্রিস্টান’ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জন্য হুমকি। ফ্রান্সের ‘লাইসিতে’ (Laïcité) বা কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হিজাব বা বোরকা নিষিদ্ধ করা, সুইজারল্যান্ডে মসজিদের মিনার নির্মাণে গণভোটের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, বা বিভিন্ন দেশে হালাল মাংসের বিরোধিতা – এইসব ঘটনা ইউরোপের বহু-সাংস্কৃতিক (Multicultural) পরিচয়কে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে এবং এর সমাজে গভীর বিভাজন তৈরি করছে। এটি তুরস্ক এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সাথে ইউরোপের সম্পর্ককেও প্রভাবিত করছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ঈশ্বরের অধীনে এক জাতি’: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারিভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যেখানে গির্জা ও রাষ্ট্র পৃথক (Separation of Church and State)। কিন্তু বাস্তবে এর সমাজ ও রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। বিশেষ করে ইভানজেলিকাল খ্রিস্টানরা (Evangelical Christians) দেশটির অন্যতম প্রভাবশালী একটি রাজনৈতিক শক্তি এবং রিপাবলিকান পার্টির ভোটব্যাংকের একটি বড় অংশ। গর্ভপাত, সমকামী বিবাহ এবং বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সমর্থনের মতো বিষয়গুলোতে তাদের রক্ষণশীল অবস্থান মার্কিন নীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে ধর্মীয় পরিভাষায় এবং ‘ভালো বনাম মন্দ’র (Good vs. Evil) বাইনারিতে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন – প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ (War on Terror) এবং ‘অশুভের অক্ষ’ (Axis of Evil) এর মতো শব্দচয়ন ধর্মীয় অনুষঙ্গে পূর্ণ ছিল।
- রাশিয়া ও অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মের পুনরুত্থান: সোভিয়েত ইউনিয়নের নাস্তিক্যবাদী শাসনের পতনের পর রাশিয়া তার জাতীয় পরিচয় এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব পুনঃনির্মাণের জন্য অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মকে একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে। রুশ অর্থোডক্স চার্চ এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সরকারের মধ্যে এক শক্তিশালী জোট তৈরি হয়েছে। পুতিন নিজেকে এবং রাশিয়াকে ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধের রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং পশ্চিমা উদারনৈতিকতাকে ‘নষ্ট’ ও ‘অবক্ষয়ী’ সংস্কৃতি বলে আক্রমণ করেন। এই ‘সভ্যতাবাদী’ (Civilizational) বয়ান ব্যবহার করে তিনি দেশের ভেতরে জনসমর্থন তৈরি করেন এবং বহির্বিশ্বে, বিশেষ করে ইউক্রেন বা জর্জিয়ার মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতে হস্তক্ষেপের নৈতিক বৈধতা খোঁজার চেষ্টা করেন।
এই উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট যে, ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিষয় নয়। এটি একটি বৈশ্বিক শক্তি, যা ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে চলেছে। একে ছাড়া আধুনিক বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্র বোঝা প্রায় অসম্ভব।
তলোয়ারের পাশাপাশি জলপাই পাতা – ধর্ম, কূটনীতি ও শান্তি
আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের মনে প্রায়শই সংঘাত, যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠও আছে। ধর্ম যেমন বিভেদ ও সংঘাতের আগুন জ্বালাতে পারে, তেমনই শান্তি, সম্প্রীতি এবং পুনর্মিলনের জলপাই পাতাও বয়ে আনতে পারে। সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় ‘ধর্মীয় কূটনীতি’ (Faith-Based Diplomacy), ‘আন্তঃধর্মীয় সংলাপ’ (Interfaith Dialogue) এবং ‘ধর্মীয় শান্তিগঠন’ (Religious Peacebuilding) বেশ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
ধর্মীয় কূটনীতি (Faith-Based Diplomacy): প্রচলিত পথের বাইরে
প্রচলিত কূটনীতি বা ডিপ্লোম্যাসি সাধারণত রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রী বা পেশাদার কূটনীতিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অনেক সময় যখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোচনা অচলাবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন ধর্মীয় নেতা বা সংগঠনগুলো পর্দার আড়ালে থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প বা ‘ট্র্যাক টু’ (Track II Diplomacy) কূটনীতির ভূমিকা পালন করতে পারে। এর কার্যকারিতার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে:
- বিশ্বাস ও নৈতিক কর্তৃত্ব (Trust and Moral Authority): ধর্মীয় নেতাদের অনেক সময় সাধারণ মানুষ এবং এমনকি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোও রাজনীতিবিদদের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে। তাদের একটি নৈতিক কর্তৃত্ব থাকে, যা তাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তারা প্রায়শই কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে বলে বিবেচিত হন।
- গোপনীয়তা ও ধৈর্য (Confidentiality and Patience): ধর্মীয় সংগঠনগুলো প্রায়শই প্রচারের আলো থেকে দূরে, নীরবে এবং ধৈর্যের সাথে কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রীয় কূটনীতিকদের মতো তাদের নির্বাচনি চাপ বা জনমতের চাপের মুখে দ্রুত ফলাফল দেখানোর তাড়া থাকে না। তারা বছরের পর বছর ধরে বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে আস্থা তৈরির কাজ করে যেতে পারে।
- সীমানা ছাড়ানো নেটওয়ার্ক (Transnational Networks): বড় ধর্মীয় সংগঠনগুলোর নেটওয়ার্ক বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত থাকে। এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে, বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে এবং সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, যা অনেক সময় রাষ্ট্রীয় কূটনীতিকদের পক্ষেও সম্ভব হয় না।
এর একটি ক্লাসিক উদাহরণ হলো ইতালির রোম-ভিত্তিক একটি ক্যাথলিক সংগঠন, ‘কমিউনিটি অফ সান্ত’এজিডিও’ (Community of Sant’Egidio)। ১৯৯০-এর দশকে আফ্রিকার মোজাম্বিকের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ অবসানে এই সংগঠনটি সফলভাবে মধ্যস্থতা করেছিল। যখন জাতিসংঘ এবং বড় বড় রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ হয়েছিল, তখন এই সাধারণ নাগরিকদের সংগঠনটি দুই বিবদমান পক্ষকে রোমে তাদের সদর দফতরে এনে দীর্ঘ দুই বছর ধরে আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল (Haynes, 2007)। একইভাবে, উত্তর আয়ারল্যান্ডের শান্তি প্রক্রিয়ায় ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের নেতারা পর্দার আড়ালে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: ঘৃণার বিপরীতে সেতু নির্মাণ
যখন দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও শত্রুতা তৈরি হয়, তখন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ একটি সেতু হিসেবে কাজ করতে পারে। এর মূল উদ্দেশ্য নিছক ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক করা নয়, বরং:
- পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি (Increasing Mutual Understanding): একে অপরের ধর্ম, বিশ্বাস, উৎসব ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং প্রচলিত ভুল ধারণা বা স্টেরিওটাইপগুলো দূর করা।
- সাধারণ মূল্যবোধ খুঁজে বের করা (Finding Common Ground): সব ধর্মেই যে শান্তি, দয়া, ন্যায়বিচার এবং মানবমর্যাদার মতো সাধারণ মানবিক মূল্যবোধ রয়েছে, সেগুলোকে সামনে নিয়ে আসা।
- ঘৃণার বয়ানকে প্রতিহত করা (Countering Hate Speech): যখন উগ্রপন্থী নেতারা ধর্মের নামে ঘৃণা ছড়ান, তখন বিভিন্ন ধর্মের নেতাদের একসাথে শান্তির পক্ষে কথা বলাটা একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়।
এই ধরনের সংলাপ হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে কাশ্মীর বা ফিলিস্তিনের মতো বড় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কিন্তু এটি তৃণমূল পর্যায়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষাক্ত পরিবেশকে বদলাতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘমেয়াদে শান্তির জন্য একটি সামাজিক ভিত্তি তৈরি করে। বসনিয়া, নাইজেরিয়া বা ভারতের মতো ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত সমাজে এই ধরনের উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম।
মানবিক সাহায্য ও উন্নয়ন: বিশ্বাসের মানবিক মুখ
বিশ্বজুড়ে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানবসৃষ্ট সংকটে ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক সংগঠনগুলো (Faith-Based Organizations – FBOs) প্রায়শই প্রথম সারির সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাদের কাজের পরিধি বিশাল এবং প্রভাব সুদূরপ্রসারী।
- বিশাল নেটওয়ার্ক ও স্বেচ্ছাসেবী: তাদের উপাসনালয়-ভিত্তিক বিশাল নেটওয়ার্ক এবং নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকদের কারণে তারা খুব দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে।
- স্থানীয় জ্ঞান ও আস্থা: তারা প্রায়শই একটি অঞ্চলে দশকের পর দশক ধরে কাজ করার ফলে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি এবং মানুষের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক থাকে। ফলে তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থাভাজন হয় এবং তাদের প্রয়োজনগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে।
- সেবার দর্শন: সেবাকে তারা ধর্মীয় দায়িত্ব বা পুণ্যকাজ হিসেবে দেখে, যা তাদের কঠিন ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও কাজ করে যেতে অনুপ্রেরণা জোগায়।
Caritas Internationalis (ক্যাথলিক), Islamic Relief Worldwide (মুসলিম), Khalsa Aid (শিখ), American Jewish World Service (ইহুদি) – এই সংগঠনগুলো কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত পরিচয় না দেখেই বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ডলারের মানবিক সাহায্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে। তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অভিনেতা।
তবে এই ক্ষেত্রেও কিছু চ্যালেঞ্জ এবং বিতর্ক রয়েছে। কখনো কখনো মানবিক সাহায্যের আড়ালে ধর্মান্তরকরণের (Proselytism) সূক্ষ্ম বা প্রকাশ্য চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে এবং সাহায্যের মূল উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এছাড়া, কিছু ধর্মীয় দাতব্য সংস্থার বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীকে অর্থায়নেরও অভিযোগ উঠেছে, যা বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে।
সুতরাং, ধর্মকে কেবল সংঘাতের অনুঘটক হিসেবে দেখা একটি একপেশে এবং অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ। এটি শান্তি, সম্প্রীতি এবং মানবকল্যাণেরও এক বিরাট উৎস হতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে বুঝতে হলে এর এই দ্বৈত ও জটিল চরিত্রকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং শান্তির জন্য এর সম্ভাবনাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই পথ খুঁজতে হবে (Johnston & Sampson, 1994)।
মানচিত্র নির্মাতাদের কথা – তাত্ত্বিকদের দূরবীনে ধর্ম ও বিশ্ব
যেকোনো জটিল বিষয় বুঝতে হলে আমাদের কিছু মানুষের সাহায্য নিতে হয়, যারা আমাদের হাতে একটি মানচিত্র বা দূরবীন তুলে দেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগৎটাও এমনই এক জটিল অরণ্য। এই অরণ্যের পথ চেনানোর জন্য কিছু চিন্তাবিদ বা তাত্ত্বিক (Theorists) তাদের জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করেছেন। তারা চেষ্টা করেছেন কিছু নিয়মকানুন, কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার করতে, যা দিয়ে এই জটিল খেলাটাকে বোঝা যায়। ধর্মের মতো একটি বিষয় যখন এই খেলায় প্রবেশ করে, তখন পুরনো মানচিত্রগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। তখন দরকার হয় নতুন মানচিত্র নির্মাতার। এই অধ্যায়ে আমরা সেইসব পুরনো ও নতুন মানচিত্র নির্মাতাদের কয়েকজনের সাথে পরিচিত হব। দেখব, তাদের দূরবীন দিয়ে ধর্ম ও বিশ্ব রাজনীতিকে কেমন দেখায়।
পুরনো কার্টোগ্রাফাররা: যারা মানচিত্রে ধর্মকে জায়গা দেননি
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্লাসিক্যাল তাত্ত্বিকদের পুরনো দিনের কার্টোগ্রাফার বা মানচিত্র নির্মাতাদের সাথে তুলনা করা যায়। তাদের মানচিত্রে পাহাড়, নদী, রাষ্ট্র আর সেনাবাহিনী ছিল, কিন্তু মানুষের বিশ্বাসের জগৎটা ছিল অনুপস্থিত। তারা এমন এক পৃথিবীর ছবি এঁকেছিলেন যা কেবল বস্তুগত শক্তি দিয়ে চালিত হয়। তাদের কাছে রাষ্ট্র ছিল একটি যন্ত্রের মতো, যার আচরণ কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম দিয়ে বোঝা সম্ভব। এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম ছিল একটি অপ্রয়োজনীয়, গোলমেলে এবং ‘অবৈজ্ঞানিক’ বিষয়, যা গণনার বাইরে রাখাই শ্রেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে ছিল ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের গভীর প্রভাব, যা যুক্তিকে (Reason) বিশ্বাসের ওপরে স্থান দিয়েছিল।
হ্যান্স মরগেনথাউ (Hans Morgenthau) ও বাস্তববাদের শীতল পৃথিবী: মরগেনথাউকে বাস্তববাদ (Realism) নামক তত্ত্বের অন্যতম জনক বলা হয়। তার বিখ্যাত বই ‘পলিটিক্স অ্যামং নেশনস’ (Politics Among Nations)-এ তিনি যে পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন, তা বড়ই শীতল ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মানুষের প্রকৃতি ক্ষমতার জন্য চিরন্তন লোভী। আর এই প্রকৃতিই আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। তার মতে, রাষ্ট্রগুলো কেবলই ক্ষমতা চায় এবং নিজেদের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে চায়। এই পৃথিবীতে নৈতিকতা বা আদর্শের কোনো স্থান নেই, যদি না তা জাতীয় স্বার্থ (National Interest) পূরণে সাহায্য করে (Morgenthau, 1948)।
মরগেনথাউয়ের দূরবীনে ধর্ম ছিল এমনই এক গৌণ বিষয়। ধর্মকে বড়জোর একটি মতাদর্শিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা দিয়ে জনগণকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায় বা কোনো আগ্রাসনকে বৈধতা দেওয়া যায়। কিন্তু ধর্ম নিজে থেকে কখনো পররাষ্ট্রনীতির চালিকাশক্তি হতে পারে না। চালিকাশক্তি হলো ক্ষমতার প্রতি মানুষের আদিম ও অপরিবর্তনীয় আকাঙ্ক্ষা। তার মানচিত্রে সৌদি আরব ও ইরানের দ্বন্দ্বের কারণ তেল, ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব এবং সামরিক শক্তি; সুন্নি-শিয়া বিভাজনটা হলো সেই আসল খেলার ওপর একটি আরোপিত আবরণ মাত্র। একজন বাস্তববাদী শাসকের কাছে ধর্ম হলো রাজার হাতের তুরুপের তাসের মতো – দরকার পড়লে ব্যবহার করা হবে, কিন্তু খেলার মূল নিয়ম নির্ধারণ করবে ক্ষমতা, বিশ্বাস নয়।
কেনেথ ওয়াল্টজ (Kenneth Waltz) ও কাঠামোর কারাগার: মরগেনথাউ যদি মানব প্রকৃতির ওপর জোর দিয়ে থাকেন, তবে কেনেথ ওয়াল্টজ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামোর (Structure) ওপর জোর দিয়েছেন। তার নব্য-বাস্তববাদ (Neo-realism) তত্ত্ব অনুযায়ী, রাষ্ট্রগুলো কেমন আচরণ করবে তা তাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্র (যেমন ধর্ম বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা) দিয়ে নির্ধারিত হয় না, বরং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নৈরাজ্যকর (Anarchic) কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত হয় (Waltz, 1979)।
ওয়াল্টজের কাছে রাষ্ট্রগুলো বিলিয়ার্ড বলের মতো। বাইরে থেকে তাদের রঙ ভিন্ন হতে পারে – কোনোটা লাল, কোনোটা নীল – কিন্তু বিলিয়ার্ড টেবিলের কাঠামোর চাপে পড়লে তারা সবাই পদার্থবিজ্ঞানের একই নিয়মে চলে। একইভাবে, একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিচয় যাই হোক না কেন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নৈরাজ্যকর কাঠামো তাকে আত্মরক্ষার জন্য ক্ষমতা বাড়াতে বাধ্য করে। এক রাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র কিনলে, পাশের রাষ্ট্রটি তাকে হুমকি হিসেবে দেখে এবং আরও বেশি অস্ত্র কেনে। এই ‘নিরাপত্তা উভয়সংকট’ (Security Dilemma) তৈরি হয় কাঠামোর কারণে, রাষ্ট্রের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নয়। এই কাঠামোগত কারাগারে ধর্মের মতো অভ্যন্তরীণ বিষয়ের কোনো স্থান নেই। তার তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি গণতান্ত্রিক ভারত, একটি কমিউনিস্ট চীন বা একটি ইসলামিক পাকিস্তান – সবাই পারমাণবিক বোমা বানাতে চাইবে, কারণ নৈরাজ্যকর বিশ্বে টিকে থাকার জন্য ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। তাদের ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পরিচয় এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।
বাস্তববাদের বাইরেও এক নীরব ঐক্যমত্য: শুধু বাস্তববাদীরাই নন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যান্য প্রধান তত্ত্বগুলোও ধর্মকে তাদের মানচিত্রের বাইরে রেখেছিল। উদারতাবাদীরা (Liberals) বিশ্বাস করতেন, গণতন্ত্র, মুক্ত বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রসারের মাধ্যমে এক শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব। তাদের চোখে, ধর্ম ছিল এক প্রাক-আধুনিক যুগের অবশেষ, যা আধুনিকতার আলোয় মিলিয়ে যাবে। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা (Francis Fukuyama) স্নায়ুযুদ্ধের শেষে যখন ঘোষণা করলেন যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিজয়ের মাধ্যমে ‘ইতিহাসের সমাপ্তি’ (The End of History) ঘটেছে, তখন তিনি আসলে এই ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী বিশ্বব্যবস্থার চূড়ান্ত বিজয়ের কথাই বলছিলেন (Fukuyama, 1992)। তাদের মানচিত্রে ছিল আপস-সম্পর্কযুক্ত বাজার আর গণতান্ত্রিক সংসদ, সেখানে গির্জা বা মসজিদের কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না।
অন্যদিকে, মার্ক্সবাদীরা (Marxists) বিশ্বকে দেখতেন শ্রেণী সংগ্রামের চশমা দিয়ে। তাদের মানচিত্রে রাষ্ট্র বা সভ্যতার বদলে ছিল শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী আর শোষিত প্রলেতারিয়েত। আর ধর্ম? ধর্ম ছিল সেই আফিম যা দিয়ে শাসক শ্রেণী শোষিতদের ঘুম পাড়িয়ে রাখে, যাতে তারা নিজেদের আসল দুর্দশার কথা ভুলে পরকালের স্বপ্নে বিভোর থাকে।
এই বাস্তববাদী, উদারতাবাদী এবং মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি ‘বিজ্ঞান’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যেখানে সবকিছু বস্তুগত শক্তি আর কাঠামোর নিরিখে মাপা যায়। ধর্ম, যা পরিমাপ করা কঠিন এবং আবেগের সাথে জড়িত, তা তাদের এই বৈজ্ঞানিক মডেলে খাপ খায়নি। তাই তারা একে সচেতনভাবেই আলোচনার বাইরে রেখেছিলেন। তাদের নিখুঁত মানচিত্রে বিশ্বাসের কোনো মহাদেশের অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু খুব শীঘ্রই এই মানচিত্রগুলো বিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হতে শুরু করে।
নতুন দিনের ভাবনারা: যারা মানচিত্রে ধর্মের সীমানা আঁকলেন
স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর যখন বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় সংঘাত ও পরিচয়ের রাজনীতি তীব্র হয়ে উঠল, তখন পুরনো মানচিত্রগুলো যে কতটা অপর্যাপ্ত, তা স্পষ্ট হয়ে গেল। পুরনো কার্টোগ্রাফারদের আঁকা পৃথিবীতে রাষ্ট্রগুলো ছিল যৌক্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ অভিনেতা। কিন্তু নতুন পৃথিবীতে দেখা গেল, অভিনেতারা প্রায়শই তাদের ধর্মীয় পরিচয় দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এই সময়ে কয়েকজন চিন্তাবিদ এগিয়ে এলেন, যারা মানচিত্রে ধর্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান তৈরি করলেন। তারা দেখালেন যে, ধর্মকে বাদ দিয়ে নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে বোঝা অসম্ভব।
স্যামুয়েল হান্টিংটন (Samuel P. Huntington) ও সভ্যতার সংঘাত: হান্টিংটন ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শান্ত, অ্যাকাডেমিক জগতে একটি বোমা ফেলেছিলেন। ১৯৯৩ সালে ‘ফরেন অ্যাফেয়ার্স’ (Foreign Affairs) জার্নালে প্রকাশিত তার ‘দ্য ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশনস?’ (The Clash of Civilizations?) প্রবন্ধ এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত বইটিতে তিনি যুক্তি দেন যে, স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে সংঘাতের মূল উৎস আর রাষ্ট্র বা মতাদর্শ থাকবে না। বরং সংঘাত হবে বিশ্বের প্রধান সভ্যতাগুলোর (Civilizations) মধ্যেকার ‘ফল্ট লাইন’ বা বিভাজন রেখা বরাবর। আর এই সভ্যতাগুলোর মূল ভিত্তি কী? ধর্ম। হান্টিংটন পৃথিবীকে মোটামুটি সাত-আটটি প্রধান সভ্যতায় ভাগ করেছিলেন: পাশ্চাত্য (Western), কনফুসীয় (Confucian), জাপানি (Japanese), ইসলামী (Islamic), হিন্দু (Hindu), স্লাভিক-অর্থোডক্স (Slavic-Orthodox), লাতিন আমেরিকান (Latin American) এবং সম্ভবত আফ্রিকান (African) (Huntington, 1996)।
তার মূল বক্তব্য ছিল, বিশ্বায়ন মানুষকে কাছাকাছি আনার বদলে তাদের মধ্যকার সভ্যতার ভিন্নতাকেই আরও বেশি করে চিনিয়ে দিচ্ছে। একজন বসনিয়াক মুসলিম সার্ব অর্থোডক্স বা ক্রোট ক্যাথলিকের সাথে থাকার চেয়ে একজন তুর্কি বা আরব মুসলিমের সাথে বেশি একাত্ম বোধ করবে। তাই ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলো হবে ‘পশ্চিম বনাম বাকি বিশ্ব’ (The West versus the Rest) এবং ইসলামী সভ্যতার রক্তাক্ত সীমানা বরাবর। বলকান যুদ্ধ, চেচনিয়া, কাশ্মীর বা নাইজেরিয়ার সংঘাতকে তিনি তার তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে হাজির করেন। ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলার পর তার তত্ত্বটি যেন এক ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা পায় এবং নীতিনির্ধারক মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে শুরু করে।
হান্টিংটনের তত্ত্বটি প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হয়। এডওয়ার্ড সাঈদের (Edward Said) মতো সমালোচকরা একে ‘অজ্ঞতার সংঘাত’ (Clash of Ignorance) বলে অভিহিত করেন। তাদের মতে, হান্টিংটন ‘ইসলাম’ বা ‘পশ্চিম’-এর মতো সভ্যতাগুলোকে একেকটি একাট্টা, অপরিবর্তনশীল এবং অভ্যন্তরীণভাবে সংঘাতহীন সত্তা হিসেবে দেখিয়েছেন, যা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ভুল। অমর্ত্য সেন (Amartya Sen) তার ‘আইডেন্টিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স’ (Identity and Violence) বইতে দেখান যে, মানুষকে কেবল তার ধর্মীয় বা সভ্যতার পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করাটা বিপজ্জনক। একজন মানুষের একই সাথে অনেক পরিচয় থাকতে পারে – সে হতে পারে একজন ভারতীয়, একজন মুসলিম, একজন প্রকৌশলী, একজন নারী এবং একজন গণতন্ত্রের সমর্থক। শুধু একটি পরিচয়কে প্রধান করে দেখাটাই সহিংসতার জন্ম দেয় (Sen, 2006)। এত সমালোচনা সত্ত্বেও, হান্টিংটনকে কৃতিত্ব দিতেই হবে যে, তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সংস্কৃতি ও ধর্মের গুরুত্ব নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি সেই নীরবতাকে ভেঙেছিলেন, যা কয়েক দশক ধরে এই বিষয়টিকে ঘিরে ছিল।
হোসে কাসানোভা (José Casanova) ও ধর্মের ‘অপবিত্রায়ন’: হান্টিংটন যেখানে ধর্মকে মূলত সংঘাতের উৎস হিসেবে দেখেছেন, সেখানে সমাজবিজ্ঞানী হোসে কাসানোভা এর ফিরে আসার প্রক্রিয়াটিকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার প্রভাবশালী বই ‘পাবলিক রিলিজিয়নস ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড’ (Public Religions in the Modern World)-এ তিনি ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তত্ত্ব’কে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি বলেন, আধুনিকতার মানে এই নয় যে ধর্ম অদৃশ্য হয়ে যাবে। বরং যা ঘটেছে, তা হলো ধর্মের ‘অপবিত্রায়ন’ (Deprivatization)। অর্থাৎ, ধর্ম যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত হয়েছিল, তা আবার জনজীবনে ফিরে আসছে। তবে এই ফিরে আসা মানে পুরনো দিনের মতো রাষ্ট্রের ওপর ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নয়। কাসানোভা তিনটি উপায়ে এই ফিরে আসাকে ব্যাখ্যা করেন:
- রাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে নৈতিক সমালোচনা হিসেবে: ধর্ম এখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতির (যেমন: গর্ভপাত, পরিবেশ দূষণ, যুদ্ধ) বিরুদ্ধে একটি নৈতিক অবস্থান থেকে কথা বলছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলনে কৃষ্ণাঙ্গ চার্চের ভূমিকা বা লাতিন আমেরিকায় লিবারেশন থিওলজির (Liberation Theology) আন্দোলন।
- রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে: ধর্মীয় সংগঠনগুলো এখন সরাসরি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে। যেমন, পোল্যান্ডে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সলিডারিটি আন্দোলনে ক্যাথলিক চার্চের ভূমিকা বা বিভিন্ন দেশে ইসলামিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশগ্রহণ।
- জাতীয় পরিচয়ের ধারক হিসেবে: অনেক দেশে, বিশেষ করে যেখানে জাতীয়তাবাদ দুর্বল, সেখানে ধর্মই জাতীয় পরিচয়ের প্রধান উপাদান হয়ে উঠছে। যেমন, ইরানে শিয়া ইসলামের ভূমিকা বা সার্বিয়ার জন্য অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মের গুরুত্ব।
কাসানোভার মতে, ধর্মের এই পুনরাবির্ভাব মানেই রাষ্ট্র ও ধর্মের পুরনো সংঘাতময় সম্পর্কে ফিরে যাওয়া নয়। বরং ধর্ম এখন আধুনিক, গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেই একটি নাগরিক শক্তি (Civil Society Actor) হিসেবে কাজ করতে পারে, যা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে প্রশ্ন করে এবং নৈতিকতার প্রশ্নগুলোকে পাবলিক বিতর্কে ফিরিয়ে আনে (Casanova, 1994)। তার বিশ্লেষণ হান্টিংটনের চেয়ে অনেক বেশি আশাবাদী এবং জটিল।
জিল কেপেল (Gilles Kepel) ও ঈশ্বরের প্রতিশোধ: ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জিল কেপেল তার ‘দ্য রিভেঞ্জ অফ গড’ (The Revenge of God) বইতে সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় পুনরুত্থানের একটি চমৎকার ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এটি কেবল কোনো একটি ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ছিল একটি বৈশ্বিক ঘটনা, যা প্রায় একই সময়ে ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্মের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। ইরানে ইসলামিক বিপ্লব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘মরাল মেজরিটি’র (Moral Majority) মতো ইভানজেলিকাল খ্রিস্টানদের উত্থান, এবং ইসরায়েলে ‘গুশ এমুনিম’ (Gush Emim) এর মতো উগ্র ইহুদি বসতি স্থাপনকারী আন্দোলনের উত্থান – এই সবই ছিল একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কেপেলের মতে, এই পুনরুত্থানের মূল কারণ ছিল ষাটের দশকের ধর্মনিরপেক্ষ এবং বামপন্থী মতাদর্শগুলোর ব্যর্থতা। এই মতাদর্শগুলো মানুষকে যে মুক্তি ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তা পূরণ করতে না পারায় মানুষ আবার পরিত্রাণের জন্য ধর্মের দিকে ফিরে যায় (Kepel, 1994)। কেপেলের কাজ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, ধর্মের পুনরাবির্ভাব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি আধুনিকতার সংকটের একটি বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া।
এই নতুন দিনের ভাবনারা আমাদের হাতে এমন এক মানচিত্র তুলে দিয়েছেন, যেখানে ধর্মের সীমানাগুলো স্পষ্টভাবে আঁকা। তারা দেখিয়েছেন যে, এই সীমানাগুলো কখনো বিভেদ তৈরি করে, আবার কখনোবা নতুন ধরনের ঐক্যের জন্ম দেয়। তাদের কাজ ছাড়া একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতি বোঝা একরকম অসম্ভব।
গভীরের ডুবুরিরা: যারা ধর্মের দ্বৈত চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন
ধর্ম কেবল বিশ্ব রাজনীতিতে ফিরে আসেনি; এটি ফিরে এসেছে এক জটিল ও পরস্পরবিরোধী রূপ নিয়ে। এটি একদিকে যেমন সহিংসতার জন্ম দিচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠারও অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। এই জটিল দ্বৈত চরিত্রকে বুঝতে চেয়েছেন আরেক দল চিন্তাবিদ। তারা শুধু ধর্মের উপস্থিতিকেই স্বীকার করেননি, বরং এর ভেতরের কার্যকারণ বোঝার জন্য গভীরের ডুবুরির মতো কাজ করেছেন।
আর. স্কট অ্যাপলবাই (R. Scott Appleby) ও পবিত্রের দ্ব্যর্থকতা: স্কট অ্যাপলবাই তার যুগান্তকারী কাজ ‘দি অ্যাম্বিভ্যালেন্স অফ দ্য স্যাক্রেড’ (The Ambivalence of the Sacred)-এ এই দ্বৈত চরিত্রের এক অসাধারণ বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। তার মূল বক্তব্য হলো, প্রায় সব ধর্মের ভেতরেই দুটি ধারা পাশাপাশি অবস্থান করে। একটি ধারা হলো চরমপন্থী, অসহিষ্ণু এবং সহিংস (Extremist)। অন্য ধারাটি হলো সহনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শান্তিবাদী (Pacifist)। কোন সময়ে কোন ধারাটি প্রভাবশালী হয়ে উঠবে, তা নির্ভর করে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর।
অ্যাপলবাই দেখান যে, ধর্মীয় নেতারা এবং সংগঠনগুলো ‘ধর্মীয় মধ্যস্থতাকারী’ (Religious Intermediaries) হিসেবে কাজ করে। উগ্রপন্থী নেতারা ধর্মগ্রন্থের বাছাই করা অংশ ব্যবহার করে ঘৃণা ও সহিংসতাকে উস্কে দেন। অন্যদিকে, শান্তিকামী নেতারা সেই একই ধর্মগ্রন্থ থেকে ক্ষমা, দয়া এবং সম্প্রীতির বাণী খুঁজে বের করে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেন। ধর্ম নিজে ভালোও নয়, মন্দও নয়; এটি একটি ‘দ্ব্যর্থক’ (Ambivalent) শক্তি। তাই আমাদের কাজ হলো সেই সব পরিস্থিতি এবং নেতৃত্বকে চেনা ও সমর্থন করা, যা ধর্মের শান্তিবাদী ধারাকে শক্তিশালী করে (Appleby, 2000)। তার এই বিশ্লেষণ আমাদের ধর্মকে সাদা-কালো বাইনারিতে দেখার প্রবণতা থেকে মুক্তি দেয় এবং এর জটিলতাকে স্বীকার করতে শেখায়।
মার্ক জুর্গেনসমেয়ার (Mark Juergensmeyer) ও মহাজাগতিক যুদ্ধ: কেন ধর্মীয় সহিংসতা এত নৃশংস এবং আপসহীন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন সমাজবিজ্ঞানী মার্ক জুর্গেনসমেয়ার। তার বিখ্যাত বই ‘টেরর ইন দ্য মাইন্ড অফ গড’ (Terror in the Mind of God)-এ তিনি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের মনোজগৎ বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই ব্যক্তিরা তাদের লড়াইকে সাধারণ রাজনৈতিক বা জাগতিক লড়াই হিসেবে দেখে না। তারা মনে করে, তারা এক ‘মহাজাগতিক যুদ্ধে’ (Cosmic War) লিপ্ত – যা ভালো এবং মন্দের মধ্যে, ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে এক অনন্তকালীন সংগ্রামের অংশ।
এই মহাজাগতিক যুদ্ধের ধারণাটি সন্ত্রাসীদের কাজকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেয়: (১) এটি তাদের লড়াইকে একটি পরম নৈতিক বৈধতা দেয়; (২) এখানে কোনো জাগতিক নিয়মের (যেমন, নিরীহ মানুষ না মারা) তোয়াক্কা করার প্রয়োজন নেই; এবং (৩) এখানে আপসের কোনো সুযোগ নেই, কারণ মন্দের সাথে আপস করা যায় না। এই মনস্তত্ত্ব বুঝতে না পারলে, ৯/১১-এর হামলাকারী বা আইসিসের যোদ্ধাদের উদ্দেশ্য বোঝা অসম্ভব (Juergensmeyer, 2003)। জুর্গেনসমেয়ার দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ নিছক পাগলামি নয়, এর পেছনে একটি নিজস্ব যুক্তি ও বিশ্ববীক্ষা রয়েছে, যা আমাদের বুঝতে হবে।
মনিকা টফট (Monica Duffy Toft) ও ধর্মের পক্ষে বাজি: সাম্প্রতিক সময়ে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনিকা টফট তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ধর্মকে প্রায়শই সংঘাতের কারণ হিসেবে দেখা হলেও, অনেক সময় এটি সংঘাতের স্থায়িত্ব এবং ফলাফলের ওপরও প্রভাব ফেলে। তিনি তার সহ-লেখকদের সাথে ‘গড’স সেঞ্চুরি’ (God’s Century) বইতে যুক্তি দেন যে, বিংশ শতাব্দীতে ধর্মীয় অভিনেতাদের (Religious Actors) উত্থান বিশ্ব রাজনীতিকে গভীরভাবে পরিবর্তন করেছে (Toft, Philpott, & Shah, 2011)। তারা দেখান যে, যখন কোনো গৃহযুদ্ধে এক পক্ষ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় যুদ্ধ করে, তখন তাদের জেতার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস যোদ্ধাদের অসীম মনোবল জোগায় এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে, তারা এও দেখান যে, ধর্মীয় মধ্যস্থতায় যে শান্তি চুক্তিগুলো হয়, সেগুলো অনেক বেশি টেকসই হয়। কারণ ধর্মীয় নেতারা চুক্তির পবিত্রতা রক্ষা করতে উভয় পক্ষকে নৈতিকভাবে বাধ্য করতে পারেন।
ডগলাস জনস্টন (Douglas Johnston) ও কূটনীতির হারানো মাত্রা: যখন অ্যাকাডেমিকরা তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত, তখন ডগলাস জনস্টনের মতো প্রাক্তন কূটনীতিক এবং চিন্তাবিদরা এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে ভেবেছেন। তিনি এবং তার সহকর্মীরা ‘রিলিজিয়ন, দ্য মিসিং ডাইমেনশন অফ স্টেটক্র্যাফট’ (Religion, the Missing Dimension of Statecraft) বইটিতে যুক্তি দেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের কূটনীতিকরা ধর্মকে উপেক্ষা করে এক বিরাট ভুল করছেন। ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার কারণে তারা ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব, ধর্মীয় অনুপ্রেরণার শক্তি এবং সংঘাত নিরসনে ধর্মের ভূমিকাকে বুঝতে ব্যর্থ হন।
জনস্টন দেখান যে, অনেক সংঘাতে ধর্মীয় নেতারা এমন ভূমিকা পালন করতে পারেন, যা সেকুলার কূটনীতিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তাদের নৈতিক কর্তৃত্ব আছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস আছে এবং তারা দীর্ঘমেয়াদে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি ‘ধর্মীয় কূটনীতি’ (Faith-Based Diplomacy) নামক একটি ধারণার প্রবর্তন করেন এবং রাষ্ট্রগুলোকে পরামর্শ দেন যে, সংঘাত নিরসন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে শত্রু না ভেবে সহযোগী হিসেবে দেখতে হবে (Johnston & Sampson, 1994)।
এই তাত্ত্বিকদের কাজ আমাদের দেখায় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ধর্মকে বোঝাটা কোনো সহজ কাজ নয়। এটি একই সাথে পরিচয়, মতাদর্শ, রাজনৈতিক হাতিয়ার, সহিংসতার উৎস এবং শান্তির অনুপ্রেরণা। পুরনো, সরল মানচিত্রগুলো ফেলে দিয়ে আমাদের এখন এই নতুন, জটিল এবং বহুমাত্রিক মানচিত্রগুলো ব্যবহার করেই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকে বুঝতে হবে।
উপসংহার
আমরা এক দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা পথ পাড়ি দিলাম। ওয়েস্টফেলিয়ার ধূসর সকাল থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর কোলাহলপূর্ণ, ডিজিটাল পৃথিবীতে এসে থামলাম। এই দীর্ঘ যাত্রায় আমরা দেখলাম, ধর্ম নামক যে শক্তিটিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল আলোচনা থেকে একরকম নির্বাসিত করা হয়েছিল, তা আজ কতটা প্রাসঙ্গিক, কতটা শক্তিশালী এবং কতটা অনিবার্য হয়ে ফিরে এসেছে।
ব্যাপারটা অনেকটা পুরনো কোনো পরিত্যক্ত বাড়ির মতো। বাইরে থেকে দেখতে শান্ত, নির্জন। কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যায়, এর প্রতিটি ইট, প্রতিটি দেয়াল কোনো এক সময়ের গল্প বলছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চকচকে, আধুনিক অট্টালিকার আড়ালে ধর্ম হলো সেই পুরনো বাড়ির কাঠামো। বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু পুরো বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে তারই ওপর। একে বাদ দিয়ে, একে না বুঝে পুরো অট্টালিকার গঠন বোঝা অসম্ভব।
আমরা জেনেছি, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তত্ত্ব – যার সরল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে আধুনিকতার আলোয় ধর্মের ছায়া মিলিয়ে যাবে – অনেক ক্ষেত্রেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বায়ন, পরিচয়ের সংকট, রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং প্রযুক্তির বিস্ফোরণ ধর্মকে ব্যক্তিগত আলমারি থেকে বের করে এনে আবার জনজীবনের বিতর্কের কেন্দ্রে স্থাপন করেছে। ধর্ম এখন কেবল রবিবারের প্রার্থনা বা শুক্রবারের নামাজ নয়; এটি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক মতাদর্শ, পরিচয়ের বর্ম, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।
আমরা দেখেছি, ধর্ম একটি দ্বিমুখী তলোয়ার, যার এক পিঠে লেখা ধ্বংস, অন্য পিঠে সৃষ্টি। এটি যেমন হান্টিংটনের ‘সভ্যতার সংঘাত’ তত্ত্বের মতো বিভেদ ও অবিশ্বাসের প্রাচীর তুলতে পারে, তেমনই আর্চবিশপ টুটুর মতো ক্ষমা ও সম্প্রীতির সেতুও নির্মাণ করতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের সুন্নি-শিয়া দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকট পর্যন্ত ধর্ম যেমন সংঘাতের বারুদে আগুন দিয়েছে, তেমনই কমিউনিটি অফ সান্ত’এজিডিওর মতো সংগঠনগুলো বিশ্বজুড়ে কূটনীতি, শান্তি ও মানবিক সেবার নীরব দূত হিসেবে কাজ করে চলেছে।
তাহলে এই দীর্ঘ আলোচনার পর শেষ কথা কী দাঁড়াল? ধর্ম কি ভালো, নাকি খারাপ?
এই প্রশ্নটাই আসলে অবান্তর। ধর্ম ভালোও নয়, খারাপও নয়। এটি একটি শক্তি। অনেকটা পারমাণবিক শক্তির মতো। এই শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে লক্ষ লক্ষ ঘর আলোকিত করা যায়, আবার এর দ্বারাই হিরোশিমা-নাগাসাকির মতো ধ্বংসযজ্ঞও ঘটানো যায়। শক্তি নিজে নিরপেক্ষ; তার ব্যবহারই তাকে ভালো বা মন্দে রূপান্তরিত করে। ধর্ম নামক এই প্রচণ্ড সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তিকে কারা, কীভাবে, কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে – সেটাই আসল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।
আজকের পৃথিবীর নীতিনির্ধারক, কূটনীতিক, সাংবাদিক এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য ধর্মকে বোঝা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ব। ধর্মকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা, একে কেবল পিছিয়ে পড়া সমাজের বৈশিষ্ট্য বলে উড়িয়ে দেওয়া, অথবা একে শুধু ‘উগ্রপন্থা’ বা ‘সন্ত্রাসবাদ’ এর সমার্থক হিসেবে দেখা – এই সবগুলো পথই বিপজ্জনক এবং ভুল। এর জটিল, বহুমাত্রিক এবং কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী চরিত্রকে স্বীকার করেই আমাদের একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা, উগ্র ও অসহিষ্ণু বয়ানকে প্রতিহত করা, এবং ধর্মকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার বিপজ্জনক প্রবণতাকে উন্মোচিত করা – এটাই হয়তো আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি।
এই জটিল, গোলকধাঁধার মতো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আমাদের শেষ পর্যন্ত এটুকুই মানতে হবে যে, মানুষের হৃদয় থেকে বিশ্বাসকে মুছে ফেলা যায় না। আর যতদিন মানুষের মনে বিশ্বাস নামক এই গভীর অনুভূতিটি থাকবে, ততদিন ধর্ম বিশ্ব রাজনীতিতে তার অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে যাবে। সেই অদৃশ্য সুতোর জট খোলার চেষ্টা তাই কখনো শেষ হবে না। এটা একটা চলমান পাঠোদ্ধারের প্রক্রিয়া, যা আমাদের সবাইকে আরও ধৈর্য, আরও সহনশীলতা এবং আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চালিয়ে যেতে হবে।
ধর্ম নিয়ে বিস্তারিত জানতে যান এখানে – ধর্ম (Religion): এক মানবিক প্রপঞ্চের ব্যবচ্ছেদ
তথ্যসূত্র
- Anderson, B. (1983). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso.
- Angell, N. (1910). The great illusion: A study of the relation of military power in nations to their economic and social advantage. G.P. Putnam’s Sons.
- Appleby, R. S. (2000). The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation. Rowman & Littlefield Publishers.
- Barber, B. R. (1995). Jihad vs. McWorld: How globalism and tribalism are reshaping the world. Times Books.
- Berger, P. L. (1967). The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion. Doubleday.
- Berger, P. L. (Ed.). (1999). The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. University of Chicago Press.
- Doyle, M. W. (1986). Liberalism and world politics. American Political Science Review, 80(4), 1151–1169.
- Fair, C. C. (2014). Fighting to the end: The Pakistan Army’s way of war. Oxford University Press.
- Finnemore, M. (1996). National interests in international society. Cornell University Press.
- Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. Free Press.
- Haynes, J. (2007). An introduction to religion and international relations. Pearson Longman.
- Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations? Foreign Affairs, 72(3), 22–49.
- Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster.
- Johnston, D., & Sampson, C. (Eds.). (1994). Religion, the missing dimension of statecraft. Oxford University Press.
- Juergensmeyer, M. (2003). Terror in the mind of God: The global rise of religious violence. University of California Press.
- Kepel, G. (1994). The revenge of God: The resurgence of Islam, Christianity, and Judaism in the modern world. Pennsylvania State University Press.
- Kepel, G. (2002). Jihad: The trail of political Islam. Harvard University Press.
- Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W. W. Norton & Company.
- Morgenthau, H. J. (1948). Politics among nations: The struggle for power and peace. Alfred A. Knopf.
- Philpott, D. (2001). Revolutions in sovereignty: How ideas shaped modern international relations. Princeton University Press.
- Robertson, R. (1995). Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson (Eds.), Global modernities (pp. 25–44). Sage Publications.
- Said, E. W. (2001, October 22). The clash of ignorance. The Nation.
- Sen, A. (2006). Identity and violence: The illusion of destiny. W. W. Norton & Company.
- Thomas, S. M. (2005). The global resurgence of religion and the transformation of international relations: The struggle for the soul of the twenty-first century. Palgrave Macmillan.
- Toft, M. D., Philpott, D., & Shah, T. S. (2011). God’s century: Resurgent religion and global politics. W. W. Norton & Company.
- Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley Pub. Co.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. International Organization, 46(2), 391-425.