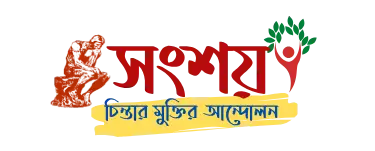ধর্ম (Religion): এক মানবিক প্রপঞ্চের ব্যবচ্ছেদ
Table of Contents
- 1 ভূমিকা
- 2 সংজ্ঞার চোরাবালি: ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করার যন্ত্রণা
- 3 জেনেসিসের সন্ধানে: ধর্মের জ্ঞানীয় ও মনস্তাত্ত্বিক উৎস
- 4 সামাজিক নীলনকশা: ধর্মের সামাজিক উৎস ও বিবর্তন
- 5 বিশ্বাসের মনস্তত্ত্ব: আমরা কেন এবং কীভাবে বিশ্বাস করি?
- 6 বিশ্বাসের বর্ণালী: ধর্মের প্রকারভেদ ও বৈচিত্র্য
- 7 ধর্মের শরীরতত্ত্ব: যা দিয়ে ধর্ম তৈরি হয়
- 7.1 বিশ্বাস, আখ্যান ও মতবাদ (Belief, Narrative, and Doctrine): ধর্মের মস্তিষ্ক
- 7.2 আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতীক (Ritual and Symbol): ধর্মের হৃদস্পন্দন
- 7.3 পবিত্র ও অপবিত্রের বিভাজন (The Sacred and the Profane): ধর্মের সীমানা
- 7.4 নৈতিক ও আইনি বিধিবিধান (Moral and Legal Codes): ধর্মের সংবিধান
- 7.5 ধর্মীয় অভিজ্ঞতা (Religious Experience): ধর্মের আত্মা
- 7.6 সামাজিক সংগঠন ও সম্প্রদায় (Social Organization and Community): ধর্মের শরীর
- 8 প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম: পবিত্রতার ধারক ও ক্ষমতার পিঞ্জর
- 9 সভ্যতার কারিগর: সমাজ ও সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব
- 10 পবিত্রতার ছায়া: ধর্মের অন্ধকার দিক
- 11 একুশ শতকে ধর্ম: সংকট ও রূপান্তর
- 12 চিন্তার কারিগর: যারা ধর্মকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন
- 13 উপসংহার: এক অসমাপ্ত মানবিক আখ্যান
- 14 তথ্যসূত্র
ভূমিকা
মানুষ বড় অদ্ভুত এক প্রাণী। সে একদিকে নক্ষত্রের দূরত্ব মাপে, কৃষ্ণগহ্বরের (Black Hole) ভেতরের মহাকর্ষীয় এককত্ব (Gravitational Singularity) নিয়ে জটিল গাণিতিক সমীকরণ তৈরি করে, আর অন্যদিকে মহাবিশ্বের অসীম, শীতল শূন্যতার দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য এক জগতের কাছে আশ্রয় খোঁজে। সেই না-দেখা জগতে তার ভয়, তার ভরসা, তার সান্ত্বনা – সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আর কল্পনার জগৎ, এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের চিরন্তন দ্বিধা, তার আদিম অনুসন্ধান, তার নিজের হাতে গড়া আশ্রয় – এর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জটিল আর সবচেয়ে প্রভাবশালী রূপটির নামই সম্ভবত ধর্ম।
ধর্ম কী? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। আপনি যদি দশজন ভিন্ন মানুষকে এই প্রশ্ন করেন, সম্ভবত দশটি ভিন্ন উত্তর পাবেন। কেউ বলবে, ধর্ম হলো ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস আর তাঁর আরাধনা। কেউ বলবে, এটি কিছু আচার-অনুষ্ঠান আর কঠোর নৈতিক নিয়মের সমষ্টি, যা আমাদের ভালো-মন্দ চেনায়। আবার একজন সমাজবিজ্ঞানী হয়তো বলবেন, ধর্ম হলো সমাজের মানুষকে একসাথে বেঁধে রাখার এক আশ্চর্য সামাজিক আঠা (Social Glue)। একজন মনোবিজ্ঞানী বলবেন, এটি আমাদের মৃত্যুভয়, একাকীত্ব আর অস্তিত্বের অর্থহীনতাকে মোকাবেলা করার এক পরিশীলিত মানসিক কৌশল (Coping Mechanism)। এই সবগুলো কথাই কোনো না কোনো দিক থেকে সত্যি, কিন্তু কোনোটিই সম্পূর্ণ চিত্রটি তুলে ধরে না। ধর্ম একটা বিশাল হাতির মতো, আর আমরা সবাই যেন সেই প্রাচীন গল্পের অন্ধের দল। যে যার মতো করে হাতিটাকে ছুঁয়ে দেখছি আর ভাবছি, এটাই বুঝি হাতির আসল রূপ। কেউ তার পা ধরে ভাবছে এটা একটা থাম, কেউ শুঁড় ধরে ভাবছে সাপের মতো, কেউ কান ধরে ভাবছে কুলোর মতো। কিন্তু আসল হাতিটা এর থেকেও অনেক বড়, অনেক বেশি জটিল এবং তার চেয়েও বেশি রহস্যময়।
এই লেখায় আমরা সেই বিশাল হাতিটাকে কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের চশমা দিয়ে দেখব না। বরং আমরা চেষ্টা করব কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে, চারপাশ থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করার। আমাদের উদ্দেশ্য কোনো বিশ্বাসকে মহিমান্বিত করা বা হেয় করা নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো, ‘বিশ্বাস’ নামের এই গভীরভাবে মানবিক অনুভূতিটা কেন তৈরি হলো, কীভাবে তা হাজার হাজার বছর ধরে মানব সমাজ ও সভ্যতাকে গড়ল ও ভাঙল, আর আজকের এই দ্রুত পরিবর্তনশীল, প্রযুক্তিচালিত বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতাই বা কতটুকু – সেই জটিল ধাঁধার কিছু অংশ উন্মোচন করার চেষ্টা করা। এটা অনেকটা বিশাল এক জিগস পাজল (Jigsaw Puzzle) মেলানোর মতো, যার হাজার হাজার টুকরো ছড়িয়ে আছে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, দর্শন আর স্নায়ুবিজ্ঞানের (Neuroscience) অলিগলিতে। চলুন, সেই টুকরোগুলো এক এক করে জোড়া লাগানোর এক দীর্ঘ ও আকর্ষণীয় সফরে বের হওয়া যাক। এই সফরে আমরা ধর্মের সংজ্ঞায়ন থেকে শুরু করে তার উৎপত্তি, বিবর্তন, মনোবিজ্ঞান, সমাজ ও সভ্যতার উপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব এবং তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পর্যন্ত অনুসন্ধান করব। এই দীর্ঘ পথচলায় কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেয়ে নতুন নতুন প্রশ্ন তৈরি করাটাই হয়তো বেশি জরুরি হবে। কারণ কিছু প্রশ্ন আছে, যার উত্তর খোঁজার মধ্যেই মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিযানগুলো লুকিয়ে থাকে। আর ধর্ম নিঃসন্দেহে সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে অন্যতম।
সংজ্ঞার চোরাবালি: ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করার যন্ত্রণা
কোনো বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় নামার আগে সেটার একটা কার্যকরী সংজ্ঞা (Working Definition) বা অন্তত একটা সাধারণ পরিচয় ঠিক করে নেওয়াটা জরুরি। এটা অনেকটা কোনো অজানা দেশে যাওয়ার আগে তার একটা মানচিত্র দেখে নেওয়ার মতো। মানচিত্রটা হয়তো দেশটির আসল সৌন্দর্যের বা জটিলতার কিছুই তুলে ধরে না, কিন্তু পথ চলতে সাহায্য করে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে এই মানচিত্র আঁকার কাজটাই প্রায় অসম্ভব, যেন এক অন্তহীন চোরাবালিতে পা রাখা। এখানে কোনো শক্ত ভূমি নেই, যার ওপর দাঁড়িয়ে পুরো ভূখণ্ডটা দেখা যায়। কারণ পৃথিবীতে হাজার হাজার ধর্ম প্রচলিত আছে এবং তাদের মধ্যে বাহ্যিক মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। তাদের বিশ্বাস, আচার, আর নৈতিকতার জগৎ এতটাই বিচিত্র যে, সবগুলোকে এক ছাতার তলায় আনার যেকোনো প্রচেষ্টা হাস্যকরভাবে অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়।
একটু ভেবে দেখুন। ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম বা ইহুদি ধর্মের মতো আব্রাহামিক ধর্মগুলোতে (Abrahamic Religions) একজন সর্বশক্তিমান, ব্যক্তি-সদৃশ ঈশ্বরের (Personal God) ধারণা কেন্দ্রীয়। তিনিই এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক এবং চূড়ান্ত বিচারক। তার ইচ্ছা, তার আইন, তার বাণীই সবকিছু। আবার অন্যদিকে, হিন্দুধর্মের বিশাল জগতে প্রবেশ করলে আমরা দেখি বহুদেবতার (Polytheism) এক বর্ণাঢ্য সমাবেশ, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব থেকে শুরু করে হাজারো দেব-দেবী রয়েছেন। কিন্তু এর দার্শনিক গভীরে প্রবেশ করলে আবার একেশ্বরবাদের (Monotheism) ধারা পাওয়া যায় (যেমন: বৈষ্ণব বা শৈব ধর্ম), সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) ছোঁয়া মেলে (যেমন: অদ্বৈত বেদান্ত, যেখানে ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন), বা এমনকি নাস্তিক্যবাদেরও (Atheism) শক্তিশালী যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় (যেমন: সাংখ্য বা মীমাংসা দর্শন)।
এই গোলকধাঁধা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন আমরা প্রাচ্যের দিকে তাকাই। বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্মের মতো প্রভাবশালী ধর্মগুলো মূলত নিরীশ্বরবাদী (Nontheistic)। সেখানে কোনো স্রষ্টা ঈশ্বরের ধারণা নেই, বা থাকলেও তা গৌণ এবং নির্বাণ লাভের পথে অপ্রয়োজনীয়। আত্মনিয়ন্ত্রণ, অহিংসা, নৈতিক উৎকর্ষ এবং নির্বাণ (Nervana) বা মোক্ষলাভই (Moksha) সেখানে মূল লক্ষ্য। ঈশ্বরের উপাসনার চেয়ে নিজের চেতনার উন্মোচনই সেখানে প্রধান। আবার জাপানের শিন্তো (Shinto) ধর্মে প্রকৃতি এবং পূর্বপুরুষদের আত্মা বা ‘কামি’ (Kami)-দের উপাসনা করা হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সর্বপ্রাণবাদে (Animism) বিশ্বাস করা হয় যে, শুধু মানুষ বা প্রাণী নয়, গাছপালা, নদী, পাহাড়, পাথর – সবকিছুর মধ্যেই আত্মা বা প্রাণশক্তি (Spirit) বিদ্যমান।
তাহলে এই এত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও আচরণকে – কোথাও একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, কোথাও হাজারো দেবতা, কোথাও কোনো ঈশ্বরই নেই, আবার কোথাও বা পাথরের আত্মা – আমরা কোন সাধারণ নামে ডাকব? কোন জাদুকরী সংজ্ঞার ফিতে দিয়ে এই বিচিত্র রূপগুলোকে একসাথে বাঁধব? এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও ধর্মতাত্ত্বিকরা মূলত দুটি ভিন্ন পথে হাঁটার চেষ্টা করেছেন। একটি পথ ধর্মের ‘ভেতরে কী আছে’ তা নিয়ে আগ্রহী, অন্যটি ‘ধর্ম কী কাজ করে’ তা নিয়ে।
উপাদানভিত্তিক সংজ্ঞা (Substantive Definition): ‘ভেতরে কী আছে?’
এই ধরনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, ধর্ম কী ‘বিশ্বাস’ করে বা ধর্মের ‘বিষয়বস্তু’ কী, তার ওপর জোর দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ধর্মের একটি অপরিহার্য বা মৌলিক উপাদান খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়, যা সব ধর্মের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এর সবচেয়ে ক্লাসিক এবং প্রভাবশালী উদাহরণ হলো উনিশ শতকের ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী স্যার এডওয়ার্ড টাইলরের (Edward Tylor) দেওয়া সংজ্ঞা। তার মতে, ধর্মের সবচেয়ে সরল ও মৌলিক ভিত্তি হলো “আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাস” (Belief in Spiritual Beings) (Tylor, 1871)। টাইলরের জন্য, এটিই ছিল ধর্মের সর্বনিম্ন সংজ্ঞা (Minimum Definition)। এই সংজ্ঞাটি তার সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল, কারণ এটি খুব সরল এবং এর পরিধি বিশাল। এটি আফ্রিকার আদিবাসীর আত্মা-ভূত বিশ্বাস থেকে শুরু করে গ্রিকদের অলিম্পিয়ান দেবতা বা খ্রিস্টানদের একেশ্বর – সবকিছুকেই ধারণ করতে পারে।
কিন্তু এই সরলতার সমস্যাও গভীর। প্রথমত, বৌদ্ধধর্মের থেরবাদ শাখার মতো নিরীশ্বরবাদী বিশ্বাস ব্যবস্থাকে এই সংজ্ঞায় ফেলা কঠিন হয়ে যায়। একজন থেরবাদী ভিক্ষু হয়তো আত্মা বা আধ্যাত্মিক সত্তার চেয়ে কর্মফল বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিয়েই বেশি চিন্তিত। তার ধর্মচর্চার কেন্দ্রে কোনো ‘সত্তা’-র প্রতি বিশ্বাস নয়, বরং একটি দার্শনিক অনুশাসন। দ্বিতীয়ত, এই সংজ্ঞা ধর্মের সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকাটিকে প্রায় পুরোটাই উপেক্ষা করে যায়। ধর্ম কেন টিকে আছে, সমাজে এর কাজ কী – এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর এখানে মেলে না।
উপাদানভিত্তিক সংজ্ঞার আরেকটি প্রভাবশালী রূপ দিয়েছেন জার্মান-আমেরিকান ধর্মতাত্ত্বিক পল টিলিখ (Paul Tillich)। তিনি ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ‘পরম উদ্বেগের বিষয়’ (Ultimate Concern) হিসেবে (Dynamics of Faith, 1957)। টিলিখের মতে, যা কিছু একজন মানুষের কাছে পরম উদ্বেগের বিষয়, যা তার জীবনের চূড়ান্ত অর্থ নির্ধারণ করে দেয়, যা তার কাছে নিঃশর্ত, অসীম এবং পবিত্র – সেটিই তার ধর্ম। এই সংজ্ঞাটি টাইলরের চেয়ে অনেক বেশি নমনীয়। এর আওতায় শুধু প্রচলিত ধর্মগুলোই নয়, জাতীয়তাবাদ, সাম্যবাদ বা এমনকি বিজ্ঞানমনস্কতাকেও ফেলা যায়, যদি সেগুলো কোনো ব্যক্তির কাছে পরম উদ্বেগের বিষয় রূপ নেয়। একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী যখন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে, তখন ‘দেশ’ তার কাছে এক ধরনের ধর্মীয় রূপ লাভ করে। কিন্তু এই সংজ্ঞার সমস্যা হলো এটি এত বেশি ব্যাপক যে, প্রায় যেকোনো তীব্র আবেগ বা বিশ্বাসকেই ‘ধর্ম’ বলে চিহ্নিত করার ঝুঁকি থেকে যায়। ফুটবল ক্লাবের প্রতি কোনো ভক্তের অন্ধ আবেগও কি তাহলে ধর্ম?
কার্যকারিতানির্ভর সংজ্ঞা (Functional Definition): ‘ধর্ম কী কাজ করে?’
এই ধারার চিন্তাবিদরা ধর্মের বিষয়বস্তুর চেয়ে বেশি আগ্রহী হলেন ধর্ম ব্যক্তি বা সমাজের জন্য কী ‘কাজ’ করে, তার ওপর। অর্থাৎ, ধর্মের ভূমিকা বা ফাংশনটাই এখানে মুখ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে বিচার করা হয় তার মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক ফলাফলের ভিত্তিতে।
ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খাইম (Émile Durkheim) এই ধারার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ The Elementary Forms of the Religious Life-এ তিনি বলেন, ধর্ম হলো “পবিত্র (Sacred) বস্তু বা ধারণা সম্পর্কিত বিশ্বাস ও আচারের এক সমন্বিত ব্যবস্থা, যা একটি একক নৈতিক সম্প্রদায়ে (Moral Community) সকলকে একত্রিত করে, যাকে চার্চ বলা হয়” (Durkheim, 1912)। ডুর্খাইমের কাছে, ধর্মের মূল কাজ হলো সামাজিক সংহতি (Social Cohesion) বা একাত্মতা তৈরি করা। মানুষ যখন একসাথে কোনো কিছুকে ‘পবিত্র’ বলে মানে এবং সেই অনুযায়ী আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের তীব্র আবেগ ও একাত্মবোধ তৈরি হয়, যাকে তিনি বলেছেন ‘সম্মিলিত উচ্ছ্বাস’ (Collective Effervescence)। এই অনুভূতি অনেকটা বড় কোনো ফুটবল ম্যাচের গ্যালারিতে বা কোনো রক কনসার্টে হাজার হাজার মানুষের একসাথে গান গাওয়ার মতো, যেখানে ব্যক্তিগত সত্তা একটি বৃহত্তর সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এই সংজ্ঞার সুবিধা হলো, এটি নিরীশ্বরবাদী ধর্মকেও সহজে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এমনকি এর পরিধি বাড়িয়ে জাতীয়তাবাদের (Nationalism) মতো আধুনিক বিশ্বাসকেও ধর্মের আওতায় ফেলা যায়, কারণ সেগুলোও এক ধরনের পবিত্র প্রতীক (যেমন: জাতীয় পতাকা), পবিত্র আখ্যান (জাতীয় ইতিহাস) এবং আচার-অনুষ্ঠানের (জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া) মাধ্যমে সামাজিক সংহতি তৈরি করে।
জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) কাছে ধর্মের কাজ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং নেতিবাচক। তিনি ধর্মকে দেখেছেন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি উপজাত বা ‘উপরিকাঠামো’ (Superstructure) হিসেবে, যা শাসক শ্রেণীর শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তার সেই বিখ্যাত উক্তি, “ধর্ম হলো জনগণের আফিম” (Religion is the opium of the people), এই ধারণাই প্রকাশ করে যে, ধর্ম শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে পারলৌকিক সুখের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ইহলৌকিক শোষণ-বঞ্চনা আর দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে রাখে, ফলে তারা বিপ্লবের পথে না গিয়ে নিজেদের ভাগ্যকে মেনে নেয় (Marx, 1844)। এটিও একটি কার্যকারিতানির্ভর সংজ্ঞা, তবে এর দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ সমালোচনামূলক।
আবার, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) ধর্মকে দেখেছেন এক ধরনের সার্বজনীন অবসেসিভ নিউরোসিস (Universal Obsessional Neurosis) বা মানসিক ভ্রম (Illusion) হিসেবে। তিনি মনে করতেন, মানুষ শৈশবে যেমন তার অসহায় অবস্থায় শক্তিশালী বাবার কাছে সুরক্ষা ও ভালোবাসা চায়, প্রাপ্তবয়স্ক জীবনেও সে তেমনই প্রকৃতির রুদ্ররোষ, রোগ-শোক, মৃত্যু এবং জীবনের নানা অনিশ্চয়তার মুখে অসহায় বোধ করে। এই অসহায়ত্ব থেকে বাঁচতেই সে একজন শক্তিশালী ‘পিতৃপ্রতিম ঈশ্বরের’ (Father Figure) কল্পনা করে নিয়েছে, যিনি তাকে রক্ষা করবেন (The Future of an Illusion, 1927)। ফ্রয়েডের কাছে ধর্মের কাজ হলো এই গভীর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা, আমাদের অসহায়ত্বের মুখে এক কাল্পনিক সুরক্ষার চাদর বিছিয়ে দেওয়া।
ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞা (Interpretive Definition): ‘ধর্ম কী অর্থ বহন করে?’
বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে অনেক নৃবিজ্ঞানী ধর্মের উপাদান বা কার্যকারিতার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ধর্ম মানুষের কাছে কী ‘অর্থ’ বহন করে, তার ওপর। এই ধারার প্রধান প্রবক্তা হলেন মার্কিন নৃবিজ্ঞানী ক্লিফোর্ড গিয়ার্ৎস (Clifford Geertz)। তাঁর মতে, ধর্ম হলো “(১) এক ধরনের প্রতীক ব্যবস্থা (a system of symbols) যা (২) মানুষের মধ্যে শক্তিশালী, ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী মেজাজ ও প্রেরণা (moods and motivations) তৈরি করে (৩) অস্তিত্বের সাধারণ ক্রম সম্পর্কে ধারণা (conceptions of a general order of existence) তৈরি করার মাধ্যমে এবং (৪) এই ধারণাগুলোকে এমন এক বাস্তবতার আবরণে মুড়ে দেয় (clothing these conceptions with such an aura of factuality) যে (৫) এই মেজাজ ও প্রেরণাগুলো অনন্যভাবে বাস্তব বলে মনে হয়” (The Interpretation of Cultures, 1973)।
এই জটিল সংজ্ঞাটিকে একটু ভেঙে বোঝা যাক। গিয়ার্ৎস বলতে চেয়েছেন, ধর্ম কিছু প্রতীক (যেমন: ক্রস, চাঁদ-তারা, স্বস্তিকা) ও গল্পের মাধ্যমে আমাদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি অর্থপূর্ণ ধারণা বা ‘বিশ্বদৃষ্টি’ (Worldview) দেয়। এটি শুধু তাই নয়, ধর্ম আমাদের একটি ‘জীবন-দর্শন’ (Ethos) বা জীবনযাপনের পদ্ধতিও বাতলে দেয়। ধর্ম এই দুটিকে এমনভাবে মিলিয়ে দেয় যে, জীবনের অর্থ আর জীবনযাপনের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো, ধর্ম এই পুরো ব্যবস্থাকে এক ‘বাস্তবতার আবেশ’ (aura of factuality) দিয়ে মুড়ে দেয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মরমী অভিজ্ঞতা এবং সম্প্রদায়ের সম্মিলিত বিশ্বাস এই গল্পগুলোকে নিছক গল্প না রেখে পরম সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ফলে মানুষ সেই অনুযায়ী বাঁচতে ও মরতে প্রস্তুত থাকে।
সংজ্ঞার ঊর্ধ্বে: পারিবারিক সাদৃশ্য এবং ক্ষমতার প্রশ্ন
এই সব সংজ্ঞা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার – ধর্মের কোনো একক, সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। কোনোটি বড্ড বেশি সংকীর্ণ, কোনোটি আবার বড্ড বেশি ব্যাপক। এই পর্যায়ে এসে দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের (Ludwig Wittgenstein) ‘পারিবারিক সাদৃশ্য’ (Family Resemblance) ধারণাটি আমাদের পথ দেখাতে পারে। ভিটগেনস্টাইন প্রশ্ন করেছিলেন, ‘খেলা’ (Game) বলতে আমরা কী বুঝি? তাস খেলা, ফুটবল খেলা, দাবা খেলা, একা একা বল ছোড়া – এই সবকিছুর মধ্যে কি কোনো একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যা সব খেলার মধ্যেই বর্তমান? উত্তর হলো, না। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো না কোনো মিলের একটি জটিল জাল বোনা আছে। দাবা আর তাসের মধ্যে কৌশল আছে, ফুটবল আর বল ছোড়ার মধ্যে বল আছে, ফুটবল আর দাবার মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে। ধর্মগুলোর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। কোনো একটি বৈশিষ্ট্য (যেমন: ঈশ্বরে বিশ্বাস) সব ধর্মে নেই, কিন্তু তাদের মধ্যে বিশ্বাস, আচার, নৈতিকতা, সম্প্রদায়, পবিত্রের ধারণা ইত্যাদি নানা উপাদানের এক ধরনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়, যা দিয়ে আমরা তাদের ‘ধর্ম’ পরিবারভুক্ত হিসেবে শনাক্ত করতে পারি।
তবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে কিছু চিন্তাবিদ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, আমরা যে ‘ধর্ম’-এর একটি সার্বজনীন সংজ্ঞা খুঁজছি, সেই ‘ধর্ম’ নামক ধারণাটিই কি সার্বজনীন ? নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ (Talal Asad) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ‘ধর্ম’কে রাজনীতি, অর্থনীতি বা বিজ্ঞান থেকে আলাদা একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জগৎ হিসেবে দেখার ধারণাটি অত্যন্ত আধুনিক এবং পশ্চিমা সৃষ্টি, যা ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তি (Enlightenment) এবং রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণের ফল (Genealogies of Religion, 1993)। আমরা এই পশ্চিমা মডেলটিকেই পৃথিবীর বাকি সব সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। অনেক অ-পশ্চিমা সমাজে ‘ধর্ম’ জীবনের সব ক্ষেত্রের সাথে এমনভাবে মিশে আছে যে, তাকে আলাদা করে সংজ্ঞায়িত করাই অর্থহীন।
সুতরাং, সংজ্ঞার এই চোরাবালি থেকে আমাদের শিক্ষা হলো, ধর্মের কোনো একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আটকে না থেকে, বরং ধর্মের বিভিন্ন উপাদান, তার বিচিত্র রূপ এবং বিভিন্ন সমাজে তার ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা অনুসন্ধান করাই বেশি যুক্তিযুক্ত। সংজ্ঞাটি কী, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কে সংজ্ঞা দিচ্ছে, কোন প্রেক্ষাপটে দিচ্ছে এবং সেই সংজ্ঞার মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইছে। এই প্রশ্নগুলো মাথায় রেখেই আমরা আমাদের পরবর্তী অনুসন্ধানে এগিয়ে যাব।
জেনেসিসের সন্ধানে: ধর্মের জ্ঞানীয় ও মনস্তাত্ত্বিক উৎস
মানুষ কেন ধার্মিক হলো? কীভাবে এই অদ্ভুত, বিমূর্ত এবং প্রায়শই অবাস্তব বিশ্বাসের জন্ম হলো আমাদের প্রাইমেট মস্তিষ্কে, যে মস্তিষ্ক তৈরি হয়েছিল আফ্রিকার সাভানায় শিকার করতে আর শিকার এড়িয়ে চলতে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আমাদের লক্ষ লক্ষ বছর আগের পূর্বপুরুষদের ধূসর মনোজগতে উঁকি দিয়েছেন। এটা অনেকটা প্রত্নতত্ত্বের মতো, তবে এখানে মাটি খুঁড়ে হাড়গোড় নয়, বরং আমাদের আজকের দিনের আচরণ ও চিন্তার প্যাটার্নের ভেতর থেকে প্রাচীন মনস্তাত্ত্বিক ফসিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। ধর্মের উৎপত্তির পেছনে কোনো একক, জাদুকরী কারণ নেই। বরং এটি ছিল মানুষের জ্ঞানীয় (Cognitive), মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) এবং সামাজিক (Social) বিবর্তনের এক জটিল, অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু শক্তিশালী উপজাত (Byproduct)। এই অধ্যায়ে আমরা এর জ্ঞানীয় ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিগুলো আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করব।
আমাদের এজেন্সি-সন্ধানী মস্তিষ্ক (Our Agency-seeking Brain): এক বিবর্তনীয় ভুল বোঝাবুঝি?
অনেক জ্ঞানীয় বিজ্ঞানী (Cognitive Scientist), যেমন প্যাসকেল বয়ার (Pascal Boyer) বা স্কট অ্যাট্রান (Scott Atran), মনে করেন যে, ধর্মের বীজ লুকানো আছে আমাদের মস্তিষ্কের বিবর্তনীয় গঠনের মধ্যেই, যা কিনা ধর্মের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয়নি। আমাদের মস্তিষ্ক হলো টিকে থাকার জন্য তৈরি এক অসাধারণ যন্ত্র, আর এই যন্ত্রের কিছু সাধারণ কাজের পদ্ধতিই (Default Settings) ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।
- হাইপারঅ্যাকটিভ এজেন্সি ডিটেকশন ডিভাইস (Hyperactive Agency Detection Device – HADD): আমাদের মস্তিষ্ক একটি ‘এজেন্সি ডিটেক্টর’ বা কর্তা শনাক্তকরণ যন্ত্রে সজ্জিত। এটি আমাদের চারপাশে কোনো সচেতন কর্তা বা এজেন্টের (অর্থাৎ, যার মন ও উদ্দেশ্য আছে) উপস্থিতি দ্রুত শনাক্ত করতে সাহায্য করে। কল্পনা করুন, মিলিয়ন বছর আগে আফ্রিকার সাভানায় আমাদের এক পূর্বপুরুষ হাঁটছেন। হঠাৎ ঝোপের আড়ালে একটা খসখস শব্দ হলো। এই শব্দের দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, এটা শুধু বাতাস (No Agency)। দুই, ওখানে একটা সিংহ লুকিয়ে আছে (Agency present)। যিনি ভাবলেন, ‘ও কিছু না, শুধু বাতাস’, তিনি যদি ভুল হন (Type I error – False Negative), তাহলে তার জিন সেখানেই শেষ। কিন্তু যিনি ভাবলেন, ‘বিপদ! ওখানে কোনো শিকারি প্রাণী আছে’ এবং পালিয়ে গেলেন, তিনি যদি ভুলও হন (Type II error – False Positive), তার সর্বোচ্চ ক্ষতি হলো কিছু শক্তি খরচ। কিন্তু দশবারের মধ্যে নয়বার ভুল হলেও তিনি বেঁচে রইলেন। দশমবারে ঠিক প্রমাণিত হয়ে তিনি নিজের প্রাণ বাঁচালেন এবং তার এই অতি-সতর্ক জিন পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দিলেন।বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী জাস্টিন ব্যারেট (Justin Barrett) মনে করেন, মিলিয়ন বছর ধরে এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) ফলে আমাদের মস্তিষ্কে এক ধরনের ‘হাইপারঅ্যাকটিভ এজেন্সি ডিটেকশন ডিভাইস’ বা সংক্ষেপে HADD তৈরি হয়েছে (Barrett, 2000)। অর্থাৎ, আমাদের এজেন্সি ডিটেক্টর এতটাই সংবেদনশীল যে, এটি প্রায়ই ভুল করে অজীব বস্তুর বা প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনেও কোনো সচেতন সত্তা বা ‘এজেন্ট’-এর উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ায়। বজ্রপাতকে আমরা শুধু মেঘের বৈদ্যুতিক ক্ষরণ হিসেবে না দেখে কোনো ক্রুদ্ধ দেবতার কাজ বলে ভাবতে শুরু করি। বন্যা বা খরাকে ভাবি কোনো রুষ্ট দেবীর অভিশাপ। অসুখ-বিসুখকে মনে করি কোনো অশুভ আত্মার কাজ। এই জ্ঞানীয় প্রবণতাই হয়তো অদৃশ্য আত্মা, ভূত-প্রেত এবং পরিশেষে আরও জটিল ও শক্তিশালী সত্তা, যেমন দেবতা ও ঈশ্বরের ধারণার জন্ম দিয়েছে। এটা যেন আমাদের মস্তিষ্কের এক ধরনের বিবর্তনীয় বাগ (Bug), যা ধর্মের মতো একটি শক্তিশালী সফটওয়্যার চলার সুযোগ করে দিয়েছে।
- মনের তত্ত্ব (Theory of Mind – ToM) এবং মানবিকীকরণ (Anthropomorphism): মানুষ হিসেবে আমাদের একটি অসাধারণ ক্ষমতা হলো, আমরা বুঝতে পারি যে অন্য মানুষেরও আমাদের মতোই মন, বিশ্বাস, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য আছে। এটাকে ‘মনের তত্ত্ব’ বা Theory of Mind (ToM) বলা হয়। আমরা অন্যের আচরণ দেখে তার মনের ভেতরের অবস্থা অনুমান করতে পারি। এই ক্ষমতাটি সামাজিক জীব হিসেবে টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। জ্ঞানীয় বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমরা এই ক্ষমতাটিকে শুধু অন্য মানুষের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করি না, বরং একে সম্প্রসারিত করে জড়বস্তু, প্রাণী বা প্রাকৃতিক শক্তির ওপরও আরোপ করি। আমরা ভাবি, নদীরও ইচ্ছা আছে, পাহাড়েরও রাগ আছে, সূর্যেরও উদ্দেশ্য আছে। এইভাবেই প্রকৃতিকে মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন (Anthropomorphize) করার প্রবণতা থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দেবতার জন্ম হতে পারে – যেমন, সূর্য দেবতা, বায়ু দেবতা বা উর্বরতার দেবী। আমরা আমাদের সবচেয়ে পরিচিত মডেল – অর্থাৎ মানুষের মন – দিয়েই সমগ্র জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করি।
- ন্যূনতম বিপরীতমুখী ধারণা (Minimally Counterintuitive Concepts): তাহলে কি যেকোনো কাল্পনিক সত্তাই দেবতা হয়ে উঠতে পারে? নৃবিজ্ঞানী প্যাসকেল বয়ার (Pascal Boyer) তার Religion Explained বইয়ে একটি আকর্ষণীয় তত্ত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ধারণাগুলো সবচেয়ে সহজে মনে থাকে এবং ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলো হলো ‘ন্যূনতম বিপরীতমুখী’ (Minimally Counterintuitive – MCI) ধারণা (Boyer, 2001)। একটি ধারণা যদি পুরোপুরি সাধারণ হয় (যেমন: একটি পাথর), তা আমাদের মনে কোনো দাগ কাটে না। আবার একটি ধারণা যদি পুরোপুরি অদ্ভুত বা বিপরীতমুখী হয় (যেমন: একটি সবুজ রঙের চারকোনা ঘুমন্ত আইডিয়া), তা বোঝা ও মনে রাখা খুব কঠিন। কিন্তু যে ধারণাগুলো আমাদের সাধারণ জগতের ধারণার (Intuitive Ontology) প্রায় সবকিছু মেনে চলে, শুধু এক-দুটি জায়গায় ব্যতিক্রম – সেগুলোই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় হয়। যেমন: একজন মানুষ যিনি অদৃশ্য হতে পারেন (আত্মা), বা একজন মানুষ যিনি সব দেখেন ও শোনেন (ঈশ্বর), বা একটি ঝোপ যা কথা বলতে পারে (বাইবেলের জ্বলন্ত ঝোপ)। এই সত্তাগুলো যথেষ্ট সাধারণ হওয়ায় আমরা তাদের উদ্দেশ্য ও আচরণ বুঝতে পারি, কিন্তু তাদের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাগুলো তাদের বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এই MCI ধারণাগুলোই হলো সফল দেবতাদের রেসিপি।
অস্তিত্বের সংকট ও মৃত্যুঞ্জয়ী আকাঙ্ক্ষা (Existential Anxiety and the Quest for Immortality)
মানুষই সম্ভবত একমাত্র প্রাণী যে নিজের মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণ এবং বিমূর্তভাবে সচেতন। এই সচেতনতা এক তীব্র অস্তিত্বের সংকট (Existential Anxiety) তৈরি করে। এই অনিবার্য ধ্বংসের উপলব্ধি, এই জ্ঞান যে একদিন আমাদের চেতনা, স্মৃতি, ভালোবাসা – সবকিছু মহাবিশ্বের অসীম শূন্যতায় বিলীন হয়ে যাবে, তা আমাদের ভেতর এক গভীর ভয় ও অর্থহীনতার জন্ম দেয়। সামাজিক মনোবিজ্ঞানী শেলডন সলোমন (Sheldon Solomon), জেফ গ্রিনবার্গ (Jeff Greenberg) এবং টম পিজিনস্কি (Tom Pyszczynski) দ্বারা বিকশিত ‘টেরর ম্যানেজমেন্ট থিওরি’ (Terror Management Theory – TMT) অনুযায়ী, মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনেক কিছুই – জাতীয়তাবাদ থেকে শুরু করে শিল্প-সাহিত্য, এমনকি নিজের নাম টিকিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা – এই মৃত্যুভয়কে অবচেতনভাবে মোকাবেলা করার একটি উপায় (The Worm at the Core, 2015)।
ধর্ম এই ভয়কে মোকাবেলা করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সরাসরি মনস্তাত্ত্বিক বর্ম সরবরাহ করে।
- আক্ষরিক অমরত্ব (Literal Immortality): প্রায় সব ধর্মই কোনো না কোনো রূপে পরকালের (Afterlife) ধারণা দেয়। মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, বরং একটি নতুন, হয়তো আরও ভালো, অধ্যায়ের শুরু – এই বিশ্বাস মৃত্যুভয়কে সহনীয় করে তোলে। মিশরীয়দের পিরামিড আর মমি তৈরির জটিল প্রক্রিয়া, খ্রিস্টানদের স্বর্গ ও নরকের ধারণা, হিন্দুদের কর্মফল ও পুনর্জন্মের (Reincarnation) চক্র, বা ইসলামে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা – এই সবকিছুই মানুষের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এই ধারণাগুলো আমাদের সান্ত্বনা দেয় যে আমাদের চেতনা বা সত্তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, আমাদের ভালোবাসার মানুষদের সাথে আবার দেখা হবে।
- প্রতীকী অমরত্ব (Symbolic Immortality): ধর্ম শুধু পারলৌকিক বা আক্ষরিক অমরত্বই নয়, এটি ইহকালেও এক ধরনের প্রতীকী অমরত্ব অর্জনের পথ দেখায়। একটি বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অংশ হয়ে, সেই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নশ্বর, ক্ষুদ্র অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। সে অনুভব করে যে, সে একটি চিরন্তন ধারার অংশ। তার মৃত্যুর পরেও তার গোষ্ঠী, তার ধর্ম, তার বিশ্বাস টিকে থাকবে এবং সে সেই বৃহত্তর সত্তার একটি অংশ হিসেবে বেঁচে থাকবে। এটি অনেকটা নিজের সন্তান বা নিজের কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকার ইচ্ছার মতোই এক গভীর আকাঙ্ক্ষা।
- অর্থ ও উদ্দেশ্যের সন্ধান (The Search for Meaning and Purpose): ধর্ম আমাদের বিশৃঙ্খল ও প্রায়শই নিষ্ঠুর জগতে একটি অর্থপূর্ণ আখ্যান (Meaningful Narrative) সরবরাহ করে। এটি মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান কী, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব এবং এই মাঝখানের সময়টুকুতে আমাদের কী করা উচিত – এইসব বড় বড় প্রশ্নের একটি সুসংহত উত্তর দেয়। ধর্ম আমাদের কষ্ট, যন্ত্রণা ও অবিচারের একটি ব্যাখ্যা দেয় (যেমন: কর্মফল বা ঈশ্বরের পরীক্ষা), যা অনেক সময় কোনো ব্যাখ্যা না থাকার চেয়েও বেশি সান্ত্বনাদায়ক। ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল (Viktor Frankl) তার Man’s Search for Meaning বইয়ে দেখিয়েছেন যে, মানুষ চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকতে পারে যদি সে তার জীবনে কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্য খুঁজে পায় (Frankl, 1946)। ধর্ম সেই অর্থের একটি তৈরি করা, শক্তিশালী উৎস।
স্বপ্ন, ট্রান্স এবং পরিবর্তিত চেতনা (Dreams, Trances, and Altered States of Consciousness)
আমাদের সাধারণ, দৈনন্দিন চেতনার বাইরেও মনের আরও অনেক স্তর আছে। স্বপ্ন, গভীর ধ্যান, সম্মোহন বা সাইকোঅ্যাকটিভ পদার্থের প্রভাবে সৃষ্ট অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের বাস্তবতার ধারণা নাড়িয়ে দিতে পারে। ধর্মের উৎপত্তিতে এই ‘পরিবর্তিত চেতনা’র (Altered States of Consciousness) একটি বড় ভূমিকা থাকতে পারে।
উনিশ শতকের নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টাইলরের (Edward Tylor) মতো অনেকেই মনে করতেন, ধর্মের উৎস নিহিত আছে আদিম মানুষের স্বপ্ন, মৃত্যু বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা করার চেষ্টার মধ্যে। তারা ভাবতেন, ঘুমের মধ্যে শরীর যখন স্থির থাকে, তখন আমাদের ভেতরের আরেকটি সত্তা বা ‘আত্মা’ (Soul or Spirit) বেরিয়ে গিয়ে দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়ায়, যা আমরা স্বপ্নে দেখি। মৃত পূর্বপুরুষদের স্বপ্নে দেখাটা এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করত। মৃত্যুর পর সেই আত্মা দেহ ছেড়ে পুরোপুরি চলে যায় এবং প্রেতাত্মা হিসেবে বিচরণ করে। এই আত্মার ধারণা থেকেই পরবর্তীকালে পূর্বপুরুষ পূজা (Ancestor Worship) এবং পরিশেষে দেবতা ও ঈশ্বরের মতো আরও জটিল আধ্যাত্মিক সত্তার জন্ম হয় (Tylor, 1871)।
বিভিন্ন সংস্কৃতির শামানরা (Shamans) প্রায়ই পুনরাবৃত্তিমূলক নাচ-গান, ড্রামের শব্দ বা বিভিন্ন সাইকোট্রোপিক বনজ উদ্ভিদ (Psychotropic Plants) ব্যবহারের মাধ্যমে এক ধরনের পরিবর্তিত চেতনা বা ট্রান্স (Trance) অবস্থায় চলে যেতেন। এই অবস্থায় তারা দাবি করতেন যে তারা ‘আত্মাদের জগতে’ ভ্রমণ করছেন, দেবতাদের সাথে কথা বলছেন বা ভবিষ্যতের পূর্বাভাস পাচ্ছেন। এই তীব্র ও অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতাগুলো শুধু শামানদের নিজেদের বিশ্বাসকেই নয়, বরং পুরো গোষ্ঠীর বিশ্বাসকেও দৃঢ় করত যে, আমাদের এই দৃশ্যমান জগতের বাইরেও আরেকটি অদৃশ্য, শক্তিশালী জগৎ বিদ্যমান।
সুতরাং, ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক শিকড় বেশ গভীর এবং বহুমুখী। এটি কোনো একক উৎস থেকে জন্মায়নি। আমাদের মস্তিষ্ক যেভাবে জগৎকে দেখে, কার্যকারণ ও উদ্দেশ্য খোঁজে; আমাদের গভীরতম ভয়গুলো, বিশেষ করে মৃত্যুভয়; এবং জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের তীব্র আকুতি – এই সবকিছু মিলেই বিশ্বাসের জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ধর্ম হয়তো আমাদের বিবর্তিত মনস্তত্ত্বরই এক অনিবার্য প্রতিধ্বনি।
সামাজিক নীলনকশা: ধর্মের সামাজিক উৎস ও বিবর্তন
ধর্ম যদি শুধু ব্যক্তিগত মনোজগতের ফসল হতো, তবে হয়তো তা গুহায় বসে ধ্যানমগ্ন কোনো ঋষির ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু ধর্ম তা নয়। ধর্ম এক প্রবল সামাজিক শক্তি। এটি মন্দির বানায়, সমাজকে শাসন করে, যুদ্ধ বাধায়, আবার শান্তিও স্থাপন করে। তাই অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, ধর্মের আসল রহস্য তার মনস্তাত্ত্বিক উৎসের চেয়েও বেশি লুকিয়ে আছে তার সামাজিক প্রয়োজনে। ধর্ম মূলত সমাজের প্রয়োজনে, সমাজের দ্বারাই তৈরি হয়েছে। এটি ব্যক্তিমানুষের জন্য যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর টিকে থাকার জন্য। এটা অনেকটা সেই অদৃশ্য সুতার মতো, যা হাজার হাজার ভিন্ন ভিন্ন পুঁতিকে গেঁথে একটি মালা তৈরি করে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সামাজিক সুতাগুলোর উৎস ও বুনন অনুসন্ধান করব।
ছোট গোষ্ঠী থেকে বড় সমাজ: নৈতিক ঈশ্বরের জন্ম
আমাদের পূর্বপুরুষরা, হোমো স্যাপিয়েন্সরা, তাদের অস্তিত্বের প্রায় ৯৫ শতাংশ সময়ই কাটিয়ে দিয়েছে ছোট ছোট শিকারি-সংগ্রাহক (Hunter-gatherer) গোষ্ঠীতে। এই গোষ্ঠীগুলো ছিল মূলত বর্ধিত পরিবার, যেখানে সদস্য সংখ্যা খুব কমই ১৫০ ছাড়াত। ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী রবিন ডানবার (Robin Dunbar) দেখিয়েছেন যে, মানুষের মস্তিষ্ক প্রাকৃতিকভাবে প্রায় ১৫০ জনের একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সাথেই স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে (Grooming, Gossip, and the Evolution of Language, 1996)। এই ‘ডানবার সংখ্যা’র (Dunbar’s Number) জগতে সবাই সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চিনত।
এই ছোট, মুখোমুখি (face-to-face) সমাজে সহযোগিতা বজায় রাখার জন্য কোনো অদৃশ্য, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল না। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল ‘সুনাম’ (Reputation) এবং ‘গসিপ’ (Gossip)। কে ভালো শিকারি, কে অলস, কে স্বার্থপর, কে পরোপকারী – এইসব তথ্য গোষ্ঠীর সবার মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত। পারস্পরিক আদান-প্রদানের (Reciprocal Altruism) অলিখিত নিয়মই যথেষ্ট ছিল। তাদের ধর্ম ছিল মূলত সর্বপ্রাণবাদী (Animistic) এবং শামানকেন্দ্রিক (Shamanistic)। তাদের দেবতারা ছিলেন স্থানীয় – পাহাড়ের আত্মা, নদীর দেবী বা জঙ্গলের পাহারাদার। এই দেবতারা নৈতিকতা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না। তাদের কাজ ছিল মূলত প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, শিকারের সাফল্য নিশ্চিত করা বা রোগ-শোক দূর করা।
কিন্তু প্রায় দশ-বারো হাজার বছর আগে কৃষি বিপ্লব (Agricultural Revolution) মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ওলট-পালট ঘটিয়ে দিল। মানুষ শিকার ও সংগ্রহের যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল। এই স্থিতিশীলতা জন্ম দিল গ্রাম, শহর এবং উদ্বৃত্ত খাদ্যের, যা দিয়ে পুরোহিত, শাসক বা সৈন্যের মতো অ-কৃষিজীবী শ্রেণীর ভরণপোষণ সম্ভব হলো। জনসংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেল। গোষ্ঠী আর ১৫০ জনের থাকল না, হয়ে গেল হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের।
এখানেই মানব সমাজ এক অভূতপূর্ব সমস্যার মুখোমুখি হলো – কীভাবে এই বড়, বেনামী (Anonymous) সমাজে শৃঙ্খলা ও সহযোগিতা বজায় রাখা যাবে? বাজারে যে লোকটির কাছ থেকে আপনি শস্য কিনছেন, আপনি তাকে চেনেন না। পাশের গ্রামের যে মানুষটির সাথে আপনাকে সেচের জল ভাগ করে নিতে হবে, সে আপনার কেউ নয়। এই পরিস্থিতিতে প্রতারণা, চুরি আর স্বার্থপরতার সুযোগ বহুগুণে বেড়ে যায়। গসিপ বা সামাজিক চাপ এখানে আর কাজ করে না। এই বিশাল সহযোগিতার সংকট (Crisis of Cooperation) সমাধানের জন্য মানুষের প্রয়োজন ছিল নতুন কোনো সামাজিক প্রযুক্তির।
বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানী আরা নরেনজায়ান (Ara Norenzayan) তাঁর Big Gods বইতে যুক্তি দিয়েছেন যে, এই সমস্যার সমাধান হিসেবেই ‘বড় ঈশ্বর’ বা নৈতিক ঈশ্বরের (Moralizing High God) ধারণার জন্ম হয়েছিল (Norenzayan, 2013)। এই নতুন ধরনের ঈশ্বররা পুরনো স্থানীয় আত্মাদের মতো নন। তাঁদের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল:
- সর্বজ্ঞ (All-knowing): তাঁরা মানুষের সব কাজকর্ম, এমনকি মনের গোপন চিন্তাও পর্যবেক্ষণ করছেন। মানুষের চোখ এড়ানো গেলেও, তাঁদের চোখ এড়ানো অসম্ভব।
- সর্বশক্তিমান বিচারক (Powerful Judge): তাঁরা শুধু দেখেনই না, বিচারও করেন। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দেন (ইহকালে বা পরকালে) এবং খারাপ কাজের জন্য কঠোর শাস্তি দেন।
- নৈতিকতার অভিভাবক (Concerned with Morality): তাঁদের আগ্রহ শুধু বলিদান বা পূজা-অর্চনায় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা মানুষের পারস্পরিক নৈতিক আচরণের (যেমন: সততা, দয়া, বিশ্বস্ততা) ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন।
এই ‘অদৃশ্য পুলিশ’ বা ‘আকাশে অবস্থিত বড় ভাই’ (Big Brother in the Sky)-এর সার্বক্ষণিক নজরদারির ভয় মানুষকে নীতিবান থাকতে, সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলতে এবং সম্পূর্ণ অপরিচিতদের সাথেও সহযোগিতা করতে বাধ্য করে। যে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই ধরনের শক্তিশালী নৈতিক ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তারা অভ্যন্তরীণভাবে আরও বেশি সুসংহত, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ফলে তারা টিকে থাকার লড়াইয়ে এবং অন্য গোষ্ঠীগুলোর সাথে যুদ্ধ ও প্রতিযোগিতায় এগিয়ে গিয়েছিল। এভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধু জৈবিক স্তরে নয়, সাংস্কৃতিক স্তরেও (Cultural Group Selection) কাজ করেছে। যে সংস্কৃতিগুলো বৃহৎ আকারের সহযোগিতা তৈরি করতে পেরেছে, সেগুলোই টিকে থেকেছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে। নৈতিক ধর্ম ছিল সেই সফল সাংস্কৃতিক অভিযোজনের (Cultural Adaptation) মূল চাবিকাঠি।
আচার-অনুষ্ঠান: সামাজিক আঠা
ধর্মের সামাজিক ভূমিকার কেন্দ্রে রয়েছে আচার-অনুষ্ঠান (Ritual)। ডুর্খাইমের মতে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো হলো সেই প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি গোষ্ঠী তার পবিত্র প্রতীকগুলোকে পূজা করে এবং নিজেদের মধ্যে সামাজিক বন্ধনকে নতুন করে ঝালিয়ে নেয়। যখন একটি গোষ্ঠীর মানুষ একসাথে প্রার্থনা করে, উপবাস করে বা কোনো ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের তীব্র আবেগ ও একাত্মতার অনুভূতি জন্মায়, যা তিনি ‘সম্মিলিত উচ্ছ্বাস’ (Collective Effervescence) বলে অভিহিত করেছেন। এই মুহূর্তে ব্যক্তি তার ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন সত্তা ভুলে গিয়ে এক বৃহত্তর, শক্তিশালী সত্তার অংশ হয়ে যায় (Durkheim, 1912)। এই অনুভূতিই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ‘আমরা’ বোধ তৈরি করে এবং সামাজিক সংহতিকে সিমেন্টের মতো জমিয়ে দেয়।
নৃবিজ্ঞানীরা আরও দেখিয়েছেন যে, অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বেশ কঠিন, সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য হয়। যেমন: দীর্ঘ সময় উপবাস, বেদনাদায়ক শারীরিক পরিবর্তন (যেমন: খৎনা বা ট্যাটু), বিপজ্জনক তীর্থযাত্রা বা বিপুল পরিমাণ সম্পদ উৎসর্গ করা। কেন মানুষ স্বেচ্ছায় এই কষ্টগুলো করে? ‘ব্যয়বহুল সংকেত তত্ত্ব’ (Costly Signaling Theory) অনুযায়ী, এই কষ্টকর আচারগুলো হলো গোষ্ঠীর প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের এক ধরনের খাঁটি এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ (Hard-to-fake signal of commitment)। যে ব্যক্তি গোষ্ঠীর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করতে রাজি, সে নিশ্চয়ই গোষ্ঠীর প্রতি অনুগত এবং তাকে বিশ্বাস করা যায়। সে কোনো সুবিধাবাদী বা প্রতারক (Free-rider) নয়, যে শুধু গোষ্ঠীর সুবিধাগুলোই ভোগ করতে চায় কিন্তু তার জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নয় (Henrich, 2009)। এভাবে কঠিন আচার-অনুষ্ঠানগুলো গোষ্ঠীর ভেতর থেকে প্রতারকদের চিহ্নিত করতে ও দূর করতে সাহায্য করে এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও সংহতি বাড়ায়।
নৃবিজ্ঞানী রয় র্যাপাপোর্ট (Roy Rappaport) দেখিয়েছেন যে, আচার-অনুষ্ঠানের আরও একটি গভীর কাজ রয়েছে। তাঁর মতে, আচার হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি সম্প্রদায় তার সবচেয়ে পবিত্র এবং প্রশ্নাতীত সত্যগুলোকে (Ultimate Sacred Postulates) প্রতিষ্ঠা ও সঞ্চালন করে (Ritual and Religion in the Making of Humanity, 1999)। আচারের পুনরাবৃত্তিমূলক এবং আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির মাধ্যমে বিশ্বাসগুলো শুধু মস্তিষ্কে থাকে না, তা শরীরে এবং অভ্যাসে পরিণত হয়। এটি সমাজকে একটি স্থিতিশীল কাঠামো দেয়।
অক্ষীয় যুগ (The Axial Age): ধর্মের বৈপ্লবিক সফটওয়্যার আপডেট
জার্মান দার্শনিক কার্ল ইয়াসপার্স (Karl Jaspers) একটি যুগান্তকারী ধারণা দিয়েছিলেন, যার নাম ‘অক্ষীয় যুগ’ বা Axenzeit (The Axial Age) (The Origin and Goal of History, 1953)। তিনি লক্ষ্য করেন যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে, মাত্র কয়েক শতাব্দীর এক সংক্ষিপ্ত পরিসরে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে (চীন, ভারত, পারস্য, ইসরায়েল এবং গ্রিস) প্রায় একই সময়ে কিছু বিস্ময়কর ও বৈপ্লবিক ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল। এই সময়টাতেই চীনে কনফুসিয়াস ও লাওৎসে, ভারতে বুদ্ধ, মহাবীর, উপনিষদ প্রবর্তক ঋষিরা, পারস্যে জরাথুস্ট্র, ইসরায়েলে একেশ্বরবাদী নবীরা (যেমন: যিশাইয়, যিরমিয়) এবং গ্রিসে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিকরা আবির্ভূত হন।
ইয়াসপার্সের মতে, এই যুগটি ছিল মানব ইতিহাসের এক কেন্দ্রীয় অক্ষ বা সন্ধিক্ষণ, যখন মানুষ প্রথম তার অস্তিত্বের সমগ্রতা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে। এই সময়কার ধর্ম ও দর্শনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা পুরনো উপজাতীয় বা ট্রাইবাল ধর্মগুলো থেকে ছিল আমূল ভিন্ন:
- অতীন্দ্রিয় জগতের ধারণা (Transcendence): এই প্রথম জাগতিক, দৃশ্যমান জগতের বাইরে এক অতীন্দ্রিয়, পারমার্থিক, অদৃশ্য জগতের ধারণা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পুরনো দেবতারা ছিলেন প্রকৃতির অংশ, কিন্তু নতুন ঈশ্বর বা পরম সত্য (যেমন: ব্রহ্ম, তাও, নির্বাণ) ছিলেন এই জগতের ঊর্ধ্বে।
- সার্বজনীন নৈতিকতা (Universal Morality): নৈতিকতার ধারণা আর ‘আমার গোষ্ঠী’ বা ‘আমার গোত্র’-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। ভালোবাসা, করুণা, ন্যায়বিচারের মতো ধারণাগুলো সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হতে শুরু করল। ‘গোল্ডেন রুল’ (Golden Rule) বা ‘তুমি অন্যের সাথে সেরূপ ব্যবহার করো, যেরূপ তুমি নিজের জন্য কামনা করো’ – এই নীতিটি এই যুগের প্রায় সব চিন্তাধারার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়।
- ব্যক্তির আত্ম-উপলব্ধি ও অভ্যন্তরীণ জগৎ (Individual Self-consciousness and Interiority): ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে আর শুধু সম্মিলিত, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান থাকল না। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ জগৎ, তার পাপ-পুণ্য বোধ, তার আধ্যাত্মিক মুক্তি বা আত্মিক উন্নতির ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া শুরু হলো। ধর্ম হয়ে উঠল এক ব্যক্তিগত সংগ্রামের পথ।
কেন এই পরিবর্তনটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় একই সময়ে ঘটল? ইতিহাসবিদরা মনে করেন, এর পেছনে ছিল সাম্রাজ্যের বিস্তার, বাণিজ্যের প্রসার, মুদ্রার উদ্ভব এবং নগরায়ণের মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। এই নতুন, জটিল সমাজগুলোতে পুরনো উপজাতীয় দেবতারা আর যথেষ্ট ছিলেন না। প্রয়োজন ছিল আরও বিমূর্ত, আরও সার্বজনীন এবং আরও নৈতিক এক বিশ্বদৃষ্টির, যা বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষকে এক সাম্রাজ্যের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।
অক্ষীয় যুগ ছিল মানব ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ, যখন প্রাচীন উপজাতীয়, আচারসর্বস্ব ধর্মগুলো রূপান্তরিত হয়ে আজকের দিনের বড় বড় বিশ্বধর্মগুলোর (World Religions) দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এটি ছিল ধর্মের এক বৈপ্লবিক সফটওয়্যার আপডেট, যা মানুষকে ছোট গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসে বিশাল সভ্যতা ও সাম্রাজ্য গঠনের আদর্শিক রসদ জুগিয়েছিল।
বিশ্বাসের মনস্তত্ত্ব: আমরা কেন এবং কীভাবে বিশ্বাস করি?
আমরা এতক্ষণ ধর্মের জ্ঞানীয় ও সামাজিক উৎস নিয়ে কথা বললাম। সেগুলো ছিল অনেকটা ওপর থেকে, পাখির চোখে দেখার মতো বিষয়। কিন্তু আসল ঘটনাটা তো ঘটে ব্যক্তিমানুষের মনের গভীরে। ঠিক কী কারণে একজন মানুষ কোনো প্রমাণ ছাড়াই এমন কিছুতে বিশ্বাস করে, যার জন্য সে জীবন দিতে বা নিতেও প্রস্তুত থাকে? বিশ্বাস কোনো সরল যৌক্তিক প্রক্রিয়া নয়, যে আমরা সব প্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। বরং এটি এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক খেলা, যার পেছনে কাজ করে আমাদের শৈশবের শিক্ষা, আমাদের মস্তিষ্কের বিবর্তনীয় গড়ন, নানা ধরনের জ্ঞানীয় পক্ষপাত (Cognitive Bias) এবং আমাদের গভীরতম আবেগ। এটা অনেকটা সেই জাদুকরের খেলার মতো, যেখানে আসল কৌশলটি আমাদের চোখের সামনেই থাকে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। এই অধ্যায়ে আমরা সেই জাদুর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কৌশলগুলো বোঝার চেষ্টা করব।
শৈশবের প্রোগ্রামিং এবং মনের ভাইরাস (Childhood Programming and Viruses of the Mind)
মানুষের ধার্মিক হওয়ার সবচেয়ে বড় এবং সরল কারণটি হলো, সে একটি ধার্মিক পরিবার ও সমাজে জন্মগ্রহণ করেছে। এই কথাটা শুনতে খুব সাধারণ মনে হলেও, এর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত শক্তিশালী। একটি শিশু যখন জন্মায়, তার মস্তিষ্ক থাকে অনেকটা নতুন কম্পিউটারের ফাঁকা হার্ড ড্রাইভের মতো। কোন অপারেটিং সিস্টেম চলবে, কোন সফটওয়্যার ইনস্টল হবে, তা পুরোটাই নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর।
শিশুরা প্রকৃতিগতভাবেই বিশ্বাসপ্রবণ (Credulous)। এটা তাদের টিকে থাকার জন্য একটি বিবর্তনীয় কৌশল। একটি শিশুকে যদি তার বাবা-মা বলে, ‘ওই আগুনে হাত দিও না, পুড়ে যাবে’ বা ‘ওই ফলটা খেয়ো না, বিষাক্ত’, তাহলে তার জন্য প্রশ্নাতীতভাবে সেটা বিশ্বাস করে নেওয়াই লাভজনক। যে শিশু প্রতিটি বিষয়ে প্রমাণ চাইবে, তার টিকে থাকার সম্ভাবনা কমে যাবে। শিশুদের মস্তিষ্ক কর্তৃত্বমূলক ব্যক্তিদের (Authority Figures) – বিশেষ করে বাবা-মা, শিক্ষক বা ধর্মগুরুদের – কথাকে প্রায় চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তৈরি।
এই নমনীয় এবং বিশ্বাসপ্রবণ মনে যখন শৈশব থেকে ক্রমাগত ধর্মীয় ধারণা, গল্প আর আচার-অনুষ্ঠান প্রবেশ করানো হয়, তখন সেগুলো মনের গভীরে অপারেটিং সিস্টেমের অংশ হয়ে যায়। এই শৈশবের বিশ্বাসগুলো এতটাই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় যে, প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে এগুলোকে প্রশ্ন করাটা নিজের পরিচয়ের ভিত্তিকেই প্রশ্ন করার মতো বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে।
বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স (Richard Dawkins) এই সাংস্কৃতিক ধারণা বা বিশ্বাসের একককে ‘মিম’ (Meme) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, জিন যেমন শরীর থেকে শরীরে প্রতিলিপি তৈরি করে ছড়িয়ে পড়ে, মেমও তেমনই মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে সংক্রমিত হয়, অনেকটা ভাইরাসের মতো। ধর্মীয় ধারণাগুলো (যেমন: ঈশ্বর, পরকাল, পাপ-পুণ্য) অত্যন্ত সফল ‘মনের ভাইরাস’ (Mind Virus), কারণ এদের টিকে থাকার এবং ছড়িয়ে পড়ার কৌশলগুলো অসাধারণ:
- বড় পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিশ্রুতি: এটি স্বর্গের মতো অকল্পনীয় পুরস্কার এবং নরকের মতো ভয়াবহ শাস্তির ভয় দেখায়, যা মানুষের মৌলিক আবেগ – লোভ ও ভয়কে – কাজে লাগায়।
- প্রশ্নাতীত বিশ্বাসকে মহিমান্বিত করা: এটি বিশ্বাস বা ‘ঈমান’-কে একটি মহৎ গুণ হিসেবে প্রচার করে এবং সন্দেহ বা অবিশ্বাসকে পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে মানুষ তার সমালোচনামূলক চিন্তার ক্ষমতাকে নিজেই দমন করে রাখে।
- নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশনা: প্রায় সব ধর্মেই ধর্ম প্রচার করাকে একটি পুণ্যের কাজ হিসেবে দেখা হয়। ‘তোমার সন্তানদের ধর্মশিক্ষা দাও’, ‘বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করো’ – এই নির্দেশনাগুলো মেমটিকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে, শৈশবের ধর্মীয় শিক্ষা এক ধরনের শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক প্রোগ্রামিং, যা বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে (The Selfish Gene, 1976)।
জ্ঞানীয় পক্ষপাত: আমাদের যুক্তির ফাঁকফোকর
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও যে আমরা এই বিশ্বাসগুলোকে আঁকড়ে থাকি, তার কারণ আমাদের মস্তিষ্ক কোনো নিখুঁত যুক্তিবাদী যন্ত্র নয়। এটি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নানা ধরনের শর্টকাট বা হিউরিস্টিকস (Heuristics) ব্যবহার করে, যা প্রায়ই ভুল বা পক্ষপাতের জন্ম দেয়। মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল কাহনেম্যান (Daniel Kahneman) দেখিয়েছেন যে, আমাদের দুটি চিন্তার পদ্ধতি আছে: ‘সিস্টেম ১’ হলো দ্রুত, স্বয়ংক্রিয় এবং আবেগচালিত; আর ‘সিস্টেম ২’ হলো ধীর, বিশ্লেষণধর্মী এবং যুক্তিনির্ভর (Thinking, Fast and Slow, 2011)। আমরা বেশিরভাগ সময়ই সিস্টেম ১ ব্যবহার করে চলি। ধর্মীয় বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের এই সিস্টেম ১-এর অন্তর্গত জ্ঞানীয় পক্ষপাতগুলো পাহারাদারের মতো কাজ করে।
- নিশ্চিতকরণ পক্ষপাত (Confirmation Bias): এটি হলো আমাদের সেই প্রবণতা, যা আমাদের বিদ্যমান বিশ্বাসকে সমর্থন করে এমন তথ্যকে খুঁজে বেড়াতে, গুরুত্ব দিতে এবং মনে রাখতে সাহায্য করে। একই সাথে, যা আমাদের বিশ্বাসের পরিপন্থী, সেই তথ্যকে আমরা এড়িয়ে যাই, উপেক্ষা করি বা অবিশ্বাস করি। একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি তার প্রার্থনার ফল পেলে সেটিকে ঈশ্বরের কৃপা হিসেবে দেখবেন, কিন্তু প্রার্থনা ব্যর্থ হলে সেটিকে ঈশ্বরের পরীক্ষা, নিজের প্রার্থনার ঘাটতি বা ‘ঈশ্বরের লীলা বোঝা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়’ বলে ব্যাখ্যা করবেন। এভাবে তিনি তার মূল বিশ্বাসকে সব পরিস্থিতিতেই অক্ষত রাখেন। এই পক্ষপাত আমাদের তথ্যের একটি ফিল্টার বাবল (Filter Bubble) তৈরি করে দেয়, যেখানে শুধু বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিই শোনা যায়।
- প্যাটার্ন খোঁজার প্রবণতা (Patternicity): আমাদের মস্তিষ্ক একটি অসাধারণ প্যাটার্ন খোঁজার যন্ত্র। এই ক্ষমতা আমাদের পূর্বপুরুষদের সাভানার ঘাসের মধ্যে বাঘের ডোরাকাটা দাগ খুঁজে পেতে বা ঋতু পরিবর্তন বুঝতে সাহায্য করত। কিন্তু এই যন্ত্রটি এতটাই সংবেদনশীল যে, এটি প্রায়ই অর্থহীন বা দৈব (Random) ডেটার মধ্যেও প্যাটার্ন খুঁজে পায়। একে বলা হয় ‘অ্যাপোফেনিয়া’ (Apophenia)। আকাশে মেঘের মধ্যে মুখ, পোড়া পাউরুটির ওপর কোনো মহাপুরুষের ছবি, বা পরপর কয়েকটি ভালো বা খারাপ ঘটনাকে কোনো দৈব শক্তির ইঙ্গিত বলে মনে করা – এই সবই প্যাটার্ন খোঁজার প্রবণতার ফল। স্কেপটিক ম্যাগাজিনের সম্পাদক মাইকেল শারমার (Michael Shermer) একে ‘প্যাটার্নিসিটি’ বলে অভিহিত করেছেন (Shermer, 2008)। ধর্ম এই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে দৈব ঘটনাগুলোকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা অলৌকিক ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করার একটি কাঠামো সরবরাহ করে।
- জ্ঞানীয় অসঙ্গতি (Cognitive Dissonance): যখন আমাদের বিশ্বাস এবং বাস্তবতার মধ্যে, বা আমাদের দুটি বিশ্বাসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তখন আমরা এক ধরনের তীব্র মানসিক অস্বস্তিতে ভুগি। এই অস্বস্তি কমানোর জন্য আমরা হয় আমাদের বিশ্বাস পরিবর্তন করি, অথবা বাস্তবতাকে নিজেদের বিশ্বাসের ছাঁচে ফেলার জন্য নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করি। সমাজবিজ্ঞানী লিওন ফেস্টিংগার (Leon Festinger) প্রথম এই ধারণাটি দেন। তার একটি বিখ্যাত গবেষণায় তিনি একটি ছোট কাল্ট (Cult) পর্যবেক্ষণ করেন, যারা বিশ্বাস করত যে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট তারিখে বন্যায় ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শুধু তারাই একটি উড়ন্ত পিরিচে করে রক্ষা পাবে। যখন সেই নির্দিষ্ট দিনে কিছুই ঘটল না, তখন তারা তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করল না। বরং তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে, তাদের প্রার্থনার কারণেই ঈশ্বর পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন! (When Prophecy Fails, 1956)। বিশ্বাস ত্যাগ করাটা তাদের জন্য এতটাই বেদনাদায়ক ছিল যে, তারা বাস্তবতাকে বদলে দিয়ে নিজেদের বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে তুলল। ধর্মীয় বিশ্বাসীরাও প্রায়ই একই কাজ করেন।
- দলগত মানসিকতা বা ব্যান্ডওয়াগন প্রভাব (Bandwagon Effect): মানুষ সামাজিক জীব। আমরা একা থাকতে পছন্দ করি না এবং দলের সাথে থাকতে ভালোবাসি। আমাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রবণতা হলো, কোনো একটি ধারণা বা আচরণকে গ্রহণ করা যদি দেখি যে দলের বেশিরভাগ মানুষই তা করছে। যখন একজন ব্যক্তি এমন একটি সমাজে বড় হয় যেখানে প্রায় সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তখন সেই বিশ্বাসকে গ্রহণ করাটাই তার জন্য সবচেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক পথ। অবিশ্বাস করা মানে শুধু একটি ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা নয়, বরং নিজের পরিবার, বন্ধু এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া। এই সামাজিক চাপ বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার এক অন্যতম শক্তিশালী অনুষঙ্গ।
নিউরোথিওলজি: মস্তিষ্কের ভেতর ঈশ্বর
সাম্প্রতিক দশকগুলোতে স্নায়ুবিজ্ঞানীরা (Neuroscientists) ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের মতো বিমূর্ত বিষয়গুলোরও মস্তিষ্কের ভিত্তি অনুসন্ধান করছেন। এই নতুন এবং বিতর্কিত শাখার নাম নিউরোথিওলজি (Neurotheology)। এর উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে খুঁজে বের করা বা বাতিল করা নয়, বরং বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সময় আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে ঠিক কী ঘটে, তা পর্যবেক্ষণ করা।
অ্যান্ড্রু নিউবার্গের (Andrew Newberg) মতো গবেষকরা ধ্যানমগ্ন তিব্বতি ভিক্ষু বা প্রার্থনারত ফ্রান্সিসকান নানদের মস্তিষ্কের স্ক্যান (SPECT scan) করে দেখেছেন যে, গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মুহূর্তে তাদের মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু অংশে রক্তপ্রবাহের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে, মস্তিষ্কের প্যারিটাল লোবের (Parietal Lobe) যে অংশটি আমাদের শরীরকে পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং আমাদের স্থান ও কালের বোধ দেয় (Orientation Association Area), সেই অংশের কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ব্যক্তি তার নিজের সত্তার সীমানা হারিয়ে ফেলে এবং এক অসীম, অনন্ত সত্তার সাথে মিশে যাওয়ার (Sense of Oneness) অনুভূতি লাভ করে, যা অনেক মরমী অভিজ্ঞতার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য (Why God Won’t Go Away, 2001)।
কানাডার নিউরোসায়েন্টিস্ট মাইকেল পার্সিংগার (Michael Persinger) তার বিখ্যাত কিন্তু বিতর্কিত ‘গড হেলমেট’ (God Helmet) পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবকে (Temporal Lobe) দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করে অনেক সাধারণ মানুষের মধ্যেও আধ্যাত্মিক বা ‘অদৃশ্য উপস্থিতি’ (Sensed Presence) অনুভব করানো সম্ভব (Persinger, 2001)। এছাড়াও, টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সিতে আক্রান্ত কিছু রোগীর মধ্যে তীব্র ধর্মীয় অনুভূতি বা হাইপার-রিলিজিওসিটি (Hyper-religiosity) দেখা যায়, যা এই অঞ্চলের সাথে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার একটি গভীর সংযোগের ইঙ্গিত দেয়।
এই গবেষণাগুলোর মানে এই নয় যে, এই অভিজ্ঞতাগুলো ‘মিথ্যা’ বা ঈশ্বর মস্তিষ্কের একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া মাত্র। বরং এটি দেখায় যে, আমাদের আধ্যাত্মিক এবং মরমী অভিজ্ঞতাগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট স্নায়বিক ভিত্তি (Neurological Correlate) রয়েছে। আমাদের মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরি যে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এটি এই ধরনের গভীর ও অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা তৈরি করতে সক্ষম। ধর্ম এই প্রাকৃতিক সক্ষমতাকেই একটি সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং অর্থ প্রদান করে।
বিশ্বাসের বর্ণালী: ধর্মের প্রকারভেদ ও বৈচিত্র্য
ধর্মের জগৎ কোনো একক রঙের ক্যানভাস নয়, বরং এটি হাজারো রঙের এক বিশাল বর্ণালী। এই বর্ণালীর এক প্রান্তে যেমন রয়েছে একজন মাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা, তেমনই অন্য প্রান্তে রয়েছে অগণিত আত্মা ও দেবতার সমাবেশ, আবার কোথাও বা কোনো ঈশ্বরের ধারণাই নেই। মানব কল্পনা ও সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্ম নিজেকে অগণিত রূপে প্রকাশ করেছে। পৃথিবীর হাজার হাজার ধর্মকে বোঝার জন্য এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য চিন্তাবিদরা নানাভাবে এদের শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এটা অনেকটা জীববিজ্ঞানে প্রজাতির শ্রেণীবিন্যাস করার মতো, যা আমাদের এই বিপুল বৈচিত্র্যকে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামোর মধ্যে দেখতে সাহায্য করে। সবচেয়ে প্রচলিত ভাগগুলো হলো উপাস্যের সংখ্যা ও প্রকৃতি, ধর্মের সাংগঠনিক কাঠামো এবং ভৌগোলিক উৎপত্তির ওপর ভিত্তি করে।
উপাস্যের সংখ্যা ও প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস
এটি ধর্মকে ভাগ করার সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রচলিত পদ্ধতি। এখানে মূল প্রশ্নটি হলো, ‘কতজন দেবতা আছেন এবং তাদের প্রকৃতি কী?’
- একেশ্বরবাদ (Monotheism): এই বিশ্বাস ব্যবস্থায় একটি মাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হয়। আব্রাহামিক ধর্মগুলো – ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম – এর প্রধান উদাহরণ। এই ধর্মগুলোতে ঈশ্বরকে সাধারণত ব্যক্তি-সদৃশ (Personal), সর্বজ্ঞ (Omniscient), সর্বশক্তিমান (Omnipotent), পরম করুণাময় (Omnibenevolent) এবং অতীন্দ্রিয় (Transcendent) হিসেবে কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ, তিনি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তিনি নিজে এই জগতের অংশ নন, এর ঊর্ধ্বে বিরাজমান। একেশ্বরবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর এক্সক্লুসিভিটি বা বর্জনশীলতা (Exclusivism)। ‘আমার ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং অন্য সব দেবতা মিথ্যা’ – এই বিশ্বাস প্রায়ই অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং ধর্ম প্রচারের (Proselytization) তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। এই কারণেই একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো, বিশেষ করে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বিস্তৃত ধর্ম হয়ে উঠেছে।
- বহুদেবতাবাদ (Polytheism): এই বিশ্বাস ব্যবস্থায় একাধিক দেব-দেবীতে বিশ্বাস করা হয়। প্রাচীন গ্রিক, রোমান, মিশরীয়, নর্স এবং আধুনিক হিন্দুধর্ম এর প্রধান উদাহরণ। এখানে প্রত্যেক দেবতার নির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন: গ্রিকদের জিউস ছিলেন দেবতাদের রাজা ও আকাশের দেবতা, পসাইডন সমুদ্রের, হেডিস পাতালের। হিন্দুধর্মে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং শিব ধ্বংসকর্তা। আবার বিদ্যার জন্য সরস্বতী, সম্পদের জন্য লক্ষ্মী। বহুদেবতাবাদী ধর্মগুলোতে দেবতাদের জগৎ অনেকটা মানুষের সমাজের মতোই – সেখানে প্রেম, ঘৃণা, হিংসা, ষড়যন্ত্র সবই আছে। এই ধর্মগুলো সাধারণত একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর চেয়ে বেশি সহিষ্ণু ও সমন্বয়বাদী (Syncretic) হয়, কারণ নতুন কোনো দেবতাকে তাদের প্যান্থিয়নে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে বিশেষ কোনো দার্শনিক বাধা থাকে না। তবে অনেক হিন্দু দার্শনিক মনে করেন, এই বিভিন্ন দেব-দেবী আসলে এক পরম, নিরাকার সত্তা ব্রহ্মের (Brahman) বিভিন্ন সাকার রূপ। তাই হিন্দুধর্মের এই দিকটি বেশ জটিল এবং একে এক ধরনের বহুরূপী একেশ্বরবাদ (Polymorphic Monotheism) বা একেশ্বরোপাসনাবাদও (Henotheism) বলা যেতে পারে।
- একক-উপাসনামূলক বহুদেবতাবাদ বা একেশ্বরোপাসনাবাদ (Henotheism): এটি বহুদেবতাবাদ ও একেশ্বরবাদের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এখানে বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, কিন্তু উপাসনা করা হয় শুধুমাত্র একজন প্রধান বা ইষ্টদেবতাকে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, প্রাচীন ইহুদিধর্ম তার প্রাথমিক পর্যায়ে একক-উপাসনামূলক ছিল। তারা অন্যান্য জাতির দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করত না, কিন্তু শুধুমাত্র নিজেদের দেবতা ‘ইয়াহওয়েহ’ (Yahweh)-এর উপাসনা করত। বেদের প্রাথমিক পর্যায়েও এই ধারার প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে ইন্দ্র, অগ্নি বা বরুণের মতো বিভিন্ন দেবতাকে একেক সময় সর্বোচ্চ দেবতা হিসেবে স্তুতি করা হয়েছে।
- সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism): এই গভীর দার্শনিক বিশ্বাস অনুযায়ী, ঈশ্বর ও মহাবিশ্ব অভিন্ন। এখানে ঈশ্বর কোনো ব্যক্তি-সদৃশ সত্তা নন, যিনি মহাবিশ্বের বাইরে থেকে একে পুতুলের মতো নিয়ন্ত্রণ করছেন, বরং সমগ্র প্রকৃতি ও অস্তিত্বই হলো ঈশ্বর (God is everything and everything is God)। গাছপালা, নদী, নক্ষত্র, এমনকি আমরা নিজেরাও সেই এক ঐশ্বরিক সত্তার অংশ। দার্শনিক বারুখ স্পিনোজা (Baruch Spinoza) এই ধারণার একজন বড় পশ্চিমা প্রবক্তা ছিলেন। আলবার্ট আইনস্টাইন-ও নিজেকে স্পিনোজার ঈশ্বরের অনুসারী বলতেন। হিন্দুধর্মের অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ (আমিই ব্রহ্ম) বা ‘তত্ত্বমসি’ (তুমিই সেই) ধারণার মধ্যে এর গভীর ছায়া খুঁজে পাওয়া যায়।
- সর্বাত্মবাদ বা প্যানএনথেইজম (Panentheism): এটি সর্বেশ্বরবাদের একটি সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রূপ। এই মতানুসারে, সমগ্র মহাবিশ্ব ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত (All is in God), কিন্তু ঈশ্বর শুধু মহাবিশ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন, তিনি এর ঊর্ধ্বেও বিরাজমান (God is more than the All)। অর্থাৎ, ঈশ্বর একই সাথে অতীন্দ্রিয় (Transcendent) এবং অন্তর্যামী (Immanent)। অনেক উদারপন্থী ধর্মতাত্ত্বিক এই ধারণার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় করার চেষ্টা করেন।
- সর্বপ্রাণবাদ (Animism): এটি সম্ভবত ধর্মের সবচেয়ে আদিম রূপ, যা আজও বিশ্বের বিভিন্ন আদিবাসী সংস্কৃতিতে প্রচলিত। ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টাইলর (Edward Tylor) একেই ধর্মের উৎস বলে মনে করতেন (Tylor, 1871)। এই বিশ্বাস অনুযায়ী, শুধু মানুষ বা প্রাণী নয়, গাছপালা, নদী, পাহাড়, পাথর, বাতাস – সবকিছুর মধ্যেই আত্মা বা প্রাণশক্তি (Spirit) রয়েছে। এই জগতটি নানা ধরনের আত্মিক সত্তায় পরিপূর্ণ – কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ, কিছু বিদ্বেষী – যাদের সন্তুষ্ট বা রুষ্ট করার ওপর মানুষের ভালো-মন্দ, শিকারের সাফল্য বা ফসলের প্রাচুর্য নির্ভর করে। শামান বা ওঝারা হলেন সেই ব্যক্তি, যারা এই আত্মিক জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।
- দ্বৈতবাদ (Dualism): এই বিশ্বাস ব্যবস্থায় জগৎকে দুটি মৌলিক, শাশ্বত এবং পরস্পরবিরোধী শক্তির (সাধারণত ভালো ও মন্দ, বা আত্মা ও জড়) দ্বন্দ্বক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়। প্রাচীন পারস্যের জরাথুস্ট্রবাদ (Zoroastrianism) এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে সর্বোচ্চ ভালো দেবতা আহুরা মাজদা (Ahura Mazda) এবং অশুভ শক্তি আংরা মাইনিউ বা আহরিমান (Ahriman)-এর মধ্যে এক মহাজাগতিক সংগ্রাম চলছে। মানুষের দায়িত্ব হলো এই সংগ্রামে ভালোর পক্ষে লড়াই করা। খ্রিস্টধর্মের ঈশ্বর ও শয়তানের ধারণা বা দর্শনের মন-শরীর দ্বৈতবাদের (Mind-Body Dualism) মধ্যেও এর প্রভাব দেখা যায়।
- নিরীশ্বরবাদ (Nontheism): কিছু ধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে না, কিন্তু বিষয়টিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অপ্রাসঙ্গিক বা গৌণ মনে করে। এদেরকে ‘নিরীশ্বরবাদী ধর্ম’ বলা যেতে পারে। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং চীনের তাওবাদ (Taoism) এর প্রধান উদাহরণ। বৌদ্ধধর্মে দেবতারা আছেন বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু তারাও কর্মফলের অধীন এবং নির্বাণ লাভ করেননি, তাই তারা উপাসনার পাত্র নন। এখানে ঈশ্বরের উপাসনার পরিবর্তে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ, ধ্যান, প্রজ্ঞা এবং আত্ম-উপলব্ধির ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়। জৈনধর্মে কোনো স্রষ্টা ঈশ্বরের ধারণাই নেই। তাওবাদে ‘তাও’ বা প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত পথকেই সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে দেখা হয়।
ভৌগোলিক ও ঐতিহ্য অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস
ধর্মগুলোকে তাদের উৎপত্তিস্থল বা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করেও ভাগ করা যায়, যা তাদের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক সাদৃশ্যকে তুলে ধরে।
- আব্রাহামিক ধর্ম (Abrahamic Religions): এই ধর্মগুলো হলো ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম। এদের এই নামে ডাকা হয় কারণ এরা সবাই আব্রাহাম/ইব্রাহিমকে তাদের একজন আদি ও গুরুত্বপূর্ণ নবী বা পিতৃপুরুষ হিসেবে মানেন। এদের মধ্যে অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন: একেশ্বরবাদ, নবীদের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী প্রেরণের ধারণা, পবিত্র ধর্মগ্রন্থের ওপর বিশ্বাস এবং ইতিহাসের একটি রৈখিক ধারণা (অর্থাৎ, জগৎ একবার সৃষ্টি হয়েছে এবং একদিন এর চূড়ান্ত বিচার হবে)।
- ভারতীয় বা ধার্মিক ধর্ম (Indian or Dharmic Religions): এই ধর্মগুলোর জন্ম ভারতীয় উপমহাদেশে। এদের মধ্যে প্রধান হলো হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও শিখধর্ম। এদের মধ্যেকার বিশ্বাস ও আচার অত্যন্ত বিচিত্র হলেও, কিছু সাধারণ দার্শনিক ধারণা এদেরকে একসূত্রে বাঁধে। যেমন: কর্মফল (Karma, অর্থাৎ কাজের ফল), সংসার (Samsara, বা জন্ম-মৃত্যুর চক্র), পুনর্জন্ম (Reincarnation) এবং এই চক্র থেকে মুক্তি বা মোক্ষ/নির্বাণ (Moksha/Nirvana) লাভের ধারণা।
- পূর্ব এশীয় বা তাওইক ধর্ম (East Asian or Taoic Religions): এই ধর্মগুলো মূলত চীনে উদ্ভূত হয়েছে এবং পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এদের মধ্যে প্রধান হলো তাওবাদ, কনফুসিয়ানিজম এবং জাপানের শিন্তো। এই ধর্মগুলো সাধারণত পারলৌকিক মুক্তির চেয়ে ইহলৌকিক জীবনে সম্প্রীতি (Harmony) স্থাপন – ব্যক্তির সাথে সমাজের, সমাজের সাথে প্রকৃতির এবং প্রকৃতির সাথে মহাজাগতিক শক্তির (তাও) ভারসাম্য রক্ষার ওপর বেশি জোর দেয়।
সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস
সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্মকে তার সামাজিক সংগঠন ও সমাজের সাথে তার সম্পর্কের ভিত্তিতেও ভাগ করেন।
- একলেসিয়া বা চার্চ (Ecclesia/Church): এটি একটি বৃহৎ, সুসংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যা সমাজের প্রভাবশালী সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর একটি পেশাদার পুরোহিত শ্রেণী, নির্দিষ্ট ধর্মমত এবং আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ থাকে। প্রায়শই এটি রাষ্ট্রধর্ম (State Religion) হিসেবে কাজ করে, যেমন: ইংল্যান্ডের অ্যাংলিকান চার্চ বা সৌদি আরবের ওয়াহাবি ইসলাম।
- ডিনোমিনেশন (Denomination): এটিও একটি বৃহৎ ও সুসংগঠিত ধর্মীয় গোষ্ঠী, কিন্তু এটি রাষ্ট্রের সাথে একীভূত নয় এবং বহুত্ববাদী (Pluralistic) সমাজে অন্য অনেক গোষ্ঠীর পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করে। যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপ্টিস্ট, মেথডিস্ট, প্রেসবিটেরিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন খ্রিস্টান ডিনোমিনেশন।
- সেক্ট (Sect): এটি মূল ধর্মীয় ধারা (চার্চ বা ডিনোমিনেশন) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি ছোট গোষ্ঠী। এরা সাধারণত মূল ধারার বিশ্বাস বা আচরণকে ‘দূষিত’ বা ‘আপোসকামী’ বলে মনে করে এবং ধর্মের একটি ‘বিশুদ্ধ’ রূপে ফিরে যেতে চায়। এরা প্রায়ই পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে নিজেদের কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখে।
- কাল্ট বা নতুন ধর্মীয় আন্দোলন (Cult or New Religious Movement – NRM): এই শব্দটি প্রায়ই নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হলেও, সমাজবিজ্ঞানে এটি এমন একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে বোঝায়, যার বিশ্বাস ও আচার পারিপার্শ্বিক সমাজের কাছে সম্পূর্ণ নতুন বা বিজাতীয় বলে মনে হয়। এদের প্রায়ই একজন ক্যারিশমেটিক নেতা (Charismatic Leader) থাকেন। অনেক বড় ধর্মই (যেমন: খ্রিস্টধর্ম) তার শুরুর দিকে একটি ছোট কাল্ট হিসেবে বিবেচিত হতো।
এই শ্রেণীবিন্যাসগুলো আমাদের ধর্মের বিপুল বৈচিত্র্যকে বুঝতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখা জরুরি যে, এগুলো কোনো নিশ্ছিদ্র বাক্স নয়। অনেক ধর্মই একাধিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই বর্ণালী আমাদের দেখায় যে, পরম সত্যের সন্ধান বা জীবনের অর্থ খোঁজার মানবিক আকাঙ্ক্ষা কত ভিন্ন ভিন্ন পথে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।
ধর্মের শরীরতত্ত্ব: যা দিয়ে ধর্ম তৈরি হয়
বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বাহ্যিকভাবে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, গভীরভাবে দেখলে তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ গাঠনিক উপাদান (Structural Elements) খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো অনেকটা মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো – আলাদা আলাদা কাজ করলেও সবগুলো মিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ শরীর তৈরি করে। ধর্মতাত্ত্বিক নিনিয়ান স্মার্ট (Ninian Smart) ধর্মের এই সাধারণ উপাদানগুলোকে ধর্মের ‘সাতটি মাত্রা’ (Seven Dimensions of Religion) বলে অভিহিত করেছেন, যা আমাদের ধর্মের এই অভ্যন্তরীণ কাঠামো বুঝতে সাহায্য করে (The World’s Religions, 1998)। এই মাত্রাগুলো হলো: আখ্যান, মতবাদ, নৈতিকতা, আচার, অভিজ্ঞতা, প্রতিষ্ঠান এবং বস্তুগত রূপ। এই অধ্যায়ে আমরা এই উপাদানগুলোকেই আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব, যা দিয়ে পৃথিবীর সব ধর্ম তার শরীর গঠন করে।
বিশ্বাস, আখ্যান ও মতবাদ (Belief, Narrative, and Doctrine): ধর্মের মস্তিষ্ক
প্রতিটি ধর্মের কেন্দ্রে থাকে তার বিশ্বাস ব্যবস্থা, যা হলো ধর্মের মস্তিষ্ক বা সফটওয়্যার। এই বিশ্বাস ব্যবস্থা সাধারণত দুটি রূপে প্রকাশ পায়: আখ্যান বা পুরাণ এবং মতবাদ বা ডগমা।
- পবিত্র আখ্যান বা পুরাণ (Sacred Narrative/Myth): ধর্ম শুধু কিছু বিমূর্ত ধারণার সমষ্টি নয়, এটি মূলত এক শক্তিশালী গল্পের জগৎ। জগৎ কীভাবে তৈরি হলো (Creation Myth), মানুষের পৃথিবীতে আগমন কীভাবে ঘটল, কেন পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট আছে, জীবনের উদ্দেশ্য কী, মৃত্যুর পর কী হয়, এবং কীভাবে একদিন এই জগতের সমাপ্তি ঘটবে (Eschatology) – এইসব বড় বড় অস্তিত্বের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ধর্মগুলো অসাধারণ সব গল্প বা আখ্যান তৈরি করে। বাইবেলের জেনেসিস, কুরআনের আদম-এর কাহিনী, হিন্দুধর্মের সমুদ্রমন্থন বা মেসোপটেমিয়ার গিলগামেশ মহাকাব্য – এগুলো নিছক শিশুতোষ গল্প নয়। বিশ্বাসীদের কাছে এগুলো হলো পরম সত্য, যা তাদের জগৎ-দৃষ্টি (Worldview) ও জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। তুলনামূলক পুরাণতত্ত্ববিদ জোসেফ ক্যাম্পবেল (Joseph Campbell) দেখিয়েছেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন পুরাণে কিছু সাধারণ থিম বা আর্কিটাইপ (Archetype) বারবার ফিরে আসে। তার বিখ্যাত ‘বীরের যাত্রা’ (The Hero’s Journey) বা ‘মনোমিথ’ (Monomyth) তত্ত্বে তিনি দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধ, যিশু, মোজেস বা রাম – অনেক ধর্মীয় মহাপুরুষের জীবনকাহিনীতেই একটি সাধারণ প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায়: সাধারণ জগৎ থেকে আহ্বান, নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে জ্ঞান বা শক্তি লাভ এবং পরিশেষে সেই জ্ঞান নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ে ফিরে আসা (The Hero with a Thousand Faces, 1949)। এই আখ্যানগুলো আমাদের জীবনের সংগ্রামের একটি রূপক মডেল সরবরাহ করে।
- মতবাদ বা ডগমা (Doctrine/Dogma): যখন এই পবিত্র আখ্যানগুলোর ভেতরের বিশ্বাসগুলোকে সুসংগঠিত, দার্শনিক এবং যুক্তিনির্ভর রূপ দেওয়া হয়, তখন তা মতবাদ বা ডগমা-তে পরিণত হয়। খ্রিষ্টধর্মের ট্রিনিটি (Trinity) বা ত্রিত্ববাদ, ইসলামের তাওহিদ বা একত্ববাদ, বৌদ্ধধর্মের চতুরার্য সত্য (Four Noble Truths) বা হিন্দুধর্মের কর্মফল ও পুনর্জন্মের ধারণা – এগুলো সবই সুসংহত মতবাদ। মতবাদগুলো ধর্মের বৌদ্ধিক ভিত্তি তৈরি করে এবং বিশ্বাসকে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো দেয়। তবে অনেক সময় এই মতবাদগুলোই আবার ধর্মের ভেতর বিভিন্ন বিভাজন ও সংঘাতের জন্ম দেয়।
আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতীক (Ritual and Symbol): ধর্মের হৃদস্পন্দন
বিশ্বাস যদি ধর্মের মস্তিষ্ক হয়, তবে আচার-অনুষ্ঠান হলো তার হৃদস্পন্দন। এটি বিশ্বাসকে জীবন্ত, মূর্ত এবং আবেগঘন করে তোলে। ধর্ম শুধু মাথায় ধারণ করার বিষয় নয়, এটি শরীরে ধারণ করার, পালন করার বিষয়।
- আচার-অনুষ্ঠান (Ritual): প্রার্থনা, পূজা, উপবাস, তীর্থযাত্রা, বলিদান, জপ – এই সবই হলো রিচুয়ালের উদাহরণ। এই পুনরাবৃত্তিমূলক এবং প্রতীকী কাজগুলোর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রথমত, এটি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া বা প্রতি রবিবার গির্জায় যাওয়া বিশ্বাসকে একটি দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করে। দ্বিতীয়ত, এটি গোষ্ঠীর মানুষকে একসাথে এনে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে (যা আমরা ডুর্খাইমের তত্ত্বে দেখেছি)। তৃতীয়ত, এটি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলোকে অর্থবহ করে তোলে। নৃবিজ্ঞানী ভিক্টর টার্নার (Victor Turner) এবং আর্নল্ড ভ্যান গেনেপের (Arnold van Gennep) কাজ থেকে আমরা জানি যে, বিভিন্ন ‘উত্তরণের আচার’ (Rites of Passage) – যেমন জন্ম, নামকরণ, বয়ঃসন্ধি (যেমন: উপনয়ন বা বার মিৎজভা), বিবাহ এবং মৃত্যু – ব্যক্তিকে জীবনের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তরণে সাহায্য করে এবং সামাজিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখে (The Ritual Process, 1969; The Rites of Passage, 1909)।
- প্রতীক (Symbol): ধর্ম প্রতীকের ভাষায় কথা বলে। একটি সাধারণ ক্রস শুধু দুটি সরলরেখা নয়, এটি ত্যাগ, মুক্তি এবং ভালোবাসার এক গভীর প্রতীক। একটি চাঁদ-তারা, একটি স্বস্তিকা, একটি ওঁ (Aum) অক্ষর বা ডেভিডের তারকা (Star of David) – এই প্রতীকগুলো একটি জটিল বিশ্বাস ব্যবস্থাকে এবং একটি সম্প্রদায়ের পরিচয়কে একটিমাত্র শক্তিশালী চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করে। প্রতীকগুলো আমাদের সাধারণ জগতের সাথে পবিত্র জগতের সংযোগ স্থাপন করে।
পবিত্র ও অপবিত্রের বিভাজন (The Sacred and the Profane): ধর্মের সীমানা
এমিল ডুর্খাইমের (Émile Durkheim) মতে, সব ধর্মের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো জগৎকে দুটি মৌলিক ও সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে ভাগ করা – পবিত্র (Sacred) ও সাধারণ বা জাগতিক (Profane)। পবিত্র বস্তু, স্থান, সময় বা ব্যক্তি সাধারণ জগৎ থেকে আলাদা এবং বিশেষ ভয়, সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য। এই বিভাজনটি ধর্মের সীমানা প্রাচীর তৈরি করে।
যেমন: মন্দির, মসজিদ বা গির্জা হলো পবিত্র স্থান, যেখানে সাধারণ জীবনের নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়। রমজান মাস বা বড়দিন হলো পবিত্র সময়। বেদ, বাইবেল বা কুরআন হলো পবিত্র বস্তু। আর পুরোহিত, ইমাম, নবী বা সন্ত হলেন পবিত্র ব্যক্তি। এই বিভাজনই ধর্মীয় জগৎকে আমাদের দৈনন্দিন, জাগতিক জগৎ থেকে আলাদা করে তোলে এবং তাকে এক বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতা দেয় (Durkheim, 1912)। এই পবিত্রের অনুভবই ধর্মকে অন্য সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে।
নৈতিক ও আইনি বিধিবিধান (Moral and Legal Codes): ধর্মের সংবিধান
প্রায় সব ধর্মই তার অনুসারীদের জন্য কিছু অবশ্য পালনীয় নৈতিক নিয়মকানুন বা সংবিধান তৈরি করে। এটি বলে দেয় কোনটি পুণ্য এবং কোনটি পাপ, কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম, কোনটি উচিত এবং কোনটি অনুচিত। ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের দশ আজ্ঞা (Ten Commandments), বৌদ্ধধর্মের পঞ্চশীল (Five Precepts) বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ইসলামের শরিয়াহ আইন (Sharia Law) বা হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম ধর্ম – এই সবই এর উদাহরণ।
এই নৈতিক বিধিগুলো একদিকে যেমন ব্যক্তির আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক এবং যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে একটি শক্তিশালী কাঠামো সরবরাহ করে। অনেক সময় এই নৈতিক নিয়মগুলোই সমাজের আনুষ্ঠানিক আইনে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম এখানে শুধু পারলৌকিক মুক্তির পথই দেখায় না, ইহলৌকিক জীবনযাপনের একটি পূর্ণাঙ্গ নীলনকশাও প্রদান করে।
ধর্মীয় অভিজ্ঞতা (Religious Experience): ধর্মের আত্মা
অনেক বিশ্বাসীর কাছে, এবং উইলিয়াম জেমসের (William James) মতো অনেক দার্শনিকের কাছেও, ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা মতবাদ নয়, বরং ব্যক্তির গভীর, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বা মরমী অভিজ্ঞতা (Mystical Experience)। এটি হতে পারে গভীর প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের উপস্থিতি বা ভালোবাসা অনুভব করা, প্রকৃতির বিশালতার (যেমন: অনন্ত নক্ষত্রখচিত আকাশ বা উত্তাল সমুদ্র) সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হওয়া, অথবা ধ্যানের মাধ্যমে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি ও একাত্মতা লাভ করা।
জার্মান ধর্মতাত্ত্বিক রুডলফ অটো (Rudolf Otto) এই মৌলিক ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে ‘নুমিনাস’ (Numinous) বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি একটি যুক্তিবহির্ভূত অনুভূতি, যা একই সাথে ‘ভয়ংকর রহস্য’ (Mysterium Tremendum) – যা আমাদের ক্ষুদ্রতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এবং ‘আকর্ষণীয় মুগ্ধতা’ (Mysterium Fascinans) – যা আমাদের সেই পরম সত্তার দিকে চুম্বকের মতো টানে (The Idea of the Holy, 1923)। উইলিয়াম জেমস তাঁর ক্লাসিক গ্রন্থ The Varieties of Religious Experience-এ দেখিয়েছেন যে, এই তীব্র অভিজ্ঞতাগুলো মানুষের জীবনকে এবং তার বিশ্বদৃষ্টিকে গভীরভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারে (James, 1902)। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করে তোলে।
সামাজিক সংগঠন ও সম্প্রদায় (Social Organization and Community): ধর্মের শরীর
ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, এটি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও। বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত করার জন্য একটি সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজন। প্রতিটি বড় ধর্মেরই একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে। এর মধ্যে রয়েছে:
- বিশেষজ্ঞ শ্রেণী: যেমন – পুরোহিত, ইমাম, পাদ্রি, রাব্বি, ভিক্ষু, পণ্ডিত – যারা ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা, আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বে থাকেন।
- সাধারণ অনুসারী (Laity): যারা এই বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা অনুসরণ করে।
- প্রতিষ্ঠান: যেমন – মন্দির, মঠ, মসজিদ, গির্জা, মাদ্রাসা, চ্যারিটি – যারা ধর্মের ভৌত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
এই সংগঠনগুলো ধর্মের শিক্ষা, ঐতিহ্য ও সম্পদকে রক্ষা করে এবং সমাজে ধর্মের প্রভাব বিস্তার করে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ‘উম্মা’ তার সদস্যদের এক ধরনের শক্তিশালী পরিচয় (Identity) এবং অন্তর্ভুক্তির (Belonging) অনুভূতি দেয়। আধুনিক, বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে এই সম্প্রদায়ের অনুভূতি অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে।
এই গাঠনিক উপাদানগুলো – বিশ্বাস, আচার, নৈতিকতা, অভিজ্ঞতা এবং সম্প্রদায় – একে অপরের সাথে জটিলভাবে জড়িত। সবগুলো মিলেই ধর্ম নামক এই শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী মানবিক প্রপঞ্চটি তৈরি করে।
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম: পবিত্রতার ধারক ও ক্ষমতার পিঞ্জর
ব্যক্তিগত বিশ্বাস যখন একটি সামাজিক কাঠামো, নির্দিষ্ট নিয়মকানুন, অনুক্রম (Hierarchy) এবং আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠিত রূপ লাভ করে, তখন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম (Institutional Religion) বলা হয়। এটি ধর্মের সেই রূপ, যা আমরা মন্দির, মসজিদ, গির্জা, মঠ বা সিনাগগের মতো দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেখতে পাই। এটি সেই কাঠামো যা ধর্মকে ব্যক্তিগত অনুভূতি বা দর্শনের জগৎ থেকে বের করে এনে একটি শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করে। কিন্তু এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপটি ধর্মের জন্য একাধারে আশীর্বাদ ও অভিশাপ। এটি যেমন পবিত্রতার ধারক, তেমনই ক্ষমতার এক লৌহ পিঞ্জরও বটে।
প্রতিষ্ঠানের জন্ম: ক্যারিশমা থেকে কোড
যেকোনো বড় ধর্মের যাত্রা শুরু হয় একজন ক্যারিশম্যাটিক (Charismatic) নেতার হাত ধরে – যেমন বুদ্ধ, যিশু বা মুহাম্মদ। এই নেতারা তাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার জোরে মানুষকে আকর্ষণ করেন। তাদের জীবদ্দশায় ধর্মটি থাকে মূলত একটি অনানুষ্ঠানিক আন্দোলন, যা গুরু-শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।
কিন্তু নেতার মৃত্যুর পর আন্দোলনটি এক গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়: কীভাবে এই বার্তা ও ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা যাবে? এখানেই সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের (Max Weber) বিখ্যাত ধারণা “ক্যারিশমার রুটিনাইজেশন” (Routinization of Charisma) প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ওয়েবারের মতে, ক্যারিশম্যাটিক নেতার অনুপস্থিতিতে আন্দোলনটিকে টিকে থাকার জন্য তার অসাধারণত্বকে সাধারণ, দৈনন্দিন এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য কাঠামোয় রূপান্তরিত করতে হয় (Weber, 1978)। এই প্রক্রিয়াতেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের জন্ম হয়। এর কয়েকটি ধাপ রয়েছে:
- ১. মতবাদের প্রতিষ্ঠা (Dogma): নেতার বিক্ষিপ্ত শিক্ষা ও বাণীগুলোকে একত্রিত করে একটি সুসংহত ধর্মমত বা ডগমা তৈরি করা হয়। পবিত্র গ্রন্থ সংকলিত হয়, যা সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়।
- ২. অনুক্রমের সৃষ্টি (Hierarchy): ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা, আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ শ্রেণী – যেমন পুরোহিত, পাদ্রি, ইমাম বা ভিক্ষু – গড়ে ওঠে। এই শ্রেণীটিই প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।
- ৩. আইন ও আচারের প্রমিতকরণ (Standardization): নৈতিক নিয়মকানুনগুলোকে সুনির্দিষ্ট আইনে (যেমন: শরিয়াহ বা ক্যানন ল) রূপান্তরিত করা হয় এবং উপাসনা বা প্রার্থনার মতো আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে একটি প্রমিত (Standardized) রূপ দেওয়া হয়, যা সবাই একইভাবে পালন করে।
প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী: সামাজিক অট্টালিকার ভিত্তি
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের এই কাঠামো সমাজের জন্য কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton)-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, এর কিছু সুস্পষ্ট (Manifest) এবং কিছু প্রচ্ছন্ন (Latent) কার্যাবলী রয়েছে (Merton, 1968)।
- ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সঞ্চালন: প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট কাজ হলো ধর্মের মূল বিশ্বাস, আখ্যান ও নৈতিকতাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রায় অবিকৃতভাবে পৌঁছে দেওয়া। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া যেকোনো আধ্যাত্মিক আন্দোলন সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যেতে বা বিকৃত হয়ে যেতে বাধ্য। এটি একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক স্মৃতি তৈরি করে।
- সম্প্রদায় ও সামাজিক সংহতি: এটি তার অনুসারীদের একটি শক্তিশালী পরিচয় এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি দেয়। এই ধর্মীয় সম্প্রদায় (যেমন: চার্চ, উম্মা বা সংঘ) তার সদস্যদের জন্য এক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Net) হিসেবে কাজ করে। সমাজবিজ্ঞানী পিটার বার্জারের (Peter L. Berger) ভাষায়, এটি আমাদের বিশৃঙ্খল জগতের ওপর এক ‘পবিত্র ছাদ’ (Sacred Canopy) বিছিয়ে দেয়, যা আমাদের অর্থহীনতার ভয় থেকে রক্ষা করে (Berger, 1967)।
- নৈতিক কাঠামো ও সামাজিক সেবা: প্রতিষ্ঠান একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য সাধারণ নৈতিকতার ভিত্তি তৈরি করে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও দাতব্য কাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সেবা প্রদান করে, যা রাষ্ট্রের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।
প্রতিষ্ঠানের বাইরে ধর্ম: মরমীবাদ থেকে লোকবিশ্বাস
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই ধর্মের একমাত্র রূপ নয়। এর সমান্তরালে বা কখনও কখনও এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ধর্মের আরও অনেক বিচিত্র প্রকাশ রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যেখানে বহির্মুখী (Exoteric), কাঠামোগত এবং সম্মিলিত, সেখানে এর বিকল্পগুলো প্রায়শই অন্তর্মুখী (Esoteric), স্বতঃস্ফূর্ত এবং ব্যক্তিগত।
- মরমীবাদ (Mysticism): প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী বিকল্প হলো মরমীবাদ। মরমীবাদের মূল কথা হলো ঈশ্বরের বা পরম সত্তার সাথে প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত এবং অপরোক্ষ (Unmediated) অভিজ্ঞতা লাভ। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যেখানে পুরোহিত, ধর্মগ্রন্থ এবং আচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর কথা বলে, সেখানে মরমীবাদ এই মধ্যস্থতাকারীদের অস্বীকার করে। সুফিবাদের (ইসলাম), কাব্বালার (ইহুদি ধর্ম), জেন বৌদ্ধধর্ম বা খ্রিস্টান মরমীদের (যেমন: সেন্ট টেরেসা অফ আভিলা) কাছে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই সর্বোচ্চ প্রমাণ। এই কারণে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রায়শই মরমীদের সন্দেহের চোখে দেখে, কারণ তাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে।
- লোকধর্ম (Folk Religion): এটি হলো সাধারণ মানুষের দ্বারা চর্চিত ধর্ম, যা প্রাতিষ্ঠানিক ‘বিশুদ্ধ’ মতবাদের সাথে স্থানীয় বিশ্বাস, প্রথা এবং প্রায়শই জাদু ও কুসংস্কারকে মিশিয়ে নেয়। লোকধর্ম ধর্মতত্ত্বের জটিল বিতর্কের চেয়ে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যা (যেমন: রোগমুক্তি, ভালো ফসল, অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা) নিয়ে বেশি আগ্রহী। পীরের মাজারে মানত করা, তাবিজ-কবচ ব্যবহার করা বা স্থানীয় দেব-দেবীর পূজা করা – এগুলো সবই লোকধর্মের উদাহরণ, যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কঠোর নিয়মকানুনের বাইরে এক সমান্তরাল জগৎ তৈরি করে।
প্রতিষ্ঠানের নেতিবাচক দিক: ক্ষমতার লৌহ পিঞ্জর
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যে কাঠামো তাকে স্থায়িত্ব ও শক্তি দেয়, সেই একই কাঠামো তার অন্ধকার দিকগুলোরও জন্ম দেয়।
- ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও গোঁড়ামি (Orthodoxy): প্রতিষ্ঠান মাত্রই ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি করে। ধর্মীয় নেতারা প্রায়শই নিজেদেরকে সত্যের একমাত্র রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং যেকোনো ভিন্নমত বা নতুন ব্যাখ্যাকে ‘ধর্মদ্রোহিতা’ (Heresy) বলে চিহ্নিত করে কঠোরভাবে দমন করেন। ইতিহাসবিদ বার্ট ডি. আরমন (Bart D. Ehrman) দেখিয়েছেন, কীভাবে আদি খ্রিস্টধর্মের বহু বিচিত্র ধারার মধ্যে থেকে একটি ধারা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার জোরে নিজেকে ‘অর্থোডক্স’ বা বিশুদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং বাকিদের বিলুপ্ত করে দিয়েছিল (Ehrman, 2003)।
- স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনে বাধা: প্রতিষ্ঠান তার স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য স্বভাবতই রক্ষণশীল হয়। ফলে এটি নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পরিবর্তিত সামাজিক মূল্যবোধ (যেমন: নারীর অধিকার বা লিঙ্গ সমতা) এবং অভ্যন্তরীণ সংস্কারের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এতে ধর্ম জীবন্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা না থেকে কিছু মৃত ডগমার সমষ্টিতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।
- আধ্যাত্মিকতার অবক্ষয়: যখন প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকাটাই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন এর আমলাতান্ত্রিক (Bureaucratic) জটিলতা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মোহ ধর্মের আধ্যাত্মিক সারবস্তুকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। তখন ধর্ম আর মুক্তির পথ থাকে না, হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। আচার-অনুষ্ঠানগুলো পরিণত হয় অর্থহীন যান্ত্রিকতায়।
- বর্জনশীলতা ও সংঘাত: শক্তিশালী ‘আমরা’ বনাম ‘ওরা’ বিভাজন তৈরি করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রায়শই অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা এবং সহিংসতার জন্ম দেয়। ইতিহাসের অধিকাংশ ধর্মযুদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের এই বর্জনশীল (Exclusionary) ভূমিকা ক্রিয়াশীল ছিল।
আধুনিক বিশ্বে সংকট ও রূপান্তর
একুশ শতকে এসে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম এক নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। পশ্চিমে “আধ্যাত্মিক কিন্তু ধার্মিক নয়” (Spiritual but not Religious – SBNR) আন্দোলনের উত্থান এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ (Fuller, 2001)। বহু মানুষ এখন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কঠোর নিয়মকানুন, রাজনৈতিক বিতর্ক এবং ক্ষমতার খেলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এক ধরনের ব্যক্তিগত, স্ব-নির্বাচিত আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করছে। এটি অনেকটা মরমীবাদের আধুনিক, ভোগবাদী (Consumerist) সংস্করণ। তারা ধর্মের আধ্যাত্মিকতাটুকু চায় – যেমন ধ্যান, যোগব্যায়াম বা প্রকৃতির উপাসনা – কিন্তু তার প্রাতিষ্ঠানিক বোঝা বহন করতে চায় না।
উপসংহারে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম একটি দ্বিধারী তলোয়ার। এটি ছাড়া কোনো ধর্মীয় আন্দোলন বিশ্বব্যাপী এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকতার এই বর্মই অনেক সময় ব্যক্তিকে বন্দী করে ফেলে। এটি পবিত্রতার সেই মাটির পাত্র, যা জলকে ধারণ করে, কিন্তু পাত্রটি অনেক সময় জলের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর তাই, ধর্মের ইতিহাসে প্রাতিষ্ঠানিক ধারার পাশাপাশি সবসময়ই সেইসব মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা পাত্রটিকে ভেঙে সরাসরি ঝর্ণার জল পান করতে চেয়েছেন।
সভ্যতার কারিগর: সমাজ ও সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব
ধর্ম মানব অভিজ্ঞতার কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; এটি সভ্যতার মূল ভূখণ্ডের সাথে সহস্র শিরা-উপশিরা দিয়ে যুক্ত। এটি কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা পারলৌকিক মুক্তির ব্যাপার নয়, বরং মানব সমাজের গঠন, বিবর্তন এবং প্রকাশের এক অন্যতম প্রধান কারিগর। মানুষের রাজনৈতিক সংগঠন, অর্থনৈতিক আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্বেষা এবং শৈল্পিক সৃজনশীলতার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রই ধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত বা কখনও কখনও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এটি যেমন অসাধারণ সব সৌধ নির্মাণ করেছে, তেমনই আবার অনেক প্রগতির পথকে রুদ্ধও করেছে। সভ্যতার এই জটিল নকশায় ধর্মের আলো-ছায়ার খেলা বুঝতে হলে এর বহুমাত্রিক প্রভাবকে আরও কাছ থেকে দেখা প্রয়োজন।
ধর্ম ও রাজনীতি: এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন
ইতিহাসের পাতায় ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক এক অবিচ্ছেদ্য কালিতে লেখা। বেশিরভাগ সময়ই এই দুটি শক্তি একে অপরের হাত ধরে চলেছে, কখনও একে অপরকে শক্তিশালী করেছে, আবার কখনও একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভয়ঙ্কর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।
- ঐশ্বরিক বৈধতা এবং ধর্মতন্ত্র: প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে শাসকের ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়ার সবচেয়ে সহজ এবং শক্তিশালী উপায় ছিল তাকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করা। প্রাচীন মিশরের ফারাওরা ছিলেন সরাসরি দেবতা হোরাসের পার্থিব রূপ। মেসোপটেমিয়ার রাজারা ছিলেন দেবতাদের প্রধান প্রতিনিধি। চীনের শাসকরা শাসন করতেন ‘স্বর্গের আজ্ঞা’ (Mandate of Heaven)-র জোরে, যা হারালে তাদের শাসনের অধিকারও চলে যেত। মধ্যযুগের ইউরোপে রাজারা শাসন করতেন ‘রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকার’ (Divine Right of Kings) তত্ত্বে, যা প্রচার করত যে রাজার ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য। এই ঐশ্বরিক বৈধতা (Divine Legitimacy) শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সরাসরি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে চিত্রিত করত, যা সাধারণ মানুষের মনে ভয় ও আনুগত্য তৈরি করত। যখন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা একীভূত হয়ে যায়, তখন জন্ম নেয় ধর্মতন্ত্র (Theocracy), যেমনটি দেখা গেছে প্রাচীন ইসরায়েল, মধ্যযুগীয় পোপশাসিত রাজ্য বা আধুনিক ইরানের শাসনব্যবস্থায়। ইসলামী খিলাফতে খলিফা ছিলেন একই সাথে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা (আমিরুল মুমিনিন), যা এই দুইয়ের একীভূত রূপকে তুলে ধরে।
- ধর্মীয় আইন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: ধর্ম শুধু শাসককে বৈধতা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, এটি সমাজের জন্য আইন ও নৈতিকতার কাঠামোও তৈরি করে দিয়েছে। ইসলামের শরিয়াহ, ইহুদি ধর্মের হালাখা বা খ্রিস্টধর্মের ক্যানন ল শুধু ব্যক্তিগত ধর্মচর্চার নিয়মকানুন নয়, এগুলো বিবাহ, উত্তরাধিকার, বাণিজ্য, অপরাধ ও শাস্তির মতো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই ধর্মীয় আইনগুলো সমাজকে একটি সুসংহত নৈতিক ভিত্তি দিয়েছে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে।
- বিপ্লব, প্রতিরোধ ও জাতীয়তাবাদ: ধর্ম যেমন স্থিতাবস্থা বজায় রাখার হাতিয়ার, তেমনই এটি বিপ্লব ও প্রতিরোধের এক শক্তিশালী উৎসও হতে পারে। শাসকের শোষণ বা অবিচার যখন চরমে পৌঁছায়, তখন প্রায়ই ধর্মীয় আদর্শ ও নেতারা সাধারণ মানুষকে এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করেছেন। আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলনে (American Civil Rights Movement) মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের মতো নেতারা ব্ল্যাক চার্চকে কেন্দ্র করে অহিংস প্রতিরোধের এক বিশাল শক্তি তৈরি করেছিলেন। ১৯৭৯ সালের ইরানের বিপ্লবে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে শিয়া ইসলামের বিপ্লবী ব্যাখ্যা শাহের পতন ঘটিয়েছিল। লাতিন আমেরিকায় নিপীড়িত দরিদ্র মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে ক্যাথলিক চার্চের একটি অংশ ‘মুক্তি-ধর্মতত্ত্ব’ (Liberation Theology)-এর জন্ম দিয়েছিল, যা মার্ক্সীয় চিন্তার সাথে খ্রিস্টীয় করুণার এক মেলবন্ধন। একইভাবে, ধর্ম জাতীয়তাবাদী পরিচিতি নির্মাণেও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। জায়নবাদ (Zionism) ইহুদি ধর্মের ভিত্তিতে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতার পর ধর্মের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।
- ধর্মনিরপেক্ষতার জটিলতা: আধুনিক যুগে ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির ফলস্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)-এর ধারণা জনপ্রিয় হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই বিচ্ছেদ খুব কম দেশেই পুরোপুরি সম্ভব হয়েছে। ফ্রান্সের লাইসিতে (laïcité)-র মতো কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে শুরু করে ভারতের মতো বহুত্ববাদী মডেল, যেখানে রাষ্ট্র সব ধর্মকে সমান চোখে দেখে – এর রূপ বিভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশেও সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট বেলা (Robert Bellah) ‘সিভিল রিলিজিয়ন’ (Civil Religion)-এর ধারণা খুঁজে পেয়েছেন। এখানে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের কথা না বলেও ‘ঈশ্বর’, ‘স্বাধীনতা’, ‘ত্যাগ’-এর মতো ধর্মীয় অনুষঙ্গ ব্যবহার করে জাতীয় ঐক্য ও উদ্দেশ্য তৈরি করা হয়। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, পতাকার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, জাতীয় বীরদের স্মরণ – এগুলো এই সিভিল রিলিজিয়নেরই আচার-অনুষ্ঠানের অংশ (Bellah, 1967)।
ধর্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর যখন ভাবা হচ্ছিল যে বিশ্ব রাজনীতি মূলত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হবে, তখন ধর্ম এক অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মঞ্চে পুনরায় আবির্ভূত হয়। এটি প্রমাণ করে যে, বিশ্বায়ন কেবল অর্থনীতি বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি ধর্মীয় পরিচয়কেও বিশ্বমঞ্চে নতুন করে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।
- সভ্যতার সংঘাত এবং পরিচয়ের রাজনীতি: এই নতুন বাস্তবতাকে বুঝতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন (Samuel P. Huntington) তাঁর বিতর্কিত কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী ‘সভ্যতার সংঘাত’ (Clash of Civilizations) তত্ত্বে যুক্তি দেখান যে, ঠান্ডা যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের প্রধান সংঘাতগুলো আর আদর্শগত বা অর্থনৈতিক হবে না, বরং সেগুলো হবে সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাভিত্তিক। আর এই সভ্যতাগুলোর মূল ভিত্তি হলো ধর্ম। হান্টিংটনের মতে, পশ্চিমা খ্রিস্টীয় সভ্যতা, ইসলামী সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা বা কনফুসীয় সভ্যতার মতো বড় বড় সভ্যতাগুলোর মধ্যকার বিভেদরেখাই (Fault Lines) হবে ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্র (Huntington, 1996)। ৯/১১-এর সন্ত্রাসী হামলা এবং তৎপরবর্তী ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ (War on Terror)-কে অনেকেই এই তত্ত্বের বাস্তব উদাহরণ হিসেবে দেখেছেন। যদিও এই তত্ত্বটি সরলীকরণের অভিযোগে সমালোচিত, তবুও এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একবিংশ শতাব্দীর অনেক আন্তর্জাতিক সংঘাত – যেমন ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংকট বা ভারত-পাকিস্তান বিরোধ – এর গভীরে ধর্মীয় পরিচয়ের রাজনীতি এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।
- আন্তর্জাতিক জোট এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিনেতা: ধর্ম কেবল সংঘাতেরই জন্ম দেয় না, এটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট ও সহযোগিতার ভিত্তিও তৈরি করে। সাধারণ ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (Organisation of Islamic Cooperation – OIC) এর একটি বড় উদাহরণ। একইভাবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই শক্তিশালী আন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিনেতা (Transnational Actor) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভ্যাটিকান বা ক্যাথলিক চার্চ শুধু একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই নয়, এটি একটি সার্বভৌম সত্তা যার বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে, আল-কায়েদা বা আইএস-এর মতো উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলো ধর্মের একটি চরমপন্থী ব্যাখ্যা ব্যবহার করে এমন এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সার্বভৌমত্বকেই চ্যালেঞ্জ করে (Thomas, 2005)।
- ধর্মভিত্তিক কূটনীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা: সহিংসতার এই চিত্রের বিপরীতে, ধর্ম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি ইতিবাচক ভূমিকাও পালন করতে পারে। এই ধারণাটি ‘ধর্মভিত্তিক কূটনীতি’ (Faith-Based Diplomacy) নামে পরিচিত। ধর্মীয় নেতা ও সংগঠনগুলো প্রায়শই এমন নৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হন, যা তাদের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে মধ্যস্থতাকারী বা শান্তিস্থাপক হিসেবে কাজ করতে সাহায্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ অবসানে আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটুর ভূমিকা বা বিভিন্ন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (Interfaith Dialogue) বিশ্বজুড়ে বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি বাড়াতে কাজ করে। এছাড়াও, বিশ্বের বৃহত্তম মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোর একটি বড় অংশই ধর্মভিত্তিক (যেমন: কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ইসলামিক রিলিফ), যারা যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিয়ে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Johnston, 2003)। সুতরাং, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ধর্ম একটি দ্বিধারী তলোয়ারের মতো – এটি যেমন বিভেদ ও সংঘাতের উৎস হতে পারে, তেমনই হতে পারে সংযোগ ও শান্তির সেতুবন্ধন।
ধর্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যান এখানে – ধর্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (Religion and International Relations): এক অদৃশ্য সুতার পাঠোদ্ধার
ধর্ম ও অর্থনীতি: ওয়েবারের থিসিস ও তার বাইরে
ধর্মকে প্রায়শই পার্থিব জগৎবিমুখ হিসেবে দেখা হলেও, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ও আচরণকে এটি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই সম্পর্কের বিশ্লেষণে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের (Max Weber) কাজকে মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়।
- ওয়েবারের প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিশাস্ত্র: ওয়েবার তাঁর বিখ্যাত বই The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism-এ দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টধর্মের কিছু নির্দিষ্ট বিশ্বাস, বিশেষ করে ক্যালভিনিজম, আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশে একটি অনুকূল মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরি করেছিল। ক্যালভিনিস্টরা ‘পূর্বনির্ধারণ’ (Predestination) তত্ত্বে বিশ্বাস করত, অর্থাৎ ঈশ্বর আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন কে স্বর্গে যাবে। এটি মানুষের মনে এক তীব্র উদ্বেগ তৈরি করত। এই উদ্বেগ থেকে মুক্তির একটি পরোক্ষ উপায় ছিল পার্থিব সাফল্য অর্জন, যা ঈশ্বরের কৃপার চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হতো। তাই তারা কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা, সততা এবং মিতব্যয়িতাকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে। অর্জিত মুনাফা ভোগবিলাসে ব্যয় না করে পুনরায় বিনিয়োগ করাটা এক ধরনের ‘পার্থিব বৈরাগ্য’ (Worldly Asceticism)-এ পরিণত হয়। ওয়েবারের মতে, এই নৈতিকতাই ছিল অবিরাম পুঁজি সঞ্চয় এবং আধুনিক পুঁজিবাদের মূল চালিকাশক্তি (Weber, 1905)। যদিও ওয়েবারের তত্ত্ব নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে এবং অনেক ইতিহাসবিদ দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদের উপাদান প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারের আগেও বিদ্যমান ছিল, তবুও তাঁর কাজ ধর্ম ও অর্থনীতির মধ্যকার গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংযোগকে উন্মোচিত করেছে।
- ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ও অর্থনৈতিক আচরণ: ধর্ম বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি কিছুর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেছে। যেমন, সুদ (Usury বা Riba)-কে ইসলাম ও মধ্যযুগীয় খ্রিস্টধর্মে একটি বড় পাপ হিসেবে গণ্য করা হতো, যা আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশে প্রভাব ফেলেছিল। এর বিকল্প হিসেবেই আজ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, যা লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে। একইভাবে, বিভিন্ন ধর্মে খাদ্য (হালাল, কোশের), পোশাক এবং জীবনযাত্রার ওপর যে নিয়মকানুন রয়েছে, তা এক বিশাল বাজার তৈরি করেছে।
- দান, যাকাত ও সম্পদ বণ্টন: প্রায় সব ধর্মেই দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করা বা দান করাকে একটি পুণ্যকর্ম হিসেবে দেখা হয়। ইসলামের যাকাত একটি বাধ্যতামূলক কর, যা ধনীদের সম্পদ থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। ইহুদি ধর্মে দ্সেদাকাহ (Tzedakah) এবং খ্রিস্টধর্মে চ্যারিটি বা দশমাংশ (Tithing) একই ধরনের ভূমিকা পালন করে। এই ব্যবস্থাগুলো সমাজে এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক সম্পদ পুনর্বণ্টন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে।
- ধর্মীয় অর্থনীতি: বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন: ভ্যাটিকান বা ভারতের বিভিন্ন মন্দির ট্রাস্ট) নিজেরাই বিশাল অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে, যারা বিপুল পরিমাণ জমি, সম্পত্তি ও বিনিয়োগের মালিক। তাছাড়া, ধর্মীয় পর্যটন বা তীর্থযাত্রা (যেমন: মক্কার হজ্জ্ব বা ভারতের কুম্ভমেলা) এক বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করে।
ধর্ম ও বিজ্ঞান: সংঘাত নাকি সংলাপ?
ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ককে প্রায়ই এক চিরন্তন সংঘাতের ময়দান হিসেবে চিত্রিত করা হয়। গ্যালিলিওর বিচার বা ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে বিতর্ক এর ক্লাসিক উদাহরণ। উনিশ শতকে জন উইলিয়াম ড্রেপার এবং অ্যান্ড্রু ডিকসন হোয়াইটের মতো লেখকদের মাধ্যমে এই ‘কনফ্লিক্ট থিসিস’ (Conflict Thesis) জনপ্রিয় হয়েছিল, যা বিজ্ঞানকে যুক্তির আলো এবং ধর্মকে অন্ধকারের শক্তি হিসেবে দেখায়।
তবে অনেক দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ মনে করেন, এই সম্পর্কটি আরও অনেক বেশি জটিল ও বহুমাত্রিক। ইয়ান বারবার (Ian Barbour) ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে চারটি সম্ভাব্য সম্পর্কের একটি প্রভাবশালী মডেল দিয়েছেন:
- সংঘাত (Conflict): এই মডেলে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একে অপরের শত্রু হিসেবে দেখা হয়, যারা বাস্তবতার প্রকৃতি নিয়ে পরস্পরবিরোধী দাবি করে। আক্ষরিক অর্থে ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী সৃষ্টিবাদ (Creationism) এবং বিবর্তনবাদের (Evolution) বিতর্ক এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।
- স্বাধীনতা (Independence): এই মতানুসারে, ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটি ভিন্ন জগৎ নিয়ে কাজ করে এবং তাদের প্রশ্নগুলোও ভিন্ন। এদের মধ্যে কোনো সংঘাতের অবকাশ নেই, কারণ তাদের কাজের ক্ষেত্র আলাদা। বিজ্ঞান কাজ করে ভৌত জগতের ‘কীভাবে’ (How) নিয়ে, আর ধর্ম কাজ করে জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার ‘কেন’ (Why) নিয়ে। বিজ্ঞানী স্টিফেন জে গুল্ড (Stephen Jay Gould) এই ধারণাকে ‘নন-ওভারল্যাপিং ম্যাজিস্টিরিয়া’ (Non-Overlapping Magisteria – NOMA) বলে অভিহিত করেছেন।
- সংলাপ (Dialogue): এই মডেলে মনে করা হয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান একে অপরের সাথে গঠনমূলক আলোচনা করতে পারে। উভয়েই মহাবিশ্ব ও বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করে এবং তারা পদ্ধতিগত সাদৃশ্য বা নৈতিকতার মতো বিষয়ে একে অপরকে সমৃদ্ধ করতে পারে। যেমন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তিগত অগ্রগতির নৈতিক সীমা নির্ধারণে বিজ্ঞান ও ধর্ম সংলাপে আসতে পারে।
- একীকরণ (Integration): এই মডেলে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একটি একক, সুসংহত বিশ্বদৃষ্টিতে একীভূত করার চেষ্টা করা হয়। প্রকৃতিবাদী ধর্মতত্ত্ব (Natural Theology) ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রকৃতির নকশার যুক্তি ব্যবহার করে। আবার পিয়ের তেয়ার দ্য শারদাঁ (Pierre Teilhard de Chardin)-এর মতো চিন্তাবিদরা বিবর্তনবাদকে একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন (Barbour, 1997)।
ঐতিহাসিকভাবে দেখলে, সংঘাতের চেয়ে সহযোগিতার উদাহরণও কম নয়। ইসলামী স্বর্ণযুগে বাগদাদের ‘বায়তুল হিকমাহ’ (House of Wisdom) বা মধ্যযুগের ইউরোপীয় মঠগুলো ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র। ইবনে সিনা, আল-খাওয়ারিজমি, গ্রেগর মেন্ডেল (জেনেটিক্সের জনক), আইজ্যাক নিউটন, জোহানেস কেপলার, ব্লেইজ প্যাসকেলের মতো অনেক যুগান্তকারী বিজ্ঞানীই গভীর ধার্মিক ছিলেন এবং তারা তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে বোঝার একটি উপায় হিসেবেই দেখতেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কার (যেমন: বিগ ব্যাং তত্ত্ব, নিউরোসায়েন্স) ধর্মের অনেক ঐতিহ্যবাহী দাবিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে, যা এই দুইয়ের মধ্যকার টানাপোড়েনকে আজও জীবন্ত রেখেছে।
ধর্ম এবং শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য
মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কিছু শৈল্পিক ও সৃষ্টিশীল অর্জন ধর্মের গভীর অনুপ্রেরণা থেকেই জন্ম নিয়েছে। ধর্ম মানুষের আবেগ, ভয়, বিস্ময় ও পরম সত্তার প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত রূপ দেওয়ার জন্য এক বিশাল ক্যানভাস তৈরি করে দিয়েছে।
- স্থাপত্য: ধর্মীয় স্থাপত্য শুধু উপাসনার স্থান নয়, এটি বিশ্বাসকে পাথর, কাঠ ও কাচের মাধ্যমে আকাশে পৌঁছে দেওয়ার এক একটি প্রচেষ্টা। মিশরের পিরামিডগুলো ছিল ফারাওদের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষার স্মারক। গ্রিসের পার্থেনন দেবী এথেনার প্রতি উৎসর্গীকৃত নিখুঁত প্রতিসাম্যের নিদর্শন। ইউরোপের গথিক ক্যাথেড্রালগুলোর সুউচ্চ চূড়া ও রঙিন কাচের জানালা দর্শকদের দৃষ্টিকে স্বর্গের দিকে টেনে নিত এবং এক স্বর্গীয় আবেশ তৈরি করত। ইসলামী মসজিদের জ্যামিতিক নকশা ও ক্যালিগ্রাফি ঈশ্বরের একত্ব ও অসীমতার বিমূর্ত ধারণাকে প্রকাশ করে। আগ্রার তাজমহল শুধু ভালোবাসার প্রতীক নয়, এটি জান্নাতের ধারণার এক পার্থিব প্রতিচ্ছবি।
- চিত্রকলা ও ভাস্কর্য: ইতিহাসের একটা বড় সময় ধরে শিল্পকলার প্রধান বিষয়বস্তুই ছিল ধর্ম। অনেক সমাজে, যেখানে সাক্ষরতার হার কম ছিল, সেখানে শিল্পের কাজ ছিল সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় আখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া। মাইকেলেঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেলের ফ্রেস্কো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ‘দ্য লাস্ট সাপার’ বা অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রগুলো ছিল নিরক্ষরদের জন্য বাইবেল বা জাতকের গল্পের মতো। হিন্দু মন্দিরের ভাস্কর্যগুলো বিভিন্ন দেব-দেবী ও পৌরাণিক কাহিনীর মূর্ত রূপ। অন্যদিকে, ইসলাম বা ইহুদি ধর্মের মতো আইকনোক্লাস্টিক (iconoclastic) বা মূর্তিবিরোধী tradizione ক্যালিগ্রাফি ও জ্যামিতিক শিল্পকলার মতো বিমূর্ত শিল্পের জন্ম দিয়েছে।
- সাহিত্য ও সঙ্গীত: পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মগুলোর একটি বড় অংশই ধর্মীয় আখ্যান বা দর্শনকে কেন্দ্র করে রচিত। রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যগুলো একটি পুরো সভ্যতার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরি করেছে। বাইবেল ও কুরআন শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, এগুলো যথাক্রমে হিব্রু ও আরবি ভাষার ধ্রুপদী সাহিত্যেরও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দান্তের ‘ডিভাইন কমেডি’ পরকালের এক মহাকাব্যিক সফর, আর মিল্টনের ‘প্যারাডাইস লস্ট’ মানুষের পতন ও মুক্তির এক অমর গাঁথা। একইভাবে, সঙ্গীতেরও জন্ম ও বিকাশ ঘটেছে ধর্মীয় আবেগকে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে – তা সে গির্জার গ্রেগরিয়ান চ্যান্ট হোক, বাখের ক্যান্টাটা হোক, সুফিদের কাওয়ালি বা মন্দিরের ভজন-কীর্তন।
ধর্ম এভাবেই রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, বিজ্ঞান থেকে শিল্পকলা – সভ্যতার প্রায় প্রতিটি তন্তুর সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। এটি একই সাথে স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনের, সৃষ্টি ও ধ্বংসের, ঐক্য ও বিভেদের এক জটিল এবং শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে গেছে, যার প্রভাব আজও আমাদের জীবনে সমানভাবে ক্রিয়াশীল।
পবিত্রতার ছায়া: ধর্মের অন্ধকার দিক
ধর্মের ইতিহাস কেবল শান্তি, ভালোবাসা আর পরোপকারের আলোয় উদ্ভাসিত নয়। এর পবিত্র আবরণ ভেদ করে প্রায়শই বেরিয়ে এসেছে এক গভীর, শীতল ছায়া। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধর্ম যেমন একদিকে মানুষকে শান্তি, সান্ত্বনা, নৈতিকতা ও ঐক্যের বার্তা দিয়েছে, তেমনই অন্যদিকে এর নামে চলেছে অবর্ণনীয় সহিংসতা, ঘৃণা, শোষণ ও চিন্তার দমন। এই দ্বৈত সত্তা বোঝা ছাড়া ধর্মের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকা অসম্ভব। ধর্ম একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, আর যেকোনো শক্তিশালী হাতিয়ারের মতোই এটি যেমন সৃষ্টি করতে পারে, তেমনই পারে ধ্বংস করতে। এই অন্ধকার দিকগুলো কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের একক সমস্যা নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই এর বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে।
ধর্মীয় সহিংসতা ও যুদ্ধ (Religious Violence and War)
ইতিহাসের পাতা খুললে ধর্মযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর গণহত্যার এমন অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়, যা মানবতাকে লজ্জিত করে। ধর্মের নামে রক্তপাত ঘটানোর এই প্রবণতার পেছনে কিছু গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে।
- একচ্ছত্র সত্যের দাবি এবং মহাজাগতিক যুদ্ধ: অনেক ধর্ম, বিশেষ করে একেশ্বরবাদী ধর্মগুলো, এক ধরনের একচ্ছত্র সত্যের দাবি (Absolutist Truth Claim) করে। ‘আমার ঈশ্বরই একমাত্র সত্য ঈশ্বর, আমার পথই একমাত্র মুক্তির পথ’ – এই বিশ্বাস যখন দৃঢ় হয়, তখন অন্য বিশ্বাসগুলোকে শুধু ভিন্নমত হিসেবে দেখা হয় না, বরং সেগুলোকে দেখা হয় মিথ্যা, শয়তানের প্ররোচনা বা পবিত্র সত্যের প্রতি হুমকি হিসেবে। এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর সহিংসতা চালানোটা আর সাধারণ অপরাধ থাকে না, তা এক ধরনের ‘পবিত্র দায়িত্ব’ (Sacred Duty) হয়ে দাঁড়ায়। সমাজবিজ্ঞানী মার্ক জুর্গেনসমেয়ার (Mark Juergensmeyer) তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ Terror in the Mind of God-এ দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় সন্ত্রাসীরা তাদের সংগ্রামকে সাধারণ পার্থিব বা রাজনৈতিক যুদ্ধ হিসেবে দেখে না। তারা একে দেখে এক ‘মহাজাগতিক যুদ্ধ’ (Cosmic War) হিসেবে – যা ভালোর সাথে মন্দের, ঈশ্বরের সাথে শয়তানের, সত্যের সাথে মিথ্যার এক অন্তহীন সংগ্রাম (Juergensmeyer, 2003)। এই মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে পার্থিব আইনকানুন, নৈতিকতা বা মানবিকতার কোনো স্থান থাকে না। তখন নিরীহ মানুষ হত্যা করাও ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণের একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে।
- ইতিহাসের উদাহরণ: মধ্যযুগের ক্রুসেড ছিল এর এক ভয়ঙ্কর উদাহরণ, যেখানে খ্রিস্টান ও মুসলিমরা পবিত্র ভূমির (জেরুজালেম) দখল নিয়ে শত শত বছর ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারের পর ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (Thirty Years’ War) প্রায় পুরো মহাদেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। স্প্যানিশ ইনকুইজিশন ‘ধর্মদ্রোহী’দের খুঁজে বের করে তাদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সময় ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিল। আধুনিক যুগেও এই ধারা অব্যাহত। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট সংঘাত, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের নিপীড়ন, বা আল-কায়দা ও আইএস-এর মতো জিহাদি গোষ্ঠীর বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ – সবকিছুর পেছনেই ধর্মের একটি শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে।
- পরকালের পুরস্কার ও শহীদের ধারণা: ধর্ম প্রায়শই সহিংসতাকে শুধু বৈধতাই দেয় না, একে মহিমান্বিতও করে। ‘ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে মরলে’ বা শহীদ হলে পরকালে অনন্ত সুখ ও পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়। এই বিশ্বাস মৃত্যুকে এক ভয়ংকর পরিণতি থেকে এক আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে, যা সাধারণ মানুষকেও আত্মঘাতী হামলাকারী বা চরম নিষ্ঠুর যোদ্ধায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম।
অসহিষ্ণুতা ও নিপীড়ন (Intolerance and Persecution)
সহিংসতার ভিত্তি তৈরি হয় অসহিষ্ণুতার জমিতে। ধর্ম প্রায়ই ‘আমাদের’ (In-group) এবং ‘ওদের’ (Out-group) মধ্যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক বিভাজন তৈরি করে। সামাজিক পরিচয় তত্ত্ব (Social Identity Theory) অনুযায়ী, মানুষ তার আত্মসম্মান অনেকাংশেই তার গোষ্ঠীর পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করে। ফলে, নিজের গোষ্ঠীকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য অন্য গোষ্ঠীকে নিকৃষ্ট, অপবিত্র বা বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা তৈরি হয়। ধর্ম এই ‘আমরা-ওরা’ বিভাজনের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তিগুলোর একটি সরবরাহ করে।
- ধর্মদ্রোহিতা ও ঈশ্বরনিন্দা: প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো তাদের মতাদর্শগত বিশুদ্ধতা বা অর্থোডক্সি (Orthodoxy) বজায় রাখার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মূল মতবাদ থেকে যেকোনো বিচ্যুতিকে ‘ধর্মদ্রোহিতা’ (Heresy) হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এর শাস্তি হতে পারে সমাজচ্যুত করা থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। একইভাবে, ঈশ্বরের বা ধর্মের কোনো পবিত্র প্রতীকের অবমাননাকে ‘ঈশ্বরনিন্দা’ (Blasphemy) হিসেবে গণ্য করা হয়। ইতিহাসে এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে। জিওরদানো ব্রুনো-কে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল কারণ তার মহাবিশ্ব সম্পর্কিত ধারণা চার্চের মতবাদের পরিপন্থী ছিল। দার্শনিক সক্রেটিসকে হেমলক পানে হত্যা করার পেছনেও একটি অভিযোগ ছিল ‘যুবকদের বিপথগামী করা এবং শহরের দেবতাদের অস্বীকার করা’। আজও বিশ্বের অনেক দেশে ব্লাসফেমি আইন প্রচলিত আছে এবং প্রায়শই তা ভিন্নমতাবলম্বী, সংখ্যালঘু বা ব্যক্তিগত শত্রুদের দমনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- সংখ্যালঘু ও সংশয়বাদীদের ওপর নিপীড়ন: যখন কোনো একটি ধর্ম রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ক্ষমতার সাথে একীভূত হয়ে যায়, তখন অন্য ধর্মের অনুসারী বা কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না এমন মানুষেরা প্রায়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। ইতিহাসজুড়ে ইহুদিরা ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিস্টান রাজ্যে নিগ্রহের শিকার হয়েছে। হিন্দু শাসকের অধীনে মুসলমান বা মুসলিম শাসকের অধীনে হিন্দুরা অনেক সময় নিপীড়নের শিকার হয়েছে। নাস্তিক বা সংশয়বাদীদের প্রায়শই ‘নৈতিকতা-বর্জিত’ বা ‘সমাজবিরোধী’ হিসেবে দেখা হয় এবং তাদের সামাজিক ও আইনগত অধিকার খর্ব করা হয়।
সামাজিক শোষণ ও বৈষম্য (Social Oppression and Discrimination)
ধর্মকে প্রায়ই বিদ্যমান সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি শক্তিশালী আদর্শিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষের তৈরি শোষণমূলক ব্যবস্থাকে যখন ‘ঈশ্বরপ্রদত্ত’ বা ‘স্বাভাবিক’ বলে প্রচার করা হয়, তখন তা প্রায় প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে।
- বর্ণপ্রথা ও দাসপ্রথা: ভারতের বর্ণপ্রথাকে (Caste System) হাজার হাজার বছর ধরে টিকিয়ে রাখার পেছনে ধর্মীয় বিধানের (যেমন: মনুসংহিতা) এবং কর্মফলের ধারণার বিশাল ভূমিকা ছিল। এই মতবাদ প্রচার করত যে, একজন ব্যক্তি কোন বর্ণে জন্মাবে তা তার পূর্বজন্মের কর্মফল দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং, নিম্নবর্ণে জন্ম নেওয়াটা তার নিজেরই কৃতকর্মের শাস্তি এবং এই ভাগ্য মেনে নিয়েই তাকে জীবন কাটাতে হবে, যাতে পরবর্তী জন্মে তার উন্নতি হয়। এই বিশ্বাস শোষিত মানুষের মনে বিদ্রোহের পরিবর্তে এক ধরনের অদৃষ্টবাদ তৈরি করত। একইভাবে, বাইবেলের কিছু অংশের (যেমন: ‘হ্যামের অভিশাপ’ বা দাসদের প্রভুর প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশনা) ব্যাখ্যা দিয়ে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে আফ্রিকানদের দাসপ্রথাকে ধর্মীয়ভাবে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল।
- নারী নির্যাতন ও লিঙ্গবৈষম্য: পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ধর্মই তাদের উদ্ভবকালে পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) সমাজে গড়ে উঠেছিল এবং সেই সমাজের লিঙ্গবৈষম্যমূলক ধারণার অনেক কিছুই তাদের ধর্মগ্রন্থ, আইন ও ঐতিহ্যের মধ্যে ধারণ করে আছে। নারীকে প্রায়শই পুরুষের অধীনস্থ, আবেগপ্রবণ, দুর্বল এবং অপবিত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। অনেক ধর্মেই নারীকে পুরুষের ‘সহকারিণী’ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, তাকে পর্দা প্রথার অধীনে রাখা হয়েছে, তার শিক্ষা, সম্পত্তি ও সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারকে সংকুচিত করা হয়েছে এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের পদ থেকে (যেমন: পুরোহিত, ইমাম) তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।
- যৌনতা ও সমকামিতা: ধর্ম প্রায়শই মানুষের যৌনতাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে এবং প্রজননকেন্দ্রিক বিষমকামী (Heterosexual) সম্পর্ক ছাড়া অন্য সব ধরনের যৌনতাকে ‘পাপ’ বা ‘অপ্রাকৃতিক’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর ফলে সমকামী, উভকামী বা রূপান্তরকামী (LGBTQ+) ব্যক্তিরা শতাব্দী ধরে সামাজিক নিগ্রহ, ঘৃণা এবং সহিংসতার শিকার হয়েছেন।
চিন্তার স্বাধীনতা হরণ (Suppression of Free Thought)
অনেক ধর্মই প্রশ্ন, সংশয় ও সমালোচনামূলক চিন্তার চেয়ে অন্ধবিশ্বাস বা ঈমান (Faith)-কে বেশি গুরুত্ব দেয়। ধর্মগ্রন্থকে অভ্রান্ত (Infallible) এবং চূড়ান্ত সত্য হিসেবে মেনে নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই অন্ধবিশ্বাস বা ডগমা (Dogma) মুক্তচিন্তা, সংশয়বাদ (Skepticism) এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যখন কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা দার্শনিক তত্ত্ব ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক ব্যাখ্যার সাথে মেলে না, তখন তাকে ‘ধর্মবিরোধী’ বলে চিহ্নিত করা হয়। গ্যালিলিওর বিচার এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ। ভ্যাটিকানের ‘নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা’ (Index Librorum Prohibitorum) শত শত বছর ধরে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। এই চিন্তার দমন শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি শিল্প, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক ভিন্নমতের ওপরও একইভাবে নেমে আসতে পারে।
মানসিক ক্ষতি (Psychological Harm)
ধর্ম অনেকের জন্য যেমন মানসিক শান্তি ও সান্ত্বনার উৎস, তেমনই অনেকের জন্য এটি তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- পাপবোধ, লজ্জা ও ভয়: শৈশব থেকে ক্রমাগত পাপবোধ (Guilt), লজ্জা (Shame) এবং নরকের অনন্ত শাস্তির ভয় (Fear of Hell) অনেকের মধ্যে গভীর উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং মানসিক বিকার তৈরি করতে পারে। নিজের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদাকেও ‘পাপ’ হিসেবে দেখার শিক্ষা ব্যক্তির সাথে তার নিজের শরীরের এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে।
- ধর্মীয় আঘাত সিনড্রোম (Religious Trauma Syndrome – RTS): যারা কোনো কঠোর, কর্তৃত্বপরায়ণ এবং শোষণমূলক ধর্মীয় গোষ্ঠী ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তারা প্রায়ই এক ধরনের জটিল মানসিক আঘাতের শিকার হয়। মনোবিজ্ঞানী ড. মার্লিন উইনেল (Dr. Marlene Winell) এই অবস্থাকে ‘রিলিজিয়াস ট্রমা সিনড্রোম’ বলে অভিহিত করেছেন। এর লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD)-এর মতো অনুভূতি, সামাজিক দক্ষতার অভাব, সিদ্ধান্তহীনতা, নিজের পরিচয় নিয়ে সংকট এবং পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গভীর যন্ত্রণা (Winell, 2011)।
এই অন্ধকার দিকগুলো আলোচনা করার অর্থ এই নয় যে, ধর্ম মানেই খারাপ বা এর কোনো ইতিবাচক দিক নেই। বরং এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ধর্ম একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তি, যা মানুষের সেরা এবং নিকৃষ্টতম – উভয় প্রবৃত্তিকেই জাগিয়ে তুলতে পারে। এর ফল নির্ভর করে মানুষ কীভাবে একে ব্যাখ্যা, ধারণ ও প্রয়োগ করছে, তার ওপর। এই ছায়াকে স্বীকার করে নিয়েই আমরা ধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপটি বোঝার পথে এক ধাপ এগোতে পারি।
একুশ শতকে ধর্ম: সংকট ও রূপান্তর
উনিশ ও বিংশ শতাব্দীর ধ্রুপদী সমাজবিজ্ঞানীরা – মার্ক্স থেকে ওয়েবার পর্যন্ত – প্রায় একমত ছিলেন যে, আধুনিকতার অগ্রযাত্রার সাথে সাথে ধর্ম ধীরে ধীরে তার সামাজিক গুরুত্ব হারাবে। আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তিভিত্তিক শিক্ষা, নগরায়ন এবং বিশ্বায়নের সম্মিলিত প্রভাবে ধর্মের অলৌকিক ব্যাখ্যা ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ফিকে হয়ে আসবে বলে মনে করা হতো। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রভাবশালী তত্ত্বটি ধর্মনিরপেক্ষকরণ তত্ত্ব (Secularization Thesis) নামে পরিচিত। কিন্তু একুশ শতকের সূর্য যখন মধ্যগগনে, তখন আমরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনেক বেশি জটিল ও পরস্পরবিরোধী চিত্র দেখতে পাই। একদিকে যেমন ধর্মের প্রভাব কমছে, অন্যদিকে তেমনই ঘটছে তার হিংস্র পুনরুত্থান। একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে মানুষ মুখ ফেরাচ্ছে, অন্যদিকে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন আধ্যাত্মিকতার রূপ। ধর্মের মৃত্যুঘণ্টা বাজার পরিবর্তে, এটি যেন নতুন রূপে, নতুন শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।
ধর্মনিরপেক্ষতার অগ্রযাত্রা এবং ‘নানস’-এর উত্থান
ধর্মনিরপেক্ষকরণ তত্ত্ব পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত না হলেও, এর প্রভাব বিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে পড়েনি। পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তর আমেরিকায়, ধর্মের সামাজিক প্রভাব স্পষ্টভাবে কমেছে। এই প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারায় লক্ষ্য করা যায়:
- ‘নানস’-এর উত্থান: সাম্প্রতিক দশকগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হলো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন মানুষের সংখ্যার নাটকীয় বৃদ্ধি। বিভিন্ন জরিপে যখন ধর্মীয় পরিচয়ের প্রশ্ন করা হয়, তখন যারা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের (যেমন: খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু) অনুসারী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেন না, তাদেরকেই পিউ রিসার্চ সেন্টারের (Pew Research Center) মতো সংস্থাগুলো ‘ধর্মীয়ভাবে সম্পর্কহীন’ বা ‘নানস’ (Nones) বলে চিহ্নিত করে। এই ‘নানস’-রা সবাই নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী নন; এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো কোনো এক ধরনের বিমূর্ত শক্তি বা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কাঠামোয় নিজেদের বাঁধতে চান না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই গোষ্ঠীর পরিমাণ গত কয়েক দশকে একক সংখ্যা থেকে বেড়ে জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশি হয়ে গেছে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই হার আরও অনেক বেশি।
- কারণসমূহ: এই ধর্মনিরপেক্ষতার পেছনে একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল। প্রথমত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে প্রাকৃতিক জগৎ (মহাবিশ্বের উৎপত্তি, প্রাণের বিকাশ) ব্যাখ্যার জন্য এখন আর ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না (“God of the gaps”)। দ্বিতীয়ত, আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়ায় ধর্মের ঐতিহ্যবাহী কিছু সামাজিক কাজ (যেমন: চ্যারিটি, শিক্ষা প্রদান) অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তৃতীয়ত, আধুনিক সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের (Individualism) উত্থান ঘটেছে, যেখানে মানুষ বাহ্যিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়। চতুর্থত, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো প্রায়শই বিভিন্ন রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি, যৌন নিপীড়নের ঘটনা এবং রক্ষণশীল রাজনৈতিক অবস্থানের (যেমন: সমকামিতার বিরোধিতা) কারণে অনেকের, বিশেষ করে তরুণদের, আস্থা হারিয়েছে।
- ধর্মের বেসরকারিকরণ: সমাজবিজ্ঞানী হোসে ক্যাসানোভা (José Casanova) দেখিয়েছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মের বিলুপ্তি নয়, বরং এর রূপান্তর। আধুনিক সমাজে ধর্ম জনপরিসর (রাষ্ট্র, আইন, অর্থনীতি) থেকে সরে এসে ব্যক্তির ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে তিনি ধর্মের ‘বেসরকারিকরণ’ (Privatization) বলে অভিহিত করেছেন (Public Religions in the Modern World, 1994)। ধর্ম এখন আর জন্মসূত্রে পাওয়া বাধ্যতামূলক কোনো পরিচয় নয়, বরং এটি বাজারের আর দশটা পণ্যের মতোই একটি বেছে নেওয়ার মতো বিকল্প।
মৌলবাদের পুনরুত্থান (Resurgence of Fundamentalism)
ধর্মনিরপেক্ষতার এই জোয়ারের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের অনেক জায়গায় ধর্মীয় মৌলবাদের (Religious Fundamentalism) হিংস্র পুনরুত্থান ঘটেছে। এটি যেন আধুনিকতার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ।
- মৌলবাদের প্রকৃতি: মৌলবাদীরা আধুনিকতা, বিশ্বায়ন এবং উদারনৈতিক মূল্যবোধকে (যেমন: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা) তাদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখে। এই হুমকির মুখে তারা নিজেদের পরিচয়কে রক্ষা করার জন্য ধর্মের এক কঠোর, বিশুদ্ধ এবং আপোসহীন রূপে ফিরে যেতে চায়। মার্টিন ই. মার্টি (Martin E. Marty) এবং আর. স্কট অ্যাপলবাই (R. Scott Appleby) সম্পাদিত The Fundamentalism Project অনুযায়ী, মৌলবাদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো: ধর্মগ্রন্থের আক্ষরিক, অপরিবর্তনীয় এবং অভ্রান্ত ব্যাখ্যায় বিশ্বাস; নিজেদের এক পবিত্র সত্যের রক্ষক হিসেবে দেখা এবং পারিপার্শ্বিক ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ; এবং সমাজ ও রাজনীতিকে সেই কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের অধীনে ফিরিয়ে আনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।
- বিশ্বায়ন ও পরিচয়ের সংকট: রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন বারবার (Benjamin Barber) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Jihad vs. McWorld-এ দেখিয়েছেন যে, বিশ্বায়ন একদিকে যেমন ‘ম্যাকওয়ার্ল্ড’ বা এক বিশ্বব্যাপী ভোগবাদী, সমরূপী সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে, তেমনই এর প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিচ্ছে ‘জিহাদ’ বা বিভিন্ন উপজাতীয়, ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়ের উগ্র রূপ (Barber, 1996)। বিশ্বায়নের ফলে যখন স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার ভয় তৈরি হয়, তখন মানুষ তার পরিচয়ের জন্য ধর্মের মতো এক শাশ্বত ও পরম আশ্রয়ের দিকে ফিরে যায়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী মৌলবাদ, আমেরিকার ‘বাইবেল বেল্ট’-এ খ্রিস্টান মৌলবাদ, ভারতে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ বা ইসরায়েলে উগ্র জায়নবাদ – এই সবই বিশ্বায়ন ও আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে পরিচয়ের সংকটের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।
আধ্যাত্মিকতা কিন্তু ধর্ম নয় (Spiritual but not Religious – SBNR)
ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মৌলবাদ – এই দুই চরম অবস্থানের মাঝখানে আরও একটি শক্তিশালী ধারা জনপ্রিয় হচ্ছে। এটি হলো ‘আধ্যাত্মিক কিন্তু ধার্মিক নয়’ (Spiritual but not Religious – SBNR)। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কঠোর নিয়মকানুন, অনুশাসন, ডগমা এবং রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে বেরিয়ে এসে এক ধরনের ব্যক্তিগত, স্ব-নির্বাচিত আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করছেন।
- আধ্যাত্মিকতার বাজার: এই নতুন আধ্যাত্মিকতা অনেকটা সুপারমার্কেটের মতো, যেখানে ব্যক্তি তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বিশ্বাস ও আচার থেকে উপাদান নিয়ে নিজের আধ্যাত্মিক প্যাকেজ তৈরি করে। তারা হয়তো খ্রিস্টধর্মের ভালোবাসা, বৌদ্ধধর্মের ধ্যান (Meditation) ও মাইন্ডফুলনেস (Mindfulness), হিন্দুধর্মের যোগব্যায়াম (Yoga) এবং প্রকৃতি উপাসনার কিছু উপাদান মিলিয়ে নিজের জন্য একটি অর্থপূর্ণ জীবনদর্শন তৈরি করে। সমাজবিজ্ঞানী গ্রেস ডেভি (Grace Davie) ইউরোপের প্রেক্ষাপটে এই প্রবণতাকে ‘বিশ্বাস করা কিন্তু অন্তর্ভুক্ত না হওয়া’ (Believing without belonging) বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের সাথে সম্পর্ক রাখে না (Davie, 1994)। এটি ধর্মের একটি বিবর্তিত, ব্যক্তিগত এবং অত্যন্ত ভোক্তাবাদী (Consumerist) রূপ।
- আপিল এবং সীমাবদ্ধতা: SBNR-এর আবেদন হলো এটি ধর্মের ইতিবাচক দিকগুলো (যেমন: শান্তি, অর্থ, সংযোগ) প্রদান করে, কিন্তু এর নেতিবাচক দিকগুলো (যেমন: পাপবোধ, কঠোর নিয়ম, অসহিষ্ণুতা) থেকে মুক্তি দেয়। তবে এর একটি সীমাবদ্ধতা হলো, এই ধরনের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা প্রায়শই সামাজিক দায়বদ্ধতাহীন এবং আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যেমন শক্তিশালী সম্প্রদায় তৈরি করতে পারে বা সামাজিক পরিবর্তনের জন্য মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারে, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতার সেই ক্ষমতা অনেক কম।
সাইবার-রিলিজিয়ন ও ডিজিটাল বিশ্বাস
একুশ শতকের প্রযুক্তি, বিশেষ করে ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া, ধর্মচর্চা এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠনের পদ্ধতিকে আমূল বদলে দিয়েছে। এই নতুন ক্ষেত্রটিকে ডিজিটাল রিলিজিয়ন (Digital Religion) বলে অভিহিত করা হয়।
- রিলিজিয়ন অনলাইন বনাম অনলাইন রিলিজিয়ন: গবেষক হেইডি ক্যাম্পবেল (Heidi Campbell) এই দুইয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য করেছেন (Digital Religion, 2012)। রিলিজিয়ন অনলাইন (Religion Online) হলো যখন বিদ্যমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ইন্টারনেটকে তাদের বার্তা প্রচার, অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা বা অনুদান সংগ্রহের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন: চার্চের লাইভ-স্ট্রিমড সার্ভিস, অনলাইন কুরআন ক্লাস বা ভ্যাটিকানের টুইটার অ্যাকাউন্ট। অন্যদিকে, অনলাইন রিলিজিয়ন (Online Religion) হলো যখন ইন্টারনেটেই সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ধর্মীয় সম্প্রদায় ও চর্চার জন্ম হয়, যা অফলাইন জগতে সম্ভব ছিল না। যেমন: অনলাইন ফোরামে ধর্মীয় বিতর্ক, ভার্চুয়াল জগতে তীর্থযাত্রা, বা ভিডিও গেমের ভেতরে তৈরি হওয়া কাল্ট।
- প্রভাব: এই ডিজিটাল রূপান্তর একদিকে যেমন ধর্মকে আরও সহজলভ্য, গণতান্ত্রিক ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছে, তেমনই এর অন্ধকার দিকও রয়েছে। ইন্টারনেট ধর্মীয় চরমপন্থা, ভুয়া খবর এবং বিদ্বেষমূলক প্রচারণার দ্রুত বিস্তারের একটি উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীদের এমন ‘ইকো চেম্বার’ (Echo Chamber) বা প্রতিধ্বনি কক্ষে আবদ্ধ করে ফেলে, যেখানে তারা শুধু নিজেদের বিশ্বাসের সমর্থনই শুনতে পায়, যা তাদের আরও বেশি কট্টরপন্থী করে তুলতে পারে।
তাহলে ধর্মের ভবিষ্যৎ কী? কানাডিয়ান দার্শনিক চার্লস টেইলর (Charles Taylor) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ A Secular Age-এ যুক্তি দিয়েছেন যে, আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা আর একমাত্র স্বাভাবিক বা ডিফল্ট অপশন নয়, বরং এটি অনেকগুলো বিকল্পের মধ্যে একটি মাত্র (Taylor, 2007)। এই ‘বিকল্পের জগৎ’-এ ধর্মের পুরনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হয়তো ক্ষয়িষ্ণু হবে, কিন্তু অর্থ, পরিচয় ও সম্প্রদায়ের জন্য মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে যাবে না। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ধর্ম হয়তো আরও ব্যক্তিগত, নমনীয়, সংকর এবং ডিজিটাল রূপ ধারণ করবে। মৌলবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির মধ্যকার টানাপোড়েন হয়তো আরও তীব্র হবে। উত্তরটা এখনো আমাদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, মানব সমাজে অর্থ ও পরিচয়ের চাহিদা যতদিন থাকবে, ধর্মও কোনো না কোনো রূপে টিকে থাকবে, রূপান্তরিত হবে এবং আমাদের পৃথিবীকে নতুন নতুন উপায়ে সংজ্ঞায়িত করতে থাকবে।
চিন্তার কারিগর: যারা ধর্মকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন
কোনো বড় বিষয় বুঝতে হলে, বিশেষ করে ধর্ম বা দর্শনের মতো জটিল বিষয়, কিছু মানুষের কাঁধে চড়ে দাঁড়াতে হয়। এই মানুষগুলো তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন আমাদের চারপাশের জগৎকে, আমাদের ভেতরের জগৎকে এবং এই দুইয়ের মধ্যকার রহস্যময় সম্পর্ককে বোঝার জন্য। ধর্ম নিয়ে আমাদের আজকের বোঝাপড়া এমনি এমনি তৈরি হয়নি। এটি বহু চিন্তাবিদের বহু বছরের পরিশ্রম, বিতর্ক আর অনুসন্ধানের ফসল। এই মানুষগুলো যেন একেকজন স্থপতি, যারা ধর্ম নামের এই বিশাল, প্রাচীন অট্টালিকাটিকে বোঝার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে এর নকশা এঁকেছেন, এর ভিত্তি খুঁড়ে দেখেছেন, এর ইট-পাথর বিশ্লেষণ করেছেন।
তারা সবাই যে একমত হয়েছেন, তা নয়। বরং তাদের মধ্যে মতের অমিলই বেশি। কেউ ধর্মকে দেখেছেন সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে, কেউ দেখেছেন শোষণের হাতিয়ার হিসেবে। কেউ এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন মানসিক শান্তির উৎস, আবার কেউ খুঁজে পেয়েছেন মানসিক রোগের লক্ষণ। তাদের এই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণগুলো অনেকটা বিভিন্ন রঙের চশমার মতো। একেকটি চশমা দিয়ে দেখলে ধর্মকে একেক রকম দেখায়। এই অধ্যায়ে আমরা সেইসব প্রধান চিন্তাবিদদের চশমা দিয়ে ধর্মকে দেখার চেষ্টা করব। তাদের বিতর্ক, তাদের তত্ত্ব – এইসব নিয়েই তো আজকের জ্ঞানকাণ্ডের বাজার। চলুন, সেই চিন্তার বাজারে একটু ঘুরে আসা যাক।
ধ্রুপদী সমাজবিজ্ঞানের তিন স্তম্ভ: মার্ক্স, ডুর্খাইম ও ওয়েবার
আধুনিককালে ধর্মকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার কাজটি শুরু করেছিলেন সমাজবিজ্ঞানীরা। তাদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তিকে বলা হয় সমাজবিজ্ঞানের ‘প্রতিষ্ঠাতা জনক’ (Founding Fathers)। ধর্ম বিষয়ে তাদের তিনজনের ভাবনা ছিল তিনটি ভিন্ন, কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী পথে চালিত।
কার্ল মার্ক্স (Karl Marx): নিপীড়িতের আফিম
কার্ল মার্ক্সকে যদি এক কথায় বর্ণনা করতে হয়, তবে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী। তার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে ছিল মানব সমাজের শ্রেণি-সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক শোষণ। তার কাছে, ধর্ম কোনো স্বাধীন সত্তা নয়, এটি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর (Economic Base) উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক উপরিসৌধ (Superstructure) মাত্র। অর্থাৎ, উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন হবে, সমাজের আইন, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং ধর্মও তেমনই হবে।
মার্ক্সের সেই বিখ্যাত উক্তি – “ধর্ম হলো জনগণের আফিম” (Religion is the opium of the people) – পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত এবং সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভুল বোঝা উক্তিগুলোর একটি (Marx, 1844)। মার্ক্স এখানে বলতে চাননি যে ধর্ম খারাপ বা ধর্মগুরুরা ষড়যন্ত্র করে মানুষকে আফিম খাওয়াচ্ছে। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন, আফিম যেমন একজন অসুস্থ বা যন্ত্রণাকাতর মানুষকে সাময়িকভাবে তার কষ্ট ভুলিয়ে দেয়, ধর্মও ঠিক সেভাবেই শোষিত, নির্যাতিত সর্বহারা শ্রেণিকে (Proletariat) তাদের ইহলৌকিক দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এটি তাদের এক ধরনের মিথ্যা চেতনা (False Consciousness) দেয়। ধর্ম তাদের শেখায়, এই জন্মে কষ্ট করলে পরকালে স্বর্গলাভ হবে। এই পৃথিবী মায়া, আসল জীবন তো মৃত্যুর পরে। এই বিশ্বাস শোষিত মানুষকে তার আসল শত্রু – অর্থাৎ শোষক শ্রেণি (Bourgeoisie) – চিনতে বাধা দেয় এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে রাখে। এটা অনেকটা সেই গরিব রিকশাওয়ালার মতো, যে ভাবে, এই জন্মে কষ্ট করছি তো কী হয়েছে, পরের জন্মে নিশ্চয়ই রাজা হব। এই পারলৌকিক আশ্বাসের কারণে সে তার ইহলৌকিক দুর্দশার কারণ খোঁজে না বা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না।
মার্ক্সের মতে, ধর্ম শুধু শোষিতের সান্ত্বনা নয়, এটি শোষক শ্রেণির জন্যও একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। শাসক শ্রেণি ধর্মকে ব্যবহার করে তাদের শোষণ ও শাসনকে একটি ঐশ্বরিক বৈধতা (Divine Legitimacy) দেয়। তারা প্রচার করে যে, রাজা বা শাসকের ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত, তাই তাদের মেনে চলাই ধর্ম। এভাবে ধর্ম স্থিতাবস্থা (Status Quo) বজায় রাখতে সাহায্য করে। মার্ক্স ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেদিন শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যেদিন মানুষ তার দুঃখ-কষ্টের আসল অর্থনৈতিক কারণ দূর করতে পারবে, সেদিন এই আফিমের আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না – ধর্ম স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
এমিল ডুর্খাইম (Émile Durkheim): সমাজের আঠা
মার্ক্স যেখানে ধর্মকে দেখেছেন বিভেদ আর শোষণের প্রতিচ্ছবি হিসেবে, সেখানে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খাইম ধর্মকে দেখেছেন সামাজিক সংহতি ও ঐক্যের মূল উৎস হিসেবে। ডুর্খাইমের কাছে, ধর্ম কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপজাত নয়, বরং এটি একটি চিরন্তন সামাজিক বাস্তবতা। সমাজের অস্তিত্বের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন।
ডুর্খাইম অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ‘আরুন্টা’ (Arunta) গোষ্ঠীর ধর্ম – টোটেমবাদ (Totemism) – গবেষণা করে তার সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, এই গোষ্ঠীর মানুষ একটি নির্দিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদকে (তাদের টোটেম) অত্যন্ত পবিত্র মনে করে এবং সেটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। ডুর্খাইম এক যুগান্তকারী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। তিনি বলেন, এই আদিবাসীরা যখন তাদের টোটেমকে পূজা করে, তখন তারা আসলে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদকে পূজা করছে না; তারা প্রকারান্তরে নিজেদের সমাজ বা গোষ্ঠীকেই পূজা করছে! টোটেমটি হলো তাদের সমাজেরই একটি প্রতীকী রূপ। এই সম্মিলিত পূজা বা আচার-অনুষ্ঠানের সময় তাদের মধ্যে এক তীব্র আবেগ ও একাত্মতার জন্ম হয়, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন ‘সম্মিলিত উচ্ছ্বাস’ (Collective Effervescence) (The Elementary Forms of the Religious Life, 1912)। এই মুহূর্তে ব্যক্তি তার ক্ষুদ্র ‘আমি’-কে ভুলে গিয়ে এক বৃহত্তর ‘আমরা’-র অংশ হয়ে যায়। এই অনুভূতিই সমাজের নৈতিক ভিত্তি তৈরি করে এবং মানুষকে একসাথে বেঁধে রাখে।
ডুর্খাইমের মতে, সব ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হলো জগৎকে দুটি ভাগে ভাগ করা – পবিত্র (Sacred) ও সাধারণ (Profane)। পবিত্র হলো সেইসব বস্তু, স্থান বা ধারণা, যা সাধারণ জগৎ থেকে আলাদা, যা ভয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আর বাকি সবকিছুই সাধারণ। ধর্ম হলো এই পবিত্র জগৎকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিশ্বাস ও আচারের সমষ্টি। ডুর্খাইমের কাছে ঈশ্বরের ধারণাটিও গৌণ। আসল বিষয় হলো এই পবিত্রের ধারণা, যা সমাজ নিজেই তৈরি করে। এক কথায়, ডুর্খাইমের কাছে, “ঈশ্বর হলেন সমাজ, যা রূপান্তরিত এবং প্রতীকীভাবে কল্পিত” (God is society, transfigured and symbolically expressed)।
ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber): অর্থের কারিগর
জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার মার্ক্স ও ডুর্খাইমের মধ্যবর্তী একটি অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি মার্ক্সের মতো ধর্মকে শুধু অর্থনীতির প্রতিফলন হিসেবে দেখেননি, আবার ডুর্খাইমের মতো শুধু সামাজিক সংহতির উৎস হিসেবেও দেখেননি। ওয়েবারের কাছে, ধর্ম বা ধর্মীয় ধারণাগুলো নিজেই সমাজে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ, ধর্ম শুধু সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এটি সমাজকে প্রভাবিতও করে।
ওয়েবারের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ হলো The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism। এই বইয়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, কীভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের (বিশেষ করে ক্যালভিনিজম) কিছু নির্দিষ্ট নৈতিক বিশ্বাস ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে উত্তর ইউরোপে আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য একটি অনুকূল মানসিক পরিবেশ তৈরি করেছিল (Weber, 1905)। ক্যালভিনিস্টরা ‘পূর্বনির্ধারণ’ (Predestination) তত্ত্বে বিশ্বাস করত, অর্থাৎ ঈশ্বর আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন কে মুক্তি পাবে আর কে পাবে না। এই বিশ্বাস মানুষের মনে এক তীব্র মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করত। তারা ভাবত, কীভাবে বোঝা যাবে যে আমি ঈশ্বরের নির্বাচিতদের মধ্যে একজন? এর একটি পরোক্ষ উপায় ছিল পার্থিব সাফল্য। কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং মিতব্যয়ী জীবনযাপন করে যদি কেউ ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারে, তবে সেটি ঈশ্বরের কৃপার লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতো। তারা অর্জিত মুনাফা ভোগবিলাসে উড়িয়ে না দিয়ে পুনরায় বিনিয়োগ করত, কারণ ভোগবিলাস ছিল পাপ। ওয়েবারের মতে, এই ‘পার্থিব বৈরাগ্য’ (Worldly Asceticism)-এর মানসিকতাই আধুনিক পুঁজিবাদের মূল চালিকাশক্তি – অর্থাৎ অবিরাম মুনাফা অর্জন ও পুনঃবিনিয়োগের ভিত্তি তৈরি করেছিল।
তবে ওয়েবার এটাও বলেছেন যে, একবার পুঁজিবাদ চালু হয়ে গেলে এর আর ধর্মীয় অনুপ্রেরণার প্রয়োজন থাকে না। এটি তখন নিজের যুক্তি অনুযায়ী চলতে থাকে এবং মানুষকে এক ‘লৌহ পিঞ্জরে’ (Iron Cage) আবদ্ধ করে ফেলে – যেখানে মানুষ যুক্তির দাস হয়ে যায়, কিন্তু জীবনের আধ্যাত্মিক অর্থ হারিয়ে ফেলে। ওয়েবারের কাজ আমাদের দেখায়, ধর্মীয় ধারণা কীভাবে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণকে এবং ইতিহাসের গতিপথকে প্রভাবিত করতে পারে।
মনস্তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ: ফ্রয়েড ও ইয়ুং
সমাজবিজ্ঞানীরা যখন সমাজ ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক খুঁজছিলেন, তখন মনোবিজ্ঞানীরা খুঁজছিলেন ব্যক্তির মনের গহীনে ধর্মের উৎস। তাদের মধ্যে সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও কার্ল ইয়ুং-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।
সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud): এক সান্ত্বনাদায়ক ভ্রম
মনোবিশ্লেষণের জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েড ছিলেন ধর্মের একজন কঠোর সমালোচক। তিনি ধর্মকে দেখেছেন এক ধরনের সার্বজনীন মানসিক বিকার বা ‘অবসেসিভ নিউরোসিস’ (Obsessional Neurosis) হিসেবে। তার মতে, ধর্মীয় বিশ্বাস কোনো যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটি আমাদের শৈশবের অসহায়ত্ব এবং আদিম আকাঙ্ক্ষার এক প্রতিফলন।
ফ্রয়েড তার বিখ্যাত ‘ইডিপাস কমপ্লেক্স’ (Oedipus Complex) তত্ত্বের আলোকে ঈশ্বরের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। শৈশবে একটি শিশু যেমন তার বাবাকে একই সাথে ভালোবাসে, ভয় পায় এবং তার কাছ থেকে সুরক্ষা চায়, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষও প্রকৃতির ভয়ংকর শক্তি, রোগ-শোক, মৃত্যু এবং জীবনের নানা অনিশ্চয়তার মুখে নিজেকে তেমনই অসহায় বোধ করে। এই অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি পেতেই সে একজন সর্বশক্তিমান, সুরক্ষাদাতা ‘পিতৃপ্রতিম ঈশ্বরের’ (Father Figure) কল্পনা করে নেয়। ঈশ্বর হলেন আমাদের শৈশবের বাবার এক মহাজাগতিক সংস্করণ।
ফ্রয়েড তার The Future of an Illusion বইয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে, ধর্ম হলো এক ধরনের ইচ্ছাপূরণকারী ভ্রম (Wish-fulfilling Illusion) (Freud, 1927)। আমরা চাই একজন শক্তিশালী কেউ আমাদের রক্ষা করুক, তাই আমরা ঈশ্বরকে কল্পনা করি। আমরা চাই মৃত্যুতেই সব শেষ না হয়ে যাক, তাই আমরা পরকালকে কল্পনা করি। ফ্রয়েডের মতে, এই ভ্রম মানবজাতির শৈশবের প্রতীক। মানব সভ্যতাকে যদি পরিপক্ক হতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই এই সান্ত্বনাদায়ক ভ্রম ত্যাগ করে বিজ্ঞান ও যুক্তির (যাকে তিনি ‘লোগোস’ বলেছেন) উপর নির্ভর করতে শিখতে হবে।
কার্ল ইয়ুং (Carl Jung): আর্কিটাইপের প্রতিধ্বনি
ফ্রয়েডেরই একসময়ের শিষ্য এবং পরবর্তীকালের সমালোচক কার্ল ইয়ুং ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনেক বেশি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। ফ্রয়েড যেখানে ধর্মকে দেখেছেন একটি বিকার বা নিউরোসিস হিসেবে, সেখানে ইয়ুং ধর্মকে দেখেছেন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে।
ইয়ুং-এর তত্ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে ‘সম্মিলিত অচেতন’ (Collective Unconscious)-এর ধারণা। এটি হলো মানবজাতির সমস্ত অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও প্রতীকের এক জন্মসূত্রে পাওয়া ভান্ডার, যা প্রতিটি মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকে। এই সম্মিলিত অচেতনের মধ্যেই বাস করে কিছু সার্বজনীন, আদিম প্রতীক বা প্যাটার্ন, যাদেরকে ইয়ুং বলেছেন ‘আর্কিটাইপ’ (Archetype) (Psychology and Religion, 1938)। যেমন: মা, বাবা, বীর, জ্ঞানী বৃদ্ধ, শয়তান এবং ঈশ্বর। ইয়ুং-এর মতে, ঈশ্বর কোনো বাহ্যিক সত্তা নন, বরং তিনি আমাদের মনের ভেতরের একটি শক্তিশালী আর্কিটাইপ – ‘সেল্ফ’ বা ‘পূর্ণ সত্তা’-র আর্কিটাইপের প্রতীক।
ধর্মীয় পুরাণ, প্রতীক এবং আচার-অনুষ্ঠানগুলো হলো এই আর্কিটাইপগুলোরই বাহ্যিক প্রকাশ। এগুলো আমাদের সচেতন মনের সাথে আমাদের গভীর অচেতন মনের সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে। ইয়ুং-এর মতে, একজন ব্যক্তির মানসিক বিকাশের (যাকে তিনি বলেছেন ‘ইনডিভিজুয়েশন’ বা স্বতন্ত্রীকরণ) জন্য এই সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক মানুষ যখন ধর্ম এবং তার প্রতীকগুলোকে হারিয়ে ফেলে, তখন সে তার মানসিক শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের মানসিক সমস্যায় ভোগে। তাই ইয়ুং-এর কাছে, ধর্ম কোনো ভ্রম নয়, বরং এটি আত্মার আরোগ্যের একটি প্রাকৃতিক এবং প্রয়োজনীয় পথ।
নৃবিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টি: এলিয়াদ ও গিয়ার্ৎস
নৃবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির ধর্মকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে এর গঠন ও অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে মির্চা এলিয়াদ ও ক্লিফোর্ড গিয়ার্ৎসের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
মির্চা এলিয়াদ (Mircea Eliade): পবিত্রের সন্ধানে
রোমানিয়ান ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মির্চা এলিয়াদ সমাজবিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানীদের মতো ধর্মকে কোনো সামাজিক বা মানসিক ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার (Reductionism) ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার মতে, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা একটি স্বতন্ত্র এবং মৌলিক মানবিক অভিজ্ঞতা (sui generis), যাকে অন্য কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।
এলিয়াদের চিন্তার কেন্দ্রে রয়েছে ডুর্খাইমের ‘পবিত্র’ (Sacred) ও ‘সাধারণ’ (Profane)-এর বিভাজন, কিন্তু তিনি একে আরও গভীর দার্শনিক মাত্রা দিয়েছেন। তার মতে, ‘ধার্মিক মানুষ’ (Homo religiosus)-এর জন্য জগৎ একসত্ত্ব নয়। এই সাধারণ, জাগতিক জগতের মধ্যেই হঠাৎ করে ‘পবিত্র’ নিজেকে প্রকাশ করে। এই প্রকাশকে তিনি বলেছেন ‘হায়ারোফ্যানি’ (Hierophany) (The Sacred and the Profane, 1957)। একটি সাধারণ পাথর যখন পবিত্র পাথর হয়ে ওঠে, একটি সাধারণ গাছ যখন হয়ে ওঠে জীবনবৃক্ষ, তখন সেখানে হিয়েরোফ্যানি ঘটে। এই পবিত্র স্থানগুলো (যেমন: মন্দির, তীর্থ) হলো জগতের কেন্দ্র বা ‘অ্যাক্সিস মুন্ডি’ (Axis Mundi), যা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালকে সংযুক্ত করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধার্মিক মানুষ সাধারণ, রৈখিক সময় (Profane Time) থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুরাণের সেই আদি সময়ে (Sacred Time) ফিরে যেতে পারে, যখন জগৎ প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। এলিয়াদের কাছে, ধর্ম হলো মানুষের এই পবিত্রের জন্য, এক পরম বাস্তবতার জন্য অনন্তকালীন আকাঙ্ক্ষা।
ক্লিফোর্ড গিয়ার্ৎস (Clifford Geertz): অর্থের জাল
মার্কিন নৃবিজ্ঞানী ক্লিফোর্ড গিয়ার্ৎস ধর্মকে দেখেছেন একটি ‘সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা’ (Cultural System) হিসেবে। তার মতে, ধর্ম কী কাজ করে বা এর উৎস কী, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো ধর্ম মানুষের কাছে কী ‘অর্থ’ বহন করে। তিনি ধর্মের যে বিখ্যাত সংজ্ঞাটি দিয়েছেন (যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে), তার মূল কথা হলো, ধর্ম কিছু প্রতীকের মাধ্যমে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি শক্তিশালী ধারণা তৈরি করে এবং সেই ধারণাকে এতটাই বাস্তব ও বাধ্যতামূলক করে তোলে যে, তা মানুষের জীবনযাপনের প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায় (The Interpretation of Cultures, 1973)।
গিয়ার্ৎসের পদ্ধতির মূল কথা হলো ‘গভীর বর্ণনা’ (Thick Description)। একজন নৃবিজ্ঞানীর কাজ শুধু বাইরে থেকে কোনো ধর্মীয় আচার পর্যবেক্ষণ করা নয় (thin description), বরং সেই আচারের সাথে অংশগ্রহণকারীদের আবেগ, বিশ্বাস এবং অর্থের যে জটিল জাল (web of significance) জড়িয়ে আছে, সেটিকে বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা। তার কাছে, ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ বা আচার-অনুষ্ঠানগুলো হলো একটি সংস্কৃতির মানুষের নিজেদের সম্পর্কে, তাদের জগৎ সম্পর্কে এবং সেই জগতে তাদের অবস্থান সম্পর্কে বলা কিছু গল্প। নৃবিজ্ঞানীর কাজ হলো সেই গল্পগুলো পড়া এবং তার অর্থ উন্মোচন করা।
আধুনিক ও সমসাময়িক কণ্ঠস্বর: বার্জার ও অন্যরা
বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং একবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম নিয়ে আরও নতুন নতুন তত্ত্ব উঠে এসেছে।
পিটার বার্জার (Peter L. Berger): পবিত্র ছাদ
পিটার বার্জার ও টমাস লাকম্যান তাদের বিখ্যাত বই The Social Construction of Reality-তে দেখিয়েছেন যে, আমরা যে জগৎকে ‘বাস্তব’ বলে জানি, তা আসলে সামাজিকভাবে নির্মিত। ধর্ম এই বাস্তবতা নির্মাণ ও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বার্জার তার The Sacred Canopy বইয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে, মানব অস্তিত্ব সহজাতভাবেই বিশৃঙ্খল এবং অর্থহীন। এই অর্থহীনতার ভয় (যাকে তিনি ‘অ্যানোমি’ বা Anomie বলেছেন) থেকে বাঁচতে মানুষ একটি অর্থপূর্ণ জগৎ বা ‘নমোস’ (Nomos) তৈরি করে। ধর্ম এই মানবনির্মিত জগৎকে একটি ‘পবিত্র ছাদ’ (Sacred Canopy) দিয়ে ঢেকে দেয় (Berger, 1967)। এটি মানুষের তৈরি নিয়মকানুন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে মহাজাগতিক বা ঐশ্বরিক বিধানের অংশ বলে প্রচার করে। ‘এই নিয়ম মানুষ বানিয়েছে’ – এই কথা বলার পরিবর্তে ধর্ম বলে, ‘এই নিয়ম ঈশ্বর বানিয়েছেন’। এভাবে ধর্ম আমাদের ভঙ্গুর সামাজিক জগৎকে একটি পরম ও চিরন্তন বৈধতা দেয় এবং অর্থহীনতার ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করে।
এই চিন্তাবিদরা ছাড়াও আরও অনেকেই ধর্ম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। উইলিয়াম জেমস (William James) তার The Varieties of Religious Experience বইয়ে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন (James, 1902)। রডনি স্টার্কের (Rodney Stark) মতো সমাজবিজ্ঞানীরা ‘র্যাশনাল চয়েস থিওরি’ (Rational Choice Theory) প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, মানুষ অনেকটা বাজারে ক্রেতার মতোই বিভিন্ন ধর্মীয় বিকল্পের মধ্যে থেকে বিচার-বিবেচনা করে নিজের জন্য সবচেয়ে লাভজনক বিকল্পটি বেছে নেয়। আবার রিচার্ড ডকিন্স, স্যাম হ্যারিসদের মতো ‘নব্য নাস্তিকরা’ (New Atheists) ধর্মকে বিজ্ঞান ও যুক্তির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে এর কঠোর সমালোচনা করেছেন।
এইসব ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব আমাদের এটাই দেখায় যে, ধর্ম নামক প্রপঞ্চটি কোনো একক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার মতো সহজ বিষয় নয়। এটি একই সাথে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তিগত। এই চিন্তাবিদরা আমাদের হাতে কোনো চূড়ান্ত উত্তর তুলে দেননি, বরং তারা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন কিছু শক্তিশালী লেন্স, কিছু ধারালো যন্ত্র, যা দিয়ে আমরা নিজেরাই এই জটিল মানবিক অভিজ্ঞতার ব্যবচ্ছেদ চালিয়ে যেতে পারি। তাদের কাঁধে চড়েই আমরা হয়তো এই বিশাল অট্টালিকার আরও কিছু অদেখা অলিন্দে প্রবেশ করার সাহস পাই।
উপসংহার: এক অসমাপ্ত মানবিক আখ্যান
আমরা এক দীর্ঘ ও জটিল পথ পাড়ি দিয়ে এলাম। ধর্মের সংজ্ঞার চোরাবালি থেকে শুরু করে তার মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উৎস, তার বিচিত্র রূপ, তার গাঠনিক উপাদান, সভ্যতার ওপর তার আলো-ছায়ার প্রভাব এবং আধুনিক বিশ্বে তার পরিবর্তিত ভূমিকা নিয়ে অনেক কথা হলো। এই দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা কোথায় এসে দাঁড়ালাম?
আমরা দেখলাম, ধর্ম কোনো আকাশ থেকে পড়া অলৌকিক বস্তু নয়। এর শেকড় অত্যন্ত গভীরভাবে প্রোথিত আমাদের বিবর্তিত মস্তিষ্কের ভেতরে, আমাদের কার্যকারণ খোঁজার প্রবণতায়, আমাদের মৃত্যুভয়ে, আমাদের একাকীত্বে, এবং এই বিশাল, উদাসীন মহাবিশ্বে একটি অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্যময় জীবনযাপনের তীব্র মানবিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। এটি এমন এক শক্তিশালী আঠা, যা দিয়ে মানুষ পরিবার ও গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে উঠে বিশাল সমাজ ও সভ্যতা তৈরি করেছে। এটি এমন এক অনুপ্রেরণার উৎস, যা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প, সাহিত্য আর স্থাপত্য। আবার, এটি এমন এক বিভাজনের প্রাচীর, যার নামে চলেছে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম রক্তক্ষয়, ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছে ভাই, এবং সত্য ও যুক্তির কণ্ঠকে বারবার স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ধর্ম একই সাথে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং তার সবচেয়ে বিপজ্জনক দুর্বলতা।
ধর্মকে বোঝা অনেকটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো। একটি স্তর সরালে আরেকটি নতুন স্তর বেরিয়ে আসে, তার নিচে আরেকটি, এবং এই প্রক্রিয়ার কোনো শেষ নেই। ধর্মকে আপনি ভালোবাসতে পারেন, ঘৃণা করতে পারেন, এর জন্য জীবন দিতে পারেন বা এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন, কিন্তু আপনি একে উপেক্ষা করতে পারবেন না। কারণ এটি কেবল কিছু বিশ্বাস বা আচারের সমষ্টি নয়, এটি মানব অভিজ্ঞতার, মানব চেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি মানুষের নিজের হাতে তৈরি করা সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জটিল এবং সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী গল্প। এই গল্প আমাদের বলে আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, এবং এই দুই অনিবার্য বিন্দুর মাঝখানের এই সংক্ষিপ্ত, ভঙ্গুর জীবনটাতে আমাদের কীভাবে বাঁচা উচিত।
হয়তো একদিন মানুষ এই প্রাচীন গল্পগুলোর ঊর্ধ্বে উঠবে। হয়তো বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ একদিন জীবনের সব বড় বড় প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে দেবে। সেদিন হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু সেদিন কি মানুষ পুরোপুরি সুখী হবে? মহাবিশ্বের এই অসীম শূন্যতা আর অনিবার্য বিলুপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে কি নিজের জন্য, নিজের সন্তানদের জন্য নতুন কোনো গল্প তৈরি করবে না? উত্তরটা আমাদের জানা নেই। এই অনুসন্ধান তাই অসমাপ্ত। মানব সভ্যতা যতদিন আছে, ততদিন হয়তো জীবনের অর্থ খোঁজার এই অভিযান চলতেই থাকবে, নতুন নতুন রূপে। কারণ মানুষ শুধু যুক্তিনির্ভর প্রাণী নয়, সে এক গল্পপ্রেমী, অর্থসন্ধানী প্রাণী। আর ধর্ম হলো সেই চিরন্তন অনুসন্ধানেরই সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিধ্বনি।
তথ্যসূত্র
- Asad, T. (1993). Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam. Johns Hopkins University Press.
- Barber, B. R. (1996). Jihad vs. McWorld: How globalism and tribalism are reshaping the world. Ballantine Books.
- Barbour, I. G. (1997). Religion and science: Historical and contemporary issues. HarperSanFrancisco.
- Barrett, J. L. (2000). Exploring the natural foundations of religion. Trends in Cognitive Sciences, 4(1), 29–34.
- Bellah, R. N. (1967). Civil religion in America. Daedalus, 96(1), 1–21.
- Berger, P. L. (1967). The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion. Doubleday.
- Boyer, P. (2001). Religion explained: The evolutionary origins of religious thought. Basic Books.
- Campbell, J. (1949). The hero with a thousand faces. Pantheon Books.
- Campbell, H. A. (Ed.). (2012). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds. Routledge.
- Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. University of Chicago Press.
- Davie, G. (1994). Religion in Britain since 1945: Believing without belonging. Blackwell.
- Dawkins, R. (1976). The selfish gene. Oxford University Press.
- Dunbar, R. I. M. (1996). Grooming, gossip, and the evolution of language. Harvard University Press.
- Durkheim, É. (1912). The elementary forms of the religious life (J. W. Swain, Trans.). George Allen & Unwin.
- Ehrman, B. D. (2003). Lost Christianities: The battles for scripture and the faiths we never knew. Oxford University Press.
- Eliade, M. (1957). The sacred and the profane: The nature of religion (W. R. Trask, Trans.). Harcourt, Brace & World.
- Festinger, L., Riecken, H. W., & Schachter, S. (1956). When prophecy fails. University of Minnesota Press.
- Frankl, V. E. (1946). Man’s search for meaning. Beacon Press.
- Freud, S. (1927). The future of an illusion (J. Strachey, Trans.). Liveright Publishing.
- Fuller, R. C. (2001). Spiritual, but not religious: Understanding unchurched America. Oxford University Press.
- Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. Basic Books.
- Henrich, J. (2009). The evolution of costly displays, cooperation, and religion: Credibility enhancing displays and their cognitive foundations. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 18(2), 63-79.
- Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster.
- James, W. (1902). The varieties of religious experience: A study in human nature. Longmans, Green, and Co.
- Jaspers, K. (1953). The origin and goal of history (M. Bullock, Trans.). Yale University Press.
- Johnston, D. (Ed.). (2003). Faith-based diplomacy: Trumping realpolitik. Oxford University Press.
- Jung, C. G. (1938). Psychology and religion. Yale University Press.
- Juergensmeyer, M. (2003). Terror in the mind of God: The global rise of religious violence. University of California Press.
- Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.
- Marx, K. (1844). A contribution to the critique of Hegel’s Philosophy of Right.
- Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure. Free Press.
- Newberg, A. B., D’Aquili, E. G., & Rause, V. (2001). Why God won’t go away: Brain science and the biology of belief. Ballantine Books.
- Norenzayan, A. (2013). Big gods: How religion transformed cooperation and conflict. Princeton University Press.
- Otto, R. (1923). The idea of the holy (J. W. Harvey, Trans.). Oxford University Press.
- Persinger, M. A. (2001). The neuropsychiatry of paranormal experiences. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 13(4), 515–524.
- Rappaport, R. A. (1999). Ritual and religion in the making of humanity. Cambridge University Press.
- Shermer, M. (2008). Patternicity: Finding meaningful patterns in meaningless noise. Scientific American, 299(6), 48.
- Smart, N. (1998). The world’s religions (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Solomon, S., Greenberg, J., & Pyszczynski, T. (2015). The worm at the core: On the role of death in life. Random House.
- Taylor, C. (2007). A secular age. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Thomas, S. M. (2005). The global resurgence of religion and the transformation of international relations. Palgrave Macmillan.
- Tillich, P. (1957). Dynamics of faith. Harper & Row.
- Turner, V. W. (1969). The ritual process: Structure and anti-structure. Aldine Publishing.
- Tylor, E. B. (1871). Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom. John Murray.
- van Gennep, A. (1909). Les rites de passage [The Rites of Passage] (M. B. Vizedom & G. L. Caffee, Trans.). University of Chicago Press.
- Weber, M. (1905). The Protestant ethic and the spirit of capitalism (T. Parsons, Trans.). Roxbury Publishing Company.
- Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922).
- Winell, M. (2011). Religious Trauma Syndrome: It’s time to recognize it. Journey Free. (Note: This is often cited from her website/articles as a primary source for the RTS concept, later elaborated in her book Leaving the Fold).