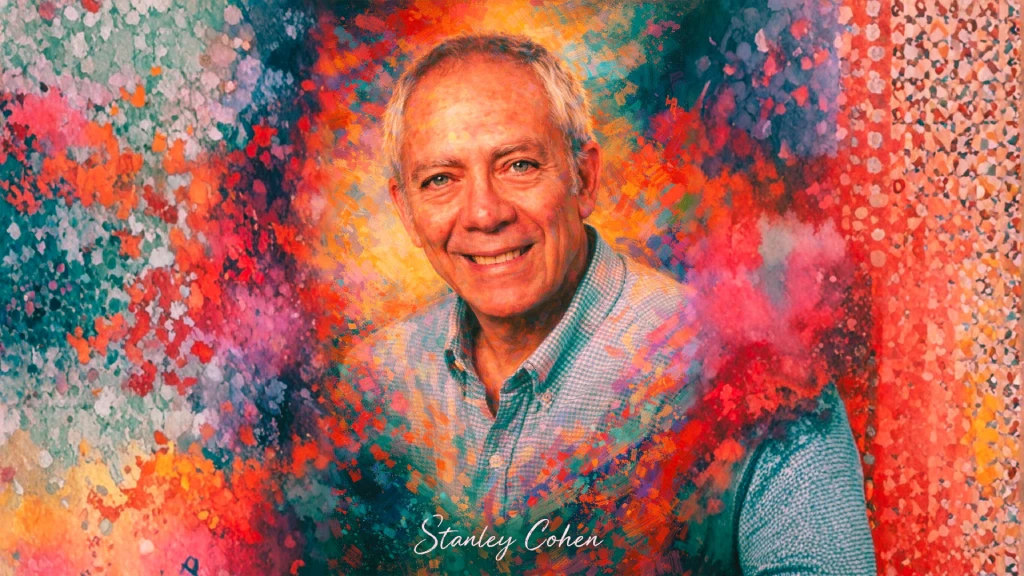স্ট্যানলি কোহেন (Stanley Cohen): সেই জাদুকর যিনি সমাজের লুকানো ভয়কে চিনতে শিখিয়েছিলেন
Table of Contents
- 1 ভূমিকা
- 2 যে মানুষটি ভয়কে ব্যবচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন
- 3 যে সময়ের গর্ভে জন্মাল এক নতুন তত্ত্ব – ষাটের দশকের সেই উত্তাল হাওয়া
- 4 স্ট্যানলি কোহেনের চশমা: যে ইতিহাস ও দর্শন তাঁকে পৃথিবী চিনতে শিখিয়েছিল
- 5 ক্ল্যাকটনের সেই মেঘলা দিন এবং আতঙ্কের সুনামি
- 6 আতঙ্কের ব্যবচ্ছেদ – মোরাল প্যানিকের ধাপসমূহ এবং এর ভেতরের কারসাজি
- 6.1 ধাপ ১: শনাক্তকরণ এবং সংজ্ঞা প্রদান (Identification and Definition)
- 6.2 ধাপ ২: মিডিয়ার সরলীকরণ, প্রতীকরূপ প্রদান এবং অতিরঞ্জন (Simplification, Symbolization, and Exaggeration by the Media)
- 6.3 ধাপ ৩: উদ্বেগের বিস্তার এবং নৈতিক উদ্যোক্তাদের আবির্ভাব (Stirring up Concern and the Rise of Moral Entrepreneurs)
- 6.4 ধাপ ৪: কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া এবং দমন-পীড়ন (Response from Authorities and Crackdown)
- 6.5 ধাপ ৫: ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং বিচ্যুতি বিবর্ধন সর্পিল (The Deviancy Amplification Spiral)
- 7 লোক-দানবের জন্ম, তার সামাজিক প্রয়োজন এবং তার নিঃসঙ্গতা
- 8 আতঙ্কের জাদুঘর – ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু মোরাল প্যানিক
- 9 কোহেনের দ্বিতীয় ইনিংস – অস্বীকারের মনোরাজ্য (States of Denial)
- 10 কোহেনের রেখে যাওয়া চশমা: তত্ত্বের পথ ধরে যারা হেঁটেছে
- 11 তত্ত্বের কাঠগড়ায় – সমালোচনা
- 12 উপসংহার
- 13 তথ্যসূত্র
ভূমিকা
আমাদের চারপাশের পৃথিবীটা মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক মঞ্চের মতো লাগে, তাই না? যেখানে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে কত শত নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে, কিন্তু আমরা তার পেছনের পরিচালক বা নাট্যকারকে দেখতে পাই না। আমরা দেখি, হঠাৎ করেই কোনো একটা বিষয় নিয়ে পুরো দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে টেলিভিশনের টক শো পর্যন্ত সবাই একই সুরে কথা বলছে, একই দিকে আঙুল তুলছে। সমাজের বুকে যেন এক অজানা জ্বরের কাঁপুনি লেগেছে। আবার কিছুদিন পর দেখি, সেই উত্তাপ কোথায় উবে গেছে, সেই আলোচনার আর কোনো চিহ্ন নেই। আমরা দেখি, কীভাবে রাতারাতি কেউ নায়ক হয়ে যায়, আবার কেউ হয়ে যায় গণশত্রু, এক সহজ খলনায়ক। এই যে সামাজিক আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন, এই যে সম্মিলিত আবেগ আর ঘৃণার হঠাৎ বিস্ফোরণ – এর পেছনে কি কোনো নিয়ম কাজ করে? কোনো নকশা আছে কি এর? নাকি সবকিছুই নিছকই কাকতালীয়?
অধিকাংশ সময় আমরা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবি না। আমরা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু মানুষ আসেন, যারা এই স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে শেখান। তাঁরা আমাদের চারপাশের চিরচেনা পৃথিবীকে দেখার চোখটাই আমূল পাল্টে দেন। তাঁরা আমাদের হাতে এমন এক আশ্চর্য চশমা তুলে দেন, যা দিয়ে আমরা এতদিন যা দেখেও দেখিনি, যা বুঝেও বুঝিনি, তা হঠাৎ করেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁরা আমাদের শেখান, সাধারণ ঘটনার আড়ালে কীভাবে অসাধারণ সব সামাজিক প্রক্রিয়া কাজ করে; কীভাবে আমাদের ভয়, ঘৃণা, উদ্বেগ আর ভালোবাসা আসলে কেবলই আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়, বরং তা সমাজের এক অদৃশ্য সুতোয় বোনা এক জটিল নকশার অংশ। সমাজবিজ্ঞানী স্ট্যানলি কোহেন (Stanley Cohen) ছিলেন ঠিক তেমনই একজন মানুষ। তিনি কোনো গোয়েন্দা ছিলেন না, তাঁর হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা পাইপ ছিল না, কিন্তু সমাজের মনস্তত্ত্বের এমন সব গভীর রহস্যের সমাধান করেছেন, যা শার্লক হোমসকেও হয়তো এক মুহূর্তের জন্য থামিয়ে দিয়ে ভাবাতো। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল আমাদের সম্মিলিত ভয়।
কোহেনের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ আমাদের দুটি শব্দগুচ্ছ উপহার দিয়েছে, যা আজ সমাজবিজ্ঞানের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ আলোচনার অংশ হয়ে গেছে: ‘মোরাল প্যানিক’ (Moral Panic) বা নৈতিক আতঙ্ক, এবং ‘ফোক ডেভিল’ (Folk Devil) বা লোক-দানব। শব্দ দুটো শুনতে বেশ ভারী আর একাডেমিক মনে হতে পারে, তাই না? মনে হতে পারে, এ আর এমন কী! কিন্তু এর পেছনের গল্পটা একেবারেই সাদামাটা, আমাদের খুব চেনা কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই দীর্ঘ লেখায় আমরা সেই স্ট্যানলি কোহেনের জগতে এক গভীর ডুব দেব। আমরা দেখব, কীভাবে ইংল্যান্ডের এক মেঘলা দিনের সমুদ্রতীরের কিছু তরুণ-তরুণীর সামান্য হাতাহাতি আর ভাঙা চেয়ারের স্তূপ থেকে তিনি বের করে এনেছিলেন মানব সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক ভয়ঙ্কর প্রবণতার নিখুঁত নকশা, এক গোপন সূত্র।
আমরা তাঁর হাত ধরে কেবল ষাটের দশকের কোলাহলমুখর, পরিবর্তনশীল ইংল্যান্ডেই ঘুরব না। কারণ, কোহেনের তত্ত্ব কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এক সার্বজনীন সত্যের উন্মোচন। আমরা দেখব, কীভাবে সেই একই নকশা, সেই একই প্রক্রিয়া আজকের ডিজিটাল জগতেও প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনকে, আমাদের চিন্তাকে, আমাদের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে চলেছে। কীভাবে আমাদের ফেসবুকের নিউজফিড, হোয়াটসঅ্যাপে ফরোয়ার্ড করা মেসেজ, আর টেলিভিশনের ব্রেকিং নিউজগুলো প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ‘লোক-দানব’ তৈরি করছে আর আমাদের এক অন্তহীন ‘নৈতিক আতঙ্কের’ মধ্যে ডুবিয়ে রাখছে। চলুন, সেই দীর্ঘ কিন্তু আকর্ষণীয় গল্পটা শুরু করা যাক। এই লেখাটি শেষ করার পর হয়তো আপনার চারপাশের পৃথিবীকে দেখার চশমাটিও কিছুটা পাল্টে যাবে।
যে মানুষটি ভয়কে ব্যবচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন
যেকোনো বড় নদীর উৎস খুঁজতে গেলে যেমন পাহাড়ের দুর্গম গভীরে যেতে হয়, তেমনি যেকোনো যুগান্তকারী চিন্তার উৎস খুঁজতে গেলেও প্রবেশ করতে হয় সেই চিন্তকের জীবনের অলিগলিতে। তাঁর বেড়ে ওঠা, তাঁর দেখা পৃথিবী, তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রাম এবং তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব – এই সবকিছুই তাঁর তত্ত্বের ডিএনএ তৈরি করে দেয়। স্ট্যানলি কোহেনের সমাজ বদলে দেওয়া তত্ত্বগুলোকে নিছক একাডেমিক ধারণা হিসেবে দেখলে তার প্রতি সুবিচার করা হয় না। সেগুলোকে বুঝতে হলে প্রয়োজন সেই মানুষটিকে চেনা, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের তীব্র আগুনের ছায়া থেকে উঠে এসে আমাদের শিখিয়েছেন সমাজের ভয়, ঘৃণা আর অস্বীকারের জটিল মনস্তত্ত্ব। এই পর্বে আমরা তাঁর তত্ত্বের জগতে বিশদভাবে প্রবেশ করব না, বরং সেই জগতের কারিগরের জীবনের দীর্ঘ ও বন্ধুর পথচলার গল্প শুনব।
স্ট্যানলি কোহেন জন্মেছিলেন ১৯৪২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি, দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় শহর জোহানেসবার্গে। তাঁর পরিবার ছিল লিথুয়ানিয়ান-ইহুদি বংশোদ্ভূত। তারা ইউরোপের বুকে ঘনিয়ে আসা ইহুদি-বিদ্বেষ এবং আসন্ন মহাপ্রলয়ের (Holocaust) অশনি সংকেত পেয়ে নতুন জীবনের আশায় আফ্রিকায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এক ধরনের নিপীড়ন থেকে পালিয়ে এসে তারা পড়ল আরেক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের মধ্যে। কোহেনের জন্মের মাত্র ছয় বছর পর, ১৯৪৮ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্ষমতা দখল করে ন্যাশনাল পার্টি (National Party) এবং রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এক ভয়ঙ্কর প্রথা – বর্ণবৈষম্য বা অ্যাপার্টাইড (apartheid)। এটি ছিল এমন এক অমানবিক ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের চামড়ার রঙের ভিত্তিতে তার ভাগ্য, তার অধিকার, তার নাগরিকত্ব, এমনকি তার ভালোবাসার অধিকার পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হতো।
শ্বেতাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও ইহুদি হিসেবে কোহেন ও তাঁর পরিবার এক ধরনের প্রান্তিকতার মধ্যেই বড় হয়েছেন। তবে তিনি ছোটবেলা থেকেই নিজের চোখের সামনে দেখেছেন রাষ্ট্র কীভাবে তার সমস্ত আইন, পুলিশ, মিডিয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি দিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো এবং অশ্বেতাঙ্গ মানুষদের দমন করে, তাদের ন্যূনতম মানবিক অধিকার কেড়ে নেয় এবং তাদের নিজ দেশেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে। তিনি দেখেছেন কীভাবে আলাদা বাস এলাকা, আলাদা স্কুল, আলাদা টয়লেট, আলাদা পার্কের বেঞ্চ – এইসবের মাধ্যমে এক কৃত্রিম এবং হিংস্র বিভাজন তৈরি করা হয়। আর এই বিভাজনকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভয়, ঘৃণা আর সন্দেহের চাষ করা হয়। তিনি দেখেছেন, কীভাবে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ‘সমস্যা’, ‘বিপদ’ বা ‘অপর’ (the other) হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ওপর সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে বৈধতা দেওয়া হয়। এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা কোহেনের চিন্তার জগতে এক স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল।
তিনি অল্প বয়স থেকেই বুঝেছিলেন যে ‘বিচ্যুতি’ (deviance) বা ‘অপরাধ’ (crime) কোনো নিরপেক্ষ বা ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত বিষয় নয়। যা একদল মানুষের কাছে বেঁচে থাকার সংগ্রাম বা প্রতিবাদের ভাষা, তা-ই অন্যদলের কাছে, অর্থাৎ ক্ষমতাশালীদের কাছে, ‘অপরাধ’ বা ‘বিপদ’ হিসেবে গণ্য হতে পারে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) কীভাবে কাজ করে এবং রাষ্ট্র কীভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে (marginalized groups) ‘শত্রু’ বা ‘দানব’ হিসেবে চিহ্নিত করে নিজের শাসনকে বৈধতা দেয় এবং সমাজের আসল সমস্যাগুলো থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়। এই গভীর বোধই ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর।
তিনি জোহানেসবার্গের মর্যাদাপূর্ণ উইটওয়াটারস্র্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Witwatersrand) সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন। ‘উইটস’ (Wits) নামে পরিচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তখন ছিল বর্ণবাদ-বিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। এখানেই কোহেন একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি সেইসব বিদ্রোহী তরুণদের একজন ছিলেন, যারা বিশ্বাস করতেন যে এই অমানবিক ব্যবস্থার পতন অবশ্যম্ভাবী এবং এর জন্য রাস্তায় নেমে লড়াই করাটা নৈতিক দায়িত্ব। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি কর্তৃপক্ষের কড়া নজরে পড়েন। একসময় তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা ছিল – হয় বর্ণবাদী সরকারের কুখ্যাত জেলে বছরের পর বছর পচে মরা, নয়তো প্রিয় মাতৃভূমি, পরিবার, বন্ধু সবকিছু ছেড়ে চিরদিনের জন্য নির্বাসনে চলে যাওয়া। কোহেন দ্বিতীয়, বেদনাদায়ক পথটি বেছে নেন। ১৯৬৩ সালে, মাত্র ২১ বছর বয়সে, তিনি ইংল্যান্ডে চলে আসেন। এই নির্বাসন তাঁর মনে এক গভীর ক্ষত তৈরি করলেও, এটিই তাঁকে সেই ‘আউটসাইডার’-এর দৃষ্টি দিয়েছিল যা দিয়ে তিনি সমাজকে ভিন্নভাবে দেখতে শিখেছিলেন।
লন্ডনে এসে তিনি বিশ্ববিখ্যাত লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস (London School of Economics – LSE)-এ সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি করার জন্য ভর্তি হন। ষাটের দশকের LSE তখন সমাজবিজ্ঞানের জগতে এক তীর্থস্থান, নতুন নতুন র্যাডিকাল চিন্তার এক উত্তাল কেন্দ্র। এখানেই তিনি তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দেওয়ার ভাষা খুঁজে পান। তিনি পরিচিত হন ‘লেবেলিং থিওরি’ (Labelling Theory) বা তকমা-আঁটা তত্ত্বের সাথে, যা মূলত শিকাগো স্কুল অফ সোসিওলজি (Chicago School of Sociology) থেকে উঠে এসেছিল। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো, কোনো কাজ বা আচরণ নিজে থেকে ‘অপরাধ’ বা ‘বিচ্যুত’ নয়। সমাজই কোনো কাজ বা কোনো ব্যক্তির গায়ে ‘অপরাধী’ বা ‘বিচ্যুত’-এর তকমা বা লেবেল সেঁটে দেয়। হাওয়ার্ড বেকারের (Howard Becker) মতো সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রভাবশালী বই ‘আউটসাইডার্স’ (Outsiders)-এ বলছিলেন, “The deviant is one to whom that label has successfully been applied; deviant behavior is behavior that people so label.” (Becker, 1963)। অর্থাৎ, বিচ্যুত আচরণ হলো সেই আচরণ, যাকে সমাজের ক্ষমতাশালী অংশ বিচ্যুত বলে চিহ্নিত করে।
এই ধারণাটি কোহেনের দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার সাথে আয়নার মতো মিলে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, রাষ্ট্র বা সমাজের ক্ষমতাশালী অংশ – যাদের বেকার একটি চমৎকার নাম দিয়েছিলেন ‘মোরাল এন্টারপ্রেনার’ (moral entrepreneurs) বা নৈতিক উদ্যোক্তা – তারাই আইন ও নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয়। তারাই ঠিক করে দেয় কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা সমাজের জন্য বিপজ্জনক। এই তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়েই কোহেন পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন তাঁর নতুন দেশ, ব্রিটেনকে। আর সেখানেই তিনি খুঁজে পান তাঁর গবেষণার সেই বিখ্যাত বিষয় – মডস এবং রকার্স, যা জন্ম দেয় ‘মোরাল প্যানিক’ তত্ত্বের এবং ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ক্লাসিক বই ‘ফোক ডেভিলস অ্যান্ড মোরাল প্যানিকস’।
পিএইচডি শেষ করার পর তিনি কিছুদিন ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান এবং এরপর যোগ দেন এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Essex), যা তখন ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানের র্যাডিকাল ধারার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। এসেক্সে থাকাকালীন তিনি তাঁর চিন্তাকে আরও বিস্তৃত করেন। তিনি কেবল মিডিয়ার তৈরি করা আতঙ্ক নিয়েই কাজ করেননি, বরং কারাগার, মানসিক হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, তা নিয়েও গবেষণা শুরু করেন।
১৯৮০ সালে তিনি ইসরায়েলে চলে যান এবং জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে (Hebrew University of Jerusalem) অপরাধবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দেন। এই পদক্ষেপটি ছিল তাঁর জীবনের এক জটিল অধ্যায়। একজন ইহুদি এবং বর্ণবাদ-বিরোধী কর্মী হিসেবে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর এক ধরনের সহানুভূতি থাকলেও, তিনি ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরায়েলি রাষ্ট্রের আচরণের একজন কঠোর সমালোচক হয়ে ওঠেন। এখানেই তিনি রাষ্ট্রীয় অপরাধ (state crime) এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে কাজ শুরু করেন। এই সময়েই তিনি তাঁর আরেকটি প্রভাবশালী বই ‘ভিশনস অফ সোশ্যাল কন্ট্রোল: ক্রাইম, পানিশমেন্ট অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন’ (Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification) প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি দেখান কীভাবে আধুনিক সমাজ শাস্তির দৃশ্যমান রূপ (যেমন কারাগার) থেকে বেরিয়ে এসে আরও সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের জাল বিস্তার করছে (Cohen, 1985)।
নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আবার ফিরে আসেন লন্ডনে, তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান LSE-তে। এখানে তিনি অপরাধবিজ্ঞানের ‘মার্টিন হোয়াইট প্রফেসর’ হিসেবে যোগ দেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। এই পর্যায়ে তাঁর কাজ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। যুগোস্লাভিয়ায় গণহত্যা, রুয়ান্ডার গণহত্যা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসানের পর ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন’ (Truth and Reconciliation Commission) গঠন – এইসব ঘটনা তাঁকে মানব সমাজের এক গভীরতর সমস্যা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। সমস্যাটি হলো – আমরা কীভাবে এত বড় অন্যায় জেনেও না জানার ভান করে বেঁচে থাকি? এই ভাবনা থেকেই জন্ম নেয় তাঁর জীবনের সেরা কাজ, ২০০১ সালে প্রকাশিত বই ‘স্টেটস অফ ডিনায়াল: নোয়িং অ্যাবাউট অ্যাট্রোসিটিস অ্যান্ড সাফারিং’। এটি ছিল মানব সমাজের সম্মিলিত নীরবতা, উদাসীনতা আর নিষ্ক্রিয়তার এক নির্মোহ এবং বেদনাদায়ক ব্যবচ্ছেদ।
শেষ জীবনে তিনি পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হন। এই দুর্বলকারী এবং নিষ্ঠুর রোগটি ধীরে ধীরে তাঁর শরীরকে অক্ষম করে দিচ্ছিল, কিন্তু তাঁর মন এবং চিন্তার ধার এতটুকুও কমেনি। ২০১৩ সালের ২রা অক্টোবর, ৭১ বছর বয়সে, তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু রেখে যান এক বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার।
স্ট্যানলি কোহেন কেবল একজন সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন গভীর মানবতাবাদী, একজন আজন্ম বিদ্রোহী এবং একজন অ্যাক্টিভিষ্ট, যিনি সবসময় ক্ষমতার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন এবং সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক, সবচেয়ে নিন্দিত, সবচেয়ে ‘দানব’ হিসেবে পরিচিত মানুষটির মধ্যেও মানবতা খুঁজে ফিরেছেন। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর তত্ত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ – এক ‘আউটসাইডার’-এর চোখে পৃথিবীকে দেখার এক দীর্ঘ, আন্তরিক এবং সাহসী গল্প।
যে সময়ের গর্ভে জন্মাল এক নতুন তত্ত্ব – ষাটের দশকের সেই উত্তাল হাওয়া
যেকোনো যুগান্তকারী তত্ত্বকে বুঝতে হলে তার জন্ম-সময় আর প্রেক্ষাপটকে বোঝাটা ভীষণ জরুরি। তত্ত্ব তো আর আকাশ থেকে পড়ে না, তার শেকড় থাকে সময়ের মাটিতে, সমাজের গভীরে। স্ট্যানলি কোহেনের ‘মোরাল প্যানিক’ তত্ত্বটি ছিল ষাটের দশকের ইংল্যান্ডের উত্তাল, পরিবর্তনশীল, আশা আর আশঙ্কার দোলাচলে দুলতে থাকা এক দ্বন্দ্বমুখর সময়ের প্রত্যক্ষ ফসল। এই সময়টাকে এর সমস্ত জটিলতা দিয়ে অনুভব করতে না পারলে তত্ত্বটির জন্মরহস্যও আমাদের কাছে অধরা থেকে যাবে। সময়টা ছিল বাইরে থেকে শান্ত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফুটতে থাকা এক আগ্নেয়গিরির মতো।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় দেড় দশক আগে। লন্ডনের আকাশে আর জার্মান বোমারু বিমানের হাহাকার নেই, রাতের বেলা ব্ল্যাকআউটের দমবন্ধ করা অন্ধকারও নেই। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নগুলো ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে, বোমায় ধ্বংস হওয়া দালানগুলোর জায়গায় উঠছে নতুন সব ঝকঝকে ইমারত। যুদ্ধকালীন মিতব্যয়িতা আর রেশনিংয়ের ধূসর দিনগুলো, যখন এক টুকরো মাখন বা এক পাউন্ড চিনির জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হতো, সেই স্মৃতি পেছনে ফেলে ব্রিটেন এক নতুন ভোরের আলো দেখছে। অর্থনীতিতে এক অভূতপূর্ব জোয়ার এসেছে, যাকে তৎকালীন রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান (Harold Macmillan) ১৯৫৭ সালে এক বিখ্যাত উক্তিতে বর্ণনা করেছিলেন এই বলে যে, “most of our people have never had it so good.”
এই যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক বুম (post-war economic boom) সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আমূল পাল্টে দিচ্ছিল। পূর্ণ কর্মসংস্থান (full employment) এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের (welfare state) প্রসারের ফলে মানুষের হাতে আগের চেয়ে বেশি টাকা, জীবনে এসেছে অবসর কাটানোর মতো ফুরসত। ফ্রিজ, টেলিভিশন, রেকর্ড প্লেয়ার, ওয়াশিং মেশিনের মতো ভোগ্যপণ্য এখন আর কেবল ধনীদের বিলাসিতা নয়, তা ধীরে ধীরে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও কর্মজীবী শ্রেণির ঘরেও জায়গা করে নিচ্ছে। এই নতুন সমৃদ্ধি এক ধরনের আশাবাদ তৈরি করেছিল, কিন্তু তার সাথেই তৈরি করেছিল এক গভীর প্রজন্মগত ফাটল (generation gap)।
এই অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার মধ্য থেকেই জন্ম নিচ্ছিল এমন এক প্রজন্ম, যারা তাদের বাবা-মায়েদের থেকে ছিল একেবারেই আলাদা। এই নতুন প্রজন্ম, যাদের আমরা ‘বেবি বুমার’ (baby boomer) প্রজন্ম বলে চিনি, তারা যুদ্ধ দেখেনি, দেখেনি ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার (Great Depression) ভয়াল রূপ। তাদের অভিজ্ঞতায় অভাব বা রেশন ব্যবস্থা ছিল না। তারা দেখেছে ক্রমবর্ধমান ভোগবাদ (consumerism) আর সম্ভাবনার এক খোলা ময়দান। তাদের বাবা-মায়েরা যেখানে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে দেখেছিলেন নিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতা, সেখানে এই নতুন প্রজন্ম খুঁজছিল উত্তেজনা, আত্মপরিচয় আর মুক্তি। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ‘টিনএজার’ (teenager) বা ‘তরুণ’ (youth) শব্দটি কেবল একটি বয়সসীমা বোঝাল না, বরং এটি একটি স্বতন্ত্র বাজার (market), একটি স্বতন্ত্র পরিচয় এবং একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি (culture) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। তাদের নিজেদের পকেটে খরচ করার মতো টাকা ছিল, নিজেদের পছন্দ ছিল, আর ছিল সেই পছন্দকে উচ্চস্বরে প্রকাশ করার মতো আত্মবিশ্বাস। তারা তাদের বাবা-মায়েদের মতো চার্চ বা কমিউনিটি হলের অনুশাসনে বাঁধা থাকতে চায়নি; তারা চেয়েছিল নিজেদের জগৎ, নিজেদের সঙ্গীত, নিজেদের ফ্যাশন। এই সময়টাকেই আর্থার মারউইক (Arthur Marwick) তাঁর বিখ্যাত বইতে ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’ (cultural revolution) বলে অভিহিত করেছেন (Marwick, 1998)।
এই নব্য আবির্ভূত তরুণ সংস্কৃতির দুটি প্রধান ধারা তখন ইংল্যান্ডের রাস্তায়, ক্যাফেতে আর ডান্স হলগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যেন দুটি ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা, বিদ্রোহের দুই ভিন্ন ভাষা। একদলের নাম ‘মডস’ (Mods), আরেক দলের নাম ‘রকার্স’ (Rockers)। এরা কেবল দুটি ভিন্ন পোশাকের স্টাইল ছিল না, ছিল দুটি ভিন্ন জীবনদর্শন, দুটি ভিন্ন পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি। সমাজতাত্ত্বিক ডিক হেবডিজ (Dick Hebdige) দেখিয়েছেন, এই উপ-সংস্কৃতিগুলো (subcultures) ছিল আসলে মূলধারার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতীকী প্রতিরোধ, যা তাদের স্টাইলের মাধ্যমে প্রকাশিত হতো (Hebdige, 1979)।
মডস (Mods)
শব্দটি এসেছে ‘মডার্নিস্ট’ (Modernist) থেকে, যা তাদের পরিচয়ের সারমর্ম। তারা ছিল ভবিষ্যৎমুখী, ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রতি আকৃষ্ট এবং ভীষণভাবে স্টাইল-সচেতন। তাদের দর্শন ছিল ‘clean living under difficult circumstances’। তাদের তীর্থস্থান ছিল লন্ডনের কার্নাবি স্ট্রিট (Carnaby Street) বা সোহোর (Soho) কোনো জ্যাজ ক্লাব। তারা পরত দর্জির বানানো নিখুঁত, স্লিম-ফিট ইতালিয়ান স্যুট, ফ্রেড পেরি (Fred Perry) পোলো শার্ট, আর পায়ে থাকত মরুভূমির বুট (desert boots) বা বোলিং শু। তাদের চুল ছিল ফরাসি সিনেমার নায়কদের মতো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। তাদের মূল বাহন ছিল ইতালিয়ান স্কুটার – ভেসপা (Vespa) বা ল্যামব্রেটা (Lambretta)। তবে সেই স্কুটার যেমন-তেমন স্কুটার নয়। সেগুলো ছিল তাদের পরিচয়ের চলন্ত বিজ্ঞাপন। সেগুলোকে সাজানো হতো ডজন ডজন আয়না, সারি সারি অতিরিক্ত হেডলাইট আর নানা রকম অলংকার দিয়ে। এই স্কুটার ছিল তাদের আভিজাত্য ও আধুনিকতার প্রতীক। মডসরা শুনত আমেরিকার নতুন ধারার কালো সঙ্গীত – মোটাউন (Motown), সোল (Soul) এবং আরএন্ডবি (R&B)। তারা ক্যাফেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসপ্রেসো কফি খেতে খেতে অস্তিত্ববাদ নিয়ে আলোচনা করত, নাচতে যেত অল-নাইটার ক্লাবে (all-nighter clubs), আর নিজেদের তারা ভাবত সমাজের বাকিদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে, রুচিশীল এবং পরিশীলিত। তাদের জীবনে গতি আনার জন্য অনেকে অ্যামফিটামিন (amphetamine) বা ‘পার্পল হার্টস’ (purple hearts) নামক ড্রাগও ব্যবহার করত, যা তাদের রাতভর নাচতে বা স্কুটার চালাতে সাহায্য করত। তারা ছিল মূলত শহুরে, বিশেষ করে লন্ডনের কর্মজীবী বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণ, যারা নিজেদের শ্রেণিগত পরিচয় ছাপিয়ে এক নতুন, আধুনিক পরিচিতি গড়তে চেয়েছিল। তাদের স্টাইল ছিল তাদের বর্ম, তাদের অস্ত্র।
রকার্স (Rockers)
অন্যদিকে রকার্সরা ছিল মডসদের সম্পূর্ণ বিপরীত – যেন অতীতের এক বিদ্রোহী প্রতিধ্বনি। তাদের শিকড় ছিল পঞ্চাশের দশকের আমেরিকান রক অ্যান্ড রোল (Rock and Roll) সংস্কৃতিতে। তারা ছিল পুরানো দিনের বিদ্রোহী, যারা আধুনিকতার চাকচিক্যকে সন্দেহের চোখে দেখত। তাদের আদর্শ ছিলেন মার্লোন ব্র্যান্ডো (Marlon Brando) (‘The Wild One’ সিনেমার বাইকার চরিত্রে) বা জেমস ডিন (James Dean)। তারা পরত কালো চামড়ার মোটরসাইকেল জ্যাকেট, যার পিঠে হয়তো তাদের ক্লাবের নাম লেখা, সাদা টি-শার্ট, জিন্সের প্যান্ট আর ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং বুট। তাদের চুল থাকত তেল (pomade) দিয়ে পেছনে আঁচড়ানো, যাকে বলা হতো ‘ডাকটেইল’ (ducktail)। তাদের বাহন ছিল ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গর্ব, শক্তিশালী এবং দ্রুতগতির মোটরসাইকেল – ট্রায়াম্ফ (Triumph Bonneville), নর্টন (Norton Commando) বা বিএসএ (BSA)। তাদের কাছে গতিই ছিল আসল কথা, মেশিনের গর্জনই ছিল তাদের সঙ্গীত। তারা শহরের বাইরের রাস্তায় তীব্র গতিতে বাইক ছোটাত, আড্ডা দিত রাস্তার পাশের ট্রান্সপোর্ট ক্যাফেগুলোতে (transport cafes), যেখানে ট্রাক ড্রাইভারদের আনাগোনা। তাদের সঙ্গীত ছিল এলভিস প্রিসলি (Elvis Presley), জিন ভিনসেন্ট (Gene Vincent) এবং এডি কোচরান (Eddie Cochran)-এর মতো পঞ্চাশের দশকের রক অ্যান্ড রোল শিল্পীরা। রকার্সদের মধ্যে এক ধরনের পৌরুষদীপ্ত, মাচো, ঐতিহ্যবাহী এবং আপসহীন বিদ্রোহী মনোভাব ছিল। তারা মডসদের মতো ইউরোপীয় ফ্যাশনের ধার ধারত না, তারা ছিল আমেরিকান বিদ্রোহী সংস্কৃতির ব্রিটিশ সংস্করণ।
এই দুই দলের মধ্যে শত্রুতা কি আগে থেকেই ছিল? সত্যি বলতে, জাতীয় পর্যায়ে তেমন প্রকটভাবে নয়। তাদের জগৎ ছিল ভিন্ন, তাদের মূল্যবোধ ছিল ভিন্ন। মডসরা রকার্সদের দেখত অপরিচ্ছন্ন, অমার্জিত, পুরনো ধ্যানধারণার ‘গ্রিজার’ (greaser) হিসেবে। আর রকার্সরা মডসদের মনে করত মেয়েলি, অতিরিক্ত সাজগোজ করা ‘পাউডার-পাফ’ (powder-puff) ছেলে, যারা আসল পৌরুষ কী তা জানেই না। তাদের মধ্যে ছোটখাটো রেষারেষি বা এলাকাভিত্তিক দ্বন্দ্ব যে ছিল না তা নয়, কিন্তু জাতীয় মিডিয়া বা বৃহত্তর সমাজ এদের নিয়ে তখনো খুব একটা মাথা ঘামায়নি। তারা ছিল ব্রিটিশ তরুণ সমাজের দুটি সমান্তরাল স্রোত, যারা নিজেদের জগতে ভালোই ছিল, একে অপরের পথ পারতপক্ষে এড়িয়েই চলত।
কিন্তু এই শান্ত পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল একটি ছুটির দিন, একটি মেঘলা আবহাওয়া, আর একদল বিরক্ত তরুণ। ১৯৬৪ সালের ইস্টার সপ্তাহের ছুটি। স্থান – ইংল্যান্ডের পূর্ব উপকূলের একটি শান্ত, নিদ্রালু, মধ্যবিত্তের অবসরযাপনের প্রিয় রিসোর্ট শহর, ক্ল্যাকটন-অন-সি (Clacton-on-Sea)। এই ধরনের শহরগুলো ছিল ব্রিটিশ ঐতিহ্যের প্রতীক, যেখানে পরিবারগুলো ছুটি কাটাতে আসত, বুড়োবুড়িরা সৈকতের ধারে চেয়ারে বসে রোদ পোহাত। এই শান্ত, পূর্বানুমেয় পরিবেশই হয়ে উঠল আসন্ন নাটকের নিখুঁত মঞ্চ। সেই ছুটির দিনে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী সেখানে গিয়েছিল একটু মুক্তির স্বাদ নিতে, দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি থেকে পালাতে। তাদের মধ্যে ছিল অনেক মডস এবং রকার্স। আর সেখানেই ঘটল সেই ছোট্ট ঘটনা, যা ব্রিটিশ সমাজকে নাড়িয়ে দিল এবং এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল।
স্ট্যানলি কোহেনের চশমা: যে ইতিহাস ও দর্শন তাঁকে পৃথিবী চিনতে শিখিয়েছিল
কোনো চিন্তা তো শূন্যে তৈরি হয় না, তাই না? প্রতিটি বড় ধারণার পেছনে থাকে সময়ের ছাপ, ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাস আর পূর্বসূরি চিন্তকদের রেখে যাওয়া পথের ধুলো। স্ট্যানলি কোহেন যে আশ্চর্য চশমাটি তৈরি করে আমাদের চোখে পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই চশমার কাঁচ কিন্তু তিনি একা তৈরি করেননি। সেই কাঁচ গড়া হয়েছিল ইতিহাসের উত্তপ্ত চুল্লিতে, আর তাকে মসৃণ করেছিল তাঁর আগের দিনের কিছু অসাধারণ দার্শনিকের ভাবনা। কোহেনের ‘মোরাল প্যানিক’ বা ‘স্টেটস অফ ডিনায়াল’-এর মতো যুগান্তকারী তত্ত্বগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। দেখতে হবে, কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে এই প্রশ্নগুলো করতে বাধ্য করেছিল, আর কোন চিন্তকদের কাঁধে দাঁড়িয়ে তিনি পৃথিবীকে এতটা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। চলুন, সেই সফরেই বের হওয়া যাক।
ইতিহাসের পাতা থেকে: যে সময় কোহেনকে বানিয়েছিল
আমরা সবাই আমাদের সময়ের সন্তান। আমাদের বেড়ে ওঠার পৃথিবী, আমাদের চারপাশের রাজনীতি, আমাদের সমাজের ভয় আর ভালোবাসা – এগুলোই আমাদের চিন্তার মানচিত্র এঁকে দেয়। স্ট্যানলি কোহেনের ক্ষেত্রে এই কথাটি ছিল অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণ আকাশ থেকে পড়েনি; বরং কয়েকটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তাঁর চিন্তার জগতে নাড়া দিয়েছিল এবং তাঁকে সেই প্রশ্নগুলো করতে শিখিয়েছিল, যা আগে কেউ সেভাবে করেনি। কোহেনের তত্ত্বকে বুঝতে হলে আমাদের সেই সময়ের উত্তাল সমুদ্রে ডুব দিতে হবে, দেখতে হবে কোন ঢেউগুলো তাঁকে আজকের পরিচিত তীরে এনে ফেলেছিল।
বর্ণবাদের জ্বলন্ত চুল্লি: দক্ষিণ আফ্রিকার সেই দিনগুলো
কোহেনের গল্পের শুরুটা বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে তাঁর শৈশবে, বর্ণবৈষম্যে (apartheid) দীর্ণ দক্ষিণ আফ্রিকায়। এটি কেবল তাঁর জন্মস্থান ছিল না; এটি ছিল তাঁর চিন্তার আঁতুড়ঘর, এক জীবন্ত ল্যাবরেটরি যেখানে তিনি ক্ষমতার কদর্য রূপকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। ১৯৪৮ সালে, কোহেনের শৈশবের শুরুতেই, দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যাপার্টাইড রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গৃহীত হয়। এটি কোনো সাধারণ বৈষম্য ছিল না, এটি ছিল রাষ্ট্রের দ্বারা পরিকল্পিত, আইন দ্বারা সমর্থিত এবং পুলিশ দ্বারা বলবৎ করা এক ভয়ঙ্কর নিপীড়ন ব্যবস্থা। মানুষের চামড়ার রঙের ভিত্তিতে তার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেওয়া হতো।
কোহেন ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন, কীভাবে রাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ‘সমস্যা’ হিসেবে চিহ্নিত করে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো মানুষদের ‘অপর’ (the other) বানিয়ে তাদের ওপর সব ধরনের অমানবিকতাকে বৈধতা দেওয়া হতো। ‘পাস ল’ (Pass Laws) এর মতো আইনের মাধ্যমে তাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হতো, ভালো চাকরি বা ভালো এলাকায় বসবাসের অধিকার কেড়ে নেওয়া হতো। তাদের জন্য আলাদা রাস্তা, আলাদা স্কুল, আলাদা হাসপাতাল – সবকিছুই ছিল এই বার্তার প্রতীক যে, তারা সমান মানুষ নয়। রাষ্ট্র নিজেই ছিল সবচেয়ে বড় ‘মোরাল এন্টারপ্রেনার’ (moral entrepreneur), যে আইন ও রাষ্ট্রীয় প্রচারণার (state propaganda) মাধ্যমে কালো মানুষদের ‘ফোক ডেভিল’ বা লোক-দানব বানিয়ে দিয়েছিল। তাদের দেখানো হতো অপরাধী, অসভ্য এবং শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার জন্য হুমকি হিসেবে। শার্পভিলের গণহত্যার (Sharpeville Massacre, 1960) মতো ঘটনা, যেখানে পুলিশ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছিল, তা দেখিয়ে দিয়েছিল এই রাষ্ট্র কতটা নির্মম হতে পারে।
এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কোহেনকে কয়েকটি মৌলিক বিষয় শিখিয়েছিল, যা তাঁর পরবর্তী সমস্ত কাজের ভিত্তি তৈরি করে দেয়:
- ক্ষমতা ও সংজ্ঞা: তিনি হাড়েমজ্জায় বুঝেছিলেন, ‘অপরাধ’ বা ‘বিচ্যুতি’ (deviance) কোনো ধ্রুব সত্য নয়। ক্ষমতা যার হাতে, সংজ্ঞাও তার হাতে। রাষ্ট্র চাইলে যেকোনো গোষ্ঠীর গায়ে ‘অপরাধী’-র তকমা সেঁটে দিতে পারে এবং সেই তকমার ভিত্তিতে তাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে পারে।
- লেবেলিং-এর শক্তি: একটি গোষ্ঠীর গায়ে যখন বারবার কোনো নেতিবাচক লেবেল বা তকমা লাগানো হয়, তখন সমাজও তাদের সেভাবেই দেখতে শুরু করে। এমনকি সেই গোষ্ঠীর মানুষও একসময় সেই লেবেলকে আত্মস্থ করে ফেলে। এই লেবেলিং প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে, তা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: তিনি দেখেছিলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) কেবল কারাগার বা পুলিশের লাঠির মাধ্যমে হয় না। এটি হয় ভয়, ঘৃণা এবং বিভাজন তৈরির মাধ্যমে, যা মানুষের মনের ভেতরেই এক অদৃশ্য কারাগার তৈরি করে। অ্যাপার্টাইড ছিল ভয়ের ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকা এক ব্যবস্থা।
- অস্বীকারের সংস্কৃতি: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি দেখেছিলেন কীভাবে দেশের শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী এই ভয়ঙ্কর অন্যায়ের পাশে থেকেও তা না দেখার ভান করে, তাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে নিজেদের দৈনন্দিন জীবন চালিয়ে যায়। এই সম্মিলিত অস্বীকার (collective denial) তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং তাঁর পরবর্তী জীবনের কাজ ‘স্টেটস অফ ডিনায়াল’-এর বীজ এখানেই রোপিত হয়েছিল।
এই জ্বলন্ত চুল্লির অভিজ্ঞতা ছাড়া কোহেন হয়তো ইংল্যান্ডের মডস ও রকার্সদের ঘটনাটিকে নিছকই কিছু তরুণের উচ্ছৃঙ্খলতা হিসেবেই দেখতেন। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার চোখ তাঁকে শিখিয়েছিল, কীভাবে ক্ষমতাশালীরা প্রান্তিক গোষ্ঠীকে ‘দানব’ বানিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। ক্ল্যাকটনের সমুদ্রতীরে তিনি আসলে জোহানেসবার্গের রাস্তারই এক ক্ষুদ্র কিন্তু অর্থপূর্ণ সংস্করণ দেখতে পেয়েছিলেন।
যুদ্ধের পরের ব্রিটেন: শান্ত হ্রদের নিচের তোলপাড়
১৯৬৩ সালে কোহেন যখন ব্রিটেনে এলেন, তখন দেশটি বাইরে থেকে ছিল বেশ শান্ত ও স্থিতিশীল। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, অর্থনীতি ভালো, মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে। এই সময়টাকে বলা হতো ‘যুদ্ধ-পরবর্তী ঐকমত্য’ (Post-War Consensus)-এর যুগ। কনজারভেটিভ বা লেবার – যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তারা কল্যাণ রাষ্ট্র (welfare state), পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং একটি স্থিতিশীল সমাজব্যবব্যবস্থা বজায় রাখতে একমত ছিল। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে এই স্থিতিশীলতাই ছিল পরম আরাধ্য। যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং তিরিশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দা দেখার পর তারা আর কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা বড় পরিবর্তন চাননি। তাদের কাছে শৃঙ্খলা, সম্মান এবং ঐতিহ্য ছিল সবচেয়ে বড় মূল্যবোধ।
কিন্তু এই শান্ত হ্রদের নিচেই তোলপাড় চলছিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলে জন্ম নেওয়া নতুন ‘টিনএজার’ প্রজন্ম এই স্থিতিশীলতাকে দেখছিল একঘেয়েমি বা ‘বোরডোম’ হিসেবে। তাদের কাছে যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের গল্প, তাদের বাবা-মায়েদের মূল্যবোধ ছিল সেকেলে। তারা চেয়েছিল নতুন কিছু – নতুন সঙ্গীত (রক অ্যান্ড রোল, ব্লুজ), নতুন ফ্যাশন, নতুন জীবনযাত্রা। এই প্রজন্মগত সংঘাত (generational conflict) ষাটের দশকের ব্রিটিশ সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। লেখক কলিন ম্যাকিনেস (Colin MacInnes) তাঁর উপন্যাস ‘অ্যাবসোলিউট বিগিনার্স’ (Absolute Beginners)-এ এই নতুন টিনএজ সংস্কৃতির উত্থানকে খুব সুন্দরভাবে ধরেছিলেন (MacInnes, 1959)।
এই প্রেক্ষাপটটি ‘মোরাল প্যানিক’ তত্ত্বের জন্য উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। কারণ:
- উদ্বেগ: বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজন্ম এবং সমাজের ক্ষমতাশালীরা (মিডিয়া, রাজনীতিবিদ, পুলিশ) তরুণদের এই নতুন সংস্কৃতিকে বুঝতে পারছিল না। আর যা বোঝা যায় না, তা-ই ভয় তৈরি করে। মডস ও রকার্সদের স্টাইল, তাদের সঙ্গীত, তাদের স্কুটার বা মোটরসাইকেলের প্রতি ভালোবাসা, তাদের সপ্তাহান্তের উচ্ছৃঙ্খলতা – এই সবকিছুই ছিল প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের প্রতি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ।
- শৃঙ্খলা হারানোর ভয়: তাদের কাছে এই তরুণরা ছিল আসন্ন বিশৃঙ্খলার প্রতীক। তাদের মনে হচ্ছিল, সমাজের নৈতিক বাঁধন বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে, সবকিছু বুঝি গোল্লায় যাচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন এবং বিশ্বমঞ্চে ব্রিটেনের প্রভাব কমে আসাও এই জাতীয় নিরাপত্তাহীনতায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। এই তরুণদের অবাধ্যতার মধ্যে তারা যেন দেশের বৃহত্তর অবক্ষয়ের ছায়া দেখতে পাচ্ছিল।
- সহজ লক্ষ্যবস্তু: সমাজের গভীরে থাকা আসল সমস্যাগুলো – যেমন শ্রেণিবৈষম্য যা তখনও প্রকট ছিল, অথবা দ্রুত শিল্পায়নের ফলে তৈরি হওয়া বিচ্ছিন্নতা (alienation) – এগুলো নিয়ে কথা বলার চেয়ে কর্মজীবী শ্রেণির (working-class) তরুণদের একটি দলকে ‘বলির পাঁঠা’ (scapegoat) বানানো অনেক সহজ ছিল। তাদের ‘দানব’ হিসেবে চিত্রিত করে সমাজের যাবতীয় উদ্বেগ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
কোহেন অসাধারণভাবে দেখিয়েছিলেন, মডস ও রকার্সদের নিয়ে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল, তা আসলে সেই তরুণদের প্রকৃত বিপদের কারণে নয়, বরং যুদ্ধ-পরবর্তী ব্রিটিশ সমাজের ভেতরে থাকা গভীর উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা এবং পরিবর্তন নিয়ে ভয়েরই প্রতিফলন ছিল (Pearson, 1983)।
টেলিভিশনের আগমন: বৈঠকখানার নতুন অতিথি
ষাট ও সত্তরের দশকে আরেকটি বিপ্লব ঘটছিল, যা ছিল প্রায় নীরব কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী। সেটি হলো গণমাধ্যমের, বিশেষ করে টেলিভিশনের বিস্তার। পঞ্চাশের দশকের শেষেও টেলিভিশন ছিল উচ্চবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্তের বিলাসিতা, কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটি ব্রিটিশদের বৈঠকখানার এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। ১৯৬৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনাল প্রায় ৩২ মিলিয়ন ব্রিটিশ দর্শক টেলিভিশনে দেখেছিল, যা এই মাধ্যমের ব্যাপকতাকে প্রমাণ করে।
এই নতুন মাধ্যমটি ‘মোরাল প্যানিক’ তৈরির প্রক্রিয়াকে বহুগুণে শক্তিশালী করে তুলেছিল:
- তাৎক্ষণিকতা ও দৃশ্যমানতা: খবরের কাগজের সাদা-কালো অক্ষরের চেয়ে টেলিভিশনের চলমান ছবির প্রভাব ছিল অনেক বেশি সরাসরি এবং আবেগপূর্ণ। ক্ল্যাকটনের সৈকতে মারামারির ছবি যখন সারা দেশের মানুষ তাদের বসার ঘরে দেখল, তখন তার প্রভাব ছিল বিশাল। মিডিয়া তাত্ত্বিক মার্শাল ম্যাকলুহান (Marshall McLuhan) যেমনটি বলেছিলেন, “the medium is the message” (McLuhan, 1964), অর্থাৎ মাধ্যমটি নিজেই বার্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। টেলিভিশনের ছবি বাস্তবতাকে আরও বেশি ‘বাস্তব’ করে তোলে, যদিও তা ছিল সম্পাদনা করা এবং বাছাই করা বাস্তবতা।
- কেন্দ্রীয় কণ্ঠস্বর: আজকের মতো শত শত চ্যানেল বা অনলাইন নিউজ পোর্টালের যুগ তখন ছিল না। হাতে গোনা কয়েকটি পত্রিকা আর বিবিসি-আইটিভির মতো দু-একটি টেলিভিশন চ্যানেলই ছিল খবরের মূল উৎস। ফলে, এই কয়েকটি মাধ্যম যা বলত, যেভাবে পৃথিবীকে দেখাত, সেটাই হয়ে উঠত জাতীয় বাস্তবতা। তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলত কে কত বেশি চাঞ্চল্যকর খবর পরিবেশন করতে পারে, যা অতিরঞ্জনের প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে দিত। তারা খুব সহজেই একটি জাতীয় ঐকমত্য বা আতঙ্ক তৈরি করতে পারত।
- বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব: টেলিভিশন ‘বিশেষজ্ঞ’ বা ‘পণ্ডিত’দের (Pundits) জন্ম দেয়। কোনো ঘটনা ঘটলেই চ্যানেলের স্টুডিওতে সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, পুলিশ কর্তা বা রাজনীতিবিদদের ডেকে এনে আলোচনা করা হতো। এই ‘বিশেষজ্ঞরা’ প্রায়শই আতঙ্ককে আরও বাড়িয়ে তুলতেন এবং ঘটনাকে একটি সাধারণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে একটি গভীর সামাজিক সমস্যার প্রতীকে পরিণত করতেন। তারা ঘটনাকে একটি বৃহত্তর নৈতিক কাঠামোর মধ্যে ফেলে ব্যাখ্যা করতেন, যা সাধারণ মানুষের ভয়কে আরও উস্কে দিত।
কোহেন বুঝেছিলেন, মিডিয়া কেবল ঘটনার নিরপেক্ষ দর্শক বা প্রতিবেদক নয়; মিডিয়া নিজেই ঘটনার একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং প্রায়শই নাটকের প্রধান পরিচালক।
তথ্য যুগ এবং দূরবর্তী দুর্ভোগ: এক নতুন নৈতিক সংকট
কোহেনের চিন্তার শেষ পর্যায়ে আরেকটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেটি হলো বিশ্বায়ন (globalization) এবং তথ্য প্রযুক্তির বিস্ফোরণ। সত্তরের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল প্রথম ‘টেলিভিশন যুদ্ধ’, যা মানুষের ড্রয়িং রুমে যুদ্ধের ভয়াবহতাকে নিয়ে এসেছিল। এরপর নব্বইয়ের দশকে বলকান যুদ্ধ (বিশেষ করে বসনিয়ায় গণহত্যা), রুয়ান্ডার গণহত্যা এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং পরবর্তীতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের চোখের সামনে ঘটতে লাগল।
এই ঘটনাপ্রবাহ কোহেনকে এক নতুন এবং আরও জটিল প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয়। প্রশ্নটি হলো: আমরা যখন এতকিছু জানি, যখন বিশ্বের অন্য প্রান্তের মানুষের দুর্ভোগ আমাদের হাতের মুঠোয়, তখন আমরা কেন কিছুই করি না? কেন আমরা নিষ্ক্রিয় থাকি? আমাদের হাতের ক্লিকেই যেখানে সাহায্যের আবেদন করা যায়, সেখানে আমরা কেন উদাসীন থাকি?
এই প্রেক্ষাপটটিই তাঁকে ‘স্টেটস অফ ডিনায়াল’ (States of Denial) লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি দেখলেন, মোরাল প্যানিকের ঠিক উল্টো একটি প্রক্রিয়াও সমাজে কাজ করে। যেখানে একটি ছোট বিষয় নিয়ে সমাজ অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া (overreaction) দেখায়, সেখানে ভয়ঙ্কর এবং বিশাল অন্যায় দেখেও সমাজ সম্মিলিতভাবে নীরব (underreaction) থাকে। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে তথ্যের অভাব নেই, কিন্তু আছে সহানুভূতির ক্লান্তি (compassion fatigue) এবং এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অসাড়তা (psychic numbing)। খবরের ২৪-ঘণ্টার চক্রে একটি ভয়াবহ ঘটনা আরেকটি ভয়াবহ ঘটনা দিয়ে ঢাকা পড়ে যায়। আমরা এত বেশি ভয়াবহতার ছবি দেখি যে, একসময় তা আমাদের আর নাড়া দেয় না। এই নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিই কোহেনকে সমাজের ‘অস্বীকার’ করার ক্ষমতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল, যা হয়তো মোরাল প্যানিকের চেয়েও গভীর এবং বিপজ্জনক এক সামাজিক ব্যাধি।
চিন্তার কারিগর: যাদের কাঁধে দাঁড়িয়ে কোহেন পৃথিবীকে দেখেছিলেন
কোনো চিন্তাবিদই একা হাঁটেন না, কোনো ধারণাই শূন্য থেকে জন্মায় না। প্রতিটি বড় চিন্তার পেছনে থাকে পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া পথের ধুলো, তাদের জ্বালিয়ে যাওয়া জ্ঞানের মশাল। স্ট্যানলি কোহেনও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি ছিলেন বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ধারার একজন মেধাবী উত্তরসূরি। তিনি তাঁর আগের দিনের চিন্তকদের কাছ থেকে কিছু মৌলিক ধারণা ধার করেছিলেন, সেগুলোকে নিজের মতো করে ঘষেমেজে নতুন রূপ দিয়েছিলেন এবং তাঁর সময়ের বাস্তবতার নিরিখে সেগুলোকে এক অনন্য কাঠামোয় দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার শিকড় বুঝতে হলে আমাদের সেইসব কারিগরদের সাথে পরিচিত হতে হবে, যারা তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন।
শিকাগো স্কুল: শহরের রাজপথে সমাজবিজ্ঞানের পাঠ
বিশ শতকের শুরুর দিকে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল সমাজবিজ্ঞানী এক নতুন ধারার সূচনা করেন, যা সমাজবিজ্ঞানকে লাইব্রেরির চার দেয়াল থেকে বের করে এনেছিল শহরের কোলাহলমুখর রাস্তায়। রবার্ট পার্ক (Robert Park), আর্নেস্ট বার্জেস (Ernest Burgess), ডব্লিউ. আই. থমাস (W. I. Thomas)-দের মতো এই চিন্তকদের বলা হয় শিকাগো স্কুল (Chicago School) অফ সোসিওলজির প্রবক্তা। তাঁদের গবেষণাগার ছিল শিকাগো শহর নিজেই – তার বস্তি, তার কারখানা, তার অভিবাসী পল্লি, তার অপরাধ জগৎ। তাঁরা অধ্যয়ন করতেন সাধারণ মানুষের জীবন – অভিবাসী, শ্রমিক, ভবঘুরে, যৌনকর্মী, জ্যাজ সঙ্গীতশিল্পী।
তাঁদের মূল অবদান ছিল ‘সিম্বলিক ইন্টারেকশনিজম’ (Symbolic Interactionism) নামক একটি ধারণা, যা জর্জ হার্বার্ট মিড (George Herbert Mead) এর কাজ থেকে অনুপ্রাণিত। এর সহজ কথা হলো, আমাদের পৃথিবীটা কোনো পূর্বনির্ধারিত বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে নেই। আমরা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময়, প্রতীক (symbol) এবং ভাষার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমাদের সামাজিক বাস্তবতাকে তৈরি করে চলেছি। ডব্লিউ. আই. থমাসের বিখ্যাত উক্তি, “If men define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas & Thomas, 1928), এই দর্শনের সারমর্ম। অর্থাৎ, আমরা যদি কোনো পরিস্থিতিকে বাস্তব বলে মনে করি, তবে তার ফলাফলও বাস্তব হবে, পরিস্থিতিটি আদতে সত্যি হোক বা না হোক।
এই স্কুল থেকেই কোহেন তাঁর কাজের দুটি মূল ভিত্তি পেয়েছিলেন:
- বাস্তবতার সামাজিক নির্মাণ (Social Construction of Reality): ‘অপরাধ’ বা ‘নৈতিকতা’র মতো বিষয়গুলো আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকে না। সমাজই আলোচনার মাধ্যমে, বিতর্কের মাধ্যমে, আইন তৈরির মাধ্যমে এগুলোকে ‘নির্মাণ’ করে। মডস ও রকার্সদের ‘সমস্যা’ হিসেবে দেখাটা ছিল এমনই এক সামাজিকভাবে নির্মিত বাস্তবতা, যা মিডিয়া এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল।
- এথনোগ্রাফিক পদ্ধতি (Ethnographic Method): মানুষের জীবনকে বুঝতে হলে তাদের কাছে যেতে হবে, তাদের সাথে কথা বলতে হবে, তাদের জগতকে তাদের চোখ দিয়ে দেখতে হবে। একে বলা হয় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (participant observation)। কোহেন মডস ও রকার্সদের নিয়ে কাজ করার সময় ঠিক এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন। তিনি কেবল পত্রিকার রিপোর্ট বা পুলিশের ফাইল পড়েননি, তিনি তাদের সাথে মিশেছিলেন, তাদের ক্যাফেতে আড্ডা দিয়েছিলেন, তাদের কনসার্টে গিয়েছিলেন (Platt, 1996)। এই পদ্ধতিই তাঁকে মিডিয়ার তৈরি করা চিত্রের ভেতরের আসল মানুষগুলোকে চিনতে সাহায্য করেছিল।
হাওয়ার্ড এস. বেকার: যিনি নিয়মকানুন তৈরির কারিগরদের চিনিয়েছিলেন
শিকাগো স্কুলেরই পরবর্তী প্রজন্মের একজন গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন হাওয়ার্ড এস. বেকার (Howard S. Becker)। তাঁর ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত বই ‘আউটসাইডার্স: স্টাডিজ ইন দ্য সোসিওলজি অফ ডেভিয়ান্স’ (Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance) কোহেনের ওপর সরাসরি এবং সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই বইটিকে লেবেলিং তত্ত্বের (Labelling Theory) বাইবেল বলা যেতে পারে।
বেকার একটি খুব সহজ কিন্তু বিপ্লবী প্রশ্ন করেছিলেন: সমাজে নিয়মকানুনগুলো (rules) কারা তৈরি করে এবং কেন করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি ‘মোরাল এন্টারপ্রেনার’ (moral entrepreneurs) বা নৈতিক উদ্যোক্তা ধারণাটির জন্ম দেন। এরা হলেন সেইসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, যারা নিজেদের নৈতিক বিশ্বাসকে সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে চান। তারা কোনো একটি আচরণকে (যেমন, মারিজুয়ানা সেবন) ‘অনৈতিক’ বা ‘বিপজ্জনক’ বলে প্রচার চালান এবং এর বিরুদ্ধে আইন তৈরির জন্য জনমত গঠন করেন। বেকার দেখান যে, বিচ্যুত আচরণ আসলে সেই আচরণ, যাকে এই নৈতিক উদ্যোক্তারা সফলভাবে ‘বিচ্যুত’ বলে তকমা সেঁটে দিতে পেরেছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি ছিল, “The deviant is one to whom that label has successfully been applied; deviant behavior is behavior that people so label” (Becker, 1963)।
কোহেন তাঁর ‘মোরাল প্যানিক’ তত্ত্বে বেকারের এই ধারণাটি সরাসরি ব্যবহার করেছেন। মডস ও রকার্সদের ঘটনায় রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বিচারক এবং ধর্মীয় নেতারা ছিলেন সেই ‘মোরাল এন্টারপ্রেনার’, যারা তরুণদের এই নতুন সংস্কৃতিকে সমাজের জন্য এক বিরাট হুমকি হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে একটি ‘নৈতিক ক্রুসেড’ (moral crusade) শুরু করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল তরুণদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পুরানো মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
এডউইন লেমার্ট: বিচ্যুতির দুই ধাপের তত্ত্ব
আরেকজন সমাজবিজ্ঞানী, এডউইন লেমার্ট (Edwin Lemert), কোহেনের ‘ডেভিয়েন্সি এমপ্লিফিকেশন স্পাইরাল’ বা বিচ্যুতি বিবর্ধন সর্পিল ধারণাটি বুঝতে একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক কাঠামো জুগিয়েছিলেন। লেমার্ট বিচ্যুতিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন: প্রাথমিক বিচ্যুতি (primary deviance) এবং গৌণ বিচ্যুতি (secondary deviance)।
- প্রাথমিক বিচ্যুতি (Primary Deviance): এটি হলো প্রথমবার নিয়ম ভাঙার কাজটি, যা হয়তো খুব গুরুতর নয়, বিক্ষিপ্ত এবং ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের (self-identity) অংশ নয়। ব্যক্তি নিজেও নিজেকে ‘অপরাধী’ বা ‘বিচ্যুত’ বলে মনে করে না। যেমন, কোনো তরুণ হয়তো বন্ধুদের সাথে মজা করার জন্য একবার একটি দোকানের জানালা ভাঙল। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।
- গৌণ বিচ্যুতি (Secondary Deviance): এটি ঘটে তখন, যখন সমাজ সেই প্রাথমিক বিচ্যুতির প্রতিক্রিয়ায় সেই ব্যক্তির গায়ে ‘গুন্ডা’ বা ‘অপরাধী’-র তকমা সেঁটে দেয়। পুলিশ তাকে হয়রানি করে, প্রতিবেশীরা সন্দেহের চোখে দেখে, শিক্ষকরা তাকে খারাপ ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। এই তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়ার (societal reaction) ফলে সে ধীরে ধীরে সমাজের চোখে দেখা পরিচয়েই নিজেকে চিনতে শুরু করে। সে ভাবতে শুরু করে, “সবাই যখন আমাকে খারাপই ভাবে, তাহলে ভালো হয়ে আর লাভ কী?” সে তখন সেই কলঙ্কিত ভূমিকাটিকেই (stigmatized role) তার মূল পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করতে থাকে। সে তখন সত্যিকারের অপরাধ জগতে প্রবেশ করতে পারে।
লেমার্টের তত্ত্বটি অসাধারণভাবে ব্যাখ্যা করে, কীভাবে সমাজের প্রতিক্রিয়া একটি ছোট সমস্যাকে বড় সমস্যায় পরিণত করে। বিচ্যুতি দমনের চেষ্টাই অনেক সময় বিচ্যুতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে (Lemert, 1951)। কোহেন দেখিয়েছেন, মডস ও রকার্সদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছিল। তাদের প্রাথমিক ছোটখাটো উচ্ছৃঙ্খলতার (প্রাথমিক বিচ্যুতি) প্রতিক্রিয়ায় মিডিয়া ও পুলিশ তাদের ‘ফোক ডেভিল’ বানিয়ে দেয়, যা তাদের আরও বেশি করে বিদ্রোহী এবং হিংস্র আচরণ করতে প্ররোচিত করে – এটিই হলো গৌণ বিচ্যুতি।
আরভিং গফম্যান: কলঙ্ক এবং পরিচয়ের নাটক
আরভিং গফম্যান (Erving Goffman) ছিলেন সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার (social interaction) এক অসাধারণ পর্যবেক্ষক। তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের সামাজিক জীবনটা অনেকটা নাটকের মঞ্চের মতো (dramaturgy), যেখানে আমরা সবাই বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে চলেছি এবং অন্যদের কাছে নিজেদের একটি নির্দিষ্ট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করি (impression management)। তাঁর ‘স্টিগমা’ (Stigma) বা ‘কলঙ্ক’ ধারণাটি কোহেনের ‘ফোক ডেভিল’ বুঝতে একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা যোগ করে।
গফম্যানের মতে, স্টিগমা হলো এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা একজন ব্যক্তিকে সমাজের চোখে ‘কলঙ্কিত’ বা ‘ত্রুটিপূর্ণ’ করে তোলে এবং তার পরিচয়কে নষ্ট করে দেয় (spoiled identity)। এই কলঙ্ক শারীরিক হতে পারে (যেমন, প্রতিবন্ধকতা), চারিত্রিক হতে পারে (যেমন, মানসিক রোগী বা মাদকাসক্ত) অথবা গোষ্ঠীগত হতে পারে (যেমন, নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা ধর্মের সদস্য হওয়া) (Goffman, 1963)।
‘ফোক ডেভিল’-রা হলো সেই গোষ্ঠী, যাদের ওপর সমাজ সম্মিলিতভাবে একটি শক্তিশালী স্টিগমা বা কলঙ্ক চাপিয়ে দেয়। ‘মড’ বা ‘রকার’ – এই পরিচয়টিই তাদের জন্য এক ধরনের কলঙ্কে পরিণত হয়েছিল। তাদের দেখলেই মানুষ তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলি বিচার না করে, সরাসরি ‘বিপজ্জনক’ বা ‘অনৈতিক’ বলে ধরে নিত। গফম্যানের কাজ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, এই কলঙ্কিত পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকাটা কতটা কঠিন এবং কীভাবে এই কলঙ্কই একজন ব্যক্তিকে সমাজের চোখে তার নির্দিষ্ট ভূমিকার মধ্যে আটকে ফেলে, তার অন্য সব পরিচয়কে মুছে দেয়।
লেসলি উইলকিন্স: বিচ্যুতি বিবর্ধনের ধারণা
যদিও কোহেনের তত্ত্বের সাথে ‘ডেভিয়েন্সি এমপ্লিফিকেশন স্পাইরাল’ কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এই ধারণাটির মূল প্রবক্তা ছিলেন অপরাধবিজ্ঞানী লেসলি উইলকিন্স (Leslie Wilkins)। উইলকিন্স দেখান যে, কোনো বিচ্যুত আচরণ সম্পর্কে যত বেশি তথ্য প্রচার করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ যত বেশি কঠোর ব্যবস্থা নেয়, তত বেশি মানুষ সেই আচরণ সম্পর্কে জানতে পারে এবং কেউ কেউ তা অনুকরণ করতেও শুরু করে। এর ফলে সেই আচরণের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়, যা কর্তৃপক্ষকে আরও কঠোর হতে বাধ্য করে – এভাবেই একটি সর্পিল চক্র তৈরি হয় (Wilkins, 1964)। কোহেন উইলকিন্সের এই মডেলটিকে মডস ও রকার্সদের ঘটনার প্রেক্ষাপটে সফলভাবে প্রয়োগ করে একে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি দিয়েছিলেন।
এইসব ঐতিহাসিক ঘটনা এবং দার্শনিক চিন্তার সংশ্লেষণ থেকেই জন্ম নিয়েছিল স্ট্যানলি কোহেনের ক্ষুরধার এবং আজও প্রাসঙ্গিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তিনি কোনো নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করেননি, কেবল আমাদের হাতে একটি নতুন মানচিত্র তুলে দিয়েছিলেন, যা দিয়ে আমরা আমাদের চেনা পৃথিবীর লুকানো পথগুলোকেও চিনতে পারি। তিনি এই চিন্তকদের কাছ থেকে ইট, কাঠ, সিমেন্ট ধার করেছিলেন, কিন্তু তা দিয়ে যে ইমারতটি তিনি তৈরি করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অনন্য।
ক্ল্যাকটনের সেই মেঘলা দিন এবং আতঙ্কের সুনামি
১৯৬৪ সালের সেই ইস্টারের সপ্তাহান্তে ক্ল্যাকটনের সমুদ্র সৈকতে ঠিক কী ঘটেছিল? যদি আমরা মিডিয়ার তৈরি করা উত্তেজনা, রাজনীতিবিদদের বাগাড়ম্বর আর সাধারণ মানুষের আতঙ্ক – এই সবকিছুকে একপাশে সরিয়ে রেখে একেবারে নিরস বাস্তব তথ্যের দিকে তাকাই, তাহলে ঘটনাটি ছিল হতাশাজনকভাবে বেশ সামান্য। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাই ব্রিটিশ সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক স্নায়বিক দুর্বলতাকে উন্মোচিত করে দিয়েছিল, ঠিক যেমন একটি ছোট পাথরের আঘাতে বাঁধের ফাটল স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
ক্ল্যাকটন-অন-সি ছিল ষাটের দশকে ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত এবং কর্মজীবী পরিবারের জন্য এক আদর্শ ছুটির গন্তব্য। এর পরিচিতি ছিল শান্ত, নিরাপদ এবং সম্মানিত একটি শহর হিসেবে। মানুষ এখানে আসত পিয়ারে হাঁটতে, হট ডোনাট বা ক্যান্ডি ফ্লস খেতে, ডেকের চেয়ারে বসে অলস সময় কাটাতে এবং নুড়ি বিছানো সৈকতে সন্তানদের খেলতে দেখতে। এটি ছিল ব্রিটিশ ঐতিহ্যের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ – শৃঙ্খলাবদ্ধ, অনুমানযোগ্য এবং শান্ত। এই শান্ত, প্রায় ঘুমন্ত পরিবেশই হয়ে উঠেছিল আসন্ন নাটকের নিখুঁত মঞ্চ, কারণ এখানেই ‘সভ্যতা’ এবং ‘বর্বরতা’-র নাটকটি সবচেয়ে জোরালোভাবে মঞ্চস্থ করা সম্ভব ছিল।
ইস্টারের ছুটি, কিন্তু আবহাওয়া ছিল বিশ্বাসঘাতক – ঠাণ্ডা, মেঘলা আর স্যাঁতসেঁতে। সমুদ্রতীরবর্তী রিসোর্ট শহরের মূল আকর্ষণই হলো রোদ ঝলমলে সৈকত, কিন্তু প্রকৃতি সেদিন সঙ্গ দিচ্ছিল না। ছুটির দিনে মুক্তির স্বাদ নিতে আসা হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর করার মতো তেমন কিছুই ছিল না। কারখানার একঘেয়ে জীবন বা অফিসের নিষ্প্রাণ ডেস্ক থেকে পালিয়ে আসা এই তরুণদের অফুরন্ত শক্তি সেই মেঘলা দিনে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। অলস সময়, তারুণ্যের শক্তি আর ছুটির দিনের একঘেয়েমি – এই তিনের মিশ্রণে যা হওয়ার তাই হলো।
কিছু মডস এবং রকার্স দলের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একে অপরকে উদ্দেশ্য করে টিটকিরি দেওয়া, যা তাদের উপ-সংস্কৃতির পরিচয়েরই অংশ ছিল। মডসরা রকার্সদের ডাকছিল ‘গ্রিজার’ (greasers) বলে, তাদের অপরিচ্ছন্ন স্টাইলকে ব্যঙ্গ করছিল। অন্যদিকে রকার্সরা মডসদের মেয়েলি ‘পাউডার-পাফ’ (powder-puff) বলে উপহাস করছিল। কে বেশি স্টাইলিশ, কার বাহন বেশি ভালো – এইসব নিয়েই ছিল তাদের তর্ক। এক পর্যায়ে এই মৌখিক আস্ফালন ছোটখাটো ধাক্কাধাক্কি এবং হাতাহাতিতে গড়ায়। সৈকতের ধারে রাখা কিছু চেয়ার (deckchairs) ভাঙা হয়, কয়েকটি দোকানের জানালায় পাথর ছোড়া হয়, আর বিয়ারের বোতল ছোড়াছুড়ি হয়। স্থানীয় পুলিশ দ্রুত এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং প্রায় ৯৭ জনকে বিভিন্ন অপরাধে, যেমন – অশোভন আচরণ, শান্তিভঙ্গ ইত্যাদি অভিযোগে গ্রেফতার করে। দিনের শেষে সবকিছু আবার আগের মতোই শান্ত হয়ে যায়। শহরে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কেউ গুরুতরভাবে আহতও হয়নি। এটি ছিল বড়জোর একটি স্থানীয় উপদ্রব, কোনো জাতীয় সংকট নয়।
যেকোনো ছুটির দিনে একটি পর্যটন শহরে এমন ঘটনা খুব বিরল নয়। বড়জোর এটি স্থানীয় পত্রিকার ভেতরের পাতায় এক কলামের একটি ছোটখাটো খবর হতে পারত, যার শিরোনাম হতো ‘ছুটির দিনে তরুণদের উচ্ছৃঙ্খলতা’। কিন্তু তা হলো না। জাতীয় পত্রিকাগুলোর সাংবাদিকরা, যারা ছুটির দিনে বড় কোনো চাঞ্চল্যকর খবরের অভাবে এক প্রকার মাছির মতো ভনভন করছিল, তারা যেন হাতে একখনি সোনার খনি পেয়ে গেল। তারা এই সামান্য ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমনভাবে পরিবেশন করল, যা ব্রিটিশ সমাজকে একেবারে নাড়িয়ে দিল এবং এক জাতীয় আতঙ্কের জন্ম দিল।
পরদিন সকালে ব্রিটেনের প্রথম সারির পত্রিকাগুলোর শিরোনাম ছিল দেখার মতো, যেন ক্ল্যাকটনে কোনো যুদ্ধ ঘটে গেছে:
- Daily Telegraph: “Day of Terror by Scooter Gangs” (স্কুটার গ্যাংদের দ্বারা সন্ত্রাসের দিন)
- Daily Express: “Youngsters Beat Up Town – 97 Arrests” (তরুণরা শহরকে পেটাল – ৯৭ জন গ্রেফতার)
- Daily Mirror: “Wild Ones Invade Seaside” (বন্যরা সমুদ্রতট দখল করেছে)
খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ছিল সংঘর্ষের অতিরঞ্জিত এবং প্রায়শই কাল্পনিক বর্ণনা। মিডিয়া ভাষার ব্যবহারে কোনো কার্পণ্য করেনি। তারা এমন সব শব্দ ব্যবহার করছিল, যা সাধারণত যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বন্যপ্রাণীর আক্রমণের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয় – ‘দাঙ্গা’ (riot), ‘অরাজকতা’ (anarchy), ‘বর্বরতা’ (barbarism), ‘যুদ্ধক্ষেত্র’ (battleground), ‘হামলা’ (invasion), ‘অবরোধ’ (siege)। ভাষাতাত্ত্বিক রজার ফাউলার (Roger Fowler) দেখিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের ভাষা কখনোই নিরপেক্ষ নয়; এটি নির্দিষ্ট শব্দচয়নের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ভাবাদর্শকে পাঠকের মনে প্রবেশ করিয়ে দেয় (Fowler, 1991)।
তারা লিখল, শত শত উন্মত্ত তরুণ একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিরীহ পর্যটকদের ওপর হামলা করেছে, শহরজুড়ে ভাঙচুর আর লুটতরাজ চালিয়েছে এবং পুরো শহরকে তাদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। কোহেন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষদর্শীদের বেছে বেছে এমন প্রশ্ন করছিল যা দিয়ে তারা আগে থেকে ঠিক করে রাখা গল্পের উপকরণ খুঁজে পাবে। একজন দোকানদার হয়তো বলেছিলেন, “কয়েকজন ছেলে বেশ ঝামেলা করছিল,” কিন্তু পত্রিকায় ছাপা হলো, “শহরবাসী আতঙ্কে কাঁপছে।” মিডিয়ার বর্ণনায় এই তরুণরা আর বেকার, পথভ্রষ্ট বা নিছকই উচ্ছৃঙ্খল তরুণ ছিল না; তারা হয়ে উঠেছিল সমাজের শৃঙ্খলা, সভ্যতা এবং ব্রিটিশ মূল্যবোধের জন্য এক বিরাট, সংগঠিত হুমকি।
এই মিডিয়া কাভারেজই ছিল ‘মোরাল প্যানিক’ নামক সামাজিক প্রপঞ্চটির আদর্শ উদাহরণ। এটি কেবল একটি ঘটনার রিপোর্ট ছিল না, এটি ছিল একটি ঘটনার ‘নির্মাণ’। মিডিয়া এখানে নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষক ছিল না, ছিল নাটকের প্রধান পরিচালক। তারা কয়েকটি ভাঙা চেয়ার আর কিছু তরুণের হাতাহাতির মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা পরিবর্তনজনিত ভয় এবং প্রজন্মগত সংঘাতের এক বিশাল আখ্যান রচনা করেছিল, যা গোটা দেশকে এক সম্মিলিত আতঙ্কের সুনামিতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।
আতঙ্কের ব্যবচ্ছেদ – মোরাল প্যানিকের ধাপসমূহ এবং এর ভেতরের কারসাজি
ক্ল্যাকটনের সমুদ্রতীরে যা ঘটেছিল তা ছিল কয়েকটি ঢেউয়ের মিলিত আস্ফালন। কিন্তু মিডিয়া এবং সমাজ তাকে এক প্রলয়ঙ্করী সুনামিতে পরিণত করেছিল। স্ট্যানলি কোহেন এই সুনামি তৈরির প্রক্রিয়াটিকে একজন সার্জনের নিপুণতায় ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই ধরনের সামাজিক আতঙ্ক কোনো আকস্মিক বা বিশৃঙ্খল ঘটনা নয়। এর পেছনে একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা নকশা কাজ করে, যা বারবার পুনরাবৃত্ত হয়। এই নকশাটিকেই তিনি বলেছেন ‘মোরাল প্যানিক’।
মোরাল প্যানিক (Moral Panic) হলো একটি তীব্র এবং প্রায়শই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত সামাজিক প্রতিক্রিয়া, যখন কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পরিস্থিতিকে সমাজের প্রচলিত নৈতিক মূল্যবোধ এবং স্বার্থের প্রতি এক বিরাট হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রতিক্রিয়াটি সাধারণত ঘটনার প্রকৃত ভয়াবহতার তুলনায় অনেক বেশি অতিরঞ্জিত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় (Cohen, 1972)। মিডিয়া এই প্রক্রিয়াতে অনুঘটকের (catalyst) কাজ করে এবং এর ফলে জনমনে যে আতঙ্ক তৈরি হয়, তা কর্তৃপক্ষকে কঠোর এবং অনেক সময় দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে।
এই প্রক্রিয়াটিকে কয়েকটি সুস্পষ্ট পর্যায় বা ধাপে ভাগ করা যায়, যা একটি চক্রের মতো কাজ করে। আসুন, মডস এবং রকার্সের ঘটনাটিকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে ধাপগুলো বিস্তারিতভাবে এবং এর ভেতরের মনস্তত্ত্ব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।
ধাপ ১: শনাক্তকরণ এবং সংজ্ঞা প্রদান (Identification and Definition)
যেকোনো মোরাল প্যানিকের শুরু হয় কোনো একটি বিষয় বা গোষ্ঠীকে ‘সমস্যা’ হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে। ক্ল্যাকটনের ঘটনার আগে মডস এবং রকার্সরা তরুণ সংস্কৃতির দুটি বিচ্ছিন্ন ধারা ছিল মাত্র। তারা ছিল সমাজের মূলধারার বাইরে থাকা দুটি উপ-সংস্কৃতি (subculture)। কিন্তু ক্ল্যাকটনের ঘটনার পর মিডিয়া তাদের গায়ে ‘সামাজিক সমস্যা’ (social problem), ‘ঝামেলা সৃষ্টিকারী’ (troublemaker), ‘গুন্ডা’ (hooligan) এবং ‘জনগণের শত্রু’ (enemy of the public) তকমা সেঁটে দিল।
এই সংজ্ঞা প্রদানের প্রক্রিয়াটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কোনো কিছুকে ‘সমস্যা’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার পরেই তার বিরুদ্ধে ‘ব্যবস্থা’ নেওয়ার প্রশ্ন আসে। মিডিয়া এই তরুণদের আর কারো সন্তান, ভাই বা কারখানার তরুণ শ্রমিক হিসেবে দেখায়নি। তারা তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের একটিমাত্র পরিচয়ে পরিচিত করিয়েছে – বিপদজনক ‘জনতা’। তাদের জীবনযাত্রা, তাদের সঙ্গীত, তাদের ফ্যাশন – সবকিছুকেই তাদের অপরাধপ্রবণতার লক্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হলো। সমাজের চোখে তারা হয়ে উঠল এক বেনামী, ভয়ঙ্কর এবং অযৌক্তিক শক্তি, যাকে দমন করা অপরিহার্য।
ধাপ ২: মিডিয়ার সরলীকরণ, প্রতীকরূপ প্রদান এবং অতিরঞ্জন (Simplification, Symbolization, and Exaggeration by the Media)
এই ধাপে মিডিয়া মূল এবং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করে। তারা এই গোষ্ঠীগুলোর জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগত পরিচয়কে মুছে দিয়ে তাদের কয়েকটি সহজ প্রতীকের (symbols) মাধ্যমে উপস্থাপন করে। জটিল পৃথিবীকে সহজ করে দেখানোর এই প্রবণতা মিডিয়ার মজ্জাগত।
- সরলীকরণ (Simplification): মিডিয়া মডস এবং রকার্সদের দুটি একাট্টা, সমজাতীয় (homogeneous) গোষ্ঠী হিসেবে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ ভিন্নতা ছিল, তাদের যে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা বা হতাশা ছিল, তাদের যে কর্মজীবী শ্রেণির সন্তান হিসেবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগ্রাম ছিল – এই সবকিছুকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হলো। তাদের সবাইকে একই ‘উন্মত্ত তরুণ’-এর ছাঁচে ফেলে দেওয়া হলো। এই সরলীকরণ দর্শক বা পাঠকের জন্য ঘটনাটি বোঝা সহজ করে দেয়, কিন্তু তা সত্যের এক বিরাট অপলাপ।
- প্রতীকরূপ প্রদান (Symbolization): তাদের পোশাক এবং বাহনকে তাদের বিচ্যুতির প্রতীকে পরিণত করা হলো। একটি ভেসপা স্কুটার বা একটি চামড়ার জ্যাকেট দেখলেই মানুষের মনে ‘বিপদ’-এর সঙ্কেত বেজে উঠত। এই প্রতীকগুলো খুব শক্তিশালী হয় কারণ এগুলো মানুষের মনে দ্রুত গেঁথে যায় এবং কোনো গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। ‘মড’ মানেই স্যুট পরা স্কুটার-আরোহী গুন্ডা, আর ‘রকার’ মানেই চামড়ার জ্যাকেট পরা হিংস্র বাইকার – এই সরল এবং বিপজ্জনক সমীকরণটি তৈরি করে দিল মিডিয়া। এই প্রতীকগুলো এক ধরনের শর্টকাটের মতো কাজ করে, যা দিয়ে একটি পুরো গোষ্ঠীকে এক মুহূর্তে বিচার করে ফেলা যায়।
- অতিরঞ্জন (Exaggeration): সাংবাদিকরা কীভাবে ছোটখাটো ঘটনাকে বড় করে দেখিয়েছে, সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দশগুণ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলেছে, এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ থেকে নিজেদের পছন্দমতো মন্তব্য বের করে এনেছে, তা কোহেনের গবেষণায় উঠে এসেছে। তারা ‘if it bleeds, it leads’ (রক্ত ঝরলে তা-ই শিরোনাম হয়) নীতি অনুসরণ করে ঘটনার সবচেয়ে নাটকীয় এবং হিংস্র দিকগুলোকে সামনে এনেছে, যদিও সেগুলো ছিল ব্যতিক্রম।
- ভাষার ব্যবহার (Use of Language): ‘সংঘর্ষ’ (scuffle) হয়ে গেল ‘দাঙ্গা’ (riot)। ‘কয়েকজন তরুণ’ হয়ে গেল ‘একদল উন্মত্ত জনতা’ (a horde of savages)। ‘কিছু ভাঙা চেয়ার’ হয়ে গেল ‘ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ’। এই ধরনের আবেগপূর্ণ এবং নিন্দাসূচক ভাষা (emotive and condemnatory language) ব্যবহার করে জনমনে ভয় এবং ঘৃণা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। ভাষা এখানে কেবল ঘটনার বিবরণ দেয় না, ভাষা নিজেই ঘটনাকে তৈরি করে।
ধাপ ৩: উদ্বেগের বিস্তার এবং নৈতিক উদ্যোক্তাদের আবির্ভাব (Stirring up Concern and the Rise of Moral Entrepreneurs)
মিডিয়ার ক্রমাগত প্রচারণার ফলে জনমনে এক ধরনের উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন, সাধারণ নাগরিকরা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হন। আর এই সুযোগেই মঞ্চে প্রবেশ করেন ‘মোরাল এন্টারপ্রেনার’ (moral entrepreneurs) বা নৈতিক উদ্যোক্তারা। হাওয়ার্ড বেকারের (Becker, 1963) কাছ থেকে নেওয়া এই ধারণাটি দিয়ে বোঝানো হয় সেইসব প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে, যারা নিজেদের নৈতিক অবস্থান থেকে কোনো একটি বিষয়কে ‘অনৈতিক’ বা ‘বিপজ্জনক’ বলে প্রচার করেন এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জনমত তৈরি করেন।
- রাজনীতিবিদ (Politicians): পার্লামেন্টে এমপি-রা এই ‘তরুণ প্রজন্মের অবক্ষয়’ এবং ‘গুন্ডামি’ নিয়ে সোচ্চার হলেন। তারা আরও কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি জানালেন, যাতে এই ‘অশুভ শক্তিকে’ অঙ্কুরেই বিনাশ করা যায়। এটি তাদের জন্য নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর এবং সমাজের ‘রক্ষাকর্তা’ হিসেবে জাহির করার একটি সহজ উপায় ছিল। তারা ‘আইন ও শৃঙ্খলা’ (law and order) ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করেন।
- পুলিশ (Police): পুলিশের ওপর চাপ বাড়ল। মিডিয়ার প্রচারণার ফলে তাদের মনে হতে লাগল যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে, তারা মডস এবং রকার্সদের দেখলেই থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। তাদের আড্ডার জায়গাগুলোতে নিয়মিত টহল দেওয়া শুরু হলো। এই পুলিশি হয়রানি (police harassment) তরুণদের আরও বেশি কর্তৃপক্ষ-বিরোধী করে তুলল।
- বিশেষজ্ঞ (Experts): মিডিয়া সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, ধর্মযাজক – সবাইকে ডেকে এনে তাদের মতামত নিতে লাগল। এই ‘বিশেষজ্ঞরা’ প্রায়শই সমস্যাটিকে আরও বড় করে দেখালেন এবং এর জন্য আধুনিক সমাজ, ভাঙা পরিবার, ভোগবাদ, পপ সঙ্গীত বা আমেরিকান সংস্কৃতির আগ্রাসনকে দায়ী করলেন। তারা ঘটনাকে একটি বৃহত্তর নৈতিক অবক্ষয়ের লক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। ফলে, সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করল যে সমস্যাটি আসলেই খুব গভীর এবং ভয়ঙ্কর।
ধাপ ৪: কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া এবং দমন-পীড়ন (Response from Authorities and Crackdown)
জনমতের চাপে এবং নৈতিক উদ্যোক্তাদের প্ররোচনায় কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। এই প্রতিক্রিয়াটি প্রায়শই হয় আতঙ্কগ্রস্ত এবং দমনমূলক, যার লক্ষ্য থাকে সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধান না করে কেবল উপসর্গকে দমন করা।
- বিচারব্যবস্থা (Judiciary): বিচারকরা এই তরুণদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিলেন। ক্ল্যাকটনের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া তরুণদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হলো, যা তাদের অপরাধের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এক বিচারক তো রায় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “এই ধরনের গুন্ডামি এই দেশে সহ্য করা হবে না… আমরা এই শহরকে আপনাদের মতো উশৃঙ্খলদের হাতে তুলে দিতে পারি না।” (Cohen, 1972)। এই কঠোর শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বাকিদের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠানো যে, এই ধরনের আচরণ বরদাস্ত করা হবে না।
- নতুন আইন (New Legislation): অনেক সময় এই ধরনের প্যানিকের ফলে নতুন, আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়, যা পুলিশের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার খর্ব করে। যেমন, পরবর্তীতে ‘মাগিং’ প্যানিকের সময় পুলিশকে রাস্তায় যেকোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে থামিয়ে তল্লাশি করার (stop and search) বর্ধিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।
ধাপ ৫: ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং বিচ্যুতি বিবর্ধন সর্পিল (The Deviancy Amplification Spiral)
এটাই মোরাল প্যানিকের সবচেয়ে পরিহাসমূলক (ironic) এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। সমাজ যে সমস্যাটিকে দমন করতে চেয়েছিল, তাদের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে সেই সমস্যাটি কমার বদলে আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে লেসলি উইলকিন্স (Leslie Wilkins, 1964) প্রথম বর্ণনা করেন এবং পরে কোহেন এর বিশদ ব্যাখ্যা দেন। এর নাম ‘ডেভিয়েন্সি এমপ্লিফিকেশন স্পাইরাল’ (Deviancy Amplification Spiral) বা ‘বিচ্যুতি বিবর্ধন সর্পিল’।
ব্যাপারটা অনেকটা দুষ্টচক্রের (vicious cycle) মতো কাজ করে:
- একটি বিচ্যুত কাজ (deviant act) ঘটে (মডস-রকার্সদের মারামারি)।
- মিডিয়া সেটিকে অতিরঞ্জিত করে রিপোর্ট করে এবং গোষ্ঠী দুটিকে ‘ফোক ডেভিল’ হিসেবে চিহ্নিত করে।
- জনমনে উদ্বেগ তৈরি হয় এবং তারা কর্তৃপক্ষের ওপর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।
- কর্তৃপক্ষ (বিশেষ করে পুলিশ) সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ (surveillance and control) বাড়িয়ে দেয়।
- এই অতিরিক্ত মনোযোগ এবং হয়রানির ফলে সেই গোষ্ঠীটি আরও বেশি বিচ্ছিন্ন (alienated) এবং কর্তৃপক্ষ-বিরোধী (anti-authority) হয়ে ওঠে। তারা সমাজের চোখে এমনিতেও ‘খারাপ’, তাই তারা সেই ‘খারাপ’ পরিচয়কেই আরও জোরালোভাবে আঁকড়ে ধরে। আগে যারা নিজেদের বিচ্ছিন্নভাবে ‘মড’ বা ‘রকার’ ভাবত, তারা এবার সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে, নিজেদের মধ্যে একাত্মতা খুঁজে পায়।
- এর ফলে তাদের মধ্যে আরও বিচ্যুত আচরণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পরবর্তী কোনো ছুটির দিনে তারা যখন আবার কোথাও মিলিত হয়, তখন মিডিয়া এবং পুলিশ আগে থেকেই সেখানে প্রস্তুত থাকে। ছোটখাটো ঘটনাও বড় আকারে রিপোর্ট করা হয়। তরুণরাও জানে যে তাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে, যা তাদের আরও বিদ্রোহী করে তোলে।
- এই রিপোর্টের ফলে জনমনে উদ্বেগ আরও বাড়ে, কর্তৃপক্ষ আরও কঠোর হয়, এবং গোষ্ঠীটি আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে… এবং এই চক্র চলতেই থাকে, ঠিক যেন একটি সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে সমস্যাটি ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে থাকে।
ক্ল্যাকটনের পর মে মাসের ছুটির দিনে ব্রাইটন (Brighton), হেস্টিংস (Hastings) এবং অন্যান্য সমুদ্রতীরবর্তী শহরগুলোতে মডস এবং রকার্সদের মধ্যে আরও বড় এবং হিংস্র সংঘর্ষ হয়। মিডিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীই যেন বাস্তবে ফলে গেল (self-fulfilling prophecy)। কিন্তু কোহেন দেখালেন, এই পরের সংঘর্ষগুলো মিডিয়ার তৈরি করা আতঙ্কেরই সরাসরি ফল ছিল। মিডিয়া এবং কর্তৃপক্ষ সমস্যাটিকে সমাধান করার বদলে তাকে আরও বড় এবং ভয়ঙ্কর এক দানবে পরিণত করেছিল।
লোক-দানবের জন্ম, তার সামাজিক প্রয়োজন এবং তার নিঃসঙ্গতা
মোরাল প্যানিকের ঝোড়ো হাওয়ার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে, তার সমস্ত নাটকীয়তার মধ্যমণিতে অবস্থান করে একটি বিশেষ চরিত্র – একই সাথে ভয়ঙ্কর এবং করুণ। স্ট্যানলি কোহেন যার নাম দিয়েছিলেন ‘ফোক ডেভিল’ (Folk Devil) বা লোক-দানব। ফোক ডেভিল ছাড়া মোরাল প্যানিক অসম্পূর্ণ; সে-ই হলো সেই অভিনেতা, যাকে ঘিরে পুরো নাটকটি আবর্তিত হয়। সে হলো সেই আয়না, যাতে সমাজ তার নিজের কুৎসিত ভয়গুলোকে দেখে আঁতকে ওঠে। প্রাচীন পুরাণে যেমন অসুর, দৈত্য বা ড্রাগনরা ছিল মানুষের অমূর্ত ভয়ের মূর্ত রূপ, আধুনিক সমাজে ফোক ডেভিলরাও ঠিক একই ভূমিকা পালন করে, তবে তাদের জন্ম কোনো পৌরাণিক কল্পনায় নয়, বরং খবরের কাগজের শিরোনামে এবং টেলিভিশনের পর্দায়।
‘ফোক ডেভিল’ কারা?
সহজ কথায়, এরা হলো সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, যাদেরকে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের যাবতীয় উদ্বেগ, ভয় এবং সমস্যার মূর্ত প্রতীক হিসেবে দাঁড় করানো হয়। তারা হয়ে ওঠে সমাজের চোখে ‘শত্রু’, ‘অন্য’ (the other) বা ‘বাইরের লোক’ (outsider)। তাদের দেখলেই মনে হয়, এরাই সব নষ্টের গোড়া, এরাই আমাদের শান্ত, সুন্দর, পরিচিত জীবনটাকে ধ্বংস করে দিতে এসেছে। তারা হলো সেই কালো ছায়া, যার ওপর সমাজের সমস্ত নেতিবাচকতা আরোপ করা হয়। মডস এবং রকার্সরা ছিল ষাটের দশকের ইংল্যান্ডের প্রথম বড় মাপের ফোক ডেভিল। তাদের আগে ছিল ‘টেডি বয়েজ’ (Teddy Boys), তাদের পরে এসেছে ‘স্কিনহেডস’ (Skinheads), ‘পাঙ্কস’ (Punks), অভিবাসী, শরণার্থী, মাদক ব্যবহারকারী, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের অনুসারী এবং আরও অনেকে। প্রতিটি যুগই যেন তার নিজস্ব দানব খুঁজে নেয়।
সাধারণত সেইসব গোষ্ঠীকেই ফোক ডেভিল বানানো সহজ হয়, যারা তুলনামূলকভাবে ক্ষমতাহীন, যাদের কথা বলার মতো কোনো শক্তিশালী মঞ্চ নেই, এবং যাদের জীবনযাত্রা সমাজের মূলধারার থেকে কিছুটা ভিন্ন এবং দৃশ্যমান। তাদের ভিন্নতাই তাদের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। ফোক ডেভিল তৈরির প্রক্রিয়াটা বেশ আকর্ষণীয় এবং এর পেছনে গভীর সামাজিক মনস্তত্ত্ব কাজ করে। এটি নিছকই ভুল বোঝাবুঝি নয়, বরং এর একটি শক্তিশালী সামাজিক কার্যকারিতা (social function) আছে।
দানব নির্মাণের কারখানা: দানবীয়করণ এবং বিমানবিকীকরণ (Demonization and Dehumanization)
ফোক ডেভিলদের আর সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখা হয় না। মিডিয়া এবং নৈতিক উদ্যোক্তারা তাদের এমনভাবে চিত্রিত করে, যেন তারা স্বাভাবিক মানবিক গুণাবলি – যেমন, ভালোবাসা, ভয়, স্বপ্ন, হতাশা – বিবর্জিত কোনো দানবীয় শক্তি। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় দানবীয়করণ বা ডিমনাইজেশন। এই কারখানায় কয়েকটি ধাপে দানব তৈরি হয়:
- একমাত্রিক চরিত্র নির্মাণ: তাদের জটিল, বহুমাত্রিক পরিচয়কে মুছে দিয়ে তাদের একটিমাত্র পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়। একটি শক্তিশালী স্টেরিওটাইপ (stereotype) তৈরি করা হয়। একজন ‘মড’ মানেই সে কেবলই একজন ‘মড’ – তার আর কোনো পরিচয় নেই। সে কারো সন্তান, কারো বন্ধু, কোনো কারখানার কর্মী, বা কোনো ফুটবল দলের সমর্থক – এইসব মানবীয় পরিচয়কে আড়াল করে দেওয়া হয়। মিডিয়া বারবার তাদের একই ধরনের ছবি (যেমন, পুলিশের সাথে সংঘর্ষের ছবি) ব্যবহার করে এই একমাত্রিক পরিচয়কে মানুষের মনে গেঁথে দেয়। সে হয়ে ওঠে তার উপ-সংস্কৃতির (subculture) একটি চলন্ত প্রতীক।
- অযৌক্তিকীকরণ (Irrationalization): তাদের আচরণকে অযৌক্তিক, উদ্দেশ্যহীন এবং নিছকই ধ্বংসাত্মক হিসেবে দেখানো হয়। তাদের বিদ্রোহের পেছনে যে কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে (যেমন, বেকারত্ব, শ্রেণিবৈষম্য বা মূলধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ), তা পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়। তাদের এমন এক শক্তি হিসেবে দেখানো হয়, যারা কোনো কারণ ছাড়াই, নিছকই ‘শয়তানি’ বা মন্দ প্রবৃত্তির বশে সমাজের ক্ষতি করে। এই অযৌক্তিকীকরণের ফলে তাদের সাথে কোনো ধরনের আলোচনা বা সহানুভূতির অবকাশ থাকে না। কারণ, যার কাজের কোনো যুক্তিই নেই, তার সাথে কথা বলে কী হবে?
- বিমানবিকীকরণ (Dehumanization): সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ধাপটি হলো বিমানবিকীকরণ বা অন্যকরণ (othering)। তাদের এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন তারা পশুর পালের মতো আচরণ করছে বা তারা কোনো সংক্রামক ব্যাধির মতো বিপজ্জনক। মিডিয়ার বর্ণনায় প্রায়শই ‘প্যাক’ (pack), ‘হোর্ড’ (horde), ‘স্যাভেজ’ (savage), ‘পোকামাকড়’ (vermin) বা ‘অ্যানিম্যাল’ (animal) এর মতো শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই বিমানবিকীকরণের ফলে তাদের ওপর যেকোনো ধরনের দমন-পীড়নকে (যেমন, পুলিশের লাঠিচার্জ বা কঠোর জেল) সমাজের চোখে বৈধতা দেওয়া সহজ হয়ে যায়। কারণ, দানব বা পশুর সাথে তো আর মানুষের মতো আচরণ করার প্রয়োজন নেই। তাদের মানবিক অধিকারের প্রশ্নটিও তখন গৌণ হয়ে যায়।
সমাজের আয়না এবং বলির পাঁঠা (Mirror and Scapegoat)
প্রশ্ন হলো, সমাজের কেন এই ফোক ডেভিলের প্রয়োজন হয়? তারা কি কেবলই মিডিয়ার তৈরি করা খলনায়ক? নাকি তাদের অস্তিত্ব সমাজের গভীরতর কোনো প্রয়োজন মেটায়? উত্তরটি বেশ জটিল।
- উদ্বেগের মূর্ত প্রতীক: ফোক ডেভিলরা আসলে সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা অমূর্ত ভয় এবং উদ্বেগের একটি মূর্ত প্রতীক বা ‘লাইটেনিং রড’ হিসেবে কাজ করে। ষাটের দশকে ব্রিটিশ সমাজ এক বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। পুরনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে, চিরাচরিত শ্রেণিবিন্যাস (class structure) দুর্বল হচ্ছে, যৌনতা নিয়ে নতুন ধারণা আসছে, নারীরা ঘরের বাইরে আসছে, আর নতুন প্রজন্ম পুরনো মূল্যবোধকে প্রশ্ন করছে। এই দ্রুত পরিবর্তন প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ (anxiety) এবং অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিল। ফোক ডেভিলরা এই অমূর্ত ভয়গুলোকে একটি মূর্ত, দৃশ্যমান এবং সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। মডস এবং রকার্সদের দানব হিসেবে চিত্রিত করার মাধ্যমে প্রবীণ প্রজন্ম আসলে নিজেদের হারানো কর্তৃত্ব এবং পরিবর্তনজনিত ভয়কেই প্রকাশ করছিল (Goode & Ben-Yehuda, 1994)। একইভাবে, অর্থনৈতিক মন্দার সময় অভিবাসীদের ‘ফোক ডেভিল’ বানিয়ে চাকরির নিরাপত্তাহীনতার মতো গভীর উদ্বেগ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।
- নৈতিক সীমানা পুনঃনির্ধারণ (Boundary Maintenance): ফোক ডেভিলদের চিহ্নিত এবং শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে সমাজ তার নৈতিক সীমানাগুলোকে (moral boundaries) নতুন করে এঁকে নেয় এবং নিজেদের মধ্যে সংহতি বাড়ায়। সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খাইম (Émile Durkheim) দেখিয়েছেন যে, অপরাধ বা বিচ্যুতি সমাজের জন্য সবসময় খারাপ নয়। এটি সমাজের সদস্যদের একত্রিত করে এবং কোনটা ঠিক ও কোনটা ভুল, সেই বিষয়ে তাদের সম্মিলিত চেতনাকে (collective consciousness) শক্তিশালী করে (Durkheim, 1895/1982)। ফোক ডেভিলদের নিন্দা করার মাধ্যমে সমাজ সমস্বরে ঘোষণা করে, “আমরা ওদের মতো নই, আমরা ভালো। আমাদের মূল্যবোধই সঠিক।” এই প্রক্রিয়া সমাজের ‘ভালো’ মানুষদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য তৈরি করে। সমাজবিজ্ঞানী কাই টি. এরিকসন (Kai T. Erikson) তাঁর বিখ্যাত বই ‘ওয়েওয়ার্ড পিউরিটানস’ (Wayward Puritans)-এ দেখিয়েছেন, কীভাবে পিউরিটান সমাজ ডাইনি এবং ধর্মদ্রোহীদের ‘দানব’ হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদের নৈতিক সীমানা এবং পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করেছিল (Erikson, 1966)।
- বলির পাঁঠা (Scapegoat): ফোক ডেভিলরা অনেকটা বলির পাঁঠার মতো কাজ করে, যাদের ওপর সমাজের সব পাপ ও ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে দেওয়া যায়। সমাজের আসল এবং জটিল সমস্যাগুলো – যেমন, বেকারত্ব, শ্রেণিবৈষম্য, শিক্ষার অভাব বা পারিবারিক ভাঙন – এগুলোর দিকে নজর না দিয়ে, সব দোষ এই তরুণদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া অনেক সহজ। এটি এক ধরনের মনোযোগ সরানোর কৌশল (diversionary tactic)। এতে সমাজের আসল রোগ নির্ণয় না করে কেবল উপসর্গের চিকিৎসা করা হয় এবং কর্তৃপক্ষকেও (যেমন, সরকার বা পুলিশ) কোনো কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। মডস ও রকার্সদের ‘গুন্ডা’ বলে চিহ্নিত করে ব্রিটিশ সমাজ খুব সহজেই এই প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছিল যে, কেন কর্মজীবী শ্রেণির এই তরুণদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বা বিনোদনের ব্যবস্থা নেই।
দানবের নিঃসঙ্গতা: একটি করুণ বাস্তবতা
এবার চলুন, সমাজবিজ্ঞানীর চেয়ার থেকে উঠে এসে একবার সেই ‘দানব’-দের চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখার চেষ্টা করি। মিডিয়ার তৈরি করা এই দানবীয় চিত্রের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক করুণ বাস্তবতা। মডস এবং রকার্সরা দানব ছিল না। কোহেন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, তারা ছিল মূলত কর্মজীবী শ্রেণির (working-class) তরুণ। তাদের অধিকাংশেরই পড়াশোনা স্কুল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল একঘেয়ে, নিম্ন বেতনের কারখানার নিষ্প্রাণ জীবন। ষাটের দশকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চাকচিক্য তারা দেখত, কিন্তু তার স্বাদ নেওয়ার সুযোগ তাদের ছিল না। তাদের জীবনে উত্তেজনা বা সৃজনশীলতার কোনো পরিসর ছিল না।
তাদের এই জমকালো পোশাক, দ্রুতগতির বাহন এবং সপ্তাহান্তের উন্মাদনা ছিল আসলে সেই ধূসর, অর্থহীন জীবনের বিরুদ্ধে এক ধরনের শৈলীগত বিদ্রোহ (stylistic rebellion)। সমাজতাত্ত্বিক ডিক হেবডিজ (Dick Hebdige) দেখিয়েছেন, এই উপ-সংস্কৃতিগুলো তাদের স্টাইলের মাধ্যমে – পোশাক, সঙ্গীত, ভাষা – প্রতীকীভাবে সমাজের মূলধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে (Hebdige, 1979)। তারা সাধারণ জিনিসপত্র (যেমন, স্কুটারের আয়না বা মোটরসাইকেলের জ্যাকেট) ব্যবহার করে নিজেদের জন্য এক নতুন অর্থপূর্ণ জগৎ তৈরি করত, যাকে বলা যায় ‘ব্রিকোলাজ’ (bricolage)। তারা তাদের স্টাইলের মাধ্যমে বলতে চাইছিল, “আমরা কেবল কারখানার শ্রমিক নই, আমরা কেবল সংখ্যামাত্র নই, আমাদেরও একটি পরিচয় আছে, একটি স্বপ্ন আছে।” তাদের এই বিদ্রোহ হয়তো খুব গোছানো বা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল না, কিন্তু তা ছিল এক ধরনের অস্তিত্বের জানান দেওয়া, নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করার এক মরিয়া চেষ্টা।
কিন্তু সমাজ তাদের এই জটিলতাকে বুঝতে চায়নি, বা বুঝতে পারলেও স্বীকার করতে চায়নি। তাদের ‘দানব’ বানিয়ে দেওয়াটাই ছিল সমাজের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং সহজ সমাধান। আর এই প্রক্রিয়ায়, কিছু বিভ্রান্ত, পথ হারানো, এবং মূলত নিরীহ তরুণ হয়ে গেল ইতিহাসের পাতায় খলনায়ক। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, সমাজের এই তীব্র প্রতিক্রিয়া এক ধরনের আত্ম-বাস্তবায়িত ভবিষ্যদ্বাণীতে (self-fulfilling prophecy) পরিণত হয়। যে তরুণদের বারবার ‘দানব’ বলা হয়, পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হয়, সমাজের চোখে ঘৃণার পাত্র হতে হয়, তারা একসময় সেই দানবের ভূমিকাটিকেই গ্রহণ করে নেয়। তারা ভাবতে শুরু করে, “সমাজ যখন আমাদের খারাপই ভাবে, তখন খারাপ হয়েই দেখাই।” এভাবেই সমাজের ভয়ই তার নিজের দানবকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে। আর এই দানবের মুখোশের আড়ালে চাপা পড়ে যায় কিছু নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ হওয়া মানুষের মুখ।
আতঙ্কের জাদুঘর – ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু মোরাল প্যানিক
‘মোরাল প্যানিক’ তত্ত্বটি কেবল মডস এবং রকার্সদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি একটি সর্বজনীন মডেলে পরিণত হয়েছে, যা দিয়ে আমরা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের গণ-উন্মাদনাকে বিশ্লেষণ করতে পারি। কোহেনের তত্ত্বটি আমাদের হাতে এমন এক আশ্চর্য চশমা তুলে দেয়, যা দিয়ে আমরা ইতিহাসের ধুলোমাখা অধ্যায়গুলোতেও পরিচিত নকশা খুঁজে পাই। চলুন, ইতিহাসের সেই আতঙ্কের জাদুঘরের কয়েকটি গ্যালারিতে প্রবেশ করা যাক। প্রতিটি গ্যালারিতে আমরা দেখব ভিন্ন ভিন্ন দানব, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের উদ্বেগ, কিন্তু আশ্চর্যভাবে একই রকম একটি চিত্রনাট্য।
ডাইনি শিকার (ইউরোপ, ১৬-১৭ শতক)
এটি হয়তো ইতিহাসের সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং ভয়ঙ্কর মোরাল প্যানিকগুলোর একটি। সেই সময়ে ইউরোপ এক বিরাট সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং তথাকথিত ‘ক্ষুদ্র বরফ যুগ’ (Little Ice Age)-এর কারণে ফসলহানি মানুষের জীবনকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার (Protestant Reformation) ক্যাথলিক চার্চের একচ্ছত্র আধিপত্যকে ভেঙে দিয়েছিল, যা মানুষের মনে গভীর আধ্যাত্মিক নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে। এই ভয় এবং অনিশ্চয়তার কারণ হিসেবে একদল সহজলভ্য ‘শত্রু’কে চিহ্নিত করা হলো – ডাইনি (witches), যারা শয়তানের পূজা করে সমাজের যাবতীয় অমঙ্গল ঘটাচ্ছে।
- ফোক ডেভিল: মূলত একা, বিধবা, ভেষজ চিকিৎসক বা সমাজের চোখে ব্যতিক্রমী নারীদের ‘ডাইনি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তারা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে ক্ষমতাহীন অংশ, যাদের রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না।
- মোরাল এন্টারপ্রেনার: চার্চ (ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয়ই) এবং রাষ্ট্র ছিল প্রধান নৈতিক উদ্যোক্তা। তারা ‘ম্যালিউস ম্যালেফিকারাম’ (Malleus Maleficarum) বা ‘ডাইনিদের হাতুড়ি’-র মতো বই ছাপিয়ে ডাইনি শনাক্তকরণ এবং শাস্তির পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল (Levack, 2015)।
- প্রক্রিয়া: গুজব, প্রতিবেশীর প্রতি হিংসা এবং জিজ্ঞাসাবাদের নামে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা হতো। একজন অভিযুক্ত ‘ডাইনি’কে বাধ্য করা হতো আরও কয়েকজনের নাম বলতে, যা এক ভয়ঙ্কর বিচ্যুতি বিবর্ধন সর্পিল (deviancy amplification spiral) তৈরি করেছিল। এর ফলে হাজার হাজার নিরীহ নারীকে পুড়িয়ে বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল। এই আতঙ্কটি ছিল আসলে এক বিশৃঙ্খল সময়ের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার এক মরিয়া ও পাশবিক প্রচেষ্টা।
কমিকস, কৈশোর এবং অপরাধপ্রবণতার আতঙ্ক (আমেরিকা, ১৯৫০-এর দশক)
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এলেও সমাজের ভেতরে এক ধরনের উদ্বেগ কাজ করছিল। ঠান্ডা যুদ্ধের পারমাণবিক আতঙ্ক, কমিউনিজমের ভয় এবং নতুন আবিষ্কৃত ‘টিনএজার’ সংস্কৃতির উত্থান – এই সবকিছু মিলিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজন্ম উদ্বিগ্ন ছিল যে আমেরিকার নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। ঠিক এই সময়েই তাদের হাতে একটি সহজ শত্রু চলে আসে – রঙিন, সস্তা এবং জনপ্রিয় ক্রাইম ও হরর কমিক বই।
- ফোক ডেভিল: কিশোর অপরাধীরা (Juvenile Delinquents), যাদেরকে এই কমিক বইগুলো বিপথে চালিত করছে বলে মনে করা হতো।
- মোরাল এন্টারপ্রেনার: এই আতঙ্কের প্রধান কারিগর ছিলেন মনোচিকিৎসক ড. ফ্রেডরিক ওয়ের্থাম (Dr. Fredric Wertham)। তাঁর ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত বই ‘সিডাকশন অফ দি ইনোসেন্ট’ (Seduction of the Innocent) ছিল এই নৈতিক ক্রুসেডের বাইবেল। তিনি তাঁর বইতে অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, কমিক বই শিশুদের মনে হিংসা, যৌন বিকৃতি এবং অপরাধপ্রবণতা ঢুকিয়ে দিচ্ছে (Wertham, 1954)।
- প্রক্রিয়া: ওয়ের্থামের ‘বৈজ্ঞানিক’ দাবিগুলো মিডিয়া লুফে নেয়। দেশজুড়ে কমিক বই পোড়ানোর হিড়িক পড়ে যায়। বিষয়টি এত বড় আকার ধারণ করে যে, মার্কিন সেনেট একটি সাব-কমিটি গঠন করে এর তদন্ত শুরু করে। এই টেলিভাইজড শুনানিতে কমিক বইয়ের প্রকাশকদের সমাজের শত্রু হিসেবে চিত্রিত করা হয়।
- ফলাফল: এই তীব্র সামাজিক চাপের মুখে কমিক বই শিল্প নিজেদের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করতে বাধ্য হয় এবং ‘কমিকস কোড অথরিটি’ (Comics Code Authority) গঠন করে, যা কয়েক দশক ধরে মার্কিন কমিক বইয়ের বিষয়বস্তুকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।
‘মাগিং’ আতঙ্ক (ব্রিটেন, ১৯৭০-এর দশক)
স্টুয়ার্ট হল (Stuart Hall) এবং তাঁর সহকর্মীরা তাদের বিখ্যাত বই ‘পলিসিং দ্য ক্রাইসিস’ (Policing the Crisis)-এ দেখিয়েছেন, কীভাবে সত্তরের দশকে ব্রিটেন ‘মাগিং’ (mugging) বা পথ চলতি মানুষের ওপর হামলা করে ছিনতাই নিয়ে এক ধরনের মোরাল প্যানিকের শিকার হয়েছিল।
- ফোক ডেভিল: এই প্যানিকের ফোক ডেভিল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কৃষ্ণাঙ্গ, বিশেষ করে আফ্রো-ক্যারিবীয় তরুণদের। ‘মাগিং’ শব্দটিই ছিল আমেরিকান আমদানি, যা অপরাধটিকে আরও বেশি ভিনদেশী এবং ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল।
- মোরাল এন্টারপ্রেনার: মিডিয়া, রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ এবং পুলিশ – এই ত্রয়ী মিলে এই আতঙ্ক তৈরি করেছিল।
- প্রক্রিয়া: হল যুক্তি দেখান যে, ব্রিটেন তখন অর্থনৈতিক মন্দা, শ্রমিক ধর্মঘট এবং সামাজিক অস্থিরতার এক গভীর সংকটের (crisis of capitalism) মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সরকার এই আসল সমস্যাগুলো থেকে জনগণের মনোযোগ সরাতে ‘মাগিং’-কে একটি বড় ইস্যু বানায় এবং এর সব দায় কৃষ্ণাঙ্গ তরুণদের ওপর চাপিয়ে দেয়। মিডিয়া এমনভাবে খবর প্রচার করতে শুরু করে, যেন রাস্তায় বের হওয়াই অনিরাপদ, যদিও পরিসংখ্যান সবসময় এই ‘অপরাধের ঢেউ’-কে সমর্থন করত না। এর ফলে একটি ‘আইন ও শৃঙ্খলা’ (law and order) ফিরিয়ে আনার শক্তিশালী জনমত তৈরি হয়, যা পুলিশকে আরও বেশি ক্ষমতা (যেমন, ‘stop and search’) দেয় এবং বর্ণবাদী পুলিশি হয়রানিকে সামাজিক বৈধতা দেয় (Hall et al., 1978)।
স্যাটানিক রিচুয়াল অ্যাবিউজ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন, ১৯৮০-৯০ দশক)
এটি ছিল এক অদ্ভুত এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মোরাল প্যানিক, যা আধুনিক গণ-হিস্টিরিয়ার (mass hysteria) এক ভয়ঙ্কর উদাহরণ।
- ফোক ডেভিল: ডে-কেয়ার সেন্টার এবং স্কুলগুলোতে কর্মরত একদল কাল্পনিক শয়তানের পূজারী (Satanists), যারা শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন চালাচ্ছে এবং ভয়ঙ্কর সব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করছে।
- মোরাল এন্টারপ্রেনার: কিছু থেরাপিস্ট যারা ‘recovered memory’ তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন, কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি চাঞ্চল্যকর টেলিভিশন টক শোগুলো (যেমন গেরাল্ডো রিভেরা-র শো) এই আতঙ্ক ছড়াতে প্রধান ভূমিকা পালন করে।
- প্রক্রিয়া: থেরাপিস্টরা শিশুদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় এমনভাবে প্রশ্ন করতেন, যা তাদের মনে মিথ্যা স্মৃতির জন্ম দিত। মিডিয়া এই ভিত্তিহীন গল্পগুলোকে কোনো রকম যাচাই ছাড়াই প্রচার করে জনমনে তীব্র ভয় ঢুকিয়ে দেয়। এর ফলে শত শত নিরীহ শিক্ষক এবং ডে-কেয়ার কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়, অনেকে বিনা দোষে বছরের পর বছর জেল খাটে। পরে এফবিআই-এর তদন্তে দেখা যায়, এই অভিযোগগুলোর প্রায় কোনোটিরই বাস্তব ভিত্তি ছিল না (Victor, 1993)।
এইডস আতঙ্ক (বিশ্বজুড়ে, ১৯৮০-এর দশক)
যখন প্রথম এইডস (AIDS) রোগটি শনাক্ত হয়, তখন এর বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিল। এই জ্ঞানের শূন্যস্থানটি পূরণ করেছিল ভয়, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার।
- ফোক ডেভিল: প্রাথমিকভাবে সমকামী সম্প্রদায়কে এই রোগের জন্য দায়ী করে তাদের ফোক ডেভিল বানানো হয়। পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হয় শিরায় মাদক ব্যবহারকারী, হাইতির অভিবাসী এবং হিমোফিলিয়া রোগীরা।
- মোরাল এন্টারপ্রেনার: কিছু মিডিয়া, ধর্মীয় নেতা এবং রক্ষণশীল রাজনীতিবিদরা এই আতঙ্ককে কাজে লাগান।
- প্রক্রিয়া: মিডিয়া এইডসকে ‘সমকামীদের রোগ’ (gay plague) বা ‘ঈশ্বরের শাস্তি’ হিসেবে চিহ্নিত করে। রোগটি কীভাবে ছড়ায়, তা নিয়ে ভয়ঙ্কর সব ভুল তথ্য ছড়ানো হয়, যেমন – একই শৌচাগার ব্যবহার করলে বা মশার কামড়েও এইডস হতে পারে। এই আতঙ্কটি সমাজের প্রান্তিক একটি গোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা এবং বৈষম্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলে এইডস আক্রান্তদের চাকরি থেকে বের করে দেওয়া, বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা এবং সামাজিকভাবে বয়কট করার মতো ঘটনা ঘটে। এই নৈতিক বিচার রোগটির বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং জনস্বাস্থ্য উদ্যোগকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছিল।
এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা মোরাল প্যানিকের মডেলটির নিখুঁত প্রতিফলন দেখতে পাই: একটি প্রান্তিক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা, মিডিয়ার অতিরঞ্জন, জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি, কর্তৃপক্ষের কঠোর প্রতিক্রিয়া এবং সবশেষে সেই গোষ্ঠীর ওপর আরও বেশি করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়া। এই জাদুঘরের গ্যালারিগুলো আমাদের দেখায়, সময়ের সাথে সাথে দানবের মুখোশ বদলায়, কিন্তু সমাজের ভয়কে ব্যবহার করার খেলাটি একই থেকে যায়।
কোহেনের দ্বিতীয় ইনিংস – অস্বীকারের মনোরাজ্য (States of Denial)
তাত্ত্বিক হিসেবে স্ট্যানলি কোহেন কেবল ‘মোরাল প্যানিক’ তত্ত্বেই থেমে থাকেননি। তাঁর চিন্তার জগৎ ছিল আরও বিস্তৃত এবং গভীর। যদি ‘মোরাল প্যানিক’ হয় সমাজের ছায়া দেখে চিৎকার করে ওঠার গল্প, তবে তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস ছিল সত্যিকারের দানবকে দেখেও চোখ বন্ধ করে থাকার এক অস্বস্তিকর আখ্যান। জীবনের শেষ দিকে তিনি এমন একটি বিষয় নিয়ে কাজ করেন, যা মোরাল প্যানিকের ঠিক বিপরীত, কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত আরও বেশি অস্বস্তিকর। তাঁর এই পর্বের সেরা কাজ হলো ২০০১ সালে প্রকাশিত যুগান্তকারী বই ‘স্টেটস অফ ডিনায়াল: নোয়িং অ্যাবাউট অ্যাট্রোসিটিস অ্যান্ড সাফারিং’ (States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering)।
এই বইতে তিনি এক ভয়ঙ্কর এবং অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলেছেন: আমরা যখন চোখের সামনে বড় ধরনের অন্যায়, অত্যাচার, গণহত্যা (genocide) বা মানবাধিকার লঙ্ঘন (human rights violation) ঘটতে দেখি, তখন কেন আমরা প্রায়শই নীরব থাকি? কেন আমরা জেনেও না জানার ভান করি? এই প্রশ্নটি তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে বসনিয়া ও রুয়ান্ডার গণহত্যার মতো ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল।
মোরাল প্যানিকে সমাজ একটি ছোট বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া (overreaction) দেখায়। আর ডিনায়াল বা অস্বীকারের ক্ষেত্রে সমাজ একটি বিশাল এবং ভয়ঙ্কর বিষয় নিয়ে প্রায় কোনো প্রতিক্রিয়াই (underreaction) দেখায় না। দুটোই আসলে বাস্তবতাকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোহেন আমাদের দেখিয়েছেন, এই দুটি প্রক্রিয়া একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।
কোহেন ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক অস্বীকার (psychological denial), যা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে আলোচিত, তা থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্বীকারের (social and political denial) দিকে মনোনিবেশ করেন। ফ্রয়েডের মতে, অস্বীকার হলো একটি ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা কৌশল, যা আমাদের মনকে বেদনাদায়ক বাস্তবতা থেকে রক্ষা করে। কিন্তু কোহেন দেখিয়েছেন, অস্বীকার কেবল ব্যক্তিগত নয়, এটি হতে পারে সম্মিলিত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং এমনকি রাষ্ট্রীয়। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে একটি পুরো সমাজ বা রাষ্ট্র কোনো একটি ভয়ঙ্কর সত্যকে সম্মিলিতভাবে অস্বীকারের সংস্কৃতি (culture of denial) তৈরি করে। এই অস্বীকারের পেছনে ভয়, উদাসীনতা, সুবিধাবাদ, জাতীয়তাবাদ, ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য এবং তথ্যের ভারে জর্জরিত হওয়ার মতো অনেক জটিল কারণ কাজ করে।
তিনি তিন ধরনের অস্বীকারের কথা বলেছেন, যা সরল থেকে জটিলের দিকে এগিয়ে যায় (Cohen, 2001):
১. আক্ষরিক অস্বীকার (Literal Denial)
এটা হলো অস্বীকারের সবচেয়ে স্থূল এবং সরাসরি রূপ, এক ধরনের মিথ্যার আরোপ করার জন্য বলপ্রয়োগের অস্ত্র (blunt force instrument of untruth)। এখানে কোনো ঘটনাকে সরাসরি ‘ঘটেনি’ বা ‘এটি সত্য নয়’ বলে দাবি করা হয়। সত্যকে স্রেফ মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। যেমন:
- হলোকস্ট অস্বীকারকারীরা (Holocaust deniers) দাবি করে যে নাৎসি জার্মানি কখনো ইহুদিদের ওপর পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা চালায়নি, গ্যাস চেম্বারের অস্তিত্ব ছিল না, এবং এটি নিছকই ইহুদিদের ষড়যন্ত্র।
- কোনো স্বৈরাচারী সরকার তাদের দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের অস্তিত্ব বা গুলাগারের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তারা বলে, “আমাদের দেশে কোনো রাজনৈতিক বন্দী নেই।”
- তুরস্ক সরকার আজও আর্মেনীয় গণহত্যাকে (Armenian Genocide) ‘গণহত্যা’ হিসেবে স্বীকার করে না, বরং এটিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি দুর্ভাগ্যজনক ‘ঘটনা’ বলে চালিয়ে দেয়।
- অনেক সময় কর্পোরেশনগুলো তাদের কারখানার বর্জ্য পদার্থ পরিবেশে মারাত্মক দূষণ ঘটাচ্ছে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যকেই সরাসরি অস্বীকার করে।
এই ধরনের অস্বীকার সাধারণত রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র (state propaganda) বা চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এর জন্য একটি শক্তিশালী ভাবাদর্শগত বা রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন।
২. ব্যাখ্যামূলক অস্বীকার (Interpretive Denial)
এই ক্ষেত্রে ঘটনাটি যে ঘটেছে, তা আক্ষরিকভাবে অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু ঘটনাটিকে ভিন্ন নামে ডেকে, ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বা ইউফেমিজম (euphemism) বা সুভাষণ ব্যবহার করে তার ভয়াবহতাকে লঘু করে দেওয়া হয়। এটি ভাষার এক অরওয়েলীয় নৃত্য (Orwellian dance), যেখানে শব্দের মারপ্যাঁচে সত্যকে বিকৃত করা হয়। এখানে বলা হয়, “হ্যাঁ, কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু আপনারা যা ভাবছেন তা নয়।” যেমন:
- যুদ্ধে বেসামরিক নাগরিক হত্যাকে ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’ (collateral damage) বা অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতি বলে চালানো হয়। এই যান্ত্রিক শব্দটি একটি শিশুর ছিন্নভিন্ন দেহকে একটি পরিসংখ্যানগত ভুলে পরিণত করে।
- বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারকে ‘বর্ধিত জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল’ (enhanced interrogation technique) বলা হয়। ‘অত্যাচার’ শব্দটি যে নৈতিক দায়বদ্ধতা তৈরি করে, এই নতুন শব্দটি তা থেকে মুক্তি দেয়।
- গণহত্যাকে ‘জাতিগত সংঘাত’ (ethnic conflict) বা ‘দাঙ্গা’ (riot) বলে বর্ণনা করা হয়, যেন উভয় পক্ষই সমানভাবে দায়ী এবং এটি কোনো পরিকল্পিত নির্মূল অভিযান নয়।
- বর্ণবাদী নীতিকে ‘পৃথক কিন্তু সমান’ (separate but equal) উন্নয়ন বলে ব্যাখ্যা করা হয়, যা বৈষম্যের নগ্ন রূপটিকে উন্নয়নের মোড়কে ঢেকে দেয়।
- একটি দেশের ওপর সামরিক আগ্রাসনকে ‘বিশেষ সামরিক অভিযান’ (special military operation) বা ‘শান্তি প্রতিষ্ঠার মিশন’ (peacekeeping mission) বলে অভিহিত করা হয়।
এই ধরনের অস্বীকার অনেক বেশি প্রচলিত এবং এটি আমাদের সত্যকে তার আসল রূপে চিনতে বাধা দেয়। এটি আমাদের নৈতিক কম্পাসকে বিভ্রান্ত করে দেয়।
৩. নিহিতার্থ অস্বীকার (Implicatory Denial)
তাঁর মতে, অস্বীকারের এই রূপটিই সবচেয়ে সূক্ষ্ম, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আমাদের আধুনিক জীবনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এখানে আমরা ঘটনা বা তার ব্যাখ্যা, কোনোটিকেই অস্বীকার করি না। আমরা তথ্যগতভাবে জানি এবং স্বীকার করি যে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটছে বা ঘটেছে। কিন্তু সেই ঘটনার সাথে আমাদের যে নৈতিক, রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা (responsibility) আছে, সেটাকে আমরা অস্বীকার করি। আমরা সেই তথ্যের নিহিতার্থ বা ইমপ্লিকেশনকে (implication) এড়িয়ে চলি। আমরা বলি, “হ্যাঁ, আমি জানি এটা ঘটছে, কিন্তু এটা আমার সমস্যা নয়” বা “আমি এ ব্যাপারে কী-ই বা করতে পারি?”
উদাহরণগুলো আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে এবং তারা আমাদের নিজেদের দিকেই আঙুল তোলে:
- জলবায়ু পরিবর্তন: জেনেও না করার ভান: আমরা প্রায় সবাই জানি যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি ভয়ঙ্কর বাস্তবতা। আমরা জানি যে এর ফলে পৃথিবী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। আমরা খবর পড়ি, ডকুমেন্টারি দেখি, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট শেয়ার করি। কিন্তু তারপরও আমরা আমাদের ভোগবাদী জীবনযাত্রায় কোনো বড় পরিবর্তন আনি না। আমরা আগের মতোই প্লাস্টিক ব্যবহার করি, ব্যক্তিগত গাড়ি চালাই, অপ্রয়োজনে বিদ্যুৎ খরচ করি। আমরা নিজেদের বলি, “আমি একা কী-ই বা করতে পারি?” বা “এটা তো সরকার বা বড় বড় কর্পোরেশনের দায়িত্ব।” এই যে জানার পরেও নিষ্ক্রিয় থাকা, ব্যক্তিগত দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া – এটাই হলো নিহিতার্থ অস্বীকারের ক্লাসিক উদাহরণ।
- ভোগবাদ এবং দূরবর্তী দুর্ভোগ: আমাদের আলমারি ও প্লেটের রক্ত: আমরা জানি যে আমাদের সস্তায় কেনা পোশাকটি হয়তো বাংলাদেশের কোনো কারখানায় (যেমন রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর আমরা জেনেছি) কোনো নারী শ্রমিকের অমানবিক শ্রমে তৈরি, অথবা আমাদের কফির বীজটি হয়তো কোনো শিশু শ্রমিকের হাতে তোলা। আমরা এই তথ্যটি জানার পরেও পরবর্তী ছাড়ে গিয়ে আবার একগাদা পোশাক কিনে ফেলি বা সস্তা কফিটাই পান করি। কারণ, এই সত্যের নিহিতার্থ স্বীকার করলে আমাদের নিজেদের ভোগ এবং ফ্যাশন নিয়ে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। আমাদের আরামদায়ক জীবনের পেছনে যে অন্যের ভোগান্তি লুকিয়ে আছে, এই সত্যের মুখোমুখি হতে আমরা ভয় পাই।
- তথ্যের বন্যা এবং সহানুভূতির মৃত্যু: আমরা টিভিতে বা ইন্টারনেটে বিশ্বের অন্য প্রান্তে ঘটা যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা গণহত্যার খবর দেখি। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ বা ইয়েমেনের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ ছবি আমাদের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে। আমরা কিছুক্ষণ বিচলিত হই, হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দুঃখ প্রকাশের পোস্ট শেয়ার করি বা কোনো অনলাইন পিটিশনে সই করি। কিন্তু তারপর আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাই। সেই দূর দেশের দুর্ভোগ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না। আমরা আমাদের দায়িত্বকে একটি লাইক বা শেয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলি। কোহেন দেখিয়েছেন, আধুনিক যুগে তথ্যের অভাব কোনো সমস্যা নয়। আমরা তথ্যের সাগরে ডুবে আছি, কিন্তু সহানুভূতির অভাবে তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছি।
এই নিহিতার্থ অস্বীকারের যুগে আমরা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অসাড়তা (psychic numbing) বা সহানুভূতি ক্লান্তির (compassion fatigue) শিকার হই। আমরা এত বেশি ভয়াবহতার সম্মুখীন হই যে, আমাদের মন একসময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য অনুভূতিগুলোকে ভোঁতা করে দেয়। ‘স্টেটস অফ ডিনায়াল’ আমাদের এক কঠোর এবং অস্বস্তিকর আয়নার সামনে দাঁড় করায়। এটি আমাদের দেখায়, কীভাবে আমরা ভালো, সহানুভূতিশীল, যুক্তিবাদী মানুষ হয়েও সম্মিলিতভাবে অন্যায়ের নীরব দর্শক এবং কখনও কখনও পরোক্ষ অংশীদার হয়ে যাই। এটি শুধু স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য লেখা বই নয়; এটি তথাকথিত মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি নাগরিকের জন্য এক নৈতিক চ্যালেঞ্জ।
কোহেনের রেখে যাওয়া চশমা: তত্ত্বের পথ ধরে যারা হেঁটেছে
বড় কোনো নদীর মৃত্যু হয় না, তাই না? সে সাগরে মিশে গিয়ে এক নতুন, বিশাল রূপ নেয়। বড় কোনো চিন্তারও মৃত্যু নেই। সেই চিন্তা সময়ের স্রোতে মিশে যায়, নতুন নতুন চিন্তার জন্ম দেয়, নতুন নতুন নদীর সৃষ্টি করে। স্ট্যানলি কোহেনের কাজও ছিল ঠিক তেমনই এক বিশাল নদী। তাঁর তত্ত্বগুলো কোনো একাডেমিক লাইব্রেরির ধুলোমাখা শেলফে স্থির হয়ে বসে থাকেনি। বরং তাঁর চিন্তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে সমাজবিজ্ঞানের নানা তীরে – অপরাধবিজ্ঞান থেকে শুরু করে মিডিয়া স্টাডিজ, মানবাধিকার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান পর্যন্ত।
তত্ত্ব তো আর কাঁচের বাক্সে সাজিয়ে রাখার জিনিস নয়, তাই না? সে এক জীবন্ত সত্তা। সময়ের সাথে সাথে সে বদলায়, নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, কখনও বা নতুন চিন্তকদের হাতে পড়ে আরও শাণিত, আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কোহেনের ‘মোরাল প্যানিক’ এবং ‘স্টেটস অফ ডিনায়াল’ – এই দুই ধারণাই তাঁর মৃত্যুর পর আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই পর্বে আমরা দেখব, কোহেনের রেখে যাওয়া সেই আশ্চর্য চশমা চোখে লাগিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তাবিদরা পৃথিবীকে কীভাবে দেখেছেন, কীভাবে তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং আজকের এই জটিল পৃথিবীতে তাঁর তত্ত্বগুলো কেন এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
নৈতিক আতঙ্কের নতুন রূপ: কোহেনের তত্ত্বের বিবর্তন
স্ট্যানলি কোহেনের ‘ফোক ডেভিলস অ্যান্ড মোরাল প্যানিকস’ ছিল একটি অসাধারণ পর্যবেক্ষণমূলক কাজ, একটি গভীর গল্প। কিন্তু তিনি নিজে এটিকে একটি কঠোর, সুনির্দিষ্ট মডেলে বেঁধে দেননি। পরবর্তী তাত্ত্বিকরা ঠিক এই কাজটিই করেছেন। তাঁরা কোহেনের মূল ধারণাটিকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করেছেন, যা দিয়ে সমাজের বিভিন্ন সময়ের গণ-উন্মাদনাকে কাটাছেঁড়া করা যায়।
রাজনীতি, ক্ষমতা এবং স্টুয়ার্ট হল
কোহেনের তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী সম্প্রসারণটি এসেছিল ব্রিটিশ কালচারাল স্টাডিজের (British Cultural Studies) ঘরানা থেকে। স্টুয়ার্ট হল (Stuart Hall) এবং তাঁর সহকর্মীরা বার্মিংহাম সেন্টার ফর কন্টেম্পোরারি কালচারাল স্টাডিজ (CCCS)-এ বসে কোহেনের কাজকে এক নতুন স্তরে নিয়ে যান। তাঁদের ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত ক্লাসিক বই ‘পলিসিং দ্য ক্রাইসিস: মাগিং, দ্য স্টেট, অ্যান্ড ল অ্যান্ড অর্ডার’ (Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order) ছিল এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ।
ব্যাপারটা কী ছিল? সত্তরের দশকে ব্রিটেন এক গভীর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংকটের (crisis) মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, বেকারত্ব বাড়ছে, শ্রমিক ইউনিয়নগুলো একের পর এক ধর্মঘট ডাকছে। যুদ্ধ-পরবর্তী সেই স্থিতিশীলতার যুগ শেষ। সমাজের ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা ও হতাশা কাজ করছিল। ঠিক এই সময়েই মিডিয়া ‘মাগিং’ (mugging) বা পথচারীদের ওপর হামলা করে ছিনতাই নিয়ে এক তীব্র আতঙ্ক তৈরি করতে শুরু করে। এই অপরাধের জন্য প্রধানত কৃষ্ণাঙ্গ, বিশেষ করে আফ্রো-ক্যারিবীয় তরুণদের দায়ী করা হতে লাগল।
স্টুয়ার্ট হল এবং তাঁর দল দেখালেন, এটি নিছকই কিছু তরুণের অপরাধপ্রবণতা নিয়ে তৈরি হওয়া আতঙ্ক ছিল না। এটি ছিল এক সুগভীর রাজনৈতিক চাল। তাঁরা যুক্তি দেখালেন:
- ভাবাদর্শগত হাতিয়ার (Ideological Tool): ‘মাগিং’ নিয়ে এই মোরাল প্যানিকটি ছিল আসলে রাষ্ট্রের ভাবাদর্শগত হাতিয়ার। শাসক শ্রেণি (ruling class) এই আতঙ্ককে ব্যবহার করে সমাজের আসল সংকট – অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট – থেকে জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দিচ্ছিল। মানুষ যখন রাস্তায় ছিনতাইয়ের ভয়ে আতঙ্কিত, তখন তারা আর বেকারত্ব বা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে ভাবার সময় পায় না।
- হেজিমনি বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা (Establishing Hegemony): ইতালীয় চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামশি (Antonio Gramsci)-র ‘হেজিমনি’ (hegemony) ধারণাটি ব্যবহার করে তাঁরা দেখান যে, রাষ্ট্র কেবল দমন-পীড়নের (coercion) মাধ্যমে শাসন করে না, সম্মতি (consent) আদায়ের মাধ্যমেও করে। ‘মাগিং’-এর ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্র জনগণের কাছে নিজেদের ‘রক্ষাকর্তা’ হিসেবে উপস্থাপন করে এবং আরও কঠোর আইন (যেমন, পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধি) প্রণয়নের জন্য তাদের সম্মতি আদায় করে নেয়।
- বর্ণবাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (Institutionalization of Racism): এই প্যানিকের ‘ফোক ডেভিল’ বা লোক-দানব ছিল কৃষ্ণাঙ্গ তরুণরা। তাদের দানব হিসেবে চিত্রিত করার মাধ্যমে সমাজে বর্ণবাদী ধারণাগুলোকে আরও পোক্ত করা হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের ওপর পুলিশের নজরদারি ও নিপীড়নকে সামাজিক বৈধতা দেওয়া হয়।
ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? কোহেন যেখানে মোরাল প্যানিককে মূলত একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক (socio-psychological) প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছিলেন, সেখানে স্টুয়ার্ট হল এবং তাঁর সহকর্মীরা এর সাথে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ক্ষমতাকে যুক্ত করলেন। তাঁরা দেখালেন, মোরাল প্যানিক কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি প্রায়শই রাষ্ট্রের সংকটকালে তার শাসনকে টিকিয়ে রাখার একটি সচেতন কৌশল (Hall et al., 1978)। এই বিশ্লেষণ কোহেনের তত্ত্বকে এক নতুন রাজনৈতিক মাত্রা দিয়েছিল।
আতঙ্কের ব্যাকরণ: গুড এবং বেন-ইয়েহুদা
কোহেনের কাজ যদি হয় একটি চমৎকার গল্প, তবে সমাজবিজ্ঞানী এরিখ গুড (Erich Goode) এবং নাচমান বেন-ইয়েহুদা (Nachman Ben-Yehuda) হলেন সেই গল্পের ব্যাকরণ রচয়িতা। তাঁরা কোহেনের মডেলটিকে আরও সুসংগঠিত এবং বিশ্লেষণধর্মী করে তোলেন। তাঁদের ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত বই ‘মোরাল প্যানিকস: দ্য সোস্যাল কনস্ট্রাকশন অফ ডেভিয়ান্স’ (Moral Panics: The Social Construction of Deviance)-এ তাঁরা একটি মোরাল প্যানিককে চেনার জন্য পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড নির্ধারণ করেন:
- উদ্বেগ (Concern): কোনো একটি গোষ্ঠীর আচরণ নিয়ে সমাজে অবশ্যই পরিমাপযোগ্য উদ্বেগ তৈরি হতে হবে, যা জনমত জরিপ বা মিডিয়ার আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হবে।
- শত্রুতা (Hostility): যে গোষ্ঠীকে নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তাদের প্রতি সমাজের মধ্যে তীব্র শত্রুতা তৈরি হবে। তাদের ‘আমরা’ বনাম ‘ওরা’ – এই বিভাজনে দেখা হবে এবং তাদের দানব হিসেবে চিত্রিত করা হবে।
- ঐকমত্য (Consensus): সমাজের একটি বড় এবং প্রভাবশালী অংশ (যদিও সবাই নয়) এই বিশ্বাসে একমত হবে যে, এই গোষ্ঠীটি সমাজের মূল্যবোধ বা নিরাপত্তার জন্য একটি বাস্তব হুমকি।
- অসামঞ্জস্যতা (Disproportionality): আতঙ্কটি ঘটনার প্রকৃত ভয়াবহতার তুলনায় অনেক বেশি অতিরঞ্জিত হবে। মিডিয়ার পরিসংখ্যান, নাটকীয় বর্ণনা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত এই অসামঞ্জস্যতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।
- অস্থিরতা (Volatility): মোরাল প্যানিকগুলো সাধারণত হঠাৎ করেই আবির্ভূত হয় এবং কিছুদিন তীব্রভাবে থাকার পর আবার হঠাৎ করেই মিলিয়ে যায়, যেন কিছুই ঘটেনি।
তাঁরা আরও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মডেলের কথা বলেন: তৃণমূল মডেল (grassroots model), যেখানে আতঙ্ক সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে তৈরি হয়; এলিট-ইঞ্জিনিয়ারড মডেল (elite-engineered model), যেখানে ক্ষমতাশালীরা সচেতনভাবে আতঙ্ক তৈরি করে; এবং স্বার্থ-গোষ্ঠী মডেল (interest-group model), যেখানে কোনো বিশেষ পেশাজীবী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে আতঙ্ক ছড়ায় (Goode & Ben-Yehuda, 1994)।
এই কাঠামোগত বিশ্লেষণের ফলে ‘মোরাল প্যানিক’ ধারণাটি গবেষকদের জন্য একটি কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাঁরা এখন এই মানদণ্ডগুলো ব্যবহার করে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে বলতে পারেন, এটি সত্যিকারের সংকট নাকি একটি পরিকল্পিত মোরাল প্যানিক।
ডিজিটাল যুগ এবং নতুন আতঙ্কের ভূ-চিত্র
কোহেন যখন তাঁর তত্ত্ব দিয়েছিলেন, তখন ছিল কয়েকটি পত্রিকা আর দুটি টিভি চ্যানেলের যুগ। কিন্তু আজকের এই ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া আর ২৪-ঘণ্টার নিউজ চক্রের যুগে তাঁর তত্ত্ব কি এখনো প্রাসঙ্গিক? উত্তর হলো – আগের চেয়েও অনেক বেশি, তবে এর রূপ কিছুটা বদলেছে।
ইন্টারনেট মোরাল প্যানিক তৈরির এক অসাধারণ উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আতঙ্কের মুখোমুখি হচ্ছি:
- সাইবার বুলিং এবং অনলাইন শিকারি (Cyberbullying and Online Predators): ইন্টারনেট শিশুদের জন্য কতটা অনিরাপদ, এই নিয়ে প্রায়শই আতঙ্ক তৈরি হয়। যদিও বিপদটি বাস্তব, মিডিয়া একে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন প্রতিটি অনলাইন চ্যাটরুমেই একজন শিকারি ওঁৎ পেতে বসে আছে।
- ভিডিও গেম আতঙ্ক: যখনই কোনো স্কুলে গোলাগুলির মতো ঘটনা ঘটে, প্রায়শই ‘কল অফ ডিউটি’ বা ‘জিটিএ’-এর মতো হিংস্র ভিডিও গেমগুলোকে দায়ী করা হয়। ভিডিও গেমারদের ‘ফোক ডেভিল’ বানিয়ে সমাজের আসল সমস্যা (যেমন, অস্ত্রের সহজলভ্যতা বা মানসিক স্বাস্থ্য) থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া হয়।
- সোশ্যাল মিডিয়া চ্যালেঞ্জ: ‘মোমো চ্যালেঞ্জ’ বা ‘ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ’-এর মতো ঘটনাগুলো ছিল ডিজিটাল মোরাল প্যানিকের ক্লাসিক উদাহরণ। প্রায় কোনো বাস্তব ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও এই চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে বিশ্বজুড়ে এমন আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল যে, স্কুল এবং পুলিশ পর্যন্ত সতর্কতা জারি করতে বাধ্য হয়।
তবে সবাই একমত নন যে, আজকের যুগে মোরাল প্যানিক আগের মতোই কাজ করে। সমাজবিজ্ঞানী অ্যাঞ্জেলা ম্যাকরবি (Angela McRobbie) এবং সারাহ থর্নটন (Sarah Thornton) ১৯৯৫ সালে একটি প্রভাবশালী প্রবন্ধে যুক্তি দেখান যে, মিডিয়ার বহুধা বিভক্তি এবং উপ-সংস্কৃতিগুলোর (subcultures) মিডিয়া-সচেতনতার কারণে আজকের দিনে একটি এককেন্দ্রিক জাতীয় মোরাল প্যানিক তৈরি করা কঠিন (McRobbie & Thornton, 1995)।
তাঁদের মতে:
- মিডিয়ার বহুত্ব: এখন আর কয়েকটি মাত্র মিডিয়া হাউস জনমত নিয়ন্ত্রণ করে না। শত শত টিভি চ্যানেল, নিউজ ওয়েবসাইট, ব্লগ, ইউটিউব চ্যানেল – এই বহুত্বের কারণে একটি একক বার্তা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন।
- সক্রিয় দর্শক: আজকের দর্শকরা আগের মতো নিষ্ক্রিয় নয়। তারা নিজেরাই কন্টেন্ট তৈরি করে, মূলধারার মিডিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। একটি উপ-সংস্কৃতিকে ‘দানব’ বানানো হলে, তারা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে পারে।
- আতঙ্কের বাণিজ্যিকীকরণ: অনেক সময় উপ-সংস্কৃতিগুলো নিজেরাই মিডিয়ার মনোযোগ চায়, কারণ এটি তাদের জনপ্রিয় করে তোলে। ‘ফোক ডেভিল’ হওয়াটা এখন এক ধরনের ‘স্ট্রিট ক্রেড’ (street cred) বা সম্মান বয়ে আনতে পারে।
তবে এর বিপরীতে বলা যায়, আজকের আতঙ্কগুলো হয়তো আর জাতীয় স্তরে এককেন্দ্রিক নয়, কিন্তু সেগুলো আরও বেশি খণ্ডিত (fragmented) এবং তীব্র। সোশ্যাল মিডিয়ার ‘ইকো চেম্বার’ (echo chambers) এবং ‘ফিল্টার বাবল’ (filter bubbles)-এর মধ্যে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্য করে খুব সহজেই তীব্র ঘৃণা এবং আতঙ্ক ছড়ানো যায়। আজকের ‘মোরাল এন্টারপ্রেনার’-রা আর কেবল রাজনীতিবিদ বা সাংবাদিক নন, তাঁরা হলেন ইউটিউবার, ইনফ্লুয়েন্সার বা বেনামী টুইটার অ্যাকাউন্ট।
অস্বীকারের উত্তরাধিকার: রাষ্ট্রীয় অপরাধ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন
কোহেনের কাজের দ্বিতীয় স্তম্ভ, ‘স্টেটস অফ ডিনায়াল’, হয়তো সাধারণ মানুষের কাছে ‘মোরাল প্যানিক’-এর মতো জনপ্রিয় নয়, কিন্তু একাডেমিক এবং মানবাধিকার জগতে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই কাজটি অপরাধবিজ্ঞানের (criminology) সংজ্ঞাই পাল্টে দিয়েছে।
প্রচলিত অপরাধবিজ্ঞান মূলত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধ (যেমন, চুরি, ডাকাতি, খুন) নিয়েই কাজ করত। কোহেন, এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত পেনি গ্রিন (Penny Green) ও টনি ওয়ার্ড (Tony Ward)-এর মতো অপরাধবিজ্ঞানীরা, এই শাস্ত্রের নজর ঘুরিয়ে দিলেন রাষ্ট্রের দিকে। তাঁরা যুক্তি দেখালেন, রাষ্ট্রের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ – যেমন, গণহত্যা (genocide), অত্যাচার (torture), যুদ্ধাপরাধ (war crimes) – সাধারণ অপরাধের চেয়ে বহুগুণে বেশি ধ্বংসাত্মক, কিন্তু এগুলোকে প্রায়শই ‘রাজনীতি’ বা ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র নামে এড়িয়ে যাওয়া হয় (Green & Ward, 2004)।
‘স্টেটস অফ ডিনায়াল’ এই রাষ্ট্রীয় অপরাধকে সম্ভব করে তোলা সামাজিক মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছে। এটি দেখিয়েছে, কীভাবে সাধারণ নাগরিক এবং আমলারা ভয়ঙ্কর অন্যায়ের অংশীদার হয়েও নিজেদের ‘ভালো মানুষ’ ভাবতে পারে, কীভাবে তারা ‘আমি তো কেবল আদেশ পালন করছিলাম’ বলে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। এই কাজটি হলোকস্ট স্টাডিজ (Holocaust Studies), ট্রানজিশনাল জাস্টিস (transitional justice) এবং মানবাধিকার গবেষণার এক অপরিহার্য পাঠ্যে পরিণত হয়েছে।
কোহেনের অস্বীকারের তত্ত্বটি আজকের বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংকটগুলো বুঝতে আমাদের সাহায্য করে:
- জলবায়ু পরিবর্তন: আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে জানি যে পৃথিবী এক ভয়ঙ্কর সংকটের মুখোমুখি, কিন্তু রাষ্ট্র, কর্পোরেশন এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা সেই সত্যের নিহিতার্থকে (implication) অস্বীকার করে চলেছি। আমরা জানি কী করতে হবে, কিন্তু করি না – এটিই হলো নিহিতার্থ অস্বীকারের (implicatory denial) সবচেয়ে বড় উদাহরণ।
- বিশ্বজুড়ে সংঘাত: সিরিয়া, ইয়েমেন বা অন্য কোনো দেশে ঘটে চলা যুদ্ধের ভয়াবহতা আমরা ইন্টারনেটে দেখি, কিন্তু তা আমাদের ভোগবাদী জীবনযাত্রায় কোনো আঁচড় কাটে না। এই ‘দূরবর্তী দুর্ভোগ’ (distant suffering) দেখেও নিষ্ক্রিয় থাকাটা আমাদের সময়ের এক নৈতিক সংকট, যা কোহেন নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেছিলেন।
স্ট্যানলি কোহেনের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার বিশাল। তিনি কেবল কয়েকটি তত্ত্ব দেননি, তিনি আমাদের একটি সম্পূর্ণ টুলকিট বা হাতিয়ারের বাক্স দিয়ে গেছেন। এই টুলকিট দিয়ে আমরা মিডিয়ার তৈরি করা বিভ্রমের জাল ছিঁড়তে পারি, ক্ষমতার লুকানো উদ্দেশ্যকে প্রশ্ন করতে পারি, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সমাজের সম্মিলিত নীরবতা ও আতঙ্কের পেছনে নিজেদের ভূমিকা নিয়েও ভাবতে পারি। তাঁর কাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, একজন সমাজবিজ্ঞানীর দায়িত্ব কেবল পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করা নয়, তাকে আরও একটু মানবিক এবং ন্যায়পরায়ণ করে তোলার জন্য লড়াই করাও। তাঁর রেখে যাওয়া চশমাটি তাই কেবল দেখার জন্য নয়, এটি আমাদের দেখানোর পথেরও দিশারী।
তত্ত্বের কাঠগড়ায় – সমালোচনা
কোনো যুগান্তকারী তত্ত্বই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। ‘মোরাল প্যানিক’ ধারণাটিও সময়ের সাথে সাথে অনেক সমাজবিজ্ঞানী দ্বারা পর্যালোচিত এবং সমালোচিত হয়েছে। এই সমালোচনাগুলো তত্ত্বটিকে বাতিল করে দেয় না, বরং একে আরও সমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী করে তোলে।
কিছু প্রধান সমালোচনা হলো:
- ‘প্যানিক’ শব্দটি কি সঠিক? কিছু সমালোচক, যেমন পি. এ. জে. ওয়াডিংটন (P.A.J. Waddington), মনে করেন যে ‘প্যানিক’ বা ‘আতঙ্ক’ শব্দটি একটু বেশি নাটকীয় এবং অতিরঞ্জিত। সমাজের প্রতিক্রিয়াটি উদ্বেগ (concern) বা দুশ্চিন্তা (anxiety) হতে পারে, কিন্তু সবসময় তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া আতঙ্ক (panic) না-ও হতে পারে। তাঁদের মতে, অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াগুলো যৌক্তিক ভিত্তি থেকেও আসতে পারে (Waddington, 1986)।
- দর্শক কি নিষ্ক্রিয়? মূল মডেলে মিডিয়ার দর্শক বা সাধারণ মানুষকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় গ্রাহক (passive consumers) হিসেবে দেখা হয়েছে, যারা মিডিয়া যা বলে তা-ই সরলভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু পরবর্তীকালের মিডিয়া স্টাডিজ (Media Studies) দেখিয়েছে যে, দর্শকরা মোটেও নিষ্ক্রিয় নয়। তারা মিডিয়ার বার্তাগুলোকে নিজেদের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং সামাজিক অবস্থান থেকে বিচার করে। তারা মিডিয়ার তৈরি করা আতঙ্ককে গ্রহণ, বর্জন বা নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করতে পারে। একে বলা হয় ‘অ্যাক্টিভ অডিয়েন্স থিওরি’ (Active Audience Theory) (Critcher, 2008)।
- ইন্টারনেটের যুগে মোরাল প্যানিক: এই তত্ত্বটি ছিল মূলত গণমাধ্যমের (mass media) যুগের তত্ত্ব, যেখানে কয়েকটি প্রভাবশালী পত্রিকা বা টিভি চ্যানেল জনমত তৈরি করত। কিন্তু আজকের ডিজিটাল যুগে, যেখানে প্রত্যেকের হাতেই একটি মিডিয়া (স্মার্টফোন), সেখানে মোরাল প্যানিকের চরিত্র বদলে গেছে। অ্যাঞ্জেলা ম্যাকরবি (Angela McRobbie) এবং সারাহ থর্নটন (Sarah Thornton) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আধুনিক মিডিয়া-স্যাচুরেটেড সমাজে মোরাল প্যানিক তৈরি করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ, এখানে শত শত মিডিয়া আউটলেট একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে, এবং অনেক উপ-সংস্কৃতি (subculture) মিডিয়ার মনোযোগকে ভয় পাওয়ার বদলে উপভোগ করে। আজকের আতঙ্কগুলো অনেক বেশি খণ্ডিত (fragmented), দ্রুত ছড়ায় (viral) এবং স্বল্পস্থায়ী হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার ‘ইকো চেম্বার’ (echo chambers) এবং ‘ফিল্টার বাবল’ (filter bubbles)-এর কারণে মানুষ এখন ভিন্ন ভিন্ন প্যানিকের শিকার হতে পারে। একদিকে যেমন ‘ব্লু হোয়েল’ (Blue Whale) চ্যালেঞ্জের মতো ভিত্তিহীন আতঙ্ক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই আবার ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলোও (conspiracy theories) মোরাল প্যানিকের রূপ নেয়।
এই সমালোচনাগুলো সত্ত্বেও, মোরাল প্যানিকের মূল ধারণাটি আজও অবিশ্বাস্যভাবে প্রাসঙ্গিক। ‘ফেক নিউজ’ (fake news), ‘পোস্ট-ট্রুথ’ (post-truth) এবং অনলাইন বিদ্বেষমূলক প্রচারণার (online hate campaigns) এই যুগে তাঁর কাজ আগের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, কীভাবে সংবাদের শিরোনামের পেছনে থাকা আদর্শগত অবস্থানকে (ideology) প্রশ্ন করতে হয়। তিনি আমাদের চিনিয়েছেন সেই আধুনিক ‘মোরাল এন্টারপ্রেনারদের’, যারা ইউটিউব, ফেসবুক বা টুইটারে বসে নিজেদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে আমাদের ভয়কে ব্যবহার করে।
উপসংহার
আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করি, যেখানে ভয় যেন বাতাসের অক্সিজেনের মতোই এক অপরিহার্য উপাদান। আমাদের ঘুম ভাঙে আশঙ্কার খবর দিয়ে, দিন কাটে উদ্বেগের মধ্যে, আর রাতে ঘুমাতে যাই ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নিয়ে। কখনও সন্ত্রাসবাদের ভয়, কখনও মহামারীর ভয়, কখনও অর্থনৈতিক মন্দার ভয়, আবার কখনও বা নতুন প্রজন্মের ‘উচ্ছৃঙ্খল’ হয়ে যাওয়ার ভয়। এই ভয়গুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে এবং প্রায়শই আমাদের একে অপরের থেকে দূরে ঠেলে দেয়, আমাদের মধ্যে অদৃশ্য বিভেদের প্রাচীর তোলে। এই ভয়ের কুয়াশার মধ্যে আমরা সহজ শত্রু খুঁজি, সহজ সমাধান খুঁজি, আর প্রায়শই ভুল মানুষকে আমাদের সব সমস্যার জন্য দায়ী করে বসি।
স্ট্যানলি কোহেন ছিলেন সেই মানুষ, যিনি আমাদের এই ভয়ের মেকানিজমটা শিখিয়েছেন। তিনি ছিলেন কুয়াশার মধ্যে এক বাতিঘর, যিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে এই ভয়কে পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়, লালন করা হয় এবং ব্যবহার করা হয়। তিনি একজন অসাধারণ গল্পকার ছিলেন। তবে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলো কোনো কাল্পনিক দানব নয়, বরং আমাদেরই সমাজের তৈরি করা কিছু ‘ফোক ডেভিল’ – কিছু প্রান্তিক, ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের ওপর আমরা আমাদের সব ব্যর্থতার দায়, সব অমীমাংসিত উদ্বেগ চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, এই দানবরা আকাশ থেকে পড়ে না। আমাদের সম্মিলিত অজ্ঞতা, আমাদের নিরাপত্তাহীনতা, আমাদের মিডিয়ার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস আর সবচেয়ে বড় কথা, প্রশ্ন করতে ভুলে যাওয়া আমাদের নীরবতাই হলো সেই উর্বর কারখানা, যেখানে প্রতিদিন এদের জন্ম হয়।
তবে তাঁর প্রজ্ঞার এখানেই শেষ নয়। তিনি আমাদের কেবল সমাজের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার (overreaction) গল্পই শোনাননি, শুনিয়েছেন তার উল্টো পিঠের গল্পও – সমাজের চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তার (underreaction) কথা। তাঁর ‘স্টেটস অফ ডিনায়াল’ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা যখন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নৈতিক আতঙ্কে ভুগি, ঠিক তখনই বিশ্বের অন্য প্রান্তে ঘটে যাওয়া গণহত্যা, পরিবেশ বিপর্যয় বা ভয়ঙ্কর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিশাল সত্যকে আমরা জেনেও না জানার ভান করি। এই বৈপরীত্যই হয়তো আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। আমরা মশা মারতে কামান দাগি, কিন্তু সত্যিকারের ডাইনোসরের সামনে চোখ বন্ধ করে বসে থাকি।
তাহলে কোহেনের কাজ থেকে আমাদের কী শেখার আছে? কেবল একটি একাডেমিক তত্ত্ব জেনে কিছু নম্বর পাওয়া? না। তাঁর কাজ আসলে এক গভীর জীবনদর্শন, এক নাগরিক দায়িত্বের আহ্বান। যখনই আপনি দেখবেন, কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমাজ একসঙ্গে ক্ষেপে উঠেছে, যখনই মনে হবে কোনো একটি বিষয় নিয়ে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হইচই হচ্ছে, তখন এক মুহূর্তের জন্য থামবেন। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানোর সাহস দেখাবেন। নিজেকে শান্তভাবে প্রশ্ন করবেন – আসল সমস্যাটা কোথায়? যাকে দানব বলে দেখানো হচ্ছে, সমস্যাটা কি তার মধ্যে? নাকি আমাদের দৃষ্টিতে, আমাদের সম্মিলিত আতঙ্কে, আমাদের জটিল পৃথিবীকে সহজ শত্রু-মিত্রের বাইনারিতে দেখার বিপজ্জনক প্রবণতায়? আমরা কি জেনে-বুঝে কোনো বলির পাঁঠা তৈরি করছি?
এই একটি প্রশ্নই হয়তো আপনাকে চারপাশের কোলাহলের ঊর্ধ্বে তুলে এক স্বচ্ছ দৃষ্টির জগতে দাঁড় করিয়ে দেবে। আর সেখানেই স্ট্যানলি কোহেনের আসল জাদু, তাঁর আসল উত্তরাধিকার। তিনি কেবল একজন সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের বিবেকের কম্পাসকে ঠিক করে দেওয়ার একজন কারিগর। তিনি আমাদের হাতে কোনো তৈরি উত্তর তুলে দেননি, বরং দিয়েছেন কিছু শাণিত প্রশ্ন, যা দিয়ে আমরা নিজেরাই সত্যকে খুঁজে নিতে পারি। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের জাদুকর, যার সবচেয়ে বড় জাদুটি ছিল আমাদের নিজেদের চোখের ওপর থেকে বিভ্রমের পর্দাটি সরিয়ে দেওয়া।
তথ্যসূত্র
- Becker, H. S. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. The Free Press.
- Cohen, S. (1972). Folk devils and moral panics: The creation of the mods and rockers. MacGibbon and Kee.
- Cohen, S. (1985). Visions of social control: Crime, punishment and classification. Polity Press.
- Cohen, S. (2001). States of denial: Knowing about atrocities and suffering. Polity Press.
- Critcher, C. (2003). Moral panics and the media. Open University Press.
- Critcher, C. (2008). Moral panic analysis: Past, present and future. Sociology Compass, 2(4), 1127–1144. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2008.00122.x
- Durkheim, É. (1982). The rules of sociological method (S. A. Solovay & J. H. Mueller, Trans.; G. E. G. Catlin, Ed.). The Free Press. (Original work published 1895)
- Erikson, K. T. (1966). Wayward Puritans: A study in the sociology of deviance. John Wiley & Sons.
- Fowler, R. (1991). Language in the news: Discourse and ideology in the press. Routledge.
- Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Prentice-Hall.
- Goode, E., & Ben-Yehuda, N. (1994). Moral panics: The social construction of deviance. Blackwell.
- Green, P., & Ward, T. (2004). State crime: Governments, violence and corruption. Pluto Press.
- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., & Roberts, B. (1978). Policing the crisis: Mugging, the state and law and order. Macmillan.
- Hebdige, D. (1979). Subculture: The meaning of style. Methuen.
- Lemert, E. M. (1951). Social pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic behavior. McGraw-Hill.
- Levack, B. P. (2015). The witch-hunt in early modern Europe (4th ed.). Routledge.
- MacInnes, C. (1959). Absolute beginners. MacGibbon & Kee.
- Marwick, A. (1998). The sixties: Cultural revolution in Britain, France, Italy, and the United States, c.1958-c.1974. Oxford University Press.
- McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. McGraw-Hill.
- McRobbie, A., & Thornton, S. L. (1995). Rethinking ‘moral panic’ for multi-mediated social worlds. The British Journal of Sociology, 46(4), 559–574. https://doi.org/10.2307/591571
- Pearson, G. (1983). Hooligan: A history of respectable fears. Macmillan.
- Platt, A. M. (1996). The child savers: The invention of delinquency (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Taylor, L. [Laurie Taylor]. (2013, January 24). Stanley Cohen obituary [Obituary]. The Guardian. https://www.theguardian.com/education/2013/jan/23/stanley-cohen
- Thomas, W. I., & Thomas, D. S. (1928). The child in America: Behavior problems and programs. Knopf.
- Victor, J. S. (1993). Satanic panic: The creation of a contemporary legend. Open Court Publishing.
- Waddington, P. A. J. (1986). Mugging, the media, and the police. The British Journal of Sociology, 37(2), 245–261. https://www.jstor.org/stable/590356
- Wertham, F. (1954). Seduction of the innocent. Rinehart & Company.
- Wilkins, L. T. (1964). Social deviance: Social policy, action, and research. Tavistock Publications.