সূচিপত্র
- 1 ভূমিকা
- 2 ধর্ষক ধর্ষণের কারণ
- 3 প্রকাশ্য পোশাকের বিরুদ্ধে বৈষম্য
- 4 নারীদের শরীরকে ধর্ষণের “কারণ” বলা
- 5 ধর্ষণ সম্পর্কিত উপকথা এবং ভিক্টিম ব্লেমিং
- 6 নারীরা প্রকাশ্য পোশাক কেন পরে?
- 7 পুরুষরা নারীদের পোশাক-কে কিভাবে করে দেখে?
- 8 পোশাক এবং যৌন নির্যাতনের মধ্যে কোনো “Correlation” বা “Causal” সম্পর্ক নেই
- 9 ভিক্টিম ব্লেমিং-এর মধ্যে পুরুষদের যৌন উত্তেজনার ভূমিকা
- 10 ধর্ষণের ভিক্টিমরা কিরকম পোশাক পরে?
- 11 Attribution Theory এবং ভিক্টিম ব্লেমিং
- 12 Theory of Ambivalent Sexism এবং ভিক্টিম ব্লেমিং
- 13 পুরুষরা কেন পোশাক-কে ধর্ষণের “কারণ” বলে?
- 14 অন্যান্য ফ্যাক্টরকে ধর্ষণের কারণ বলে ধর্ষণকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা
- 15 Right Wing Authoritarianism (RWA) এবং ভিক্টিম ব্লেমিং
- 16 “পাগল ধর্ষক”-এর উপকথা
- 17 পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বিশেষাধিকার
- 18 কেন মানুষ নারীদের পোশাককে “প্রভোকেটিভ” বলে?
- 19 “প্রভোকেটিভ” পোশাক এবং মানুষের দায়বদ্ধতা
- 20 শুধুমাত্র Objectification-এর কারণে নারীদের Sexualization ক্ষতিকর হতে পারে
- 21 পোশাক কোনোভাবেই সম্মতির প্রমান নয়
- 22 উপসংহার
- 23 তথ্যসূত্র
ভূমিকা
বাংলাদেশে কোথাও ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে খুব সচেতনভাবেই নারীর পোশাককে ধর্ষণের কারণ হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়, বরং একইসাথে তার আচার আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্টের ভিত্তিতে যৌন আক্রমণের ভুক্তভোগীদের আদালতের মধ্যেও আইনিভাবে দোষারোপ করা হয়। প্রায়শই আসামীগণের বিরুদ্ধে যৌন আক্রমণের ভুক্তভোগীদের মামলাকে এসব বিবেচনা করে বাতিল করে দেওয়া হয়। অবশ্য, পুরুষদের পোশাক কখনো আলোচনার বিষয় হয়ই না, এবং “পোশাক ধর্ষণের কারণ” বিবৃতিটি নারীদের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র প্রয়োগ করা হয়। যার ফলে নারীরা তাদের বাস্তব জীবনে সমাজ এবং আইনি স্তরে বাধাগ্রস্ত হয়। একইসাথে, এই বিবৃতির ভিত্তিতে নারীদের মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়; যথা- স্বাধীনভাবে পোশাক পরার বা নিজেকে প্রকাশের মানবাধিকার।
প্রায়শই এই বিষয়ে সমাজের কিছু মানুষকে বিজ্ঞ মতামত দিতে খুব উৎসাহী হতে দেখা যায়। সাধারণত এইসব বিজ্ঞ মতামতের মধ্যে যা থাকে তা হচ্ছে, “ঐ ছেড়িরও দোষ আছে। ছেড়ির চলাফেরা ভাল না। রাইত বিড়াতে বাইরে যায়। পোলাগো লগে ঘুরে।” অর্থাৎ, সেই মেয়ের যেহেতু চরিত্র ভাল না, তাই তাকে ধর্ষণ করা যেতেই পারে! যেহেতু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কঠিনভাবে পুরুষতান্ত্রিক, তাই এসব কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য সাধারণ বুদ্ধিমত্তার মানুষের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়। কারণ আমাদের সমাজে মেয়েদের চলাফেরা, পোশাক আশাক থেকে শুরু করে সবকিছুই নিয়ন্ত্রন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং সব সাধারণ মানুষই এতে বেশ দক্ষ। এরা অবলীলায় ধর্ষণের ঘটনায় ধর্ষক ধর্ষিতা উভয়ই দোষী বানিয়ে ছেড়ে দেয়। এরা বলে, “ধর্ষিতাই বা কেন উত্তেজক জামা পড়ে ধর্ষকের যৌনানুভূতিতে আঘাত দিল? ধর্ষণ তো হবেই!” সেই সাথে এই বিষয়টি উল্লেখ করে নারীর লেখাপড়া, চাকরিবাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাধানিষেধ আরোপ করা সম্ভব হয়, ধর্ষণের ভয় দেখিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ইচ্ছাকে নিরুৎসাহিত করা হয়।
“পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে” বাক্যটি মৌলিকভাবে ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করে। কেননা, “সূর্যে শুকাইতে দেয়া রশিতে ঝুলানো পোশাক-কে ধইরা কেউ চুম্মা-চাট্টি করলেও”- তা আমরা ধর্ষণ হিসাবে গণ্য করি না। অতএব, যখন বলা হয় যে “পোশাক ধর্ষণের কারণ” তখন ভুক্তভোগীর পোশাক পরিধান করা, অর্থাৎ, ভুক্তভোগীর নিজের সচেতন সিদ্ধান্তকে (অর্থাৎ পোশাক পরিধান করার সিদ্ধান্তকে) ধর্ষণের কারণ হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়।
নারীবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধর্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন উপকথা, বা “rape myth”-কে খণ্ডন করেছে, এবং দেখিয়েছে যে এই ধরণের উপকথা প্রমাণিকভাবে ভুল হওয়ার পাশাপাশি, শুধুমাত্র ভুক্তভোগী দোষারোপের একটি পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ন্যায্যতা দেয়, এবং ধর্ষণকারীর অপরাধকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ধর্ষণ সম্পর্কে উপকথার মধ্যে সব চেয়ে প্রচলিত হলো এই ধারণা যে পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে। মুমিনরা যেভাবে করে “আল্লাহ মহাবিশ্বের সৃষ্টির কারণ হতে পারে” বলে দাবি করে, “পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে” দাবিটি একইভাবে প্রমান দ্বারা সমর্থিত নয়। তবে একজন মুমিন “আল্লাহ মহাবিশ্বের সৃষ্টির কারণ হতে পারে” কথাটা অন্য কাউকে আঘাত না করে, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস এবং পোষণ করতে পারে। তবে “পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে” বাক্যটি মৌলিকভাবে ক্ষতিকর এবং এবং এই মিথ্যা ধারণার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগ সর্বদা ভুক্তভোগী দোষারোপে অবদান রাখে। নারীবাদী সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রকাশ্য পোশাক এবং ধর্ষণ বা যৌন আক্রমণের সাথে কোনো “causal” বা এমনকি “correlation”-এর কোনো সম্পর্ক নেই।
একইসাথে, “পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে” এই মিথ্যা ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে যে ধর্ষণের ভুক্তভোগী তার কর্মের মাধ্যমে (অর্থাৎ তার পোশাক পরার মাধ্যমে) ধর্ষণটি ঘটিয়েছে। এটি সাধারণত আরেকটি মিথ্যা ধারণার উপরে ভিত্তি করা যে নারীরা পুরুষদেরকে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরিধান করে। নারীবাদী স্কলাররা গবেষণার মাধ্যমে প্রমান করেছে যে বেশিরভাগ নারীদের ক্ষেত্রে তাদের প্রকাশ্য পোশাক পরার সিদ্ধান্তের সাথে কোনোভাবেই তাদের যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার, যৌন আগ্রহ যোগাযোগ করার বা পুরুষদেরকে সিডিউস করার কোনোই উদ্দেশ্য থাকে না। এমনকি, নারীবাদী স্কলাররা আরো দেখিয়েছে যে আদালতের মধ্যে ভুক্তভোগীর মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য যাচাই করার ক্ষেত্রে সেই ভুক্তভোগীর পোশাক কোনোভাবেই probative/গ্রহণযোগ্য প্রমান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।
নারীদের প্রকাশ্য পোশাক যে পুরুষদের মধ্যে এমন শক্তিশালী যৌন লালসার উদ্ভব ঘটায় যে পুরুষরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না- এই দাবিকেও খণ্ডন করে নারীবাদী স্কলাররা দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানসিকভাবে স্বাভাবিক হয়ে থাকে। তবে, নারীবাদী স্কলাররা বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারী পুরুষরা যে নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না- এটি একটি Rape Myth/উপকতা যা প্রমাণিকভাবে এবং ধারণাগতভাবে অসমর্থিত (conceptually and empirically unsupported)। এমনকি, মনোবিজ্ঞানীরা ধর্ষণকারীদের মধ্যে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ খুঁজে বের করার অসংখ্য চেষ্টা করার সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছে। এই তথ্যটি পরামর্শ দেয় যে ধর্ষণকারীদের অপরাধকে “মানসিক বিকৃতি” বা “কম সংখ্যার অপরাধ” হিসাবে কোনোভাবেই শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না, কেননা ধর্ষণ সামাজিকভাবে ব্যতিক্রমী হওয়ার পরিবর্তে, ধর্ষণ সাংস্কৃতিকভাবে নির্দেশিত, যেখানে ধর্ষণের মনোভবকে পোষণ করা হয়, এবং অতএব, ধর্ষণকে অপরাধের পরিবর্তে “স্বাভাবিক” হিসাবে দেখা হয়।
প্রকাশ্য পোশাক পরিধানের বিপদের অজুহাতে “পোশাক ধর্ষণের কারণ” ধারণাটির প্রচলন ঘটে, যার ভিত্তিতে নারীদের স্বাধীন প্রকাশের অধিকার unfair ভাবে সীমাবদ্ধ হয়। একইসাথে, যেসব নারীরা একটি sexualized appearance গ্রহণ করে, তাদেরকে “বেপরোয়া” হওয়ার জন্যে সমালোচনা করা হয়, যেন sexualized appearance গ্রহণ করা একটা অপরাধ। তবে, নারীবাদী সাহিত্যে, এটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত যে শুধুমাত্র অন্যদের দ্বারা Objectification-এর কারণে, একটি নারী যিনি একটি sexualized appearance গ্রহণ করেছে, তিনি যৌন সহিংসতার সম্মুখীন হতে পারে। এই তথ্য পরামর্শ দেয় যে নারীদেরকে তাদের sexualized appearance-এর জন্যে সমালোচনা করা, এবং দোষারোপ করা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক।
ধর্ষক ধর্ষণের কারণ
Scenario#1-এর কথা বিবেচনা করুন। এখানে দুটি ফ্যাক্টর রয়েছে- ধর্ষক এবং “প্রকাশ্য” পোশাক। ফলাফল হলো ধর্ষণ। এখন Scenario#2-এর কথা বিবেচনা করে দেখুন। এখানেও দুটি ফ্যাক্টর রয়েছে – একজন মানুষ যিনি ধর্ষক নয় এবং প্রকাশ্য পোশাক। প্রকাশ্য পোশাকের উপস্থিতির সত্ত্বেও এখানে কোনো ধর্ষণ সংগঠিত হচ্ছে না। Scenario#2 হলো সেই প্রমান, যা দেখায় যে পোশাক কখনো ধর্ষণের কারণ হতে পারে না। ধর্ষণের কারণ শুধুমাত্র ধর্ষক। কেননা, পোশাক যদি ধর্ষণের কারণ হয়ে থাকতো, তাহলে Scenario#2-এর মধ্যেও ধর্ষণ ঘটতো। তবে, একজন নারী প্রকাশ্য পোশাক বা এমনকি ন্যাংটা অবস্থায় থাকলেও, একজন মানুষ যে ধর্ষক নয় সে কখনো সেই নারীটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পর্শ পর্যন্ত করবে না।
একজন মানুষ যে ধর্ষক না- তার নুনু যতই খাড়াইয়া থাকুক- সে যতই যৌন উত্তেজনা অনুভব করুক- যদি সে ধর্ষক না হয়ে থাকে, সে কখনোই কোনো নারীকে যৌনভাবে আক্রমণ করবে না। শুধুমাত্র একটা ধর্ষক মনে করবে যে যেহেতু একটা নারী প্রকাশ্য কাপড় পড়েছে, এবং যেহেতু সেই ধর্ষকটা যৌনভাবে উত্তেজিত হয়েছে, তাই সেই ধর্ষক এখন ধর্ষণ করতে পারবে। যৌন উত্তেজনা কোনো খারাপ জিনিস না। যারা ধর্ষক না, তারা কখনোই যৌন উত্তেজনার ভিত্তিতে ধর্ষণ করে না। এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যৌন উত্তেজনা এবং প্রকাশ্য পোশাক- কোনোটাই ধর্ষণের কারণ হতে পারে না। ধর্ষণের কারণ শুধুমাত্রই ধর্ষক, অর্থাৎ সেসব মানুষ যারা যৌন উত্তেজনার ভিত্তিতে অন্য কোনো মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে যৌনভাবে আক্রমণ করে।
ধরেন একজন হিন্দুত্ববাদী একটি মুসলিম দেশ আক্রমণ করার পর, একটা হিজাবি নারীকে দেখলো। এরপর সেই হিন্দুত্ববাদী সেই মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলো। এখানে কি নারীর পোশাক (অর্থাৎ নারীর হিজাব পরিধান করা) সেই ধর্ষণের কারণ?
অবশ্যই না। এই ক্ষেত্রেও, ধর্ষণের কারণ শুধুমাত্র ধর্ষক নিজেই। ধরেন আরেকটি হিন্দুত্ববাদী সেই একই হিজাবি নারীকে দেখলো, তবে সেই হিন্দুত্ববাদী সেই নারীকে ধর্ষণ করলো না। সেই দ্বিতীয় হিন্দুত্ববাদী একজন হিন্দুত্ববাদী তো বটেই, তবে সে একজন ধর্ষণকারী নয়। ধর্ষণটি শুধুমাত্র ধর্ষণকারীর উপলব্ধি, মনোভাব এবং কর্মের কারণে সংগঠিত হচ্ছে; ভুক্তভোগীর (হিজাবি মুসলিম নারীর) পোশাক পরিধান করার সিদ্ধান্ত নয়। উপরোক্ত পরিস্থিতির মধ্যেও, ধর্ষণের কারণ সেই ধর্ষণকারী হিন্দুত্ববাদী যে নারীর সম্মতি লঙ্ঘন করেছে।
প্রকাশ্য পোশাকের বিরুদ্ধে বৈষম্য
বিভিন্ন গবেষক পোশাকের ধারণা নিয়ে রিসার্চ করে দেখতে পেরেছেন যে সমাজের অনেকেই প্রকাশ্য পোশাকের ভিত্তিতে ভিক্টিম ব্লেমিং করে। উদাহারস্বরূপ, Edmonds & Cahoon (১৯৮৬) এবং Kanekar & Koswala (১৯৮০) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সমাজ দ্বারা প্রকাশ্য পোশাকের ভিত্তিতে ধর্ষণের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করাটা বেশ সাধারণ। [1] [2] এমনকি Whatley (১৯৯৬) অনুযায়ী ধর্ষণের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করার ক্ষেত্রে, সেই ভুক্তভোগীর পোশাক অন্যান্য সকল ফ্যাক্টরের তুলনায় মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। [3] Whatley (১৯৯৪) আরো দেখেছেন যে যারা নারী-বিদ্ধেষী মানসিকতা পোষণ করে, তারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করে থাকে, সেসব মানুষদের তুলনায় যারা নারীদের প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে। [4] Simonson & Subich (১৯৯৯)-ও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে যারা যৌনতা সম্পর্কে প্রথাগত/সাংস্কৃতিক/রক্ষণশীল/conservative ধারণা রাখে, তারাই নারী ভিক্টিমদের উপরে দোষ দেয়। [5] এর পাশাপাশি Whatley (২০০৫) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে মানুষ বৈবাহিক ধর্ষণের ভুক্তভোগীদেরকেও দোষারোপ করে থাকবে যদি তারা জানতে পারে যে তারা ধর্ষণের সময় প্রকাশ্য পোশাক পরে ছিল। [6]
যারা পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলে থাকে, তারা কখনোই jeans, T-shirt, suit ইত্যাদি জাতীয় পোশাকের কথা বলে না, বরং miniskirt, shorts, tank tops জাতীয় পোশাকের বিরুদ্ধেই তাদের মূল আপত্তি থেকে থাকে। যেন এরা মনে করে যে ধর্ষণের অর্থ হলো যখন কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার পোশাক ছিড়ে, পোশাকের সাথে চুম্মা-চাট্টি শুরু করে দেয়। যারা পোশাককে ধর্ষণের “কারণ” বলে, তারা প্রায়শই সমাজের পোশাক সম্পর্কে উপলব্ধি তুলে ধরে বলে, “এইযে দেখসোস ভাই দেখসোস! মানুষ পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলে মনে করে, এবং তাই, পোশাক ধর্ষণের কারণ।”
এখন ধরে নেন পৃথিবীতে এক হাজার কোটি মানুষ একসাথে বললো, “আমরা যখন ঘুমাতে যাই, তখন সূর্য অস্ত যায়। এবং তাই, আমাদের ঘুমাতে যাওয়া হলো সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণ।” সেই ক্ষেত্রে আমরা কি সেই এক হাজার কোটি মানুষের ঘুমাতে যাওয়াকে সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণ হিসাবে মেনে নিবো? সমাজের পোশাক সম্পর্কে উপলব্ধি পোশাককে ধর্ষণের কারণ হিসাবে কোনোভাবেই প্রমান করে না। বরং, তা খালি দেখায় যে সমাজের ভিক্টিম-ব্লেমিং করার প্রবণতা রয়েছে, এবং শুধুমাত্র দেখায় যে সমাজ প্রকাশ্য পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলে মনে করে।
নারীদের শরীরকে ধর্ষণের “কারণ” বলা
পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলার একটি মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্ষণকারীর বাহিরে ধর্ষণের কারণকে প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু কোনো ধর্ষক পোশাককে উপভোগ করার উদ্দেশ্যে বর্ষণ করে না, ধর্ষণকারীর পরিবর্তে পোশাককে ধর্ষণের “কারণ” বলার মাধ্যমে নারীদের শরীরকে ধর্ষণের কারণ বলে উপস্থাপনা করা হয়। নারীদের শরীরকে ধর্ষণের কারণ বলার মাধ্যমে জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নারীদের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করা বৈধ হয়ে যায়। এর ফলে, নারীদের ব্যক্তিগত মনুষ্য কর্মক্ষমতা (agency) সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।
“ The absence of a developed rapist character results in a focus on and pathologising of female characters. This positions female bodies as the cause of rape, rather than societal problems or rapists themselves, creating ‘rape spaces’. The positioning of female bodies as the cause of rape sanctions public and state control of those bodies, removing a female’s subjective agency and right to manage her own body.” [7]
ধর্ষণ সম্পর্কিত উপকথা এবং ভিক্টিম ব্লেমিং
“Rape Myth”-এর সংজ্ঞা
“Rape Myth” হলো ধর্ষণ সম্পর্কে সেসব বিশ্বাস যা ভিক্টিমের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়, এবং যা ধর্ষণকারীর কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে দোষ মুছে ফেলে। “Female precipitation” হচ্ছে সবথেকে সাধারণ rape myth, কারণ তা ধর্ষণের জন্যে সরাসরি ভিক্টিমকে দায়ী করে। Female precipitation হলো সেই বিশ্বাস যে ধর্ষণ হলো ভিক্টিমদের দ্বারা কোনোভাবে উৎসাহিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ, এমন বিশ্বাস যে ভিক্টিমটি অনিরাপদ আচরণ (যেমন মদ্যপান) অথবা তার পোশাকের মাধ্যমে ধর্ষণকে উৎসাহিত করেছিল।
আরেকটি সাধারণ rape myth হলো এমন ধারণা যে পুরুষরা তাদের যৌন আবেগ সামলাইতে পারে না। পুরুষদের যৌনতা একটি rape myth হিসাবে কাজ করে। কেননা যদিও তা ধর্ষণের কারণকে ধর্ষণকারীর মধ্যে অবস্থিত করে, তা একই সাথে ধারণ করে যে পুরুষরা তাদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং তাই, নারীরা যদি ধর্ষণ থামাতে যায়, তাহলে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
“Rape myths are those beliefs about rape that function to blame the victim and exonerate the rapist [8]. Female precipitation is the most common rape myth because it directly holds the victim responsible for the rape. Female precipitation is the belief that the rape was provoked in some way by the victim, e.g., by the victim engaging in unsafe behaviors (such as drinking), by how she dressed, or by how she generally behaved.
Another common rape myth is the idea that men cannot control their sexual urges [9]. Male sexuality functions more indirectly as a rape myth because, although it places the cause of rape in the perpetrator, it proposes that men cannot control their sexual urges, making women responsible for preventing rape.” [10]
Rape Myth সর্বপ্রথম Burt (১৯৮০) দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল- “ধর্ষণ, ধর্ষণের ভিক্টিম, এবং ধর্ষণকারীদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক, বাঁধাধরা অথবা মিথ্যা বিশ্বাস।” যদিও এই সংজ্ঞাটি বর্ণনামূলক, এটি একটি formal definition হিসাবে বিবেচনা করার মতন যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বাসগুলি কাদের বিরুদ্ধে এবং কিভাবে বৈষম্যমূলক? এখানে একটি মৌলিক বিষয় হলো “myth” শব্দটি দ্বারা কি বুঝানো হচ্ছে। বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলার দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করলে “myth” শব্দটির প্রকৃতি এবং function প্রকাশ পায়। বিশেষ করে, “Myth”-এর তিনটি বৈশিষ্ট দেখা যায়-
১) বিশ্বাসগুলি মিথ্যা অথবা বিশ্বাসগুলির সত্যতা সন্দেহজক, এবং ব্যাপক সংখ্যার মানুষ সেই বিশ্বাসগুলিকে পোষণ করে।
২) বিশ্বাসগুলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করছে।
৩) বিশ্বাসগুলো বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে ন্যায্যতা দেয়।
এই বিশ্লেষণ যখন ধর্ষণের সাংস্কৃতিক থিওরির সাথে মিলিত করা হয়, তখন Rape Myth-এর একটি পরিষ্কার সংজ্ঞা প্রস্তাব করা যায়। Rape Myths হলো সেসব মনোভব এবং বিশ্বাস যেগুলো সাধারণত মিথ্যা কিন্তু তবুও ব্যাপক সংখ্যার মানুষ সেই বিশ্বাসগুলিকে পোষণ করে, এবং যেগুলো নারীদের বিরুদ্ধে পুরুষদের আগ্রাসন-কে অস্বীকার করে এবং ন্যায্যতা দেয়।
Rape Myth-কে বাঁধাধরা ধারণা/stereotype হিসাবে সবথেকে ভালো ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যান্য stereotype-এর মতন, যৌন আক্রমণের কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা Rape Myth-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। শুধুমাত্র সেসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হয়, যেগুলি myth-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে, myth-এর বিপরীতে অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনাগুলি যা সেই myth-কে contradict করে, সেগুলো সম্পূর্ণবাবে উপেক্ষা করা হয়। একই সাথে, অনেকগুলো myth কোনোভাবেই যাচাই করা যায় না, যেমন এই বাক্যটি- “অনেক নারীদের ধর্ষিত হওয়ার একটি অবচেতন চাহিদা আছে।” এই myth-গুলির সত্যতার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে এই myth-গুলো সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা হয়, এবং বিচারকের রায়, পাবলিক নীতি এবং যৌন আক্রমণের ভিক্টিমদের সাথে মানুষের আচরণে myth-গুলির প্রতিফলন হয়। [11]
“ভিক্টিম ব্লেমিং”-এর সংজ্ঞা
ভিক্টিম ব্লেমিং বলতে বোঝায়- “হিংস্রতা বা অবিচারের শিকার কোন মানুষকে তার সাথে ঘটা অপরাধের জন্য দোষী বলা এবং এটি এমন একটি অস্ত্র যেটি ব্যবহার করা হয় সেই সকল মানুষদের বিরুদ্ধে যারা যেকোনো ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবিচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে।”
“Victim blaming refers to assigning fault to people who experience violence or wrongdoing and is used as a tool to discredit people of marginalized groups who speak out against microaggressions or any injustices.” [12]
মনোবিজ্ঞানীক সাহিত্যে ভিক্টিম ব্লেমিং বলতে বুঝায় সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে মানুষকে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা। ভিক্টিম ব্লেমিং ব্যক্তিগত স্তরে ঘটতে পারে (যেমন যৌনভাবে আক্রমণের স্বীকার হওয়ার জন্যে একজন নারীকে দোষী সাব্যস্ত করা) এবং একই সাথে সাম্প্রদায়িক/যৌথ সামাজিক পরিচয়ের স্তরেও ঘটতে পারে (যেমন অর্থনৈতিক ত্রুটির জন্যে আফ্রিকান-আমেরিকান সংস্কৃতিকে দোষী সাব্যস্ত করা)। ভিক্টিম ব্লেমিং-কে এক ধরণের testimonial injustice-এর রূপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেখানে পূর্বনির্ধারিত নেতিবাচক স্টেরিওটাইপের ভিত্তিতে ভিক্টিমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করা হয়। ভিক্টিম ব্লেমিং-এর মাধ্যমে একটি নেতিবাচক ফলাফলের দোষ ভিক্টিমের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়।
“In psychological literature, victim blaming is usually defined as fully or partially blaming people for their misfortunes [13]. However, victim blaming can occur on an individual level (e.g., blaming a woman for getting sexually assaulted) and collective social identity level (e.g., blaming African American culture for economic disparities) [14]. Victim blaming can be conceptualized as a form of testimonial injustice in which the victim’s credibility may be undermined by preconceived notions based on negative stereotypes. This process results in the placement of responsibility about an objectively negative outcome onto the victim.” [12]
পোশাককে ধর্ষণের কারণ বলে ভিক্টিমদের দায়ী করা
যৌন সহিংসতার কোনো ভিক্টিমকে তার নিজের victimization-এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা আমাদের বর্তমান সমাজের সাধারণ চর্চা। এই ধরণের বাঁধাধরা/স্টেরিওটিপিকাল উপলব্ধি বা মনোভাব “Rape Myth” নামে পরিচিত। Rape Myth এই ধারণাকে কেন্দ্র করে যে ভিক্টিমরা তাদের নিজেদের victimization-এ অবদান রাখে এবং তাই, তাদের উপরে হয়ে যাওয়া আক্রমণের জন্যে তাদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
ধর্ষকরা তাদের নিজেদের রক্ষার্থে এই জাতীয় দাবি প্রায়শই করে থাকে। এবং এই জাতীয় তর্ককে সমর্থন করতে আমাদের সমাজ বেশ ইচ্ছুক; এমনকি আগ্রহী। এবং যাদের উপরে আক্রমণটা করা হয়েছিল, তাদের কাঁধেই দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এভিডেন্স আমাদেরকে দেখায় যে সাধারণ জনগণের মধ্যে এই ধরণের বৈষম্যমূলক বিশ্বাস অত্যন্ত প্রচলিত- জনসাধারণের প্রায় ৫০% “Rape Myth”-এর কোনো না কোনো রূপকে সমর্থন করে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে নারীদের তুলনায় পুরুষরা এই জাতীয় Rape Myth-কে আরো বেশি করে সমর্থন করে।
Rape Myth-এর সবথেকে প্রচলিত রূপ হলো যৌন সহিংসতা এবং ভিক্টিমের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। এই Rape Myth-এর পিছনে তর্কটি হলো যে নারীরা পুরুষদের Seduce করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে, এবং প্রকাশ্য পোশাকের মাধ্যমে নারীরা আসলে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদের ইচ্ছাকে যোগাযোগ করছে। পুরুষদেরকে Seduce করার অভিযুগে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে সেই নারীদেরকে তাদের উপরে হয়ে যাওয়া যৌন আক্রমণের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
“Blaming the victim of sexual violence for precipitating her own victimization is a rather common practice in present society [15]. These stereotyped attitudes, generally subsumed in the term “rape myths” [16], typically revolve around the notion that victims somehow contributed to their own victimization and are therefore responsible for its occurrence [17]. Perpetrators frequently use these claims in their defense, and society is all too willing, even eager, to cooperate with this line of argumentation and lay the bulk of the blame on those who were attacked. Evidence attests to a fairly wide acceptance of these prejudiced collective beliefs among the general population, with over 50% of the public endorsing them to some degree or another [18]. Significantly, men appear to endorse them to a considerably greater degree than women [19].
Among the most prevalent of these allegations is a charge linking sexual aggression to the victim’s so called “provocative”, revealing wear [20]. The premise behind this particular rape myth is that women dress in body-revealing attire in order to seduce men and convey an interest in sexual advances. This supposedly makes them culpable for any subsequent sexual invasions by the men they had allegedly seduced.” [21]
ধর্ষণের উপকথা: তুমি যদি মাগীর মতন পোশাক পরে থাকো, তুমি ধর্ষিত হবাই। তুমি যদি “মাগীর মতন পোশাক পরে” শহরে ঘুরতে বের হয়ে থাকো তাইলে তুমি ধর্ষণের শিকার হওয়ার জন্যে নিজেকে উপস্থাপনা করছো।
উপকথার খণ্ডন:
ক) এটাকেই বলে ভিক্টিম ব্লেমিং আর এইটা সম্পূর্ণভাবে বুলশিট (bullshit)।
খ) তুমি কি পোশাক পরে আছো তা নিয়ে কিছুই যায় আসে না, কেননা একটা পুরুষ যদি তোমাকে ধর্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, সে তোমাকে ধর্ষণ করবেই।
গ) বেশিরভাগ নারী এমন জায়গায় ধর্ষিত হয়েছিল যেখানে তারা পূর্বে নিরাপত্তা বোধ করতেন, এবং এমন পুরুষের দ্বারা তারা ধর্ষিত হয়েছিল যাদের উপরে সেই নারীদের পূর্ব আস্থা এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল। তাই, ধর্ষিত হওয়া এবং “মাগীর মতন পোশাক পরে” শহরে ঘুরতে যাওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
“Rape myth:
If you dress like a slut, you’ll get raped. Just by being out in town “dressed like a slut” (which is what, exactly? high heels? tight skirt? showing cleavage? spangles? a combination of the above?), you set yourself up as a target for rape.
Myth busted:
a) This is called victim blaming, and it is bullshit.
b) It doesn’t matter what you wear if a man decides he will rape you.
c) Most women are raped in places they felt safe by men they thought they could trust. So there is no real correlation between being out on the town (while dressed like a slut) and being a rape survivor.” [22] [23]
নারীরা প্রকাশ্য পোশাক কেন পরে?
প্রকাশ্য পোশাক পরার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১০ সালে Ashley Moor-এর গবেষণায় দেখা গেছিলো যে প্রায় ৬৩% নারী “প্রকাশ্য” পোশাক অন্তত কিছু কিছু সময় পরতো। এই ৬৩% নারীদের মধ্যে ৮২.১% নারী বলেছিলো যে এই জাতীয় পোশাক পরার পিছনে তাদের প্রধান কারণ ছিল যে তারা এই জাতীয় পোশাককে পছন্দ করে। ৭২% নারী এই জাতীয় পোশাক পরার পিছনে তাদের দ্বিতীয় কারণ হিসাবে দিয়েছিলো যে এই জাতীয় পোশাক তাদের সুন্দর লেগেছিলো। কেবলমাত্র ৩.২% নারী বলেছিলো যে তারা পুরুষদেরকে যৌনভাবে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে। এবং, শুধুমাত্র ৫.৩% বলেছিলো যে পুরুষদের সিডিউস করার উদ্দেশ্যে তারা প্রকাশ্য পোশাক পরে। ২.১% নারী বলেছিলো যে তারা এই জাতীয় পোশাক পরে যেন তাদের দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকে। এবং শুধুমাত্র ২.৩% নারী বলেছিলো যে অন্যদের দ্বারা স্পর্শ হওয়ার জন্যে তারা এরকম পোশাক পরে।
“In the direct assessment of the motivation for wearing revealing clothes, female participants who reported an inclination to dress in this fashion at least some of the time (63% of the female sample) were asked about their intentions in doing so. The majority of these women, 82.1%, identified a liking for this look as their primary motive for adopting it. A wish to look attractive was endorsed by 72% of the women as their second reason. Only 3.2% said they had intended to arouse men with their style of clothing, and the percentage of those who meant to seduce was a mere 5.3%. Very few women reported a desire to be touched or stared at as their motivation for dressing this way, 2.1% and 2.3% respectively.” [24]
বিভিন্ন ধররণের প্রশ্নাবলীর উত্তরে, নারীরা প্রকাশ্য পোশাক পরার পিছনে তারা প্রকাশ্য পোশাকের বিভিন্ন সামাজিক, আন্তঃব্যক্তিক, এবং ব্যক্তিগত সুবিধা তুলে ধরেছিলেন। প্রকাশ্য পোশাক পরার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসাবে তারা প্রকাশ্য পোশাকের আকর্ষণীয়তা এবং আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেছিলেন। পূর্ববর্তী গবেষণা এবং থিওরির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; নারীদের এই উত্তরগুলি দেখায় যে তাদের একটি sexualized appearance গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের সাথে তাদের মূল্যবান হওয়ার এবং মূল্যবান বোধ করার ইচ্ছা যুক্ত থাকে। [25] [26] [27] [28] কেননা, সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে নারীদের sexualized appearance এবং নারীদের বিবেচিত মূল্য একসাথে বাঁধা হয়। অন্যদিকে, অন্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বেশিরভাগ নারীদের প্রকাশ্য পোশাক পরার সিদ্ধান্তে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। তাই, নারীদের বিরুদ্ধে এই সাধারণ অভিযোগ যে প্রকাশ্য পোশাকের মাধ্যমে নারীরা আসলে তাদের উপরে যৌন সহিংসতা চেয়ে নিচ্ছে, তা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, কেননা নারীরা কখনোই এমন কোনো উদ্দেশ্য রিপোর্ট করে নাই। এটি ধর্ষণের ভিক্টিমদের অন্যান্য রিপোর্ট-এর সাথে মিলে যায়, যেখানে তারা জোর দিয়ে বলেন যে তাদের পোশাকের পিছনে তারা কোনো ভাবেই তাদের সাথে যৌন আচরণে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য ছিল না। [29]
নারীদের প্রকাশ্য পোশাক সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটি লিঙ্গ-ভিত্তিক উপলব্ধি এই ধারণাকে আরো শক্তিশালী করে তুলে। যেখানে নারী এবং পুরুষ উভয় প্রকাশ্য পোশাক-কে “sexy” এবং “আকর্ষণীয়” হিসাবে বিবেচনা করে, লিঙ্গগুলির মধ্যে যেখানে দ্বিমত, তা হলো নারীদের যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে। বেশির ভাগ পুরুষ মনে করে থাকে যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাক তাদের যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে যোগাযোগ করছে। তবে, বেশিরভাগ নারীদের জন্যে, তাদের প্রকাশ্য পোশাক কোনো ভাবেই যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে যোগাযোগ করে না। বরং, প্রকাশ্য পোশাকের মাধ্যমে নারীরা শুধুমাত্র অন্যদের আকর্ষণ করতে চায়। নারীরা সমর্থন করে যে পুরুষরা কিছু ক্ষেত্রে তাদের পোশাকে যৌন উত্তেজনা অনুভব করতে পারে, কিন্তু যৌন উত্তেজনা উৎসাহিত করা কখনোই তাদের লক্ষ্য থাকে না। বরং, অন্যদের যৌন উত্তেজনা নারীদের কাছে অন্যান্য লক্ষ্যে পৌঁছানোর ফলাফল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, মূলত-
১) একটি নির্দিষ্ট পুরুষকে আকর্ষণ করতে (একাধিক পুরুষদের নয়) এবং
২) যেন তারা নিজেরা মূল্যবান বোধ করে।
নারীদের কাছে, পুরুষরা তাদের পোশাকের কারণে যা যৌন উদ্দীপনা অনুভব করে, তা শুধুমাত্র নারীদের সৌন্দর্যের নিশ্চয়তা হিসাবে তাদের নিজেদের দ্বারা বিবেচনা করা হয়। নারীদের লক্ষ্য কখনো এটি নয় যে তাদের দিকে যেন অন্যরা সীমাহীনভাবে তাকিয়ে থাকে, অথবা চোখ দিয়ে ধর্ষণ করে। একই সাথে নারীরা কখনোই চায় না যেন অন্যরা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পরে। অন্য কোথায়, নারীরা কখনোই sex object/যৌন ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার হতে চান না।
তবে আমরা এমন একটি নিপীড়নমূলক সমাজে বাশ করি যেখানে পুরুষদের যৌন উপভোগের জন্যে নারীদেরকে sex object/যৌন ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি এবং উৎসাহ পায়। [30] [31]
একই সাথে, আমাদের সমাজে নারীদের sexualized appearance তাদের সামাজিক মূল্যের সাথে যুক্ত থাকে। [25] [32] [33] ফলস্বরূপ, এটি মোটেও আশ্চর্যজনক নয় যে নারীরা এই সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সামাজিক প্রত্যাশার সাথে নিজিদের মিলিয়ে নিয়ে একটি sexualized appearance গ্রহণ করে। [24]
পুরুষরা নারীদের পোশাক-কে কিভাবে করে দেখে?
সেই একই গবেষণায় Ashley Moor নারীদের পোশাক সম্পর্কে পুরুষদের উপলব্ধি এবং ধারণা যাচাই করেছেন, এবং দেখতে চেয়েছেন যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে সম্মুখীন হয়ে পুরুষরা কি ধরণের প্রক্রিয়া করে। বেশিরভাগ পুরুষ মনে করে থাকে যে নারীরা তাদেরকে যৌনভাবে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে। ৩০.৬% পুরুষ মনে করে থাকে যে নারীরা তাদেরকে যৌনভাবে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে। ২০.২% পুরুষ মনে করে থাকে যে নারীরা তাদের সাথে যৌন আচরণে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে। নারীদের প্রকাশ্য পোশাকে পুরুষদের যৌন উত্তেজনা এবং যৌন উত্তেজনার মাত্রাও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ২৯.৮% পুরুষ বলেছিলো যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাকে তারা সর্বক্ষেত্রে যৌনভাবে উত্তেজিত হয়। ৫৮.১% পুরুষ বলেছিলো যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাকে তারা বেশির ভাগ সময় যৌনভাবে উত্তেজিত হয়ে থাকে। ৪৮.৪৫% পুরুষ সর্বক্ষেত্রে নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে যখন সেই নারীরা প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে। একই সাথে ৪৬.১% পুরুষ বেশির ভাগ সময় নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে যখন সেই নারীরা প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে।
“In response to direct questioning regarding their perceptions of women’s sexualized appearance, men expressed a belief that temptation and seduction are the primary intentions of women who dress that way. To the questions of whether they assumed that women dressed in sexy clothing were trying to arouse them or elicit sexual advances from them, 30.6% and 20.2% respectively stated that those were uniformly the intentions, in their opinion. An additional 53.2% and 55.6% thought those were the intentions most of the time.
The men were also asked to indicate the degree to which they felt sexually aroused by women’s revealing attire. Close to thirty percent (29.8%) reported feeling aroused all of the time when viewing women in revealing clothes and an additional 58.1% felt aroused most of the time. In addition, most men expressed enjoyment in gazing at women so dressed; 48.45 felt that way all of the time and an additional 46.1% almost always, and similar proportions of the male participants (35.8% and 55.3% respectively) expressed a liking of this form of dress (See table 1).” [24]
পোশাক এবং যৌন নির্যাতনের মধ্যে কোনো “Correlation” বা “Causal” সম্পর্ক নেই
এর পাশাপাশি, Ashley Moor-এর এই গবেষণায়, পোশাকের স্টাইল এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার মাত্রা নির্ধারণ করার জন্যে বেশ কয়েকটি analysis/এনালাইসিস করা হয়েছিল। প্রথমটি দেখেছিলো যে যেসব নারীরা প্রকাশ্য পোশাক পরে, তারা কি অন্য নারীদের তুলনায় বেশি মাত্রায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয় কি হয় না (অর্থাৎ সেসব নারীদের তুলনায় যারা প্রকাশ্য পোশাক পরে না)। দ্বিতীয়টি দেখেছিলো যে পুরুষরা মনে করে কি করে না যে প্রকাশ্য পোশাক পরা নারীদের উপর যৌন অগ্রগতির বৈধতা দেয়। একইসাথে তা দেখেছিলো যে প্রকাশ্যে পোশাকের কারণে পুরুষদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষয় হয় কি হয় না।
প্রথম এনালাইসিস-এর জন্যে পোশাকের স্টাইল এবং যৌন নির্যাতন-এর মাঝে একটি Pearson Correlation Analysis করা হয়েছিল। প্রকাশ্য পোশাক এবং সকল ধরণের যৌন নির্যাতনের সাথে কোনো ধরণের Correlation-এর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেলো না। Appearance-এর ভিত্তিতে একটি Distribution Analysis-এর মাধ্যমে দেখা গেছে যে যেসব নারীরা যৌন নির্যাতনের ভিক্টিম এনং যেসব নারীরা যৌন নির্যাতনের ভিক্টিম নয়, তারা উভয় একই মাত্রায় প্রকাশ্য পোশাক পরার প্রবণতা প্রকাশ করে। যেসব নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেলো, তাদের মধ্যে ৬০%-৬৪% নারী কিছু কিছু সময়ে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকতো। একই সাথে যেসব নারীরা কখনোই যৌন নির্যাতনের শিকার হয় নাই, তাদের মধ্যেও ৬৩%-৬৫% নারী কিছু কিছু সময় প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকতো।
“Several analyses were conducted to examine the relations between style of dress and sexual victimization. The first was aimed at ascertaining whether women who dress revealingly experience more sexual violence than those who do not; the second checked whether men believe that such attire legitimizes sexual advances on the one hand, and causes men to lose self-control, on the other.
To test the first question, a Pearson correlation analysis between style of dress and victimization was performed. As can be seen in Table 4, no correlation was found between a revealing form of dress and any type of sexual victimization. In addition, a distribution analysis of victims of sexual violence by type of appearance demonstrated that the percentage of women who reported an inclination to wear sexy clothing was practically identical among victims and non-victims of sexual violations. Between 60- 64% of the former reported wearing such attire from time to time in comparison to 63- 65% of the women who were never victimized.” [24]
স্ট্যাটিসটিকাল পরীক্ষার ফলাফল
পোশাকের স্টাইল এবং যৌন আক্রমণের ভুক্তভোগী হওয়ার মাত্রার উপর Pearson Correlation Analysis-এর ফলাফল নিম্নলিখিত-
জোরপূর্বক যৌন সঙ্গম- 0.050
জোরপূর্বক যৌন যোগাযোগ- 0.035
অবাঞ্ছিত যৌন স্পর্শ- 0.005
অবাঞ্ছিত যৌন মন্তব্য- 0.054
সকল ফলাফল এখানে non-significant। অর্থাৎ, এই ফলাফল আমাদেরকে দেখায় যে যৌন আক্রমণের ভুক্তভোগী হওয়ার সাথে পোশাকের স্টাইল-এর কোনো সম্পর্ক নেই- হোক সেটা Causal সম্পর্ক অথবা এমনকি Correlation-এর সম্পর্ক। [24]
“পোশাক ধর্ষণের কারণ”- ধারণাটি অবাস্তবিক
এই অভিযোগ যে প্রকাশ্য পোশাক পরার মাধ্যমে নারীরা তাদের উপরে যৌন আক্রমণ চেয়ে নিচ্ছে- তা সম্পূর্ণভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। একই সাথে এই অভিযোগটি রিসার্চের মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে খন্ডন করা হয়েছে, যা আমাদেরকে দেখায় যে পোশাকের স্টাইল এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার মাত্রার সাথে কোনো ধরণের Correlation-এর সম্পর্ক নেই।
“Not only is the accusation that in wearing revealing clothing women are asking for sexual intrusion inconsistent, on the whole, with the present findings, it also seems to be factually refuted by the lack of correlation between sexual victimization and style of dress documented in this study. According to the findings, there is absolutely no connection between appearance and the occurrence of sexual violence, which necessarily refutes the claims embodied in the provocatively dressed victim-blaming myths. In other words, inasmuch as no significant differences were found between victims and nonvictims in their style of dress, it becomes clear that women do not bring sexual violence upon themselves by wearing revealing clothes. This finding resonates with similar claims made in many previous studies in which the validity of these charges have been questioned and disproved [34].” [24]
ভিক্টিম ব্লেমিং-এর মধ্যে পুরুষদের যৌন উত্তেজনার ভূমিকা
Ashley Moore-এর গবেষণা থেকে আমরা দেখতে পারি যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাক পরার উদ্দেশ্য এবং নারীদের প্রকাশ্য পোশাক সম্পর্কে পুরুষদের উপলব্ধির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একই সাথে, নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে সম্মুখীন হয়ে পুরুষরা যেইভাবে আচরণ করে, তা কোনোভাবে নারীদের উদ্দেশ্যের সাথে মিলে না। পুরুষরা বেশি মাত্রায় নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে যৌনতার ধারণা যুক্ত করে থাকে, এবং তাই পুরুষরা নারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল উপলব্ধি করে। যেখানে কেবলমাত্র ৩.২% নারী পুরুষদেরকে যৌনভাবে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পরে বলে রিপোর্ট করেছে; ৫৩.২% পুরুষ ভুলভাবে উপলব্ধি করে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নারীরা যৌনভাবে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে। এর পাশাপাশি, যেখানে শুধুমাত্র ৫.৩% নারী পুরুষদেরকে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে বলে রিপোর্ট করেছে, ৫৫.৬% পুরুষ ভুলভাবে উপলব্ধি করে যে নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকে। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে পুরুষদের নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে নারীদের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে ভুলভাবে যুক্ত করার প্রবণতা রয়েছে। অন্যদিকে, বেশিরভাগ নারীদের ক্ষেত্রে, তাদের প্রকাশ্য পোশাক পরার সাথে তাদের যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছা যুক্ত থাকে না। পুরুষরা একইসাথে নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের সাথে সম্মুখীন হয়ে উল্লেখিত মাত্রায় যৌন উত্তেজনা অনুভব করেছে বলে রিপোর্ট করে। ২৯.৮% পুরুষ রিপোর্ট করেছে যে তারা “সর্বক্ষেত্রে” প্রকাশ্য পোশাকের পরিপ্রেক্ষিতে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে, এবং ৫৮.১% পুরুষ রিপোর্ট করেছে যে তারা “বেশিরভাগ ক্ষেত্রে” নারীদের প্রকাশ্য পোশাকের পরিপ্রেক্ষিতে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে। একই সাথে, কেবলমাত্র ২.৩% নারী রিপোর্ট করেছে যে তাদের প্রকাশ্য পোশাক পরার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল তাদের দিকে যেন মানুষ তাকিয়ে থাকে, ৪৮.৪৫% পুরুষ রিপোর্ট করেছে যে তারা সবসময় প্রকাশ্য পোশাক পরা নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে।
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে- পুরুষরা নারীদের প্রকাশ্য পোশাক পরার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না কেন?
যেহেতু পুরুষরা প্রকাশ্য পোশাকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে, এই যৌন উদ্দীপনা হলো সেই ভিত্তি যার উপরে পুরুষরা নারীদের উদ্দেশ্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। পুরুষদের নিজেদের যৌন লালসা তাদের লালসার বিষয়ের উপরে চাপিয়ে দিয়ে তারা ভুলভাবে একটি স্বার্থপর উপসংহারে পৌঁছায় যে যেহেতু তারা যৌনভাবে উত্তেজিত হয়েছে, তা নিশ্চই সেই নারীটার লক্ষ্য ছিল। Ashley Moor-এর এই গবেষণার মধ্যে পুরুষদের যৌন উত্তেজনা এবং নারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরুষদের ভুল ব্যাখ্যার শক্তিশালী পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা এই ধারণাটি প্রমাণিত হয়। যেহেতু প্রকাশ্য পোশাকের পরিপ্রেক্ষিতে যৌন উত্তেজনা অনুভব করা পুরুষদের মাত্রা এবং নারীদের পোশাক-কে ভুলভাবে seduction হিসাবে পুরুষদের বিবেচনা করার মাত্রা প্রায় সমতুল্য; এটি ইঙ্গিত দেয় যে হয়তো পুরুষদের যৌন উত্তেজনার কারণেই তারা ভুলভাবে নারীদের প্রকাশ্য পোশাক-কে seduction হিসাবে বিবেচনা করে। উল্টা-টি যদিও সম্পূর্ণভাবে রিজেক্ট করা যায় না, এটি প্রমান করা খুবই কঠিন যে যেহেতু পুরুষরা বিশ্বাস করে যে নারীরা প্রকাশ্য পোশাক তাদেরকে সিডিউস করার উদ্দেশ্যে পরে, তাই তারা যৌন উত্তেজনা অনুভব করে।
নারীদের উদ্দেশ্যের এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে অবাঞ্চিত যৌন যোগাযোগের ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করা হয়। নারীদের উপরে যৌন লালসা চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতার কারণে, পুরুষদের জন্যে এটি কঠিন হয়ে পরে যে তারা নিজেদেরকে নারীদের সম্মতি লঙ্ঘন করার জন্যে দোষারোপ করবে। কেননা পুরুষরা মনে করে যে তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে সিডিউস করা হয়েছে। তাছাড়া, এটি ব্যাখ্যা করে যে নারীদের তুওলনায় পুরুষদের মধ্যে ভিক্টিম ব্লেমিং করার প্রবণতা ব্যাপখাবে বেশি। অন্যদিকে, নারীরা যখন sexualized look-এর পিছনে অন্যদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে (যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের যৌন ইচ্ছার সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত নয়), তাদের মধ্যে এই নির্দিষ্ট ধরণের ভিক্টিম ব্লেমিং করার সম্ভাবনা কমে যায়।
“Inasmuch as men are highly aroused by the revealing look, it stands to reason that this very stimulation may be the basis for their misconstruction of women’s aims. In essence, men may be projecting their own arousal onto the object of their lust, erroneously concluding, in a rather self-centered manner, that since they have become aroused this must have been her goal. Indeed the significant correlations between these two sets of variables in the present investigation seem to substantiate such a supposition. The fact that the percentage of men who reported being aroused by the revealing look and those who perceived seduction in this type of appearance are almost entirely identical seems to imply that the former may in fact be responsible for the latter. This claim is especially conceivable given that it would be quite difficult to make a case for the opposite direction of causality, as it is hard to see how believing that the exposed apparel is intended to arouse would cause such a response, although such directionality cannot be entirely rejected by the present investigation.
Such misconstruction of motivation may then result in blaming the victims of unwanted sexual exchanges. To the extent that such projection indeed occurs, it may make it difficult for those men who experience it to place the responsibility for women’s sexual violation upon those whom they believe were deliberately seduced. Moreover, it can explain why such victim-blaming is a lot more rampant among men than among women [35]. Inasmuch as women have a clear understanding of the genuine motives underlying the sexualized look, all of which have very little to do with an outright interest in sex, their likelihood of endorsing this line of victim-blaming is much diminished in comparison to men.” [24]
ধর্ষণের ভিক্টিমরা কিরকম পোশাক পরে?
What Were You Wearing একটি এক্সহিবিট যা এই সাধারণ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে প্রকাশ্য পোশাক আসলে ধর্ষণের কারণ। ধর্ষণের ভিক্টিমদের নিজেদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার পাশাপাশি, What Were You Wearing দেখায় যে ধর্ষণের ভিক্টিমরা কি ধরণের পোশাক পরে ছিল যখন তাদের উপরে আক্রমণটা হয়েছিল। এটি সর্বপ্রথম ২০১৪ সালে থেকে University of Akransas-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে এই এক্সহিবিট-টি বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। [36] এমনকি, এই এক্সহিবিট-টি United Nations দ্বারাও প্রকাশিত হয়েছিল। [37] এই এক্সহিবিট-এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে নারীরা যেই ধরণের পোশাক পরে থাকুক না কেন, তারা পুরুষদের দ্বারা ধর্ষিত হয়, এবং বেশির ভাগ সময়, নারীরা তাদের সমাজে বিবেচিত “শালীন” পোশাক পরা থাকা অবস্থায় ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। এক্সহিবিট থেকে কয়েকটা ধর্ষণের ভিক্টিমদের পোশাক নিচে দেখানো হয়েছে।
খাকি কাপড়ের প্যান্ট এবং একটি ড্রেস শার্ট- “সেদিন আমার কমিউনিকেশনস ক্লাসের জন্যে একটা প্রেসেন্টেশন দিতে হয়েছিল। হাসপাতালে ধর্ষণ আসলে হয়েছিল নাকি না, তা পরীক্ষা করার সময় আমার পোশাকগুলো তারা নিয়ে গিয়েছিলো। আমি ঠিক জানি না পরবর্তীতে সেই পোশাকগুলোর কি হয়েছিল।”
হলুদ রঙের শার্ট- “সেটা আমার সবথেকে প্রিয় হলুদ রঙের শার্ট ছিল। কিন্তু আমার ঠিক মনে নাই আমি কি ধরণের প্যান্ট পরে ছিলাম। আমার খালি মনে আছে যে আমি অত্যন্ত বিভ্রন্ত বোধ করছিলাম। আমি আমার ভাইয়ের রুম থেকে বের হতে চাচ্ছিলাম এবং আমার কার্টুন দেখায় ফেরত যেতে চাচ্ছিলাম।”
টি-শার্ট এবং জিন্স-এর প্যান্ট- “আমার জীবনে তা [ধর্ষণ] ঘটে গেছে তিনবার, তিনটি ভিন্ন মানুষের দ্বারা। প্রত্যেকবার আমি টি-শার্ট আর জিন্স-এর প্যান্ট পরে ছিলাম।”
টি-শার্ট এবং জিন্স-এর প্যান্ট- “আমার সাথে তা [ধর্ষণ] ঘটে যাওয়ার পর আমি কয়েকদিন অফিস-এ যেতে পারি নাই। আমি যখন আমার বস-কে বলি যে আমার সাথে আসলে কি হয়েছিল, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি ধরণের পোশাক পরে ছিলা?’ আমি উত্তরে বললাম, ‘টি-শার্ট এবং জিন্স-এর প্যান্ট, শালা কুত্তা কোথাকার। বাস্কেটবল খেলার সময় মানুষ আর কি পরবে?’ আমি এরপর বের হয়ে চলে গেলাম এবং সেখানে আর জীবনেও ফেরত যাই নাই।”
বিকিনি/সুইমসুট- “আমরা সারাদিন নদীতে নৌকা চালাচ্ছিলাম। বেশ মজাদার একটা সময় যাচ্ছিলো। এরপরে তারা আমার টেন্ট-এর মধ্যে চলে আসে যখন আমি আমার পোশাক পাল্টাচ্ছিলাম।”
ইউনিভার্সিটি টি-শার্ট এবং কার্গো প্যান্ট- “এটা আসলে হাস্যকর যে কেউ আমাকে কখনোই জিজ্ঞেস করে নাই যে আমি কি ধরণের পোশাক পরে ছিলাম। বরং তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে যেহেতু আমি ধর্ষিত হয়েছি, তার মানে কি আমি আসলে একজন সমকামী? অথবা তারা জিজ্ঞেস করে আমি কি [ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে] লড়াই করার চেষ্টা করেছিলাম নাকি না। অথবা তারা জিজ্ঞেস করে কিভাবে সেটা [ধর্ষণ] আমি আমার উপরে হতে দিলাম। কিন্তু তারা কখনোই আমার পোশাকের কথা জিজ্ঞেস করে না।”
শাড়ী- “আমি একটা শাড়ী পরে ছিলাম। সেই একই পোশাক যা আমি বেশির ভাগ সময় পরে থাকতাম। শাড়ী পরতে আমার বেশ আরাম বোধ লাগতো। সেটা আমাকে আমার বাড়ি, পরিবার এবং পরিচয়ের কথা মনে করিয়ে দিতো। এখন শুধুমাত্র সেটা আমাকে সেই পুরুষের [ধর্ষণকারীর] কথা মনে করিয়ে দেয়।”
সেনাবাহিনীর যুদ্ধের ইউনিফর্ম- “সেনাবাহিনীর যুদ্ধের ইউনিফর্ম-একই সাথে আমার কাছে একটা বন্দুক ছিল। তবে তা কিছুই থামাতে পারলো না।”
Attribution Theory এবং ভিক্টিম ব্লেমিং
Attribution- কোনো একটা জিনিসকে অন্য কোনো মানুষ বা জিনিসের কারণে ঘটেছে বলে মনে করা।
“Attribution (noun)- The action of regarding something as being caused by a person or thing.” [38]
ভিক্টিম ব্লেমিং-এর প্রক্রিয়াটি বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যে বেশ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন ধর্ষণের ভিক্টিমদের সম্পর্কে মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধি যাচাই করা হয় (নারী ভিক্টিমদের সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি)। [39] বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যের একটি বড় অংশ ধর্ষণের ভিক্টিমদের সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি যাচাই করে প্রকাশ করেছে যে যারা কোনো অপরাধের ভিক্টিম হয়, অন্য মানুষ তাদেরকে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাদের জন্যে তাদেরকেই দোষী বলে সাব্যস্ত করে। অপরাধের ভিক্টিমদের সাথে এই আশ্চর্জনক প্রক্রিয়া Attribution Theory দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। [40] একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ কিভাবে (অর্থাৎ কোন পদ্ধতির মাধ্যমে) অন্যদের প্রতি দোষ চাপিয়ে দেয়, বা অন্যদের দোষকে মানুষ কিভাবে বিবেচনা করে, তা সম্পর্কে Attribution Theory কথা বলে। রিসার্চ দেখায় যে ভিক্টিমদের প্রতি মানুষের এই দোষ চাপানোর প্রক্রিয়া বেশ নমনীয় এবং মানুষের বিভিন্ন ধরণের জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্দেশ্যমূলক bias/পক্ষপাতের দ্বারা প্রভাবিত। এই পক্ষপাতের ফলে, মানুষের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার একটি মিথ্যা ব্যাখ্যার সৃষ্টি হয়, যা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত নয়। [41] [42] [43] [44] যে সকল মানুষ একটি ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করছে, তারা তাদের ব্যক্তিত্বের স্বভাবের কারণে তাদের নিজেদের পক্ষপাতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই, ভিন্ন মানুষের দ্বারা একই ঘটনাকে তাদের নিজেদের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভিন্ন ভাবে বিবেচনা এবং ব্যাখ্যা করা হয়। ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য ভিক্টিমদের প্রতি মানুষের উপব্ধিকেও প্রভাবিত করে। [45] অতএব, বিভিন্ন ব্যক্তিগত, মানসিক এবং পরিস্থিতিগত ফ্যাক্টর দ্বারা অন্যদের উপরে মানুষের দোষ চাপানোর প্রক্রিয়াটি সংগঠিত।
Attribution Theory-এর মাধ্যমে, গবেষকরা বুঝতে পারে মানুষ কিভাবে অপরাধের ভিক্টিমদের উপলব্ধি করে। Fiske & Taylor (১৯৯১) অনুযায়ী- “সামাজিক অনুধাবনকারীরা কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করে কোনো কারণগত ব্যাখাতে পৌঁছায়, তা সম্পর্কে Attribution Theory কাজ করে। কোন ধরনের তথ্যগুলি মানুষের দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং কিভাবে মানুষ সেই তথ্যগুলি মিলিত করে কারণগত বিচারে পৌঁছায়, তা Attribution Theory যাচাই করে।” [46] অতএব, Attribution Theory মানুষে ইনফরমেশন প্রসেসর হিসাবে বর্ণনা করে যারা তথ্য সংগ্রহ করে কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে। [47] Attribution Theory ধারণ করে যে মানুষ তাদের জীবনের ঘটনাগুলি স্বেচ্ছায় ব্যাখ্যা করে, এবং ধারণ করে যে ঘটনা ব্যাখ্যা করার সময় তারা যৌক্তিক চিন্তার পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এটি মানুষকে তাদের চারিপাশের বিশ্বকে বুঝতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। [40] Heider (১৯৫৮) দুটি ধরণের Attribution-এর মধ্যে পাথক্য করেছে, মূলত-
১) Internal Attribution- অর্থাৎ, মানুষ যখন তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো বৈশিষ্টের কারণে একটি নির্দিষ্ট ভাবে আচরণ করছে।
২) External Attribution- অর্থাৎ, যখন কোনো মানুষ তাদের পরিস্থিতির কোনো বৈশিষ্টের কারণে একটি নির্দিষ্ট ভাবে আচরণ করছে।
এই দ্বিধাবিভক্তি যখন ধর্ষণের কোনো পরিস্থিতির উপরে প্রয়োগ করা হয়, তখন বলা যেতে পারে যে ভিক্টিমদের উপরে বেশি দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় যখন Internal Attribution ব্যবহার করা হয় (অর্থাৎ যখন ফোকাস ভিক্টিমের উপরে থাকে)। অন্যদিকে বলা যেতে পারে যে, ভিক্টিমদের উপরে কম দোষ চাপানো হয় যখন External Attribution ব্যবহার করা হয় (যখন ফোকাস ভিক্টিমের পরিবর্তিতে পরিস্থিতির উপরে থাকে)। [48]
ভিক্টিম ব্লেমিং-এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্যে, বিভিন্ন থিওরির প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি যা বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে, তা হলো Defensive Attribution Hypothesis। [49] [50] [51] [52] [53] এই Hypothesis অনুযাই, ভিক্টিমের সাথে বিবেচিত ঐক্যবদ্ধ এবং ভবিষ্যতে একই ভাবে শিকার হওয়ার সম্ভাবনার উপরে ভিত্তি করে ভিক্টিমের উপরে দোষ কমানো বা বাড়ানো হয়। Defensive Attributions প্রেডিক্ট করে যে পর্যবেক্ষক এবং ভিক্টিমের সাথে বিবেচিত ঐক্যবদ্ধ বাড়ার সাথে সাথে ভিক্টিমের প্রতি একটি নেতিবাচক উপলব্ধি কমে যাবে। এটি একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যেন ভবিষত্যে নিজের সাথে একই ঘটনা ঘটলে যেন দোষ চাপানো না হয়। ভিক্টিম ব্লেমিং সম্পর্কে আরেকটি জনপ্রিয় থিওরি হলো Just World Theory। [54] [55] এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পৃথিবীকে ভালো এবং ন্যায্য হিহাবে বিবেচনা করার জন্যে মানুষের একটি অনুপ্রেরণামূলক প্রয়োজন রয়েছে। তাই, অনেকেই মনে করে যে আচরণগত ফলাফল মানুষের জন্যে প্রাপ্য এবং ধারণ করে যে মানুষ যা পায়, সেটাই তারা পাওয়ার প্রাপ্য, এবং তারা যতটুকু পাওয়ার প্রাপ্য, ততটুকুই তারা পেয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মধ্যে পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকারিতার একটি অনুভূতিকে বজায় রাখে। যদি তারা মনে করতো যে মানুষের সাথে কারণ ছাড়াই খারাপ জিনিস হওয়া সম্ভব, সেটা পৃথিবীকে বিশৃঙ্খল হিসাবে প্রমাণিত করতো এবং মানুষের নিয়ন্ত্রনবোধের সাথে সংঘর্ষে আসতো। অন্যদিকে, তারা যদি ভিক্টিমকে এমনভাবে উপলব্ধ করে যে তারাই তাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে দোষী এবিং দায়ী, সেটা তাদের মধ্যে শৃঙ্খল, ভালো এবং ন্যায়সঙ্গত হিসাবে বিশ্বের আরামদায়ক দৃশ্যকে পুনরুদ্ধার করে।
রিসার্চ আমাদেরকে দেখায় যে ধর্ষণের ঘটনার অনেক ক্ষেত্রে, ভিক্টিম ব্লেমিং ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান। একটি অপরাদের ভিক্টিম হওয়ার সত্ত্বেও, ধর্ষণের ভিক্টিমদের উপরে এমন পরিমানের দোষ চাপানো হয় যে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ধর্ষণের জন্যে তাদেরকেই দায়ী করা হয়। [56] [49] [57] [58] [59] [60] ভিক্টিমের উপরে দোষের মাত্রা প্রয়োগ করার সাথে বিভিন্ন variable জড়িত যার মধ্যে রয়েছে- [61]
১) উপলব্ধিকারীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস।
২) ভিক্টিমের বৈশিষ্ট।
৩) পরিস্থিতিগত ফ্যাক্টর।
তাই, ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে পর্যবেক্ষকের দ্বারা দোষের প্রয়োগ অসীম সংখ্যার ফ্লাকচুএটিং ভেরিএবল দ্বারা প্রভাবিত, যা প্রত্যেক ঘটনার উপরে আলাদাভাবে এবং unpredictable পদ্ধতিতে প্রভাবিত করে। মানুষ কেন এবং কিসের ভিত্তিতে ভিক্টিম ব্লেমিং করে, তা বুঝার জন্যে আমাদের সেই সকল অবদানকারী ফ্যাক্টরের কথা বিবেচনা করতে হবে, যেগুলোর ফলে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ধর্ষণের ভিক্টিমদের ছোট করা হয়, এবং তাদের উপরে দোষ চাপানো হয়। [62]
Attribution Theory/এট্রিবিউশন থিওরির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে একটা ধর্ষণের ভিক্টিমের ধরণ, আকার ও পোশাক (অর্থাৎ appearance) সেই ভিক্টিমকে দোষী সাব্যস্ত করতে মানুষের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। Attribution/এট্রিবিউশন বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন মানুষ অন্যদের আচরণ বুঝার জন্যে এবং ব্যাখ্যা করার জন্যে সেই আচরণের কারণগত অনুমান (causal inference) করে থাকে। এই থিওরি অনুযায়ী, একজন ব্যক্তির আচরণ তাদের internal causes/আন্তরিক কারণ এবং তাদের external causes/বহিরাগত কারণ-এর জন্যে ঘটছে। আন্তরিক কারণ হলো সেসব কারণ যা একজন মানুষের প্রচেষ্টা এবং ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বহিরাগত কারণ হলো সেসব কারণ যা একজন মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে, যেমন একজন মানুষের পরিস্থিতি অথবা একজন মানুষের কারাপ/ভালো ভাগ্য। এট্রিবিউশন থিওরি দ্বারা ভিক্টিমের appearance-এর কারণে সেই ভিক্টিমকে অন্যরা কত পরিমানের দোষী সাব্যস্ত করবে, তা predict করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পোশাক পরা সর্বদা আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কর্মের কারণে সম্ভব হয়। একজন মানুষ মনে করতে পারে যে একজন ধর্ষণের ভিক্টিমের সাথে যা ঘটেছে সেটা আসলে সেই ভিক্টিমের আন্তরিক কারণে ঘটেছে। যেহেতু একজন ভিক্টিমের পোশাক সেই ভিক্টিমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই পরিস্থিতিতে বলা যেতে পারে যে একজন ভিক্টিমের পোশাকের জন্যে অন্যরা মনে করবে যে সেই ভিক্টিমটাই তার সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের “কারণ।” অর্থাৎ, ভিক্টিমের পোশাকের জন্যে ভিক্টিমের উপরে তার সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের জন্যে একটা attribution দেওয়া হবে। এর কারণে বলা যেতে পারে যে এমন একটা পরিস্থিতিতে একটা ধর্ষণের ভিক্টিমকে আরো বেশি দোষী সাব্যস্ত করা হবে।
“Attribution theory provides a framework within which to understand how the appearance of a rape victim may influence attributions of victim responsibility. Attribution refers to the process of how people make causal inferences in understanding and explaining others’ behavior [63]. According to the theory, the causes of an individual’s behavior can be attributed to internal causes (those causes seemingly under the control of an individual such as an individual’s effort or ability) or external causes (those not under the control of an individual such as an individual’s situation or bad/good luck). Attribution theory can be used to predict the potential effect of the appearance of a victim on attributions of victim responsibility. For example, a clothed appearance is generally assumed to be internally caused through effort or ability. If an individual believes that what happened to a rape victim had something to do with internal causes, then it could be predicted that the victim’s clothed appearance, assumed to be under the victim’s control, would influence attributions made about the victim. Consequently, it could be predicted the victim would be assigned significant responsibility for the rape.” [64]
Theory of Ambivalent Sexism এবং ভিক্টিম ব্লেমিং
ঐতিহ্যগত নারী-পুরুষ সম্পর্কের মৌলিক কাঠামোর দুটি বৈশিষ্ট বিবেচনা করুন-
১) পুরুষ এবং নারীদের লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান।
২) দুটি শ্রেণীর মানুষ একে অন্যের উপরে শক্তিশালীভাবে পরস্পর-নির্ভরশীল।
এর কারণে, লিঙ্গভিত্তিক মনোভব সর্বদা লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিধাদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। Glick & Fiske (১৯৯৬,১৯৯৯) [65] [66] এই প্রক্রিয়াকে “ambivalent sexism” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। বিশেষ করে, Theory of Ambivalent Sexism অনুযায়ী-
১) পুরুষদেরকে নারীদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা এবং মর্যাদা দেওয়া হয়।
২) নারী এবং পুরুষদেরকে তাদের সামাজিক ভূমিকা এবং বৈশিষ্টের ভিত্তিতে আলাদাপ্রাপ্ত করা হয়।
৩) যৌন প্রজনন এবং ঘনিষ্টতা নারী এবং পুরুষদের সম্পর্কের উপরে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা প্রভাব বিস্তার করে।
এই তিনটি ফ্যাক্টর “পুরুষতান্ত্রিকতা”, “লিঙ্গ-ভিত্তিক পার্থক্যকরণ” এবং “যৌন প্রজনন” বলে পরিচিত, যা লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীগুলোর মধ্যে শত্রুতা এবং স্নেহবোধ- উভয়ের জন্ম দেয়। [67] Ambivalent Sexism-এর চারটি ভিন্ন রূপের সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।
Hostile Sexism (HS) হলো (নারীদের প্রেক্ষাপটে) লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্ককে প্রতিপক্ষের সম্পর্ক হিসাবে দেখা, যেখানে নারীদেরকে এমনভাবে উপলব্ধি করা হয় যেন তারা পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, এবং যেখানে বিবেচনা করা হয় যে নারীরা পুরুষদের ক্ষমতা দখল করতে চায়।
Benevolent Sexism (BS) হলো নারীদেরকে আদর্শিক, বিশুদ্ধ প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করা, যাদেরকে সুরক্ষিত রাখা উচিত এবং সাপোর্ট করা উচিত এবং মনে করা যে নারীদের ভালোবাসা একটা পুরুষকে সম্পূর্ণ করে। তবে এটি, ধারণ করে যে নারীরা দুর্বল এবং শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত লিঙ্গিক ভূমিকার জন্যেই উপযুক্ত।
Hostility toward men (HM) পুরুষদের অধিপত্য এবং ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের উপরে তিক্ততাকে বোঝায়।
Benevolence toward men (BM) হলো পুরুষদের প্রতি আপেক্ষিক ইতিবাচক মনোভব, যা রক্ষাকারী এবং প্রদানকারী হিসাবে পুরুষদের ঐতিহ্যগত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার প্রশংসার উপরে ভিত্তি করা। একই সাথে এটি সেই সকল বিশ্বাসকে অন্তুর্ভুক্ত করে যে পুরুষদের গার্হস্থ্য এবং মাতৃ যত্নের জন্যে নারীদের প্রয়োজন লাগে (উদাহরণ- বাড়িতে পুরুষদের যত্ন করা)।
এই তাত্ত্বিক কাঠামোর উপরে ভিত্তি করা গবেষণা পরামর্শ দেয় যে যেসব মানুষ সেক্সিস্ট মনোবাব পোষণ করে, তারা Rape Myths-কে বেশি মাত্রায় সমর্থন করে সেসব মানুষদের তুলনায় যারা সেক্সিস্ট মনোভব পোষণ করে না। যেসব মানুষ লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার অতিহ্যগত ধারণাকে সমর্থন করে, তাদের ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করার সম্ভাবনা বেশি সেসব মানুষদের তুলনায় যারা লিঙ্গ সম্পর্কিত অপ্রথাগত ধারণা পোষণ করে। [68] [69] [70] নারীদের প্রতি Ambivalent Sexism-এর মাত্রা যাচাই করার সময়, Abrams et. al, (২০০৩) প্রকাশ করেছিল যে যেসব মানুষের Benevolent sexism (BS)-এর মাত্রা বেশি, তাদের দ্বারা পরিচিত মানুষের হাতে ধর্ষিত হওয়া ভিক্টিমদের দোষারোপ করার সম্ভাবনা বেশি সেসব মানুষদের তুলনায় যাদের Benevolent Sexism (BS)-এর মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। একই গবেষণার মধ্যে, Benevolent Sexist-দের দ্বারা সেই পরিস্থিতিতে থাকা নারীকে এমনভাবে উপলন্ধি করা হয়েছিল যে সেই নারীটা লিঙ্গ-ভিত্তিক প্রথা লঙ্ঘন করার কারণে তারা আসলে দোষারোপের প্রাপ্য। বিপরীতে, সেই গবেষণায় দেখা গেছে যে Hostile Sexism (HS) যৌন সহিংসতাকে যুক্তিসঙ্গত হিসাবে উপস্থাপনা করতে কাজ করে, কেননা গবেষকরা Hostile Sexism (HS) এবং ধর্ষণ করার প্রবণতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। Canto et. al, (২০১৪)-এর Rape Myth Acceptance এবং Hostile Sexism (HS)-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকার গবেষণায় একই জিনিস দেখা গিয়েছিলো। বিশেষ করে, তারা খুঁজে পেয়েছিলো যে উভয় লিঙ্গের মধ্যে Rape Myth Acceptance-এর জন্যে, Hostile Sexism (HS) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী predictor। একই সাথে, নারীদের মধ্যে Benevolent Sexism (BS) তাদের Rape Myth Acceptance-এর জন্যে একটি predictor। [71]
পুরুষরা কেন পোশাক-কে ধর্ষণের “কারণ” বলে?
যেসব পুরুষদের ধর্ষণ করার সম্ভাবনা বেশি এবং যেসব পুরুষদের ধর্ষণ করার সম্ভাবনা কম, তাদের মধ্যে ধর্ষণ সম্পর্কিত ধারণা এবং মনোভবে কিছু পার্থক্য রয়েছে। পুরুষদের ধর্ষণ করার সম্ভাবনার সাথে তাদের পরিস্থিতিগত প্রাসঙ্গিকতা জড়িত। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে সেই পুরুষরা নিজেরা ধর্ষণ করতো নাকি না। যেসব পুরুষদের ধর্ষণ করার সম্ভাবনা বেশি, তারাই ধর্ষণকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করে এবং ধর্ষণকারীদের সমর্থন করে থাকে। একই সাথে, সেই পুরুষরা ধর্ষণের ভিক্টিমদের সমর্থন করে না। এই রিসার্চের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে একজন পুরুষের ধর্ষণ করার সম্ভাবনা যত বেশি হবে (অর্থাৎ যত বেশি পরিস্থিতিগত প্রাসঙ্গিকতা); সেই একই পুরুষ আরেকটি পুরুষ ধর্ষণকারীকে তত কম দোষী সাব্যস্ত করবে। একই সাথে একজন পুরুষ যত বেশি ধর্ষণকারীদের সমর্থন করে (অর্থাৎ যত বেশি ব্যক্তিগত প্রাসঙ্গিকতা); সেই একই পুরুষ ধর্ষণকারীদের কম দোষী সাব্যস্ত করবে এবং ভিক্টিমদের বেশি দোষী সাব্যস্ত করবে।
“Furthermore, attitudes toward rape, rape victims, rapists, and belief in rape myths differentiate between men who report the highest likelihood to rape and men who are less likely to rape [72]. A man’s likelihood to rape is analogous to situational relevance, the likelihood that such an event could happen to him. Men reporting the highest likelihood to rape had more accepting attitudes toward rape, rapists, and rape myths, but less accepting attitudes toward rape victims [73]. Based on these studies, it might be predicted that the greater a man’s likelihood to rape (greater situational relevance), the less responsibility he will attribute to a male perpetrator. Likewise, the more accepting a man’s attitudes toward rapists (i.e., greater personal relevance), the less responsibility he will attribute to a perpetrator and the more he will attribute to a victim.” [74]
অন্যান্য ফ্যাক্টরকে ধর্ষণের কারণ বলে ধর্ষণকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা
পুরুষদের Rape Myth-এর সমর্থন করা তাদের নিজেদের যৌন আগ্রাসনে জড়িত হওয়ার প্রবণতাকে ন্যায্যতা দিতে এবং যুক্তিসঙ্গত হিসাবে উপস্থাপনা করতে কাজ করে। এই ধরণের myth, যা ধর্ষণের জন্য নারীদেরকে দোষারোপ করে, যা ধর্ষণের দাবিকে অবিশ্বাস করে এবং যা অপরাধীকে নির্দোষ হিসাবে সাব্যস্ত করে, নারী এবং পুরুষদের মধ্যে ভিন্নভাবে কাজ করে। ধর্ষণের পৌরাণিক কাহিনীগুলি যৌন আগ্রাসনের অপরাধের জন্য নির্দেশক হিসাবে কাজ করতে পারে, যেমন-
১) যেসব নারীরা পুরুষদেরকে tease করে, প্রভোকেটিভ পোশাক পরে অথবা যৌনতায় লিপ্ত থাকে, তাদেরকে ধর্ষণ করা ন্যায়সঙ্গত।
২) নারীরা যখন “না” বলে তখন তারা আসলে “হ্যাঁ” যোগাযোগ করছে।
৩) নারীরা আসলে ধর্ষিত হতে চায়।
“For men, rape myth acceptance served as a “means to rationalize and justify their own tendencies to engage in sexual aggression” [75]. Thus, myths that blame women for rape, disbelieve claims of rape, and exonerate the perpetrator operate differently in women and men [76] [77]. Rape myths can also provide cautionary tales of what could happen when women are incautious or unguarded (e.g., women invite rape by engaging in overtly sexual behavior or wearing provocative dress; only certain women are raped— those who drink too much, sleep around, or hang out in the wrong places). Finally, rape myths can be used as guidelines or instructions for the perpetration of sexual aggression (e.g., it’s okay to rape women who tease men, dress provocatively, or engage in sexual behavior; women mean yes when they say no; and women want to be raped).” [78]
Right Wing Authoritarianism (RWA) এবং ভিক্টিম ব্লেমিং
লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ভিক্টিমদের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের জন্যে তাদেরকেই আংশিকভাবে দোষী হিসাবে উপলব্ধি করা বেশ প্রচলিত একটা ঘটনা। গবেষকরা অনেক পরিশ্রম খাটিয়ে ভিক্টিম ব্লেমিং এর অবদানকারী ভ্যারিয়েবলগুলি আলাদাপ্রাপ্ত করেছে। [62] [79] ভিক্টিমের বৈশিষ্টের মধ্যে অনেকগুলো অধ্যয়ন খুঁজে পেয়েছে যে ভিক্টিমদের শারীরিক ধরণ- যেমন পোশাক, [1] প্রকাশিত ত্বকের পরিমাণ [80] এবং sexualization [81] হলো সেসব ফ্যাক্টর্স যা অন্যদের উপলব্ধির মধ্যে ভিক্টিমদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। যেহেতু ভিক্টিম ব্লেমিং শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকদের মনের মধ্যে একটি পক্ষপাত/bias হিসাবে বিদ্যমান, ভিক্টিম ব্লেমিং শুধুমাত্র ভিক্টিমের পোশাকের উপরে নির্ভর করে না।
লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতাকে প্রশমিত করার মাধ্যমে ভিক্টিম ব্লেমিং লিঙ্গ-ভিত্তিক অনুক্রমকে আরো শক্তিশালী করে তুলে এবং ভিক্টিম ব্লেমিং একই সাথে সমাজের বিদ্যমান লিঙ্গ-ভিত্তিক স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখতে কাজ করে। [82] ভিক্টিমদের অবমাননার জন্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রেডিক্টর হলো পর্যবেক্ষকদের নিজেদের রক্ষণশীল মতাদর্শ। [83] ভিক্টিম ব্লেমিং করার প্রবণতার সাথে লিঙ্গ-ভিত্তিক রক্ষণশীল মতাদর্শের ভূমিকার পিছনে অনেক গবেষণা করা হয়েছে, তবে দোষের নির্দিষ্ট বিচার করার পিছনে একটা ব্যাপক রক্ষণশীল মতাদর্শ কি ভূমিকা পালন করে, তা এতটা স্পষ্ট নয়। [84] [71]
ভিক্টিম ব্লেমিং-এর প্রক্রিয়ার মধ্যে Right Wing Authoritarianism (RWA) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে পারে। RWA হলো তিনটি সম্পর্কিত ভ্যারিয়েবল-এর covariation:
১) স্বৈরাচারী অধিনস্ততা
২) স্বৈরাচারী আগ্রাসন
৩) প্রচলিততা
স্বৈরাচারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ মেনে চলে, সামাজিক পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সামঞ্জস্যতা, রক্ষণশীলতা এবং নিরাপত্তাকে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচনা করে। [85] [86] RWA-এর অদ্ভুত বৈশিষ্টের কারণে, তা ভিন্নমতাবলম্বী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাবের একটি প্রেডিক্টের। কেননা, RWA-এর কারণে, ভিন্নমতাবলম্বী জনগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যগত আদর্শ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে একটি হুমকি হিসাবে উপলব্ধি করা হয়। [87] ধারাবাহিকভাবে, স্বৈরাচারীরা সেসব নারীদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা প্রয়োগ করে, এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা নিয়ে আচরণ করে, যারা প্রথাগত লিঙ্গ নিয়মকে অতিক্রম করে। [88] [89] এমনকি, রিসার্চ-এ দেখা গেছে যে যাদের RWA-এর মাত্রা বেশি, তারা Benevolent Sexism (BS) [89] এবং Rape Myth [90]-উভয়কে সমর্থন করে থাকে। যাদের মধ্যে Benevolent Sexism (BS)-এর মাত্রা বেশি, তারা ধর্ষণের ভিক্টিমদের বেশি মাত্রায় দোষারোপ করে, কেননা তারা ভিক্টিমদের আচরণকে অগ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচনা এবং ঐতিহ্যগত লিঙ্গিক নিয়মের বিরুদ্ধে হিসাবে বিবেচনা করে। [68] তাই, stranger harrassment-এর sexualized victims-দের ক্ষেত্রে, তাদের ভিক্টিম ব্লেমিং-এ Right Wing Authoritarianism (RWA) একটি তৃতীয় variable হিসাবে প্রভাব বিস্তার করে। [91]
রিসার্চ অনুযায়ী, একটি sexualized appearance স্পষ্ট লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ভিক্টিমদের উপলব্ধির মধ্যে একটি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। [81] [92] তবে, ক্ষুদ্র সহিংসতার (example: stranger harassment) নারী ভিক্টিমদের উপলব্ধির মধ্যে একটি sexualized appearance কিরকম প্রভাব বিস্তার করে, তার উপরে বেশি একটা মনোযোগ দেওয়া হয় না। তাই, নিচের রিসার্চ-টি যাচাই করার চেষ্টা করেছে যে মানুষের রক্ষণশীল মতাদর্শ (যা RWA দ্বারা নির্ধারণ করা) ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মধ্যে sexualized নারী ভিক্টিমদের উপরে ভিক্টিম ব্লেমিং-এ কোনো প্রভাব বিস্তার করে নাকি না।
পূর্ববর্তী রিসার্চ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ [93] [94], এই গবেষণায়-ও দেখা গেছে যে পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপটের উপরে ভিত্তি করে stranger harrassment-এর তীব্রতার উপলব্ধি পরিবর্তন হয়। রাস্তায় ঘটে যাওয়া stranger harassment-কে একটা উদযাপনের মধ্যে ঘটে যাওয়া stranger harassment-এর তুলনায় আরো বেশি ভয়ানক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর কারণে একটি double standard উঠে আসে। একই অপরাধকে কম ভয়ানক হিসাবে বিবেচনা হতে পারে শুধুমাত্র এই কারণে যে সেই অপরাধটি এমন একটি পরিবেশে ঘটেছে, যেখানে পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপটে যৌনতা যুক্ত ছিল- যেমন একটি house party-এর মধ্যে। যদিও পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মানুষের মধ্যে stranger harassment-এর তীব্রতার উপলব্ধি পরিবর্তন হলেও, পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপট ভিক্টিম ব্লেমিং-এর মাত্রার উপর এই গবেষণায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।
বরং, এই গবেষণার ফলাফল পূর্ববর্তী রিসার্চ-এর মতন [1] [81] [74] প্রমান করে যে stranger harassment-এর ক্ষেত্রেও, মানুষ সেসব ভিক্টিমদের বেশি মাত্রায় দোষারোপ করে, যারা একটি sexualized appearance গ্রহণ করেছিল। তাই, ক্ষুদ্র লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার পরিস্থিতির মধ্যেও, ভিক্টিমদের ধরণের উপরে ভিত্তি করে তাদের সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধির মধ্যে একটি পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে, সেই ঘটনার অভিনেতাদের ভূমিকা স্মপর্কে উপলব্ধি উল্টিয়ে যায়- ভুক্তভোগীকে আসামি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
Stranger Harassment-এর ভিক্টিমদের দোষারোপ করার জন্য RWA যৌথভাবে সেই ভিক্টিমের-এর sexualization-এর উপলব্ধির সাথে কাজ করে। বিশেষ করে, আমরা দেখেছি যে গড় এবং উচ্চ স্তরের RWA সহ লোকেরা stranger harassment-এর sexualized ভিক্টিমদের বেশি পরিমাণে দোষারোপ করে, যেখানে নিম্ন স্তরের RWA সহ লোকেদের জন্য ভিক্টিমদের sexualization অনুসারে দোষারোপের মাত্রা পরিবর্তিত হয় না।
স্বৈরাচারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেসব নারীদের বিরুদ্ধে সত্রুতা পোষণ করে, যারা ঐতিহ্যগত লিঙ্গিক আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে। [88] [89] স্বৈরাচারীরা আরো বেশি মাত্রায় Benevolent Sexism (BS)-কে সমর্থন করে থাকে, যার কারণে ভিক্টিমদের উপরে স্বৈরাচারীদের দোষ প্রয়োগের মাত্রা প্রভাবিত হয়। [68] এইভাবে, স্বৈরাচারীদের মতে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা “বিপথগামী” নারীদের “শাস্তি” দিতে কাজ করে, এবং নারীদের উপর পুরুষদের অধিপত্যকে বজায়ে রাখে। [84]
এই গবেষণার ফলাফলের একটি সম্বাভ্য ব্যাখ্যা হলো যে গড় এবং উচ্চ স্তরের RWA সহ লোকেরা stranger harassment-এর sexualized ভিক্টিমদের বেশি পরিমাণে দোষারোপ করে কারণ[90]-
১) তারা ভিক্টিমদেরকে “বিপথগামী” হিসাবে বিবেচনা করে।
২) তারা ভিক্টিমদের পোশাক-কে “প্রভোকেটিভ” হিসাবে বিবেচনা করে।
৩) তারা ভিক্টিমদের আচরণ-কে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গগত নিয়মের বিরুদ্ধে হিসাবে বিবেচনা করে।
এবং তাই, ডানপন্থী স্বৈরাচারীরা ভিক্টিমদেরকে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের জন্যে তাদেরকেই দোষী বলে মনে করে। এই ভিক্টিম ব্লেমিং করার প্রবণতা বিশেষ করে উচ্চ মাত্রার সহ লোকেদের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে- যারা যারা এই রক্ষণশীল এবং পুরুষতান্ত্রিক আদর্শগুলি অভ্যন্তরীনভাবে গ্রহণ করেছে যে ভিক্টিমদের দোষারোপ করা একটি শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া হয়ে পরে, কেননা তাদের মতে সেই ভিক্টিমরা লিঙ্গগত নিয়মকে ভঙ্গ করেছে। [91]
“পাগল ধর্ষক”-এর উপকথা
ধর্ষণের বিরুদ্ধে অনেক আইন রয়েছে যা নারীবাদী প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করে। কেননা সেই আইনগুলি “পাগল ধর্ষক”-এর myth/উপকথার উপরে ভিত্তি করা। এই myth/উপকথাটি ধারণ করে যে যে সকল পুরুষ ধর্ষণ করে থাকে, তারা আসলে sadistic, হিংস্র আক্রমণকারী, যারা যৌনভাবে বিপথগামী, এবং যারা সহিংসতা এবং শারীরিক শক্তির মাধ্যমে তাদের ভিক্টিমের উপরে আক্রমণ করে থাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে, সমাজবিজ্ঞান থেকে পাওয়া data এই myth/উপকথাকে সম্পূর্ণভাবে debunk/খণ্ডন করে এবং দেখায় যে ধর্ষণকারীরা সাধারণত মানসিকভাবে স্বাভাভিক হয়ে থাকে। তার উপর দিয়ে, অনেক রিসার্চ-এ দেখা গেছে যে বেশিরভাগ নারীরা তাদের ধর্ষণকারীদের চিনে থাকে। এর পাশাপাশি, খুব কম পরিমানের ধর্ষণের মধ্যে ধর্ষণ থেকে আলাদা কোনো সহিংসতা অন্তর্ভুক্ত থাকে (যেমন মারধর, খাবার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি)। “পাগল ধর্ষক”-এর /উপকথা খণ্ডন করার নারীবাদী প্রচেষ্টার সত্ত্বেও, এই উপকথাটি ব্যাপকভাবে সমাজে প্রচলিত। জনসাধারণের কাছে এই জিনিসটা বুঝানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পরিচিতদের হাতে ধর্ষিত হওয়াটাও যে আসলে জোরপূর্বক ধর্ষণ। এমনকি Susan Estrich (১৯৭৮) বিভিন্ন নারীবাদী স্কলারদের কথা তুলে ধরে বলেছেন যে সমাজের মধ্যে যা আমরা “যৌনতা/sex” হিসাবে বিবেচনা করি, তা আসলে বলপ্রয়োগের উপরে ভিত্তি করা।
“In reality, these new laws substantially undermine feminist efforts. They do so by reinforcing the myth that men who rape are “brutish male aggressors … [and] sex crazed deviant sociopaths … [who are] violent and sadistic [and] use extreme force to violate [their] victim.” [95] Modem social science data debunks this myth and suggests that the average rapist is psychologically normal. [96] Moreover, many studies suggest that most women know their rapists and that only a small portion of rapes involve violence extrinsic to the rape itself. [97] While a significant part of the feminist agenda has been the deconstruction of this myth, especially as it relates to the campaign for public recognition that “acquaintance rape” is also forcible rape, the “myth of the crazed rapist” remains deeply entrenched.” [98] [99]
ধর্ষণকারীরা কি নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না?
জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে একটি সাধারণ উপলব্ধি হলো যে তারা গলির চিপার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাইকোপ্যাথ যারা ভিক্টিমদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষায় রয়েছে, এবং যারা তাদের আচরণ এবং আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সমাজ বৈজ্ঞানিক রিসার্চ থেকে আমরা জানতে পারি যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে এই চিত্রটি আইনি স্তরে বিদ্যমান, এবং পুলিশ অফিসার, প্রসেকিউটর, বিচারপতি এবং জুরির সদস্যের মধ্যেও এই চিত্রটি বেশ প্রচলিত। এমনকি ধর্ষণের অনেক ভিক্টিম তাদের অভিজ্ঞতাকে ধর্ষণ ছাড়া অন্য একটা জিনিস হিসাবে বর্ণনা করে কারণ তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ধর্ষণটি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণের উপলব্ধির সাথে মিলে না।
এই চিত্রটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার সত্ত্বেও, তার পিছনে কোনো তথ্য বা প্রমান নেই। এই চিত্রটির বিরুদ্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো-
১) যেমনটি নারীবাদীরা গত দশক ধরে বলে আসছেন, বেশিরভাগ নারী অপরিচিতদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয় না। অপরিচিতদের হাতে নারীরা অবশ্যই ধর্ষিত হয়ে থাকে, তবে স্ট্যাটিসটিক্স অনুযায়ী ৭৫% ধর্ষণের ভিক্টিম তাদের পরিচিতদের হাতে ধর্ষিত হয়ে থাকে।
২) যেসব পুরুষরা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ধর্ষণ করে থাকে, তারা কোনোভাবেই মানসিকভাবে অসুস্থ নয়।সমাজ বৈজ্ঞানিক রিসার্চ অনুযায়ী, ৫%-এর ও কম ধর্ষণকারী ধর্ষণের সময় কোনো মনোব্যাধিতে ভুগছিল।
নারীদের যৌনতার সাথে সম্মুখীন হয়ে, ধর্ষণকারীদের অসহায়ত্ত্বার দাবির সত্ত্বেও এমন কোনো এভিডেন্স নেই যা দেখায় যে ধর্ষণকারীরা তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
Steven J. Morse (১৯৯৮) অনুযায়ী- “বেশিরভাগ যুক্তি যা সহজেই পরামর্শ দেয় যে যৌন আবেগ বা যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তা ধারণাগতভাবে এবং প্রমাণিকভাবে অসমর্থিত (conceptually and empirically unsupported)।”
Bruce J. Winick (১৯৯০) অনুযায়ী- “একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা অসম্ভব এবং একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা হয় নি- দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।”
Paul Schewe & William O’Donohue (১৯৭২) অনুযায়ী- “এই পর্যায়ে, এটি পরিষ্কার যে বিপথগামী যৌন উত্তেজনা ধর্ষণের একটি প্রয়োজনীয় বা পর্যাপ্ত কারণ নাও হতে পারে, কারণ কিছু গবেষক রেপিস্ট এবং নন-রেপিস্ট জনসংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।”
Check & Malamuth (১৯৮৫) অনুযায়ী- অনেক কলেজ বয়সী পুরুষ নিজেরা ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছে যদি তারা কোনো নেতিবাচক পরিণামের সম্মুখীন না হতো। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ধর্ষণকারীরা তুলনামূলকভাবে “স্বাভাবিক” হয়ে থাকে। এই নির্দিষ্ট গবেষণার মধ্যে দেখা গেছে যে ৩৫% পুরুষ ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছিল যদি তারা সেই অপরাধের জন্যে ধরা না খেতো।
Katherine Baker অনুযায়ী- “যেসব পুরুষ ধর্ষণকারী হয়ে থাকে, তারা এতটাই “স্বাভাবিক” যে মনোবিজ্ঞানীরা তাদের মধ্যে ‘অস্বাভাবিকতা”-এর কোনো ধরণের প্রমান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।”
যেসব পুরুষরা ধর্ষণকারী হয়ে থাকে, তাদেরকে একটি মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বাকি পুরুষ জনসংখ্যার থেকে আলাদাপ্রাপ্ত করা অসম্ভব। অবশ্যই, ধর্ষণকারীদের কিছু শনাক্তকারী বৈশিষ্ট রয়েছে, যা তাদেরকে নন-রেপিস্ট থেকে আলাদাপ্রাপ্ত করে; তবে এই বৈশিষ্টগুলি মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে সেগুলি সামাজিকভাবে গঠিত। অতএব, যেসব পুরুষ ধর্ষণ করেছে, অথবা ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছে, তারা বেশি মাত্রায়, Rape Myth, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং যৌনতা সম্পর্কে বাঁধাধরা ধারণাকে (sexual stereotypes) সমর্থন করে থাকে। মানসিকভাবে বিপথগামী হওয়া দূরের কথা- যেসব পুরুষ ধর্ষণ করে, তারা শুধুমাত্র যৌন ভূমিকার নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক আদর্শকে অভন্তরীণভাবে গ্রহণ করেছে।
“Taken together, these beliefs reveal a public image of rapists as “psychopaths lurking in dark alleys waiting to pounce on any likely victim and inflict their uncontrollable desires upon her.”‘ [100] Social science research suggests that this image also prevails among members of the legal system, including police officers, [101] [102] [103] prosecutors, [104] [105] [106] judges, [107] and jurors. [108] [109] [110] Many rape victims characterize their experience as something other than rape because they were not victimized in accordance with public perceptions of rape. [111] [112]
Despite its prominence, the image of the crazed rapist is unsupported in fact. First, as feminists have been pointing out for decades, most women are not raped by strangers. While stranger rape clearly occurs, statistics indicate that over seventy-five percent of rape victims are raped by someone they know. [113] Second, most men who rape adult women are neither mentally ill nor compulsive. Social science studies suggest that “less than 5 percent of rapists are psychotic at the time of the commission of the rape.’ [114] In addition, despite sex offenders’ claims of helplessness in the face of female sexuality, there is no evidence that sex offenders are unable to control their actions. [115] As Katharine Baker notes, many researchers conclude that “men who rape are ‘normal’ to the extent that psychologists fail to find evidence of abnormality. ‘ [116] In fact, men who rape are, from a psychopathology standpoint, essentially indistinguishable from the male population as a whole. [117] [118] [119] [120] To be sure, men who rape do share some identifiable characteristics distinguishing them from the non-rapist population. Those characteristics, however, tend to be socially constructed rather than related to psychopathology. Thus, men who have raped or who admit to a likelihood of committing rape have greater acceptance of rape myths, violence against women, and sexual stereotypes. [121] [122] Far from being mentally deviant, men who rape have simply internalized certain cultural and sex role norms.” [99]
মানসিকভাবে স্বাভাবিক মানুষ ধর্ষণকারী হয়ে থাকে
একটি সাধারণ ধারণা হলো যে ধর্ষণকারীরা বিকৃত আসামী, যারা সংখ্যায় কম, এবং যাদেরকে সহজেই চেনা যায়। তবে,গত ৫০ বছরের গবেষণা স্পষ্টভাবে প্রমান করে যে ধর্ষণকারীরা কোনো ভাবেই সংখ্যায় কম না, এবং তাদেরকে “বিকৃত” হিসাবেও শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। ধর্ষণকারীদের জনসংখ্যাকে কোনোভাবেই “ছোট” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। নিচে এর সাপেক্ষে কিছু গবেষণা উল্লেখ করা হয়েছে-
১) Mary P. Koss, (1998) Hidden Rape: Sexual Aggression and Victimization in a National Sample of Students in Higher Education, in Rape And Sexual Assault,- ১৯৮৮ সালে, United States-এর মধ্যে ৬১০০ কলেজের ছাত্রদের দেশব্যাপী জরিপে ১২-টি কলেজ বয়সী পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ ধর্ষণ করেছে বলে স্বীকার করে।
২) Karen R. Rapport & C. Dale Posey, (1991) Sexually Coercive College Males, in Acquaintance Rape: The Hidden Crime- ৪৩% কলেজ বয়সী পুরুষ জোরপূর্বক যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে বলে স্বীকার করে। তাদের জবরদস্তির range নারীর প্রতিবাদ উপেক্ষা করা থেকে শুরু করে নারীদের উপরে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করা পর্যন্ত ছিল। এই গ্রুপের পনের শতাংশ (১৫%) পুরুষ স্বীকার করে যে তারা তাদের পরিচিতদের ধর্ষণ করেছিল; এবং এগারো শতাংশ (১১%) পুরুষ স্বীকার করেছিল যে তারা নারীদের উপরে শারীরিক সংযম ব্যবহার করেছিল বলে স্বীকার করে।
৩) Eugene J. Kamin, (1969) Selected Dyadic Aspects of Male Sex Aggression- কলেজে প্রবেশের পর থেকে ২৫% কলেজ বয়সী পুরুষ যৌন জবরদস্তিমূলক আচরণে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।
৪) Mary P. Koss & Cheryl J. Oros, (1982) Sexual Experiences Survey: A Research Instrument Investigating Sexual Aggression and Victimization- ১৮৪৬ কলেজে বয়সী পুরুষদের একটি random sample-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “তুমি কি কখনো এতটাই যৌনভাবে উত্তেচিত হয়েছিলা যে নারীটা না চাওয়ার সত্ত্বেও, তুমি নিজেকে থামাতে পারো নাই?” তাদের মধ্যে ২৩% উত্তরে, “হ্যা” বলে। যদিও এই পুরুষরা একাত্তরের যুধ্যের সময় পাকিস্তান সৈন্যদের মতন আচরণ করে নাই, তাদের অপরাধকে অবশ্যই “ধর্ষণ” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।
৫) James V.P. Check & Neil Malamuth, (1985) An Empirical Assessment of Some Feminist Hypotheses About Rape, International Journal of Women’s Studies- এটি নারীবাদী গবেষণা সাহিত্ত্বের একটি তাত্বিক বিশ্লেষণ, যেখানে দেখা গেছে যে যেসব পুরুষ ধর্ষণ করে থাকে, তারা এতটাই “স্বাভাবিক” যে মনোবিজ্ঞানীরা তাদের মধ্যে “অস্বাভাভিকতার” কোনো ধরণের প্রমান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।
৬) Koss, M. P., Leonard, K. E., Beezley, D. A., & Oros, C. J. (1985). Nonstranger sexual aggression: A discriminant analysis of the psychological characteristics of undetected offenders. Sex Roles– এই গবেষণায় দেখা গেছে যে পুরুষদের যৌন আগ্রাসনের মাত্রা Psychopathic Deviate Scale-এর উচ্চ মাত্রার স্কোরের সাথে কোনো ধরণের সম্পর্ক রাখে না। Psychopathic Deviate Scale হলো Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)-এর একটি অংশ, যা ব্যক্তিদের ইন্টারভিউ নেওয়ার মাধ্যমে তাদের score response-কে সেসব ব্যক্তিদের score respose-এর সাথে সম্পর্ক যাচাই করে, যারা মনোব্যাধিতে আক্রান্ত।
৭) Lucy W. Taylor, (1993) The Role of Offender Profiling in Classifying Rapists: Implications for Counselling- কারাগারে ধর্ষকদের নিয়ে কাজ করা মনোবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে ধর্ষকদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার মাত্রা দুই (২%) থেকে বিশ শতাংশের (২০%) মধ্যে পরিবর্তিত হয়। ধর্ষণের জন্য আইনিভাবে দোষী সাব্যস্ত পুরুষদের অন্যান্য ধর্ষকদের তুলনায় সাইকোপ্যাথলজি থাকার সম্ভাবনা বেশি, কারণ তারাই এমন পুরুষ যারা পর্যাপ্ত বার এমনভাবে ধর্ষণ করেছে যা আইনিভাবে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট গুরুতর ছিল।
গবেষকরা রেপিস্ট এবিং নন-রেপিস্ট জনসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেও, তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছে। ধর্ষণটি ছাড়া, এরকম কোনো প্রমান নেই, যা objectively ইঙ্গিত দেয় যে বেশিরভাগ ধর্ষণকারী বিকৃত মানসিকতা ধারণ করে। তবে, ধর্ষণ করার প্রবণতাকে কিছু objective variable-এর সাথে যুক্ত করা যায়। ধর্ষণ সম্পর্কে গবেষণা প্রকাশ করে যে ধর্ষণের ব্যাপকতার সাথে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রক্রিয়া পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত, যেমন- লিঙ্গ-ভিত্তিক অসমতার সমর্থন, ক্ষতিকর এবং নারী-বিদ্বেষী পর্নোগ্রাফি, এবং একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলার মাত্রা। একই সাথে, ধর্ষণ করার self-report-এর সম্ভাবনার সাথে Rape Myth-এর সমর্থন, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সমর্থন এবং ঐতিহ্যগত লিঙ্গ-ভিত্তিক ভূমিকা অনুযায়ী বাঁধাধরা ধারণা রাখা খুবই শক্তিশালীভাবে সম্পর্কিত।
যেসব রাষ্ট্রের ধর্ষণের মাত্রা বেশি, সেই মাত্রাটি প্রায় ৫ থেকে ১০ গুন বেশি সেসব রাষ্ট্রের তুলনায় যেখানে ধর্ষণের মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। তাই, ধর্ষণের ব্যাপকতা সাম্প্রদায়িক আদর্শের সাথে জড়িত। এই তথ্যটি পরামর্শ দেয় যে ধর্ষণ এমন একটি অপরাধ যা সাংস্কৃতিকভাবে বিপথগামী হওয়ার পরিবর্তে, তা সাংস্কৃতিকভাবে নির্দেশিত। ধর্ষণকে উত্সাহিত করে এমন সামাজিক নিয়মগুলির ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই নিয়মগুলিকে ধরে রাখা পুরুষদের শ্রেণীকে “কম সংখ্যক” এবং “অস্বাভাবিক” হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।
এই একই জিনিস নারীবাদী গবেষকরা বলে আসছেন। Catherine A. Mackinnon (1989) যুক্তি দেখান যে পুরুষদের চিন্তাধারা অনুযায়ী ধর্ষণের অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা হয়, এবং তাই নারীরা ধর্ষণের অভিযোগ করে না, কারণ আইনি ব্যবস্থা নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ষণকে উপলব্ধি করে না। Mackinnon নিজে বলেন- “নারীবাদী বিশ্লেষণে, ধর্ষণ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা নৈতিক লঙ্ঘন বা ব্যক্তিগত আদান-প্রদানে ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং গোষ্ঠীগত পরাধীনতার বিস্তারিত এবং পদ্ধতিগত প্রসঙ্গের মধ্যে সন্ত্রাসীর ও নির্যাতনের একটি কাজ।”
“The first argument that was proffered in the legislative history suggests that, because rapists constitute a “small class of depraved criminals,” [123] they can be distinguished. As explained below, however, the last twenty-five years of research clearly demonstrate that the class of rapists is neither small nor particularly likely to be depraved. In a 1988 nationwide survey of more than 6100 college students, one in twelve college men admitted to committing rape. [124] Another study found forty-three percent of college males reporting that they had engaged in coercive sex. [125] The coercion ranged from ignoring women’s protests to using physical force. [126] Fifteen percent of this group acknowledged committing acquaintance rape; eleven percent admitted using physical restraint. Twenty- three percent of a random sample of 1846 college-age men responded “yes” to the question: “Have you ever been in a situation where you became so sexually aroused that you could not stop yourself even though the woman didn’t want to? [127] These men may not all have been committing acts that resemble the acts of the soldiers at My Lai or the stranger with an ice pick, but they were all committing rape. [128] “Small” simply does not describe the size of the rapist class.
Numerous studies have also found that men who rape are “normal” to the extent that psychologists fail to find evidence of abnormality. [129] Male levels of sexual aggression do not correlate with elevated scores on the Psychopathic Deviate scale. [130] One well-cited study found that thirty-five percent of college men indicated a likelihood to rape if they were sure that they could get away with it. Psychologists working with rapists in prison report that the incident of mental illness among rapists varies from only two to twenty percent. [131] Researchers have consistently failed to find significant psychological differences between the rapist and nonrapist populations.” [132] There is simply no evidence, save the rape itself, suggesting that all or even most rapists are objectively depraved.
Nonetheless, a tendency to rape can be linked to objective variables. Macrosociological research on rape strongly suggests that the prevalence of rape is positively correlated with a variety of social phenomena, including the acceptance of gender inequality, the prevalence of [harmful and sexist] pornography, and the degree of social disorganization in a community. [133] The self-reported likelihood to rape is also strongly related “to acceptance of rape myths, acceptance of violence against women, and sex role stereotyping.’ [134] States with a high incidence of rape have a rate that is five to ten times greater than states with a low incidence of rape, thus suggesting that the prevalence of rape is linked to community norms. [135] What this suggests, in contradistinction to the legislative assumption and in support of feminist theory on the subject [136] is that rape is culturally dictated, not culturally deviant. Given the prevalence of the social norms that encourage rape, one can hardly define the class of men who hold these norms as abnormal.” [137]
ধর্ষণ কোনো সামাজিক বা যৌন ব্যতিক্রম নয়
কল্পনা করুন যে কেউ আপনার মাথায় বন্দুক ধরেছে এবং আপনাকে তাদের সাথে যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে। এমন একটি দৃশ্য ধর্ষণ। একইভাবে, যখন একজন নারীর জীবনকে ঘিরে সামাজিক, পারিপার্শ্বিক এবং অর্থনৈতিক ফ্যাক্টরগুলো এমন হয় যে তারা না চাইলেও যৌনতায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়, তখন সেটাকেও ধর্ষণ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। এমনকি যখন মহিলাটি তার “না” মৌখিকভাবে প্রকাশ করে না, তখনও এটি ধর্ষণ কেননা অনেক ক্ষেত্রেই, “না” বলার ফলে তাদের স্বামীর কাছ থেকে ক্ষতি বা নির্যাতনের সম্মুখীন হতে পারে।
আমাদের সমাজের মধ্যে বেশির ভাগ বিদ্যমান যৌনতা আসলে যৌনতা নয়, বরং ধর্ষণ। বিভিন্ন নারীবাদী স্কলার, যেমন Catherine MacKinnon বলেছেন যে সাধারণ বিষমকামিতা নারীদের বিরুদ্ধে এমন সহিংসতার উপরে ভিত্তি করা যে দৈনন্দন যৌনসঙ্গম এবং যৌন সহিংসতার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব।
আমাদের মনের মধ্যে “যৌনতা” শব্দটি ভালোবাসা, প্রেম এবং romance জাতীয় ধারণার সাথে যুক্ত। তবে, যৌনতার এমন একটি চিত্র সমাজের বেশির ভাগ নারী উপভোগ করতে পারে না। “যৌনতা” অর্থাৎ সম্মতিমূলক, আনন্দদায়ক যৌনতা সমাজের মধ্যে একটি বিশেষাধিকার যা খুব কম মানুষ উপভোগ করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেমন, ১০০% নারী বিবাহের প্রথায় আবদ্ধ থাকলে, তারা তাদের স্বামীর হাতে আইনগততভাবে ধর্ষিত হতে পারে, যেখানে তার স্বামীকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করা হবে না। একই সাথে, নারীদের যৌন আনন্দকে সাধারণ বিষমকামী যৌনকর্মের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। কোনো নারী যদি বিষমকামী সম্পর্কের মধ্যে অর্গাজম উপভোক করে, তোলে সেটি তাদের বিশেষাধিকার বা privilege। পদ্ধতিগত স্তরে, নারীদের জন্যে “ভালো, আনন্দদায়ক” যৌনতা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।
Germaine Greer একজন দ্বিতীয় তরঙ্গ নারীবাদী, যিনি সমাজের মধ্যে ধর্ষণ সংস্কৃতির প্রভাব তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে এর ফলে, ভালো আনন্দদায়ক যৌনতা অদৃশ্য হয়ে উঠেছে, এবং সমাজের দৈনন্দিন যৌনতার চর্চা আসলে ধর্ষণের চর্চা। উনার বই, The Female Eunuch-এর মধ্যে তিনি সমাজের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিকতার কারণে নারীদের যৌন আনন্দের অভাবকে তুলে ধরেছেন। নিচে উনার ধর্ষণের মডেলের ছবি দেওয়া হয়েছে এবং ছবির ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।
নীল বৃত্ত- আমাদের সমাজে যেভাবে যৌনতা বিদ্যমান, অর্থাৎ “সাধারণ বিষমকামিতা।”
কমলা বৃত্ত- যেই সকল যৌনতার মধ্যে নারীদের যৌন আনন্দের উপস্থিতি নেই অর্থাৎ, “আনন্দহীন যৌনতা।”
হলুদ বৃত্ত- যেই সকল ধর্ষণ দৈনন্দিন যৌনকর্ম হিসাবে লুকিয়ে রাখা হয়, অর্থাৎ “দৈনন্দিন ধর্ষণ।”
লাল বৃত্ত- “আক্রমণাত্মক ধর্ষণ”।
সবুজ বৃত্ত- “ভালো আনন্দদায়ক যৌনতা” অর্থাৎ যেই যৌনতা পারস্পরিক আনন্দের উপরে ভিত্তি করা। “ভালো আনন্দদায়ক যৌনতা” সাধারণ বিষমকামিতার বাহিরে।
এই তথ্যটি পরামর্শ দেয় যে ধর্ষণ এমন একটি অপরাধ যা সাংস্কৃতিকভাবে বিপথগামী হওয়ার পরিবর্তে, তা সাংস্কৃতিকভাবে নির্দেশিত। ধর্ষণকে উত্সাহিত করে এমন সামাজিক নিয়মগুলির ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই নিয়মগুলিকে ধরে রাখা পুরুষদের শ্রেণীকে “কম সংখ্যক” এবং “অস্বাভাবিক” হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। [138]
পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বিশেষাধিকার
যখন ধরেই নেওয়া হয় যে পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষা বিবেচনা করে নারীদের আচরণ এবং পোশাক নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, তখনি পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষাধিকার দেওয়া হয়। যখনি আমরা শুনতে পাই যে ধর্ষণের কোনো অপরাধ ঘটেছে, সামাজিক উপলব্ধির মধ্যে আমরা এই বিশেষাধিকারের প্রতিফলন দেখতে পারি–যখন সমাজের মানুষ সেই ধর্ষণের ভিক্টিমকে “ছোট পোশাক” না পরার “পরামর্শ” দেয়। এই “পরামর্শ” প্রকাশ করে যে সমাজের দ্বারা পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিবেশের একটি অপরিবর্তনীয় এবং এমনকি বিপজ্জনক দিক হিসাবে বিবেচিত হয়। এবং তাই, যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্যে নারীদের আচরণ তাদের নিজেদেরকেই পরিবর্তন করতে হবে। তবে, নারীদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে পুরুষদেরকে তাদের আচরণকে একইভাবে পরিবর্তন করতে বলা হয় না। এবং, নারীদের প্রতি পুরুষদের যৌন আচরণের ন্যায্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করা হয় না।
পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বিশেষাধিকার আমরা স্কুল ইউনিফর্মের ড্রেস কোড-এর মধ্যেও দেখতে পারি। এই ড্রেস কোড গুলি প্রায়শই মেয়েদের “প্রকাশ্য” বা “টাইট-ফিটিং” পোশাক-কে টার্গেট করে থাকে এই ভিত্তে যে এই ধরণের পোশাক ছেলেদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে। [139] কিন্তু, ছেলেদের পোশাক যে মেয়েদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে, তা কখনো উল্লেখই করা হয় না। কখনোই বলা হয় না যে নারীদের যৌন আকাঙ্ক্ষা বিবেচনা করে পুরুষদেরকে তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, যেন তারা নারীদেরকে তারা যৌনভাবে উত্তেজিত না করে। এটা প্রকাশ করে যে পুরুষদের যৌন আচরণের জন্যে নারীদেরকে দায়বদ্ধ করা হয়, কিন্তু নারীদের যৌন আচরণের জন্যে পুরুষদেরকে দায়বদ্ধ করা হয় না।
আইন প্রয়োগের মধ্যেও আমরা পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বিশেষাধিকার বিদ্যমান। পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষাধিকার দেওয়া হয় যখন বিবেচনা করা হয় যে নারীদের উপরে পুরুষদের সহিংসতা “যুক্তিসঙ্গত” বা “স্বাভাবিক” যদি সেই সহিংসতা Sexual Jealousy অথবা Sexual Possessiveness দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। যখন বিবেচনা করা হয় যে রিজেক্ট করার জন্যে বা সম্পর্ক ভেঙে ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে নারীদের উপরে পুরুষদের সহিংসতা একটা যুক্তিসঙ্গত প্রক্রিয়া, তখন পুরুষদেরকে বিশেষাধিকার দেওয়া হয়, কেননা তা এই দৃষ্টিভঙ্গির উপরে ভিত্তি করা যে নারীরা পুরুষদের রিজেক্ট করলে বা সম্পর্ক ভেঙে ছেড়ে চলে গেলে, পুরুষদের হিংস্রতা এবং Sexual Possessiveness-এর অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে “স্বাভাবিক”। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সেসব আইনের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়, যেগুলো প্ররোচনার ভিত্তিতে আইনি প্রতিরক্ষার মানদণ্ড পূরণ করার অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে আসামীর অপরাধ প্রশমিত করে, যা অবশেষে পুরুষদের Sexual Jealousy এবং Sexual Possessiveness-কে ন্যায্যতা দেয়।
ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতনের ট্রায়াল-এর মধ্যে (এবং মিডিয়া দ্বারা সেসব ট্রায়ালের আলোচনার মধ্যে) পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বিশেষাধিকার বিদ্যমান যেখানে পোশাক এবং আচরণের ভিত্তিতে ভিক্টিমকে প্ররোচনার অভিযোগে দোষারোপ করা হয়। [140] [141] [142] এই প্রক্রিয়া পুরুষদের যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়বদ্ধতাকে নারীদের উপরেই চাপিয়ে দেওয়া হয়। বিপরীতে পুরুষদেরকে কখনোই বলা হয় না যে নারীদেরকে যৌনভাবে প্রলোভন না করার জন্যে, পুরুষদের নিজেদের আচরণ এবং পোশাক নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। নারীদের যৌন আকাঙ্ক্ষা কখনোই বিপজ্জনক হিসাবে উপস্থাপনা করা হয় না, যার কথা বিবেচনা করে, নিজেদেরকে যৌন আক্রমণ এবং হ্যারাসমেন্ট থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে পুরুষদের জীবনযাপন করতে হবে।
সামাজিক এবং আইনি প্রেক্ষাপটের মধ্যে পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষার বিশেষাধিকার “প্রভোকেটিভ” পোশাকের ধারণার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহের উদ্ভব ঘটায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে যেহেতু পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষা বিপজ্জনক হতে পারে, তাই পোশাকের মাধ্যমে নারীরা পুরুষদের প্রলোভন না করার জন্যে দায়ী, তা নারীদের পোশাক এবং নারীদের পোশাক পরার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিথ্যা অনুমানের উপরে ভিত্তি করা। এটা সত্য যে অনেক নারী এবং পুরুষ উভয় নারীদের নির্দিষ্ট পোশাক-কে যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রমান হিসাবে ধরে নেয়, যা দেখায় যে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের অনেক মানুষ পোষণ করে থাকে। তবে নারীদের পোশাক সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা একটি মিথ্যা বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করা যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাক পরার সিদ্ধান্তের সাথে পুরুষদের সাথে নারীদের যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাটি সরাসরি জড়িত। এই ব্যাখ্যার সাথে এই মিথ্যা অনুমানও জড়িত যে, নারীদের পোশাক যদি পুরুষদের যৌনভাবে উত্তেজিত করে, তাহলে সেই নারীটা নিশ্চয়ই তা ঘটাতে চেয়েছিলো। [24]
তবে যদিও “প্রভোকেটিভ’ পোশাকের ধারণা নারীদের পোশাক পরার সিধান্ত সম্পর্কে মিথ্যা বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করা, এটা জিজ্ঞেস করা বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে পুরুষরা যেভাবে নারীদের পোশাকে সাড়া দেয়, তার জন্যে কি নারীদের কোনো ধরণের দায়বদ্ধতা আছে না নেই? যেহেতু সমাজে এমন বিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে প্রকাশ্য পোশাকের মাধ্যমে নারীরা তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা যোগাযোগ করছে, প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে তাদের পোশাকের ভিত্তিতে পুরুষদের আচরণের জন্যে নারীরা কিছুটা দায়ী। কেননা, কিছু নারী এই ব্যাপারে সম্পর্কে সচেতন হতে পারে যে পুরুষরা তাদের পোশাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবে। এটি নারীদের জন্যে একটা দ্বিধার উদ্ভব ঘটায়-
১) প্রকাশ্য পোশাক অবাঞ্চিত যৌন যোগাযোগের ঝুঁকি নেওয়া সেসব পুরুষদের থেকে যারা সেই পোশাককে যৌনতার দাওয়াত হিসাবে বিবেচনা করে।
অথবা,
২) পুরুষদের “ভুল মেসেজ” পাঠানোর ভয়ে প্রকাশ্য পোশাক পরা থেকে বিরত থাকা। [143]
এটা বুঝার জন্যে যে পুরুষদের যৌন আচরণের জন্যে নারীরা যে কোনোভাবেই কোনো ধরনের দায়বদ্ধতা রাখে না, তার জন্য আমাদের আগে বুঝতে হয়ে যে কেন মানুষ নারীদের পোশাককে যৌনভাবে “প্রভোকেটিভ” বলে। এরপরে আমরা জানতে পারবো যে প্রকাশ্য পোশাক পরার জন্যে নারীদের কোনো দায়বদ্ধতা আছে নাকি নেই।
কেন মানুষ নারীদের পোশাককে “প্রভোকেটিভ” বলে?
যখন কোনো নারীর পোশাককে যৌনভাবে “প্রভোকেটিভ” বলে বর্ণনা করা হয়, প্রায়শই বর্ণনাটি বোঝায় যে পোশাকটি প্রকাশ্য, টাইট-ফিটিং অথবা যৌনতাকে ইঙ্গিত করছে। [144] “প্রভোকেটিভ” পোশাকের একটি প্রস্তাবিত সংজ্ঞা হলো- “নারীদের সকল ধরণের স্টাইল যা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির গ্রহণযোগ্য আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যৌনতা এবং শারীরিক প্রকাশের দিকে নিয়ে যায়।” [145] এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটা beach-এর মধ্যে নারীদের বিকিনি পরা “প্রভোকেটিভ” হিসাবে সাব্যস্ত করা হবে না, কেননা beach-এর জন্যে বিকিনি হলো একটি গ্রহণযোগ্য পোশাক। তবে, এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটি bar-এর মধ্যে বিকিনি পরা beach-এর মতন একইভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। [146]
বিভিন্ন ধরণের রিসার্চ আমাদেকে দেখায় যে নারী এবং পুরুষ উভয় নারীদের নির্দিষ্ট পোশাককে নারীদের যৌন ইচ্ছার প্রমান হিসাবে বিবেচনা করে। [144] [147] [24] একটি রিসার্চ-এ দেখা গেছে যে ছেলে এবং মেয়ে উভয় রিপোর্ট করেছিল যে নারীরা যখন ট্রান্সপারেন্ট ব্লাউজ, ছোট টপ অথবা টাইট প্যান্ট পরে, তখন তাদের মতে সেই নারীটা তার নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষা যোগাযোগ করছে। [147] সাধারণভাবে, মানুষ এই বিষয়ে একমত যে নির্দিষ্ট পোশাক হিসাবে বিবেচনা করা হয়-বিশেষ করে সেসব পোশাক যা নারীদের শরীরের আকার এবং যা নারীদের যৌন অঙ্গ, যেমন স্তনকে প্রকাশ করে। তাই, কোনো পোশাককে “প্রভোকেটিভ” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা বিভিন্ন ফ্যাক্টরের জটিল সম্পর্ককে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন-
১) নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ড্রেস কোড।
২) নারীদের যৌনতা সম্পর্কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাঁধাধরা ধারণা।
৩) পোশাক পরিধানকারীর পোশাক পরার পিছনে উদ্দেশ্যের অনুমান।
তবে, বিভিন্ন রিসার্চ-এ দেখা গেছে যে নারীদের তুলনায় পুরুষরা আরো বেশি বেশি করে নারীদের পোশাকের সাথে যৌনতার অর্থ যুক্ত করে থাকে। অতএব, নারীদের যদি পুরুষদের যৌনভাবে প্রভোক করার উদ্দেশ্য নাও থাকে, সেই ক্ষেত্রেও নারীদের পোশাক-কে “প্রভোকেটিভ” হিসাবে বিবেচনা করা হবে। যদি একজন নারী এমন পোশাক পরে যা “প্রভোকেটিভ” হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে পর্যবেক্ষকরা- বিশেষ করে পুরুষরা- সেই নারীটার আসল, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নির্বিশেষে তার উপর যৌনভাবে প্রভাকে করার উদ্দেশ্য চাপিয়ে দিবে। এই ধরণের অনুমানের সমস্যা হলো যে বেশির ভাগ সময়, নারীদের প্রকাশ্য পোশাক পরার সিদ্ধান্তের সাথে পুরুষদের সাথে তাদের যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা কোনোভাবেই যুক্ত থাকে না।
আমাদের সমাজের মধ্যে নারীরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন কারণে প্রকাশ্য পোশাক পরার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন নারী প্রকাশ্য পোশাক পরতে পারে যদি তিনি মনে করেন যে আকর্ষণীয় হিসাবে নিজেকে উপস্থাপনা করার মাধ্যমে তার নিজের ক্যারিয়ার-কে তিনি উন্নত করতে পারবেন। [148] একই সাথে নতুন ফ্যাশন আগের ফ্যাশন-এর তুলনায় আরো প্রকাশ্য হয়ে থাকে, এবং তাই, নারীরা নিজেদেরকে মডার্ন হিসাবে উপস্থাপনা করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য পোশাক পরে থাকতে পারে। নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে নিজেকে মানানসই করার উদ্দেশ্যেও নারীরা প্রকাশ্য পোশাক পরতে পারে, বা এমনকি যৌনতার উদ্দেশ্যেও একজন নারী প্রকাশ্য পোশাক পরতে পারে। বেশিরভাগ সময়, একজন পর্যবেক্ষকের দ্বারা পোশাকের মাধ্যমে নারীদের যৌন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। [149] নারীদের প্রকাশ্য পোশাক-কে “প্রভোকেটিভ” হিসাবে বর্ণনা করা একটি assumption/অনুমানের উপরে ভিত্তি করা যে প্রকাশ্য পোশাক পরার মাধ্যমে নারীরা তাদের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার জন্যে খুবই স্পষ্টভাবে দাওয়াত দিচ্ছে। আশ্চর্যজনকভাবে, পোশাক পরিধানকারীর উদ্দেশ্যের উপরে ফোকাস করার পরিবর্তে কিভাবে সেই নারীকে অন্যরা কিভাবে সেই নারীকে উপলব্ধি করে, তা নিয়েই আইন ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির মূল ফোকাস।
পোশাকের প্রেক্ষাপটের মধ্যে “প্রভোকেটিভ”-কে “sexy” বা “প্রকাশ্য”-এর সাথে প্রায়শই সমতুল্য করা হয়। তবে এই শব্দগুলিকে একিসাথে মিলিয়ে ফেলা এই সত্যকে লুকিয়ে রাখে যে পুরুষদের “সেক্সি” পোশাক-কে খুব কম সময় “প্রভোকেটিভ” হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এমনকি, নারীদের পোশাকের বিপরীতে, পুরুষদের “sexy” পোশাক সম্পর্কে এমন কোনো সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি নেই। “প্রভোকেটিভ” যদি “sexy”-এর সমতুল্য আসলেই হয়ে থাকে, তাহলে নারী ও পুরুষ উভয়ের পোশাক-কে “প্রভোকেটিভ” হিসেবে বর্ণনা করা হতো। তাহলে sexy পোশাক পরা একটা পুরুষকে (যেইভাবেই এই ধারণাকে সংগায়িত করা হোক) কেন “প্রভোকেটিভ” হিসাবে বর্ণনা করা হয় না? উত্তরটি “প্রভোকেশন” এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে।
যখন বলা হয় যে একজন নারী “প্রভোকেটিভ” পোশাক পরেছে, তা দিয়ে শুধুমাত্র এটি যোগাযোগ হচ্ছে না যে তিনি অন্যদের সামনে সুন্দর/আকর্ষণীয় হিসাবে নিজেকে উপস্থাপনা করার উদ্দেশ্যে সেই পোশাকটা পরছে। যখন একজন নারীর পোশাককে “প্রভোকেটিভ” বলা হয়, তখন বোঝানো হয় যে সেই পোশাকটি পর্যবেক্ষকের মধ্যে যৌন অনুভূতির উদ্ভব ঘটাবে, এবং যারা সেই পোশাকে প্রতিক্রিয়া করছে, তারা তাদের আচরণের জন্যে দায়ী নয়। প্রভোকেশন এবং দায়বদ্ধতার সম্পর্কটি বেশি একটা স্পষ্ট নয় যখন “প্রভোকেটিভ” শব্দটা একটি adjective হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যেমন- “এই পোশাকটি প্রভোকেটিভ।” তবে সেই সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে উঠে যখন বলা হয়, “সেই পোশাকটি তাকে প্রভাকে করেছিল।” পরের বাক্যটির মধ্যে দুটি দাবি বিদ্যমান-
১) সেই ধরণের পোশাক পর্যবেক্ষকের মধ্যে যৌন লালসার অত্যন্ত শক্তিশালী অনুভূতি জাগিয়ে দেয়।
২) সেই অনুভূতিগুলি পর্যবেক্ষককে এমন আচরণে লিপ্ত হতে পরিচালিত করেছিল যা সে অন্যথায় লিপ্ত হতো না।
যখন বলা হয় যে “সেই পোশাকটি তাকে প্রভাকে করেছিল” তখন বোঝানো হয় যে সেই পোশাকের ফলস্বৰূপে পুরুষদের দুর্ব্যবহারকে আংশিকভাবে ন্যায়সঙ্গত হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, এবং তাই, সেই পুরুষের খারাপ আচরণকে মাফ করা যেতে পারে।
একটি নৈতিক অজুহাত হিসাবে আসামির প্রশমিত দায়িত্বের দাবিটি পরামর্শ দেয় যে একজন নারীর পোশাক দ্বারা যৌনভাবে উত্তেজিত একজন পুরুষকে অন্তত আংশিকভাবে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত যদি সেই পুরুষের যৌন উত্তেজনা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে সে তার নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ছিল। বিকল্পভাবে, সেই পুরুষের আচরণকে আংশিকভাবে ন্যায়সঙ্গত হিসাবে বোঝানো যেতে পারে যদি কোনো নারীর পোশাকের মাধ্যমে সেই নারীটার যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হয়ে থাকে। নারীদের পোশাকের প্রেক্ষাপটে “প্রভোকেশন”-এর এই ধারণাটি “প্রভোকেশন”-এর আইনি ধারণার সাথে মানানসই। বেশিরভাগ পশ্চিম দেশগুলিতে আসামিপক্ষ “প্রভোকেশন”-এর উপরে ভিত্তে করে প্রশমিত দায়িত্বের partial defense উপভোগ করে। [150] [143]
“প্রভোকেটিভ” পোশাক এবং মানুষের দায়বদ্ধতা
প্রকাশ্য পোশাক পরার জন্যে নারীদেরকে দোষারোপ করার পিছনে একটি তর্ক হলো এমন- যদি নারীরা জেনে থাকে যে পুরুষরা কিছু নির্দিষ্ট পোশাককে “প্রভোকেটিভ” হিসাবে দেখেই ছাড়বে, তাহলে এটা বোকামি, এমনকি বিপজ্জজনক যদি নারীরা সেই ধরণের পোশাক পরে অযাচিত যৌন অগ্রগতির সম্মুখীন হয়ে সেটার অভোযোগ তুলে। তবে, এই উপসংহারটিও বোকামি। এই যুক্তির মধ্যে নারীদেরকে আসলে কোন জিনিসের জন্যে দোষারোপ করা হচ্ছে? উপরোক্ত যুক্তির মধ্যে বলা হচ্ছে যে নারীদের উপর পুরুষদের অযাচিত যৌন আচরণের জন্যে পুরুষরা কম দোষের প্রাপ্য, কেননা পুরুষরা ন্যায়সঙ্গতভাবে নারীদের প্রকাশ্য পোশাককে যৌনতার দাওয়াত হিসাবে বিবেচনা করে। এবং এই চিন্তাধারা অনুসারে পুরুষরা নারীদের উপরে দোষারোপ করে যখন নারীরা যৌনতার সাপেক্ষ্যে পুরুষদেরকে “না” বলে।
নারীদের পোশাক-কে যৌনতার দাওয়াত হিসাবে অনুমান করে পুরুষদের আচরণ কোনো ভাবেই ক্ষমা করা যায় না যখন আমরা বুঝতে পারি যে-
১) নারীদের পোশাক থেকে যৌনতায় দাওয়াতের অনুমান করার পুরুষদের প্রবণতাটি prima facie অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য।
২) পুরুষদের যৌন লালসা কোনো ভাবেই তাদের অনুপযুক্ত যৌন আচরণকে ক্ষমা করে দিতে পারে না।
প্রকাশ্য পোশাক পরার জন্যে নারীদেরকে দোষারোপ করার পিছনে আরেকটি তর্ক হলো এমন- পুরুষদের প্রকাশ্য পোশাক থেকে নারীদের যৌনতার দাওয়াত অনুমান করার প্রবণতা অগ্রহণযোগ্য হলেও, হয়তোবা ব্যাপরোয়া হওয়ার কারণে নারীদেরকে সমালোচনা করা যেতে পারে, কেননা তারা এমন পোশাক পরেছে যেটা তারা জানে যে যৌনতার দাওয়াত হিসাবে পুরুষরা সেটাকে বিবেচনা করবে। এই তর্কটি প্রমথমটির থেকে আলাদা, যেখানে নারীদের যৌন উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরুষদের অনুমানের কারণে পুরুষদেরকে কম দোষের প্রাপ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একজন নারীকে ব্যাপরোয়া হওয়ার জন্যে সমালোচনা করার অর্থ হলো সেই নারীকে তার নিজের স্ব-নিরাপত্তা না বজায় রাখার জন্যে সমালোচনা করা। কিন্তু, এই ধরণের সমালোচনা কোনোভাবে ইঙ্গিত দেয় না যে নারীদের যৌনভাবে harass করার জন্যে পুরুষরা কম দোষের প্রাপ্য। তবে ব্যাপরোয়া হওয়ার কারণে যদি নারীদের স্বাধীনতা সমাবদ্ধ করার কথা বলা হয়, তাহলে তখন সমস্যা জগতে পারে। এটি বুঝার জন্যে এই উপমাটি বিবেচনা করুন-
ধরে নেন ভারতে একটি গ্রাম আছে যেখানে বর্ণবাদের প্রথা বেশ প্রচলিত। এখন ভাবুন যে সেই গ্রামে একজন শূদ্র বর্ণের ছেলে একটি ব্রাহ্মণ বর্ণের নারীর সাথে কথা বলার সময় ধরা পড়লো। এর ফলে, সেই শূদ্র ছেলেকে ধরে সেই ব্রাহ্মণ নারীর পরিবার মেরে রক্তাক্ত করে দিলো। এই পরিস্থিতিতে হয়তো সেই শূদ্র ছেলের আচরণকে সমালোচনা করা যেতে পারে এই ভিত্তিতে যে শূদ্র ছেলেটা তার নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যে যথেষ্ট যত্ন রাখেন নি। তবে এখানে মূল একটি প্রশ্ন উঠে আসে- কেন সেই শূদ্র ছেলের জন্যে সেই ব্রাহ্মণ নারীর সাথে কথা বলাটি বিপজ্জনক? একজন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের মধ্যে কথপোকথন মৌলিকভাবে বিপজ্জনক নয়। তবে সেই গ্রামের মধ্যে তা বিপজ্জনক শুধুমাত্র বিদ্যমান পূর্ব-নির্ধারিত বর্ণবাদী বিশ্বাস এবং অনুশীলনের কারণে, যা একটি সাধারণ মনুষ্য কর্মক্ষমতার প্রয়োগকে (শূদ্র আর ব্রাহ্মণ মানুষের কথাপোকথনকে) বিপজ্জনক করে তুলে। এখন আমরা যদি সেই শূদ্রের ব্যাপরোয়া আচরণের জন্যে সমালোচনা করার মাধ্যমে শূদ্রদের বিরুধ্যে বর্ণবাদী বিপদকে কমাতে পারবো? যদি আমরা নিরাপত্তার নামে শূদ্র আর ব্রাহ্মণের কথা বলাকে নেতিবাচক আলোতে দেখি, তা কি কোনো লাভ আদায় করতে পারবে?
আমরা এমন একটি পৃথিবী চাই, যেখানে সকল বর্ণের মানুষ কোনো ভয় ভীতি ছাড়া স্বাধীনভাবে একে অন্যের সাথে কথা বলতে পারে। এই লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এমন বাক্য যে “সেই শূদ্রের আসলে উপর বর্ণের মানুষের সাথে কথা বলা উচিত ছিল না” কখনোই সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের সাহায্য করতে পারবে না।
ঠিক একইভাবে, নারীদের প্রকাশ্য পোশাক মৌলিকভাবে বিপজ্জনক নয়। এই ধরণের পোশাক এবং এমনকি নারীদের মানবদেহ মৌলিকভাবে sexual নয়। উদাহরণস্বরূপ- আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে, নারীদের স্তনকে sexualize করা হয় না, এবং নারীদের টপলেস পোশাক বেশ সাধারণ। [151] পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যেও অনেক প্রেক্ষাপট রয়েছে যেখানে টাইট-ফিটিং পোশাক এবং এমনকি নারীদের নগ্নতাকে sexualize করা হয় না- যেমন নগ্ন মডেলের সাথে ছবি আকার ক্লাস-এ, নাচের রিহার্সাল-এর মধ্যে, সাঁতার শিখার ক্লাস-এ এবং জিম-এর মধ্যে।
প্রকাশ্য পোশাক এবং নারীদের শরীরের sexualization বিভিন্ন ফ্যাক্টরের সমগ্র প্রভাবের উপরে নির্ভর করে, বিশেষ করে ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট। এইভাবে, নারীদের প্রকাশ্য পোশাক পরাটা বিপদজনক হতে পারে শুধুমাত্র বিদ্যমান নারী বিদ্বেষী বিশ্বাস, মনোভাব এবং অনুশীলনের কারণে। এই বিশ্বাস এবং অনুশীলনগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত-
১) এই ধারণা যে যেসব নারীরা প্রকাশ্য বা tight-fitting পোশাক পরে থাকে,তারা আসলে sexual attention চাচ্ছে।
২) এই ধারণা যে সেই সকল নারীরা যৌন সংযোগ চাচ্ছে।
৩) এই ধারণা যে সকল পুরুষের এই অধিকার রয়েছে যে তারা যৌন উদ্দেশ্যে যেকোনো নারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে।
৪) এই ধারণা যে পুরুষদের যৌন আচরণের জন্যে নারীরা দায়প্রাপ্ত।
এই সকল বিদ্যমান বিশ্বাস এবং অনুশীলন একজন নারীর পোশাক পরার সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি unfair প্রভাব রাখে। একই সাথে, এই বিশ্বাসগুলি নারীদের মধ্যে “ভুল মেসেজ পাঠানোর” এবং যৌন আক্রমণের ঝুঁকি সম্পর্কে ভয়ের উদ্ভব ঘটায়।
তার উপর দিয়ে, অন্যরা একজন মানুষের পোশাক-কে কিভাবে করে বিবেচনা করবে, তা প্রেডিক্ট করা অত্যন্ত কঠিন। এই কারণে, একজন নারী যতই নিজেকে desexualize করার চেষ্টা করুক, তা কখনো সফল হবে না। উদাহরণস্বরূপ, অনেক নারীদেরকে তাদের পোশাক নিয়ে সমালোচনা করা হয় এই ভিত্তিতে যে তাদের পোশাক সেই সময়ের জন্যে appropriate/গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে, সেই নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের পোশাক সেই সময়ের জন্যে আসলে appropriate/গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে, নারীদের পোশাক পরার সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত পরিচয় এবিং নীতির উপরে ভিত্তি করে না। বরং, তাদের সিদ্ধান্ত একইসাথে যৌনযুক্ত বৈশিষ্টের সংমিশ্রনের একটি সমগ্র হিসাবে নারীসলুভ দেহের সামাজিক উপলব্ধিকেও কেন্দ্র করে থাকে (for example- breasts, hips, buttocks, etc)। একজন নারী নিজেকে একজন ব্যক্তি হিসাবে দেখতে পারে, যার আচরণ তার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলন করে। আবার একইসাথে, সেই একই নারী নিজেকে পুরুষদের যৌন মনোযোগের একটি নির্জীব বিষয়বস্তু হিসাবেও বিবেচনা করতে পারে। অন্য মানুষ কিভাবে নারীদের পোশাক-কে ব্যাখ্যা করবে, তার উপরে নারীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এর কারণে, একজন নারীর নিজের শরীরের উপর মালিকানার অনুভূতিটি যৌন আক্রমণের ঝুঁকির ছায়াতলে অদৃশ্য হয়ে যায়। [143]
শুধুমাত্র Objectification-এর কারণে নারীদের Sexualization ক্ষতিকর হতে পারে
Khandis et al (2016)-এর গবেষণায় দেখা গেছে যে শুধুমাত্র অন্যদের দ্বারা objectification-এর কারণে প্রকাশ্য পোশাক পরা নারীরা যৌন আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারে। তাদের রিসার্চ আর্টিকেল-এর মধ্যে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পারি যে ধর্ষণের ককরণ শুধুমাত্র ধর্ষণকারী এবং সেই ধর্ষণকারীর ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং কর্মের প্রয়োগ।
নিজ-ইচ্ছাকৃত Sexualization
“Self-sexualization”-এর সংজ্ঞা হলো যৌন আচরণকে প্রকাশ্যে স্বাভাবিক হিসাবে গ্রহণ করা। [152] “Self-Sexualized” আচরণের উদাহরণ হলো- pole-dancing, প্রকাশ্য পোশাক পরা, এবং সেক্সটিং করার সময় নুড শেয়ার করা। Self-sexualization নারীদেরকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করে নাকি তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা নিয়ে এক্সপার্টদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। নারীদের যৌন চাহিদা বাস্তবায়িত করার সাপেক্ষে Self-sexualization নারীদেরকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করতে পারে। [153] [154] আবার অন্য দিকে, অন্যদের দ্বারা নারীদেরকে কিভাবে উপলব্ধি করা হয়, এবং নারীদের সাথে যেইভাবে আচরণ করা হয়- এই সাপেক্ষে Self-Sexualization নারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। [155]
এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে Risk-Free Sex বা ঝুঁকিহীন যৌনতা বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই। উধারণস্বরূপ, আমরা যদি গাড়ি চালানোর কথা বিবেচনা করি, এখানে বিদ্যমান ঝুঁকিগুলি শুধুমাত্র সেই সকল মানুষদের জন্যে প্রযোজ্য যারা গাড়ি ব্যবহার করে। যারা গাড়ি চালায় না, তাদের জন্যে “গাড়ি চালানোর” কোনো ঝুঁকি নেই। তবে, এই ঝুঁকিগুলির নির্বিশেষে, মানুষ গাড়ি চালায়, এবং মানুষের গাড়ি চালানোর অধিকার রয়েছে। মানুষের কাছে গাড়ি চালানো কোনো ধরণের মূল্য রাখতে পারে, বা তাদের গাড়ি চালানোর কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে।
নারীরা তাহলে Self-Sexualized আচরণে লিপ্ত কেন হয়? তাদের জন্যে Self-Sexualization কি মূল্য রাখে? Self-Sexualization-এর প্রয়োজনীয়তা কি?
নারীদের Self-Sexualized আচরণে লিপ্ত হওয়ার কারণগুলি বৈচিত্রময় এবং জটিল। নারীরা Self-Sexualization-কে আকর্ষণীয় হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপনা করা এবং নিজেরা আকর্ষণীয় বোধ করা হিসাবে বিবেচনা করে, এবং সম্ভ্যাব্য সঙ্গী আকর্ষণ করা হিসাবে বিবেচনা করে। [156] [157] নিজেদের আকর্ষণীয়তা বাড়ানো নারীদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কেননা শারীরিক সৌন্দর্যতা রোমান্টিক পার্টনার হিসাবে নারীদের সামাজিক স্টেটাস এবং মূল্যকে বাড়িয়ে দেয়। [158] নারীদেরকে সমাজ দ্বারা নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য নারীত্বের সীমানা অতিক্রম করার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে, Self-Sexualization নারীদেরকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করতে পারে। একই সাথে Self-Sexualization যৌনতার সাপেক্ষে নারীদের Sexual Agency/মনুষ্য কর্মক্ষমতাকেও প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। [159] [154] Sexual Agency হলো এই ধারণা যে নারীরা তাদের নিজেদের স্বার্থ বিবেচনা করে নিজেদের শরীরকে যৌন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে। এইভাবে, Self-Sexualization-এর মাধ্যমে, নারীরা নানা ধরণের সুবিধা উপভোগ করতে পারে, এবং যেসব নারীরা Self-Sexualized আচরণে লিপ্ত হয়, তারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোধ করতে পারে। [160]
Self-Sexualization-এর ইতিবাচক দিকগুলোর নির্বিশেষে, অনেক নারী Self-Sexualized আচরণে লিপ্ত হতে একটি সামাজিক চাপ অনুভব করে। [157] American Psychological Association-এর Task Force on the Sexualization of Girls প্রকাশ করেছে যে নারীদের উপরে খুব অল্প বয়স থেকে Self-sexualize করার চাপটি শুরু হয়। [161] এর পাশাপাশি, সেই রিপোর্টার মধ্যে Self-sexualization-এর সাথে সম্পর্তিক্ত নেতিবাচক প্রভাবগুলো তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে দেখা গেছে যে নারীরা Self-sexualization-এর মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোধ করলেও, অনেক নারী Self-sexualization-এর কারণে সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। [155] এই সকল মর্মে, Self-sexualization অবচেতনভাবে নারীদের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। [162]
অন্যদের দ্বারা Objectification
Objectification হলো সেই পদ্ধতি, যার অধীনে একজন মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয় না, বরং একটি পণ্য হিসাবে স্বীকৃত পায়, যা শুধুমাত্র অন্যদের দ্বারা সেটির ব্যবহার এবং উপভোগের জন্যে মূল্য দেওয়া হয়। [163] Objectification-এর একটি পরিণতি হলো যে মানুষ বুঝতে ব্যর্থ হয় যে Objectified মানুষদেরও আপেক্ষিক অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি রয়েছে। [164] বরং, মানুষ objectified মানুষদের এমনভাবে বিবেচনা করে যেন তারা মানবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাই, তারা objectified মানুষদের নিজেদের সুবিদার্থে জিনিস হিসাবে ব্যবহার করে।
Objectifed মানুষদের দুটি মানবিক বৈশিষ্ট উপেক্ষা করা হয়-
১) তাদের Agency অর্থাৎ, তাদের কর্মক্ষমতা (Mental Agency + Moral Agency)
২) তাদের Capacity for Experience অর্থাৎ তাদের অনুভব করার ক্ষমতা (Mental Experience + Moral Patiency)
Agency বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তির সচেতনভাবে চিন্তা করার মানসিক ক্ষমতা (mental agency)। একই সাথে Agency-এর মধ্যে নৈতিক সত্তা হিসাবে একজন মানুষের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত, যেখানে তারা নৈতিক এবং অনৈতিক আচরণের মাধ্যমে তাদের পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারে; অর্থাৎ একজন মানুষের moral agency। [165] [166]
Experience বলতে বোঝায় আবেগ ও সংবেদন অনুভব করার মানসিক ক্ষমতা (mental experience)। একই সাথে Agency-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নৈতিক ও নৈতিক আচরণের গ্রহণকারী হিসাবে একজন মানুষের নৈতিক ক্ষমতা (moral patiency)। [165] [166]
এই চারটি ফ্যাক্টরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের নির্বিশেষে, গবেষণায় খুঁজে পাওয়া বিপুল প্রমান আমাদেরকে ইঙ্গিত করে যে Mental Agency, Moral Agency, Mental Experience এবং Moral Patiency তাত্বিকভাবে সম্পর্কিত, এবং একে অন্যের সাথে overlap করে। [167] [166] [168]
একই সাথে আমরা জানতে পারি যে নারীদেরকে অন্যরা করে এবং সেই নারীদের Agency ও Experience-কে উপেক্ষা করা হয়। [169] এই Objectification-এর একটা ব্যাখ্যা হলো যে Objectification তাত্বিকভাবে মানুষের লক্ষ্য সন্ধানের (goal pursuit) জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার উপরে ভিত্তি করা। [170] পুরুষদের মধ্যে যৌন লক্ষ্য সক্রিয় করার কারণে নারীদের sexualized প্রতিনিধিত্ব পুরুষদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলে যে তারা নারীদেরকে যৌন তৃপ্তি মেটানোর একটি যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করে, যা Objectification বাড়িয়ে দিতে পারে। [171] [172] নারীরা অন্যান্য sexualized নারীদেরকেও Objectify করে। এর মাধ্যমে, নারীরা তাদের নিজেদের লিঙ্গের স্বভাবও সমস্যাযুক্ত বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব থেকে দূরে থাকার সুযোগ দেয়। [171] Self-Sexualized নারীরা এইভাবে করে নারী এবং পুরুষ- উভয় দ্বারা Objectified হতে পারে।
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে নারীদেরকে যখন Objectified করা হয়, তখন সেই নারীদের জন্যে ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ Objectification পুরুষদের অ্যালকোহল পান করা এবং তাদের যৌন সহিংসতা করার মধ্যে একটি mediating variable হিসাবে কাজ করে থাকে। [173] নারীদের Agency এবং Experience উপেক্ষা করা সেই সেই নারীটা ইতিবাচক আচরণের প্রাপ্য না এবং ক্ষতির থেকে নিরাপত্তার প্রাপ্য না বলে উপলব্ধি সৃষ্টি করতে পারে। [174] বিশেষভাবে, নারীদের Agency-কে অস্বীকার করা যৌন সহিংসতা বাড়ানোর জন্যে একটি অন্যতম প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একটি Self-sexualized নারীকে যদি এইভাবে বিবেচনা করা হয় যে তার কোনো Agency নেই, তাহলে সেই নারীকে এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন সেই নারীর সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলে তার মন পরিবর্তন করা যাবে, অথবা যেন সেই নারীটা যৌন অগ্রগতি প্রতিরোধ করবে না, এবং এমনকি পুলিশের কাছে যেন সেই নারীটা যৌন সহিংসতা রিপোর্ট করবে না। এই সকল কারণের জন্যে, প্রশমিত Agency-এর উপলব্ধি (যা নারীদের Objectification-এর একটি ফলাফল, যেখানে সেই নারীদেরকে যৌনতায় উন্মুক্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়) নারীদের যৌন সহিংসতার টার্গেট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
Blake et al-এর এই গবেষণার মধ্যে Self-sexualization মৌলিকভাবে নারীদের উপরে যৌন সহিংসতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় না। এই কারণে, Self-sexualization এবং Sexual Assault-এর মধ্যে একটি X causes Y জাতীয় causal relationship বিবেচনা করতে পারি না। বরং, Self-sexualization যৌন সহিংসতার সাথে শুধুমাত্র তখনি সম্পর্কিত হতে পারে যদি দুটি শর্ত পূরণ করা হয়-
১) Self-sexualization নারীদের যৌনতায় উন্মুক্ত হওয়ার অনুমান বাড়িয়ে দেয়।
২) যৌনতায় উন্মুক্ত নারীদেরকে এমনভাবে উপলব্ধি করা হয় যেন তাদের কোনো Agency নেই।
সকল উপলব্ধিকারীরা এইভাবে করে চিন্তা করবে না, কিন্তু যখন তারা তা করবে, তখন নারীদেরকে এমনভাবে উপলব্ধি করা হবে যেন তাদের সাথে বেশ সহজেই যৌন সহিংসতা করা যাবে।
যদিও Blake et al-এর এই গবেষণাটি নারীদের -কে কেন্দ্র করে, তাদের তথ্যকে কখনোই নারীদেরকে ভিক্টিম-ব্লেমিং করার অনুমুতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত না। নারীদেরকে সত্যিকারের এবং কাল্পনিক ধর্ষণের জন্যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, এবং লেখণ্ডের উদ্দেশ্য কখনো এটি না যে এই আগুনে তারা বেশি বেশি করে তেল ঢেলে দিবে। নারীদের উপরে যেকোনো ধরণের অপরাধ শুধুমাত্র সেই অপরাধীরই দোষ। তবে, পোশাক সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি যৌন আক্রমণকারীদের মানসিক প্রক্রিয়া বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করে। [162]
Agency Mediation Model- নারীদের Sexual Openness-কে যত বেশি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাদেরকে সেই পরিমানে সেই নারীদের Agency-এর অভাব আছে বলে উপলব্ধি করা হয়। Self-sexualization একা নারীদের Sexual Openness-এর উপলব্ধি অথবা যৌন এগ্রেশন-এর perceived vulnerability-এর উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। এই কারণে, Self-sexualization, যৌনতায় উন্মুক্ত হওয়ার অনুমান, এবং Perceived Sexual Aggression Vulnerability-এর মধ্যে Arrows-গুলি dashed lines দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, এবং “NS” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যার মানে হলো Non-Significant। অর্থাৎ, Self-sexualization, এবং Perceived Sexual Aggression Vulnerability-এর মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ Statistical সম্পর্ক নেই, হোক সেটা Causal অথবা Correlation-এর সম্পর্ক।
বরং, একজন Self-sexualized নারীর Perceived Sexual Aggression Vulnerability বাড়িয়ে দেয় যখন অন্যরা সেই নারীকে Sexually Open হিসাবে অনুমান করে এবং সেই নারীটার কম Agency হিসাবে অনুমান করে। এই কারণে, লেখকগণ উপসংহারে পরিষ্কারভাবে লিখে যে পুরুষরা নারীদেরকে শুধুমাত্র তখনি যৌন সহিংসতার জন্যে টার্গেট করবে যদি দুটি শর্ত পূরণ করা হয়-
১) যদি মানুষ অনুমান করে যে একজন Self-sexualized নারী বেশি মাত্রায় Sexually Open।
২) সেই Sexual Openness-এর অনুমান সেই নারীটার কম Agency আছে বলে একটি উপলব্ধি সৃষ্টি করে। [162]
পোশাক কোনোভাবেই সম্মতির প্রমান নয়
পোশাক যে যৌন সঙ্গমের সম্মতি হতে পারে, তা এই এম্পিরিক্যাল তথ্যের উপরে ভিত্তি করা যে অনেক মানুষ অন্যদের উদ্দেশ্য এবং মনোভাব তাদের পোশাকের মাধ্যমে অনুমান করে থাকে। যেহেতু এই ধরণের অনুমান সাধারণত ভুল হয়ে থাকে,পোশাক কখনো পোশাক পরিধানকারীর উদ্দেশ্য বা মনোভাব যাচাই করার জন্যে কোনো প্রাসঙ্গিক প্রমান নয়। এই সকল কারণের জন্যে, আদালতের মধ্যে, পোশাক-কে কখনোই বাদীর উদ্দেশ্য বা মনোভাবের প্রমান হিসাবে গণ্য করা উচিত না।
প্রমাণকে “Probative” হিসাবে গণ্য করা হয় যখন সেই প্রমান কোনো মালমার প্রাসঙ্গিক তথ্যকে সত্য বা মিথ্যা হিসাবে স্থাপন করতে সাহায্য করে। ধর্ষণ এবং যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগীর মনোভাব এবং উদ্দেশ্য আইনিভাবে প্রাসঙ্গিক। তবে, ভুক্তভোগীর সেই মনোভাবের প্রমান হিসাবে পোশাক-কে গণ্য করা উচিত না, কারণ পোশাক সেই মনোভাব যাচাই করার জন্যে Probative নয়। যেহেতু, উদ্দেশ্য এবং মনোভাব নির্ধারণ করার জন্যে পোশাকের কোনো Probative Value নেই, পোশাক কোনো ভাবেই প্রাসঙ্গিক নয়।
ধর্ষণ, যৌন হয়রানি বা যৌন আক্রমণকে “স্বাগত” করার জন্যে বা সেখানে ভুক্তভোগীর সম্মতি নির্ধারণ করার জন্যে যদি ভুক্তভোগীর পোশাক-কে প্রমান হিসাবে আনা হয়, তাহলে সেটাকে সহজাতভাবে অগ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। অবশ্যই, বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে পোশাক রক্ত, ময়লা এবং বীর্যের দাগ দেখাতে পারে, অথবা পোশাকের মধ্যে ছিদ্র জোরপূর্বকভাবে পোশাক খুলে দেওয়ার প্রমান হতে পারে। এই সকল পরিস্থিতির মধ্যে, পোশাক অবশ্যই গ্রহণযোগ্য প্রমান হিসাবে গণ্য। তবে, ভুক্তভোগীর মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য এবং মনোভব যাচাই করার জন্যে, পোশাক কখনোই গ্রহণযোগ্য প্রমান নয়।
সম্মতি জানানোর জন্য পোশাক-এর ব্যবহারের একটি মূল সমস্যা হল যে যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে পোশাক অন্তর্নিহিতভাবে অস্পষ্ট। পর্যবেক্ষক এবং প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীলতার কারণে এবং পোশাকের অস্পষ্ট এবং অকেন্দ্রিক প্রকৃতির কারণে যোগাযোগের একটি ফর্ম হিসাবে পোশাককে ভাষার সাথে সমতুল্য করা যায় না। এই সমস্যার সত্ত্বেও, অনেকেই অন্যদের ব্যাপারে চরিত্র অনুমান করে তাদের পোশাকের মাধ্যমে। যেহেতু সমাজবৈজ্ঞানিক রিসার্চ আমাদেরকে দেখায় যে এই ধরণের অনুমান প্রায়শই ভুল হয়ে থাকে, আদালতের মধ্যে পোশাকের সূচনাটি সমস্যাদায়ক। অতএব, একজন ভুক্তভোগীর পোশাক সেই ভুক্তভোগীর সম্মতি নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত না, কেননা পোশাক কোনো মানুষের মনোভাব, উদ্দেশ্য বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের accurate indicator নয়।
পোশাকের মাধ্যমে অনুমানগুলি শুধুমাত্র ভুলই নয়, সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে পর্যবেক্ষকের লিঙ্গের উপরে ভিত্তি করে সেই অনুমানগুলির মধ্যে পক্ষপাতিত্ব/bias ঢুকে যায়। যেহেতু নারীদের তুলনায় পুরুষরা নারীদের আচরণকে যৌন প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে থাকে, পুরুষ jurors, judges এবং attorneys যৌন আক্রমণ ও যৌন হয়রানির নারী ভুক্তভোগীদের আচরণকে বেশি করে যৌন প্রেক্ষাপটে দেখবে; নারী jurors, judges এবং attorneys-দের তুলনায়। তাই, এটি সম্ভাব্য যে আদালত ভুক্তভোগীর পোশাককে সম্মতির প্রমান হিসাবে গ্রহণ করে নিতে পারে, যখন কোনোভাবেই সম্মতি দেওয়া হয় নি। একইসাথে, নারীরা এই সমস্যার সমাধান সর্বদা করতে পারে না। সমাজবৈজ্ঞানিক রিসার্চ থেকে আমরা জানতে পারি যে নারীরাও ভুক্তভোগীর পোশাকের প্রাসঙ্গিকতাকে সঠিকভাবে যাচাই করতে পারে না, কেননা নারীরা ভুক্তভোগীদের প্রতি একটি পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব পোষণ করতে পারে । তবে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ভুক্তভোগীদের প্রতি পুরুষ এবং নারীদের এই পক্ষপাতিত্ব/bias সম্পূর্ণভাবে আলাদা এবং ভিন্ন।
আদালত যখন সম্মতি নির্ধারণ করার জন্যে পোশাককে প্রমান হিসাবে গণ্য করার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের অবশ্যই পোশাকের probative value এবং পোশাকের prejudicial effect-কে একইসাথে বিবেচনা করতে হবে। তবে, এই পদ্ধতিও অগ্রহণযোগ্য কেননা বিচারক অন্যান্য সকল মানুষের মতন একইভাবে সমাজের বাঁধাধরা ধারণা অনুসরণ করে ভুক্তভোগীর পোশাকের উপর ভিত্তি করে ভুলভাবে ভুক্তভোগীর সম্মতির অনুমান করতে পারে। এর উপর দিয়ে, jury-কে ভুক্তভোগীর পোশাককে গ্রহণ না করার নির্দেশ একইভাবে অগ্রহণযোগ্য কেননা গবেষণা আমাদেরকে দেখায় যে মানুষকে সঠিকতার নির্দেশ দেওয়া সেই মানুষের অনুমানকে সঠিক করে দেয় না। ভুক্তভোগীর আইনজীবী পর্যন্ত আদালতের পোশাককে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপত্তি নাও তুলতে পারে, কেননা তারাও সেই বাঁধাধরা ধারণা অনুসরণ করে ভুল অনুমান করতে পারে। যেহেতু অন্য কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই, যৌন আক্রমণ, হয়রানি বা ধর্ষণের মধ্যে ভুক্তভোগীর সম্মতির প্রমান হিসাবে ভুক্তভোগীর পোশাককে সকল রাষ্ট্রের সহজাতভাবে অগ্রহণযোগ্য হিসাবে ঘোষণা করে দেওয়া উচিত।
আসামিপক্ষ যখন ভুক্তভোগীর পোশাককে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করতে চায়, তখন তারা দাবি করে থাকে যে ভুক্তভোগী নিজেই তার সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের মধ্যে অবদান রেখেছে। যেহেতু সাধারণ সামাজিক মনিভাবগুলি বিচারকদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, এটি সম্ভাব্য যে তারা বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাসের উপর কাজ করে যে পোশাকের মাধ্যমে একজন নারী তার সাথে গোটা যাওয়া অপরাধের মধ্যে নিজেই অবদান রাখতে পারে। যেহেতু এই ধরনের অনুমানগুলি ভুল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং যেহেতু বিচারকরা সেই অনুমানগুলি নিজেরাই করার সম্ভাবনা রাখে, তাই, এমন আইন দরকার যা পোশাককে জুরির কাছে পৌঁছাতে দিতে দেয় না। [175]
উপসংহার
“পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে” বাক্যটি যখন নারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়, তখন ধর্ষণকারী পুরুষের আচরণের দায়বদ্ধতা unfair ভাবে নারীদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেই ব্যাপক মাত্রায় এই ধারণার প্রচলন ঘটে, সেই একই মাত্রায় ধর্ষণ সম্পর্কিত উপকথা বা Rape Myth-এর প্রচলন ঘটে। সমাজের মধ্যে ধর্ষণের এই উপকথা বা Rape Myth-এর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগ পুরুষতান্ত্রিক ধর্ষণ সংস্কৃতিকে ন্যায্যতা দেয়, যেখানে নারীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতাকে স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য আচরণ বলে গণ্য করা হয়। মৌলিকভাবে, এই বাক্যটি ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করে, এবং একইসাথে, গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত, ধর্ষণের ভুক্তভোগী হওয়ার সাথে প্রকাশ্য পোশাক পরিধান করার কোনো causal বা correlation-এর সম্পর্ক নেই। প্রমান দ্বারা অসমর্থিত হওয়ার পাশাপাশি, এই বাক্যটি পুরুষদের যৌনতার বিশেষাধিকারকে বজায় রাখে- যেই যৌনতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীরা নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। কেবলমাত্র আশাই করা যায় যে একদিন এই ধরণের প্রত্যাশা, এবং stereotypical/বাঁধাধরা উপলব্ধি থেকে সমাজ একদিন বেরিয়ে আসতে পারবে।
তথ্যসূত্র
- Edmonds, E. M., and Cahoon, D. D. (1986). Attitudes concerning crimes related to clothing worn by female victims. Bull. Psychon. Soc. 24: 444–446.[↑][↑][↑]
- Kanekar, S., and Kolsawalla, M. B. (1980). Responsibility of a rape victim in relation to her respectability, attractiveness, and provocativeness. J. Soc. Psychol. 112: 153–154.[↑]
- Whatley, M. A. (1996). Victim characteristics influencing attributions of responsibility to rape victims: A meta-analysis. Aggression Violent Behav. 1: 81–95.[↑]
- Whatley, M. A. (1994, November). Factors Affecting Attributions of Blame for Date Rape. In Poster session presented at the annual meeting of the Society for Southeastern Social Psychologists, Winston-Salem, NC.[↑]
- Simonson, K., and Subich, L. M. (1999). Rape perceptions as a function of gender-role traditionality and victim-perpetrator association. Sex Roles 40(7–8): 617–634.[↑]
- Whatley, M. (2005). The Effect of Participant Sex, Victim Dress, and Traditional Attitudes on Causal Judgments for Marital Rape Victims. Journal of Family Violence, 20, 191–200.[↑]
- Altrows, A. (2016). Rape Scripts and Rape Spaces: Constructions of Female Bodies in Adolescent Fiction. International Research in Children’s Literature, 9(1), 50–64.[↑]
- Burt, 1991; Lonsway & Fitzgerald, 1994[↑]
- Burt, 1991[↑]
- Cowan, G. (2000). Beliefs About the Causes of Four Types of Rape. 17. p.808-809[↑]
- Lonsway, K. A., & Fitzgerald, L. F. (1994). RAPE MYTHS. In Review. Psychology of Women Quarterly, 18(2), 133–164.[↑]
- Johnson, V., Nadal, K., Sissoko, G., & King, R. (2021). “It’s Not in Your Head”: Gaslighting, ‘Splaining, Victim Blaming, and Other Harmful Reactions to Microaggressions. Perspectives on Psychological Science, 16, 1024–1036.[↑][↑]
- Harber et al., 2015[↑]
- Mekawi & Todd, 2018; Ryan, 1976[↑]
- Ardovini-Brooker & Caringella-MacDonald, 2002; Burt, 1980; Cowan, 2000; De Judicibus & McCabe, 2001; Lonsway & Fitzgerald, 1994; Kopper, 1996; Koss & Harvey, 1991[↑]
- Lonsway & Fitzgerald, 1994[↑]
- Koss & Harvey, 1991[↑]
- Buddie & Miller, 2002; Burt 1980[↑]
- De Judicibus & McCabe, 2001; Jimenez & Abreu, 2003; Kopper, 1996; Russell, 2004[↑]
- Burt 1980; Lonsway & Fitzgerald, 1994; Koss & Harvey, 1991[↑]
- Moor, A. (2010). She Dresses to Attract, He Perceives Seduction: A Gender Gap in Attribution of Intent to Women’s Revealing Style of Dress and its Relation to Blaming the Victims of Sexual Violence. 11, 14[↑]
- come again? 2011[↑]
- Mendes, K. (2015). Representing the Movement: SlutWalk Challenges Rape Culture. In K. Mendes (Ed.), SlutWalk: Feminism, Activism and Media (pp. 86–112). Palgrave Macmillan UK.[↑]
- Moor, A. (2010). She Dresses to Attract, He Perceives Seduction: A Gender Gap in Attribution of Intent to Women’s Revealing Style of Dress and its Relation to Blaming the Victims of Sexual Violence. 11, 14[↑][↑][↑][↑][↑][↑][↑][↑][↑]
- Calogero, R. (2004). A test of objectification theory: The effect of the male gaze on appearance concerns in college women. Psychology of Women Quarterly, 28, 16-21.[↑][↑]
- Fredrickson, B. L. & Roberts, T. A. (1997). Objectification Theory: Toward understanding women’s lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly, 21, 173-206.[↑]
- Noll, S. M. & Fredrickson, B. L. (1998). A mediational model linking self-objectification, body shame, and disordered eating. Psychology of Women Quarterly, 22, 623-633.[↑]
- Strelan, P., & Hargreaves, D. (2005). Women who objectify other women: The vicious circle of objectification. Sex Roles, 52, 707-712.[↑]
- Johnson, K. P., Hegland, J. E., & Schofield, N. A. (1999). Survivors of rape: Functions and implications of dress in a context of coercive power. In K. P. Johnson & S.J.Lennon (Eds.), Appearance and Power (pp. 11-32). NY: Berg.[↑]
- Berger, J. (1972). Ways of seeing. London: Penguin.[↑]
- MacKinnon, C. A. (1989). Sexuality, pornography, and method: “Pleasure under Patriarchy”. Ethics, 99, 314-346.[↑]
- LeMoncheck, L. (1985). Dehumanizing Women: Treating Persons as Sex Objects. Rowman & Allanheld Publishers.[↑]
- Muehlenkamp, J. J. & Saris-Baglama, R. N. (2002). Self objectification and its consequences for college women. Psychology of Women Quarterly, 26, 371-379.[↑]
- Buddie & Miller, 2002; Cowan, 2000; Koss & Harvey, 1992[↑]
- e.g., De Judicibus & McCabe, 2001; Jimenez & Abreu, 2003; Kopper, 1996; Russell, 2004[↑]
- Wikipedia- What Were You Wearing?[↑]
- United Nations- What Were You Wearing?[↑]
- Google: Oxford Languages[↑]
- Whatley, M. A. (1996). Victim characteristics influencing attributions of responsibility to rape victims: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 1(2), 81-95.[↑]
- Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley.[↑][↑]
- Jones, E. E., & Davis, K. E. (1965). From acts to dispositions: The attribution process in social psychology. In L. Berkowitz (ed.), Advances in experimental social psychology (Volume 2, pp. 219-266), New York: Academic Press.[↑]
- Jones, E. E., & Nisbett, R. E. (1971). The Actor and the Observer: Divergent Perceptions of the Causes of Behavior. New York: General Learning Press.[↑]
- Kelley, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology. Nebraska Symposium on Motivation, 15, 192-238[↑]
- Wegner, D., & Vallacher, R. (1977). Implicit Psychology. New York: Oxford University Press.[↑]
- Maddux, W. W., & Yuki, M. (2006). The “ripple effect”: Cultural differences in perceptions of the consequences of events. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(5), 669-683.[↑]
- Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1991). Social Cognition. New York: McGraw-Hill, Inc.[↑]
- Kim, K., Johnson, P., & Workman, J.E., (1994). Blaming the Victim: Attributions Concerning Sexual Harassment Based on Clothing, Just-World Belief and Sex of Objects. Family and Consumer Sciences Research Journal, 22, 382-400.[↑]
- Rotter, J. (1996). Generalized expectancies for internal vs. external control of reinforcement. Psychological Monograms, 80, 1-28.[↑]
- Cann, A., Calhoun, L. G., & Selby, J. W. (1979). Attributing responsibility to the victim of rape: Influence of information regarding past sexual experience. Human Relations, 32, 57-68.[↑][↑]
- Kanekar, S., & Vaz, L. (1983). Determinants of perceived likelihood of rape and victim’s fault. Journal of Social Psychology, 120, 147-148.[↑]
- Muller, R., Caldwell, R., & Hunter, J. (1994). Factors predicting the blaming of victims of physical child abuse or rape. Canadian Journal of Behavioral Science, 26, 259-279.[↑]
- Shaver, K. (1970). Defensive attribution: Effects of severity and relevance of responsibility assigned for an accident. Journal of Personality and Social Psychology, 14, 101-113.[↑]
- Thornton, B., Ryckman, R., & Robbins, M. (1982). The relationship of observer characteristics to beliefs in causal responsibility of victims of sexual assault. Human Relations, 35, 321-330.[↑]
- Kleinke, C., & Meyer, C. (1990). Evaluation of a rape victim by men and women with high and low belief in a just world. Psychology of Women Quarterly, 14, 343–53.[↑]
- Lerner, M., & Matthews, G., (1967). Reactions to suffering of others under conditions of indirect responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 5(3), 319-325.[↑]
- Calhoun, L. G., Selby, J. W., & Warring, L. J. (1976). Social perception of the victim’s casual role in rape: An exploratory examination of four factors. Human Relations, 29, 517-526.[↑]
- Donnerstein, E., & Berkowitz, L. (1981). Victim reactions in aggressive erotic films as a factor in violence against women. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 710-724[↑]
- Janoff-Bulman, R., Timko, C., & Carli, L. (1985). Cognitive biases in blaming the victim. Journal of Experimental Social Psychology, 21(2), 161-177.[↑]
- Muehlenhard, C. & MacNaughton, J. (1988). Women’s beliefs about women who “lead men on”. Journal of Social and Clinical Psychology, 7, 65-79.[↑]
- Muehlenhard, C.L., & Rogers, C.S., (1993). Narritive descriptions of “token resistance to sex”. In C.L. Muehlenhard, C.L (Chair), “Token resistance” to sex: Challenging a sexist stereotype. Symposium conducted at the annual meeting of the American Psychological Association, Toronto, Canada.[↑]
- Horgan, D., & Reeder, G. (1986). Sexual harassment: The eye of the beholder. American Association of Occupational Health Nursing Journal, 34, 83-86.[↑]
- Grubb, A., & Turner, E. (2012). Attribution of blame in rape cases: A review of the impact of rape myth acceptance, gender role conformity and substance use on victim blaming A Grubb, E Turner Aggression and Violent Behavior. Aggression and Violent Behavior, 17, 443–452[↑][↑]
- Kelley & Michela, 1980[↑]
- Lewis, L., & Johnson, K. K. P. (1989). The effect of dress, cosmetics, sex of subject, and causal inference on attribution of victim responsibility. Clothing and Textiles Research Journal, 22–29.[↑]
- Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70(3), 491-512.[↑]
- Glick, P., & Fiske, S. T. (1999). The ambivalence toward men inventory. Psychology of Women Quarterly, 23(3), 519-536.[↑]
- Glick, P., & Fiske, S. T. (2001). An ambivalent alliance: Hostile and benevolent sexism as complementary justifications for gender inequality. American Psychologist, 56(2), 109.[↑]
- Abrams, D., Viki, G. T., Masser, B., & Bohner, G. (2003). Perceptions of stranger and acquaintance rape: the role of benevolent and hostile sexism in victim blame and rape proclivity. Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), 111-125.[↑][↑][↑]
- Canto, J. M., Perles, F., & Martín, J. S. (2014). The role of right-wing authoritarianism, sexism and culture of honour in rape myths acceptance/El papel del autoritarismo de derechas, del sexismoy de la cultura del honor en la aceptación de los mitos sobre la violación. Revista de Psicología Social, 29(2), 296-318.[↑]
- Chapleau, K. M., Oswald, D. L., & Russell, B. L. (2007). How ambivalent sexism toward women and men support rape myth acceptance. Sex Roles, 57(1-2), 131-136.[↑]
- Rollero, C., & Tartaglia, S. (2019). The Effect of Sexism and Rape Myths on Victim Blame. Sexuality & Culture, 23(1), 209–219[↑][↑]
- Quackenbush, 1991; Tieger, 1981[↑]
- Koss, Leonard, Beezley, & Oros, 1985; Muehlenhard & Linton, 1987[↑]
- Workman, J. E., & Freeburg, E. W. (1999). An Examination of Date Rape, Victim Dress, and Perceiver Variables Within the Context of Attribution Theory. Sex Roles, 41(3), 261–277. [↑][↑]
- Bohner, G., Eyssel, F., Pina, A., Siebler, F., & Viki, G. T. (2009). Rape myth acceptance: Cognitive affective and behavioural effects of beliefs that blame the victim and exonerate the perpetrator. In M. Horvath & J. Brown (Eds.), Rape: Challenging contemporary thinking (pp. 17–45). Devon: Willan p. 34[↑]
- Bohner, G., Eyssel, F., Pina, A., Siebler, F., & Viki, G. T. (2009). Rape myth acceptance: Cognitive affective and behavioural effects of beliefs that blame the victim and exonerate the perpetrator. In M. Horvath & J. Brown (Eds.), Rape: Challenging contemporary thinking (pp. 17–45). Devon: Willan[↑]
- Lonsway, K. A., & Fitzgerald, L. F. (1995). Attitudinal antecedents of rape myth acceptance: A theoretical and empirical reexamination. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 704–711.[↑]
- Ryan, K. (2011). The Relationship between Rape Myths and Sexual Scripts: The Social Construction of Rape. Sex Roles, 65, 774–782.[↑]
- Van der Bruggen, M., & Grubb, A.R. (2014). A review of the literature relating to rape victim blaming: An analysis of the impact of observer and victim characteristics on attribution of blame in rape cases. Aggression and Violent Behavior, 19(5), 523-531.[↑]
- Workman, J. E., & Freeburg, E. W. (1999). An Examination of Date Rape, Victim Dress, and Perceiver Variables Within the Context of Attribution Theory. Sex Roles, 41(3-4), 261-277.[↑]
- Loughnan, S., & Pacilli, M. G. (2014). Seeing (and treating) others as sexual objects: toward a more complete mapping of sexual objectification. TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 21(3), 309-325.[↑][↑][↑]
- Kay, A. C., Jost, J. T., & Young, S. (2005). Victim derogation and victim enhancement as alternate routes to system justification. Psychological Science, 16(3), 240-246.[↑]
- Anderson, K. B., Cooper, H., & Okamura, L. (1997). Individual Differences and Attitudes Toward Rape: A Meta-Analytic Review. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(3),295-315.[↑]
- Lambert, A. J., & Raichle, K. (2000). The Role of Political Ideology in Mediating Judgments of Blame in Rape Victims and their Assailants: A test of the Just World, Personal Responsibility, and Legitimization Hypotheses. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(7), 853-863.[↑][↑]
- Altemeyer, B. (1981). Right-Wing Authoritarianism. Winnipeg, Manitoba, Canada: University of Manitoba Press.[↑]
- Altemeyer, B. (1988). Enemies of freedom: Understanding Right-Wing Authoritarianism. San Francisco, CA: Jossey-Bass.[↑]
- Duckitt, J. (2006). Differential Effects of Right Wing Authoritarianism and Social Dominance Orientation on Outgroup Attitudes and Their Mediation by Threat From and Competitiveness to Outgroups. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(5), 684-696.[↑]
- Jost, J. T., & Kay, A. C. (2005). Exposure to Benevolent Sexism and Complementary Gender Stereotypes: Consequences for Specific and Diffuse Forms of System Justification. Journal of Personality and Social Psychology, 88(3), 498-509.[↑][↑]
- Sibley, C. G., Wilson, M. S., & Duckitt, J. (2007). Antecedents of men’s hostile and benevolent sexism: The dual roles of social dominance orientation and right-wing authoritarianism. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(2), 160-172.[↑][↑][↑]
- Manoussaki, K., & Veitch, F. (2015). Ambivalent Sexism, Right Wing Authoritarianism and Rape Myth Acceptance in Scotland. International Journal of Gender and Women’s Studies, 3(1), 88-100.[↑][↑]
- Spaccatini, F., Pacilli, M. G., Giovannelli, I., Roccato, M., & Penone, G. (2019). Sexualized Victims of Stranger Harassment and Victim Blaming: The Moderating Role of Right-Wing Authoritarianism. Sexuality & Culture, 23(3), 811–825.[↑][↑]
- Pacilli, M. G., Pagliaro, S., Loughnan, S., Gramazio, S., Spaccatini, F., & Baldry, A. C. (2017). Sexualization reduces helping intentions towards female victims of intimate partner violence through mediation of moral patiency. British Journal of Social Psychology, 56(2), 293-313.[↑]
- Fairchild, K., & Rudman, L. A. (2008). Everyday Stranger Harassment and Women’s Objectification. Social Justice Research, 21(3), 338-357.[↑]
- McCarty, M. K., Iannone, N. E., & Kelly, J. R. (2014). Stranger Danger: The Role of Perpetrator and Context in Moderating Reactions to Sexual Harassment. Sexuality & Culture, 18(4), 739-758.[↑]
- Aviva Orenstein, No Bad Men: A Feminist Analysis of Character Evidence in Rape Trials, 49 HASTINGS L.J. 663, 677-78 (1998); see also Joyce E. Joyce E. Williams & Karen A. Holmes, The Second Assault: Rape And Public Attitudes 118 (1981) (discussing study finding that most people believe rapists are “crazy”).[↑]
- See, e.g., Katharine K. Baker, Once A Rapist? Motivational Evidence and Relevancy In Rape Law, 110 Harvard Law Review 563, 576-78 (1997) (reviewing social science data regarding the “normality” of rapists).[↑]
- National Victim Center And Crime Victims Research And Treatment Center, Rape In America: A Report to the Nation 4 (1992) [hereinafter RAPE IN AMERICA] (summarizing results of the National Women’s Survey); see also infra notes 129, 143, 144[↑]
- Diane E.H. Russell, The Politics of Rape: The Victim’s Perspective 82-86 (1974) (discussing rape by lovers); Estrich, Rape, supra note 7, at 1092-93 (citing feminist writers who assert “that most of what passes for ‘sex’ in our capitalist society is coerced”).[↑]
- Wells, C. E., & Elliott, E. (2001). Reinforcing the Myth of the Crazed Rapist: A Feminist Critique of Recent Rape Legislation. BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW, 81, 73.[↑][↑]
- Stevi Jackson, The Social Context of Rape, in RAPE & SOCIETY 16 (Patricia Searles & Ronald J. Berger eds., 1995).[↑]
- See Hubert S. Feild, Attitudes Toward Rape: A Comparative Analysis of Police, Rapists, Crisis Counselors, and Citizens, 36 J. PERSONALITY & SOC. PSYCHOL. 156, 169 (1978), discussing police attitudes towards rapists including their belief, similar to that of rapists themselves, that they are not mentally normal[↑]
- Duncan Chappell & Susan Singer, Rape in New York City: A Study of the Material in the Police Files and Its Meaning, in FORCIBLE RAPE: THE CRIME, THE VICTIM & THE OFFENDER 245 (Duncan Chappell et al., eds. 1977), noting that New York police found 24% of acquaintance rape cases to be without merit as opposed to only 5% of stranger rape cases[↑]
- Estrich, Rape, supra note 7, at 1087-88 describing police officers’ response to her rape by a stranger with a weapon as legitimate because of circumstances[↑]
- Many prosecutors, like police, consider stranger rape to be more serious than acquaintance rape and more vigorously pursue those cases. See, e.g., Robert A . Weninger, Factors Affecting the Prosecution of Rape: A Case Study of Travis County, 64 VA. L. REV. 357, 380 (1978) noting that “the probability of an indictment was highest in cases of strangers and lower, not in cases of friends, but in those cases of acquaintances”; id. at 385 (suggesting that juries may demand greater evidence of nonconsent in acquaintance rape, and “[tihese expectations of jury reaction seem likely to have influenced prosecutors’ perceptions of their chances for success at trial and, therefore, their decisions to indict”). To be sure prosecutors’ reluctance to pursue acquaintance rape cases could be related to their belief in their likelihood of success at trial rather than to a firmly held belief regarding the “crazed” nature of rapists.[↑]
- See Bryden & Lengnick, supra note 92, at 1246-54 (discussing prosecutorial disinclination to pursue “unwinnable” cases and noting that acquaintance rape cases are more difficult to win than stranger rape cases). Even so, the decision to prosecute is directly related to what a prosecutor thinks the public will believe. Given the public’s firmly held belief in the crazed rapist, prosecutors at least partly utilize the myth in their decision-making. Moreover, prosecutors frequently use the image of rapist as “crazed beast” in their arguments in stranger rape cases, thus solidifying the myth.[↑]
- See Lisa A. Binder, “With More Than Admiration He Admired”: Images of Beauty and Defilement in Judicial Narratives of Rape, 18 HARV. WOMEN’S L.J. 265, 274 (1995) (discussing and citing instances of prosecutorial use of the image of rapists as beasts).[↑]
- See WILLIAMS & HOLMES, supra note 9, at 19 (citing a study of judicial attitudes classifying “genuine” rape as those involving women attacked by “a stranger leaping out of the shadows of a dark alley”).[↑]
- In a comprehensive jury study, Professors Kalven and Zeisel revealed that juries were far less likely to convict an accused man of rape when the rape was not stereotypical – i.e., where there was no extrinsic violence or multiple assailants and where the victim and assailant knew one another. See HARRY KALVEN, JR. & HANS ZEISEL, THE AMERICAN JURY 252-3 (1966);[↑]
- see also Biyden & Lengnick, supra note 92, at 1263 n.442 (citing later studies tending to confirm Kalven & Zeisel’s conclusions); FEILD & BIENEN, supra note 121, at 56 (study of potential jurors revealed that 85% viewed rapists as “not normal” and 57% viewed them as mentally ill);[↑]
- Wenniger, supra note 125, at 370 (noting that the rape victim often carried a greater burden because “grand jurors were especially inquisitive if a prior relationship existed or if there was any question concerning consent to intercourse”).[↑]
- See Mary P. Koss et al., Stranger and Acquaintance Rape, 12 PSYCHOL. WOMEN Q. 1, 4 (1988) (57% of women surveyed who were raped did not realize that the sex in which they were forced to engage was rape);[↑]
- WARSHAW, supra note 93, at 26 (only 26% of women surveyed whose sexual assault met the legal definition of rape thought of themselves as rape victims).[↑]
- See RAPE IN AMERICA, supra note 11, at 4 (“The National Women’s Survey clearly dispels the common myth that most women are raped by strangers.”). The offender statistics break down as follows: husbands or ex-husbands (9%), fathers or step-fathers (11%), boyfriends or ex-boyfriends (10%), other relatives (16%), and non-relative acquaintances (29%).[↑]
- G.G. Abel, J.V. Becker, & L.J. Skinner, Aggressive Behavior and Sex, 3 PSYCHIATRIC CLINICS OFN. AM. 133, 140 (1980).[↑]
- Steven J. Morse, Fear or Danger, Flight From Culpability, 4 PSYCHOL. PUB. POL’Y & L. 250, 263 (1998) (“Most arguments that facilely suggest that sexual impulses or desires, or any other kind, are necessarily uncontrollable are conceptually and empirically unsupported.”). Many scholars note that while sexual offenders often claim to feel unable to control their desires, there is “a considerable difference between a desire not resisted and an irresistible desire.” Bruce J. Winick, Sex Offender Law in the 1990s: A Therapeutic Jurisprudence Analysis, 4 PSYCHOL. PUB. POL’Y & L. 505, 521 (1998).[↑]
- Baker, supra note 10, at 577. For studies regarding the “normality” of men who rape, see James V. Check & Neil Malamuth, An Empirical Assessment of Some Feminist Hypotheses About Rape, 8 INT’L J. WOMEN’S STUD. 414,415 (1985).[↑]
- See Paul Schewe & William O’Donohue, Rape Prevention: Methodological Problems and New Directions, 13 CLINICAL PSYCHIATRY REV. 667, 668 (1972) (“At this point, it appears that deviant arousal may not be a necessary or sufficient cause of rape, as some researchers have failed to find significant differences between rapist and nonrapist populations.”). Studies reporting that a substantial portion of college males indicate a likelihood of committing rape if there were no negative consequences also support the proposition that rapists are relatively normal.[↑]
- Check & Malamuth, supra note 132, at 416 (study found that 35% of men questioned would rape if they were assured of not getting caught); Neil M. Malamuth, Rape Proclivity Among Males, 37 J. SOC. ISSUES 138, 140 (describing the results of the previously cited study). Moreover, a number of “normal” college men have admitted to committing rape.[↑]
- See Mary P. Koss, Hidden Rape: Sexual Aggression and Victimization in a National Sample of Students in Higher Education, in 2 RAPE & SEXUAL ASSAULT 1, 11 (Ann Wolbert Burgess ed., 1988) (nationwide survey of over 6100 college males revealed that I in 12 admitted to committing rape);[↑]
- Karen Rapaport & C. Dale Posey, Sexually Coercive College Males, in ACQUAINTANCE RAPE, supra note 87, at 217, 219-20 (43% of college males surveyed admitted to engaging in coercive sex); see also sources cited in Baker, supra note 10, at 576 n.61 (describing the results of the Rapaport & Posey study and surveying the results of several other studies that “found lower, but nonetheless startling percentages of men who admit to engaging in coercive sex”).[↑]
- See Check & Malamuth, supra note 132, at 415 (describing studies linking sexual aggressivity to “socially acquired attitudes about rape, women, and sexual relations” and a self-reported likelihood of committing rape to “acceptance of rape myths … violence against women, and sex-role stereotyping”);[↑]
- Mary P. Koss et al., Nonstranger Sexual Aggression: A Discriminant Analysis of the Psychological Characteristics of Undetected Offenders, 12 SEx ROLES 981, 989 (1985) (noting that sexually aggressive men are more likely to “attribute adversarial qualities to interpersonal relationships, to accept sex-role stereotypes, to believe myths about rape, to feel that rape prevention is the woman’s responsibility, and to view as normal an intermingling of aggression and sexuality”).[↑]
- Karp, supra note 24, at 24.[↑]
- See Mary P. Koss, Hidden Rape: Sexual Aggression and Victimization in a National Sample of Students in Higher Education, in Rape And Sexual Assault, Ann Wolbert Burgess ed., 1988[↑]
- See Karen R. Rapport & C. Dale Posey, Sexually Coercive College Males, in Acquaintance Rape: The Hidden Crime (Andrea Parrot & Laurie Bechhofer eds., 1991) [hereinafter ACQUAINTANCE RAPE]. Although this study relied on a self-report method, it was based in part on studies of adjudicated rapists. Other studies have found lower, but nonetheless startling percentages of men who admit to engaging in coercive sex. See Eugene J. Kamin, Selected Dyadic Aspects of Male Sex Aggression, 5 J. SEX. REs. 12, 27 (1969) (finding that 25% of college men reported involvement in sexually coercive behavior since they entered college); Mary P. Koss & Cheryl J. Oros, Sexual Experiences Survey: A Research Instrument Investigating Sexual Aggression and Victimization, 50 J. CONSULTING & CLINICAL PSYCH. 455, 455-57 (1982) (finding that 23% of men admitted to engaging in coercive sex).[↑]
- See Rapport & Posey, supra note 61, at 219-20.[↑]
- Koss & Oros, subra note 61, at 455-57.[↑]
- “Rape” is a notoriously difficult term to define. The generic term “rape” is used to mean, at a minimum, behavior that is clearly admissible under Rule 413, which is “contact, without consent, between any part of the defendant’s body or an object and the genitals or anus of another person . . . [or] contact, without consent, between the genitals or anus of the defendant and any part of another person’s body,” FED. R. EVID. 413 (d)(2), (3).[↑]
- See James V.P. Check & Neil Malamuth, An Empirical Assessment of Some Feminist Hypotheses About Rape, 8 International Journal of Women’s Studies, 415 (1985).[↑]
- The Psychopathic Deviate scale of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory measures the score response correlation between interviewed subjects and people with known psychoses.[↑]
- See Lucy W. Taylor, The Role of Offender Profiling in Classifying Rapists: Implications for Counselling, COUNSELLING PSYCHOL. Q. 325, 334 (1993). Men convicted of rape are probably the most likely of all rapists to have some sort of psychopathology, because these are the men who have raped enough times in ways that are sufficiently egregious to be convicted.[↑]
- See, e.g., Paul Schewve & William O’Donohue, Rape Prevention: Methodological Problems and New Directions, 13 Clinical Psychiatry Review 667, 668-72 (1993); Taylor, supra note 69, at 334.[↑]
- See Larry Baron & Murray A. Strays, Four Theories of Rape in American Society: A State-level Analysis 185 (1989). Social disorganization theory posits that certain disruptive community influences, such as immigration, cultural heterogeneity, and technological change, damage the integrity of communities, which in turn leads to various forms of antisocial individual behavior.[↑]
- Check & Malamuth, supra note 66, at 415.[↑]
- From 1980 to 1982, the rape rate in Alaska was 83.3 per 100,000, whereas in North Dakota, it was 9.3 per 100,000. See Baron & Straus, supra note 71, at 52. The studies also showed that the rape rate stayed consistent across urban and rural areas within states: states with high rape rates in their urban areas also had high rape rates in their rural areas.[↑]
- See generally Brownmiller, supra note 31, at 11-15 (hypothesizing about the earliest cultural roots of rape); Mackinnon, supra note 42, at 85-92 (arguing, inter alia, that the crime of rape is defined according to what men think violates women, and that women continue not to report rape because the legal system does not perceive rape from their point of view). MacKinnon also states: “If sexuality is central to women’s definition and forced sex is central to sexuality, rape is indigenous, not exceptional, to women’s social condition. In feminist analysis, a rape is not an isolated event or moral transgression or individual interchange gone wrong, but an act of terrorism and torture within a systemic context of group subjection.” Catherine A. Mackinnon, Toward A Feminist Theory of The State 171-83 (1989).[↑]
- Baker, K. K. (1997). Once a Rapist? Motivational Evidence and Relevancy in Rape Law. Harvard Law Review, 110(3), 563.[↑]
- দৈনন্দিন ধর্ষণ- একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা[↑]
- Laura Bates, How School Dress Codes Shame Girls and Perpetuate Rape Culture, TIME MAG, May 22, 2015[↑]
- Chen Shen, Study: From Attribution and Thought-Process Theory to Rape-Shield Laws: The Meanings of Victim’s Appearance in Rape Trials, 5 J.L. & FAM. STUD. 435, 447–48 2003[↑]
- Annie-Rose Strasser & Tara Culp-Ressler, How the Media Took Sides in the Steubenville Rape Case, THINKPROGRESS Mar. 18, 2013 For example, in media coverage of the 2012 Steubenville trial of two teenage boys for the rape of a classmate several media outlets referred to the victim as “drunken.”[↑]
- James C. McKinlley, Jr., Vicious Assault Shakes Texas Town, N.Y.TIMES, March 8, 2011 A New York Times article on the gang rape of an 11-year old girl quoted residents of the area in which the girl lived as saying: “she dressed older than her age, wearing makeup and fashions more appropriate to a woman in her 20s.”[↑]
- Wolfendale, J. (2015). Provocative Dress and Sexual Responsibility. SSRN Electronic Journal[↑][↑][↑]
- Annette Lynch, Expanding the Definition of Provocative Dress: An Examination of Female Flashing Behavior on a College Campus, 25 CLOTHING & TEXTILES RES. J. 185, 186 (2007).[↑][↑]
- Duncan Kennedy, SEXY DRESSING ETC: ESSAYS ON THE POWER AND POLITICS OF CULTURAL IDENTITY 163–164 1993[↑]
- Duncan Kennedy, Sexual Abuse, Sexy Dressing and the Eroticization of Domination, 26 NEW ENG. L. REV. 1309,1344 (1992) A woman’s race, age, and weight can also influence whether her outfit is perceived as sexually provocative. For example, given the highly sexualized images of African-American women in the media (such as in music videos), African-American women who wear body-revealing outfits are more likely tobe viewed as “slutty.”[↑]
- Sharron J. Lennon et al., Forging Linkages between Dress and Law in the U.S., Part I: Rape and Sexual Harassment, 17 CLOTHING & TEXTILES RES. J. 144, 156 (1999) (quoting Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 57, 68–69 1986.[↑][↑]
- Gabrielle Lofthouse, Press Release June 2010: Half Of Women Believe They Perform Better at Work When Dressed Sexily[↑]
- There are some contexts where it would be reasonable for an observer to infer a desire for sexual attention from a woman’s outfit, for example, if she was a prostitute in a known red-light district. Although, it is not clear whether the prostitute is signaling a desire for sex so much as a desire for business.[↑]
- Joshua Dressler, Rethinking Heat of Passion: A Defense in Search of a Rationale, 73 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 421, 422 (1982).[↑]
- Aborigines’Fury Over Topless Ban, BBC NEWS Feb. 27, 2004, 4:02 PM[↑]
- Nowatzki, J., & Morry, M. (2009). Women’s intentions regarding, and acceptance of, self-sexualizing behavior. Psychology of Women Quarterly, 33, 95–107.[↑]
- Kipnis, L., & Reeder, J. (2013). White trash girl: The interview. In A. Newitz & M. Wray (Eds.), White Trash: Race and Class in America (pp. 113–130). New York, NY: Routledge.[↑]
- Lerum, K., & Dworkin, S. L. (2009). “Bad girls rule”: An interdisciplinary feminist commentary on the report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Journal of Sex Research, 46(4), 250–263.[↑][↑]
- Infanger, M., Rudman, L. A., & Sczesny, S. (2014). Sex as a source of power? Backlash against self-sexualizing women. Group Processes & Intergroup Relations, 19, 110–124.[↑][↑]
- Smolak, L., Murnen, S. K., & Myers, T. A. (2014). Sexualizing the self: What college women and men think about and do to be “sexy”. Psychology of Women Quarterly, 38, 379–397.[↑]
- Yost, M. R., & McCarthy, L. (2012). Girls gone wild? Heterosexual women’s same-sex encounters at college parties. Psychology of Women Quarterly, 36, 7–24.[↑][↑]
- Barber, N. (1995). The evolutionary psychology of physical attractiveness: Sexual selection and human morphology. Ethology and Sociobiology, 16, 395–424.[↑]
- Baumgardner, J., & Richards, A. (2004). Feminism and femininity: or how we learned to stop worrying and love the thong. In A. Harris (Ed.), All About The Girl: Culture, Power and Identity (pp. 59–67). New York: Routledge.[↑]
- Liss, M., Erchull, M. J., & Ramsey, L. R. (2011). Empowering or oppressing? Development and exploration of the Enjoyment of Sexualization Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 55–68.[↑]
- American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls. (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Washington, DC.[↑]
- Blake, K. R., Bastian, B., & Denson, T. F. (2016). Perceptions of low agency and high sexual openness mediate the relationship between sexualization and sexual aggression. Aggressive Behavior, 42(5), 483–497.[↑][↑][↑]
- Fredrickson, B. L., & Roberts, T.-A. (1997). Objectification theory. Psychology of Women Quarterly, 21, 173–206.[↑]
- Nussbaum, M. C. (Ed.). (1999). Objectification. New York: Oxford University Press.[↑]
- Gray, H. M., Gray, K., & Wegner, D. M. (2007). Dimensions of mind perception. Science, 315, 619.[↑][↑]
- Gray, K., & Wegner, D. M. (2009). Moral typecasting: Divergent perceptions of moral agents and moral patients. Journal of Personality and Social Psychology, 96 505-520[↑][↑][↑]
- Cikara, M., Farnsworth, R. A., Harris, L. T., & Fiske, S. T. (2010). On the wrong side of the trolley track: Neural correlates of relative social valuation. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5, 404– 413[↑]
- Gray, K., Young, L., & Waytz, A. (2012). Mind perception is the essence of morality. Psychological Inquiry, 23, 101–124[↑]
- Holland, E., & Haslam, N. (2013). Worth the weight: The objectification of overweight versus thin targets. Psychology of Women Quarterly, 37, 462–468.[↑]
- Vaes, J., Loughnan, S., & Puvia, E. (2013). The inhuman body: When sexual objectification becomes dehumanizing. In P. Bain, J. Vaes, & J. P. Leyens (Eds.), Humanness and Dehumanization (pp. 186– 204). NY: Psychology Press.[↑]
- Vaes, J., Paladino, M., & Puvia, E. (2011). Are sexualized women complete human beings? Why men and women dehumanize sexually objectified women. European Journal of Social Psychology, 41, 774–785.[↑][↑]
- Confer, J. C., Perilloux, C., & Buss, D. M. (2010). More than just a pretty face: Men’s priority shifts toward bodily attractiveness in short-term versus long-term mating contexts. Evolution and Human Behavior, 31, 348–353.[↑]
- Gervais, S. J., DiLillo, D., & McChargue, D. (2014). Understanding the link between men’s alcohol use and sexual violence perpetration: The mediating role of sexual objectification. Psychology of Violence, 4, 156–169.[↑]
- Bastian, B., Laham, S. M., Wilson, S., Haslam, N., & Koval, P. (2011). Blaming, praising, and protecting our humanity: The implications of everyday dehumanization for judgments of moral status. British Journal of Social Psychology, 50, 469–483.[↑]
- Lennon, T. L., Lennon, S. J., & Johnson, K. K. P. (n.d.). Is Clothing Probative of Attitude or Intent—Implications for Rape and Sexual Harassment Cases. 11.[↑]
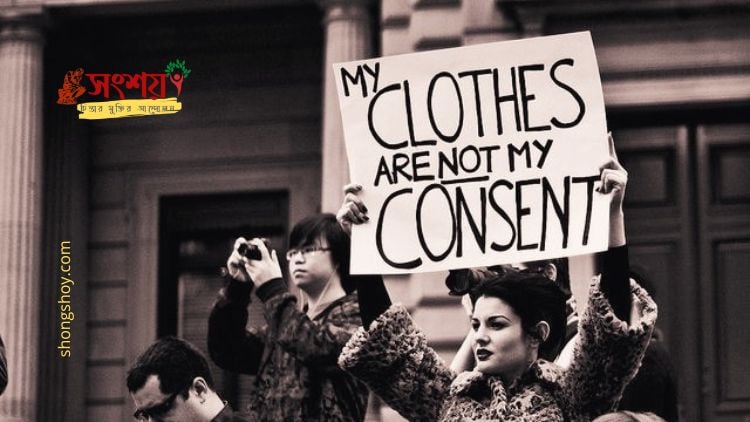
Leave a Comment