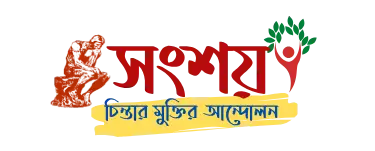নিচের লেখাটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, এখনো এই লেখাটির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। পাঠকদের অনুরোধ, কিছুদিন পরে আবারো লেখাটি পড়বেন এবং তথ্যসূত্রগুলো যাচাই করবেন।
মুহাম্মদের জীবন, নবুয়ত, বিবাহ ও যুদ্ধসমূহ – ক্রমিক টাইমলাইন
সীরাত অনুযায়ী, এক ভ্রমণে আবদুল মুত্তালিব (মুহাম্মদের দাদা) বানু যুহরা গোত্রের নারী হালা বিনতে উহাইর-কে বিয়ে করেন এবং একই দিনে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (মুহাম্মদের পিতা) হালার কাজিন আমিনা বিনতে ওয়াহব-কে বিয়ে করেন; দুজন নারীই একই বংশের (বানু যুহরা) সদস্য। [1]
আমিনার সঙ্গে বিবাহের অল্প কিছুদিন পরই পিতা আবদুল মুত্তালিবের নির্দেশে আবদুল্লাহ বাণিজ্য কাফেলায় যোগ দিয়ে সিরিয়া অঞ্চলের দিকে রওনা হন [2]। ফেরার পথে ইয়াসরিবে (মদিনা) অসুস্থ হয়ে তিনি মারা যান; ঐতিহাসিকভাবে এটি এক ধরনের সাধারণ আরব বাণিজ্য–ঝুঁকির করুণ ফল। [3]
সীরাতকার ইবনে সা‘দ ও আল-ওয়াকিদী-এর মতে হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব মুহাম্মদের প্রায় দুই থেকে চার বছর আগে জন্মেছিলেন [4] । এই হিসাব থেকে তার জন্ম আনুমানিক ৫৬৬–৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে ধরা যায়; তিনি একই সঙ্গে মুহাম্মদের চাচা ও কিছু বর্ণনায় দুধভাই হিসেবেও উল্লেখিত। পরবর্তী সামরিক পর্বে হামজা মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধা হয়ে ওঠেন, যদিও তাঁর ব্যক্তিগত প্রারম্ভিক বিশ্বাস–ধারার সম্পর্কে পরিষ্কার তথ্য খুব সীমিত। তবে একটি স্পষ্ট বিবরণ থেকে জানা যায়, একবার হামযা মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় নবী মুহাম্মদকে তার পিতার গোলাম বলে গালাগালি করেছিল [5]। মুহাম্মদ এই গালি খেয়ে চুপচাপ সেখান থেকে চলে যায়।
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মক্কায় তথাকথিত “হাতির বছর”-এ জন্মগ্রহণ করেন; ঘটনাটিকে সাধারণত প্রায় ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি ধরা হয়। তাঁর জন্মের আগেই পিতা আবদুল্লাহ মারা যান, ফলে তিনি জন্ম থেকেই পিতৃহীন শিশু। দাদা আবদুল মুত্তালিব নাকি কাবার কাছে গিয়ে নাম “মুহাম্মদ” রাখেন, পরে ধর্মীয় আখ্যান এটাকে “প্রশংসিত” নামের ইশতেহার হিসেবে ব্যবহার করে [6]।
শৈশবের প্রথম কিছু বছর মাতা আমিনা ও আশপাশের আত্মীয়দের তত্ত্বাবধানে কাটে; সীরাতে গ্রামীণ দুধমা–প্রথা ও গ্রামে পাঠানোর নানা কাহিনি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর ঐতিহাসিকতা নিশ্চিত নয়। প্রায় ছয় বছর বয়সে ইয়াসরিব সফর থেকে ফেরার পথে আমিনা মারা যান বলে বর্ণিত, এবং ছোট্ট শিশু মুহাম্মদের ওপর আবার অভিভাবক–পরিবর্তনের মানসিক চাপ পড়ে। পরে ইসলামী আখ্যান এই ধারাবাহিক ক্ষতিগুলোকে “আল্লাহর পরীক্ষিত প্রিয় বান্দা”–ধারণার ফ্রেমে রোমান্টিসাইজ করে।
আমিনার মৃত্যুর পর দাদা আবদুল মুত্তালিব এই এতিম নাতির দায়িত্ব নেন, তাকে কুরাইশ নেতৃবর্গের আসরে নিয়ে যান—যা ভবিষ্যতে গোত্র–রাজনীতির ভেতরের ক্ষমতার খেলাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ দেয়। প্রায় আট বছর বয়সে আবদুল মুত্তালিব মারা গেলে মুহাম্মদ আবার অভিভাবক হারান এবং এবার চাচা আবু তালিবের ঘরে আশ্রয় নেন, যিনি নিজেও আর্থিকভাবে দুর্বল ছিলেন। জীবনের প্রথম দশক জুড়ে বারবার অভিভাবক হারানোর এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে “আশ্রয়দাতা আল্লাহ” ও “উম্মাহ–ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব” কথাবার্তাকে মানসিকভাবে বোধগম্য করে তোলে, যদিও আখ্যান এগুলোকে চরম অলৌকিক পরিকল্পনা হিসেবে তুলে ধরে।
চাচা আবু তালিব অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই মুহাম্মদ পরিবারের সহায়তার জন্য কাজ করতে শুরু করেন। হাদিসে উল্লেখ আছে, তিনি অল্প পারিশ্রমিকে মক্কার লোকদের ভেড়া চরাতেন; অর্থাৎ শৈশব ও কৈশোরের একটি বড় অংশ কেটেছে গরিব রাখাল হিসেবে মরুভূমিতে পশুচারণ করেই। পরবর্তীতে “নবীরা ভেড়া চরিয়েছেন” ধরনের আখ্যান এই দরিদ্র কর্মজীবনকে ধর্মীয় রোমান্টিকতা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, বাস্তবতা ছিল অর্থনৈতিক চাপ ও নিম্ন সামাজিক অবস্থান।
এই সময়ে মুহাম্মদের সাথে দেখা হয় হানীফ চিন্তাধারার অনুসারী যায়দ ইবনে আমর ইবন নুফায়লের, যিনি মূর্তি–পূজা বর্জন করে ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণে আহ্বান করতেন। ইসলামী সূত্র অনুযায়ী, মুহাম্মদ তাঁর কাছে থেকেই প্রথমবারের মতো বহুদেবতাবাদ–বিরোধী বিশ্বাস ও “দ্বীনে ইব্রাহিম” ধারণার সরাসরি পরিচয় লাভ করেন। যায়দের ছেলে সাইদ পরে বিখ্যাত “জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত” সাহাবিদের একজন হন, এবং বলা হয় মুহাম্মদ তাঁকে বলেছিলেন—যায়দ কেয়ামতের দিন একাই এক উম্মত হিসেবে উঠবেন। যায়দের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন ওয়ারাকা ইবন নওফল—খাদিজার চাচাতো ভাই—যিনি যায়দের মৃত্যুর পর শোকগাথাও রচনা করেন, যা দেখায় তাঁদের হানীফ চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক। একবার মুহাম্মদ তাঁকে খাবার দিলে যায়দ তা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তা ছিল কাবার দেবদেবীদের নামে জবাই করা পশু—এই কড়া আপত্তি দেখায় যে তখনই তিনি প্রচলিত ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চরম অসম্মতি পোষণ করতেন।
আবু তালিবের ঘরে বড় হওয়ার সময় তিনি চাচাতো বোন উম্মে হানী বিনতে আবি তালিব-কে বিয়ের প্রস্তাব দেন বলে সীরাতে উল্লেখ আছে। আবু তালিব নাকি প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন এই যুক্তিতে যে কুরাইশের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি তার কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে—“মর্যাদাবানদের সমকক্ষ মর্যাদাবানই হওয়া চাই” [7] । এই ঘটনা মুহাম্মদের তরুণ বয়সে সামাজিক–অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থানকে ইঙ্গিত করে, যা পরে নবুয়তের পর হঠাৎ ক্ষমতা–বৃদ্ধির সঙ্গে তীব্র বৈপরীত্য তৈরি করে।
প্রায় ২৫ বছর বয়সে মুহাম্মদ ধনী বিধবা ব্যবসায়ী খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ-এর বাণিজ্য কাফেলার ব্যবস্থাপনা করেন এবং পরবর্তীতে তাকে বিয়ে করেন। অধিকাংশ সীরাতে খাদিজার বয়স ৪০ বছর বলা হলেও বিকল্প মত অনুযায়ী ২৮–৩৫ বছরের মধ্যেও উল্লেখ আছে; যাই হোক, অর্থনৈতিকভাবে তিনি স্পষ্টভাবেই অধিক শক্তিশালী ছিলেন। এই বিয়ের পর মুহাম্মদ দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর একগামী দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করেন এবং মূলত খাদিজার মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করেন; নবুয়ত–পর্বে এই সম্পদ ও নেটওয়ার্কই রাজনৈতিক উত্থানের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।
মক্কায় বন্যা ও ক্ষতির পর কাবা পুনর্নির্মাণের সময় অভ্যন্তরের ৩৬০টি মূর্তি সাময়িকভাবে সরিয়ে পরবর্তীতে আগের মতই ফিরিয়ে রাখা হয়। এই কাজে মুহাম্মদ সরাসরি অংশ নেন এবং “হাজরে আসওয়াদ বসানো” নিয়ে গোত্র–বিরোধ মেটানোর ঘটনাও উল্লেখ আছে। এই সময়ে হাজরে আসওয়াদ পাথরটির সাথে মুহাম্মদের একটি অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, কারণ এই পাথরটি জায়গামত বসানোর বুদ্ধিটি মুহাম্মদই দিয়েছিল বলে প্রচলিত আছে। পরবর্তীতে একই কাবাকে “তওহিদের কেন্দ্র” ঘোষণা করে সব মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়; কিন্তু কালো পাথর বা হাজরে আসওয়াদটি বিশেষ মর্যাদা পায়, যেই পাথরটি নাকি কেয়ামতের দিন আল্লাহর পাশে বসে এই পাথরকে চুম্বন করা মানুষদের পক্ষে আল্লাহর কাছে উকালতি করবে বলে মুহাম্মদ ঘোষণা করেন। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটে। কাবা মেরামত করার সময় ( মুহাম্মদ সে সময়ে ছিলেন ৩৫ বছর বয়সী পুরুষ) একবার সবার সামনে নবীর লুঙ্গিটি তার চাচা আব্বাস খুলে নিয়েছিল। নবী মুহাম্মদ লজ্জায় অপমানে সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে কাবার সামনেই কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, ন্যাংটু অবস্থায় [8]
আধুনিক গবেষণা ও আরবীয় মৌখিক ঐতিহ্য অনুযায়ী, মুসায়লামা ইবন হাবীব ইয়ামামার হাজর এলাকায় মুহাম্মদের হিজরতের বহু বছর আগেই ধর্মীয়–সামাজিক নেতা বা স্থানীয় “নবীস্বরূপ পুরোহিত” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তাঁর অনুসারীরা তাকে “রহমানুল ইয়ামামা” নামে ডাকত। ইসলামী সীরাত পরে তাকে মুহাম্মদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তুলে ধরে “কাজ্জাব” বলে আখ্যা দিলেও, ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখায়—আরবের মধ্যাঞ্চলে তিনি তখনই জনপ্রিয় ও স্থিতিশীল আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বাণী ছিল এক ধরনের আঞ্চলিক একেশ্বরবাদ–মিশ্র ধর্মীয় রীতি, যেখানে ভবিষ্যদ্বক্তা ও গোত্রনেতার ভূমিকা মিলেমিশে ছিল, যা আরব সমাজে নতুন কিছু ছিল না। ফলে মুহাম্মদের নবুয়তের উদ্ভবের সময় আরব উপদ্বীপে ইতোমধ্যেই বিকল্প আধ্যাত্মিক নেতাদের উপস্থিতি ছিল—যারা সামাজিক কাঠামো, রাজনীতি ও ধর্মীয় ভাষ্য গঠনে সমান্তরাল ভূমিকা পালন করছিল। [9]
প্রায় ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে (নবী ঘোষণার আগের সময়), একটা বড় বন্যা কাবা ক্ষতিগ্রস্ত করে। কুরাইশরা তখন কাবা পুনর্নির্মাণ করে, আর সেই সময়েই কাবার দরজা উঁচু করে বসানো হয় যাতে ভবিষ্যতের বন্যায় পানি ভেতরে কম ঢোকে। এটা ইসলামী মিথোলজি নয়, মক্কার ভৌগোলিক প্রকৃতি বিবেচনায় পুরোপুরি যৌক্তিক এবং ঐতিহাসিকভাবে সঠিক। উপত্যকা প্লাবিত হওয়া ছিল নিয়মিত ব্যাপার।
পুরো আরব অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা, বন্যা এবং অন্যান্য কারণে শাম অঞ্চলে বাণিজ্য কমে যাওয়ার সাথে সাথে মুহাম্মদ ধীরে ধীরে ব্যবসা থেকে সরে এসে হেরা গুহায় একাকী ধ্যান–চিন্তায় অভ্যস্ত হন। হেরা পর্বতের গুহায় এরকম উপাসনা করার পদ্ধতি তার পৌত্তলিক দাদা আবদুল মুত্তালিব শুরু করেন বলে জানা যায় [10]। পরবর্তী মুসলিম আখ্যান এসব উপাসনাকে সরাসরি “ওহীর প্রস্তুতি” হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও, একে সামাজিক–অর্থনৈতিক হতাশা থেকে উদ্ভূত আধ্যাত্মিক মোড়–খোঁজাও বলা যায়।
প্রচলিত বর্ণনা অনুযায়ী হেরা গুহায় একা ধ্যান করার সময় মুহাম্মদ হঠাৎ এক অদৃশ্য শক্তির চাপ অনুভব করে ভয় পেয়ে যান এবং দ্রুত নিচে নেমে এসে খাদিজাকে বলেন—“জাম্মিলুনি, জাম্মিলুনি” অর্থাৎ আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি কাঁপছিলেন এবং বলছিলেন যে তিনি কিছু অদ্ভুত দেখেছেন বা অনুভব করেছেন; খাদিজা তাকে শান্ত করেন এবং ঘটনা বিস্তারিত জেনে বোঝার চেষ্টা করেন তিনি আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আছেন। পরিস্থিতি বুঝে খাদিজা তাকে তার বিদ্বান চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফলের কাছে নিয়ে যান, যিনি খ্রিস্টান নেস্টোরিয়ান ঐতিহ্যে দীক্ষিত ছিলেন এবং পূর্ববর্তী শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। ওয়ারাকা মুহাম্মদের অভিজ্ঞতাকে “ফেরেশতা” বা “ওহীর শুরু” হিসেবে ব্যাখ্যা করেন—যা ইসলামী আখ্যানের নবুয়তের সূচনাকে নির্ধারণ করে। যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোন থেকে, এই ধারাবর্ণনা একজন ব্যক্তির গভীর ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, তীব্র ভয়, মনস্তাত্ত্বিক সংকট এবং পরে আশেপাশের ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ব্যাখ্যা দ্বারা এটি “নবুয়ত” আকার নেওয়ার প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে [11]।
প্রথম দিকে খাদিজা, আলী, যায়েদ, আবু বকরসহ অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধু ইসলাম গ্রহণ করেন। দাওয়াত মূলত নৈতিক শিক্ষা, কিয়ামতের ভয় ও এক আল্লাহর ইবাদতে কেন্দ্রীভূত ছিল; সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা তখনো মূল লক্ষ্য হিসেবে দৃশ্যমান নয়। তবে এই প্রাথমিক ছোট দলই পরবর্তী সময়ে নতুন ধর্মীয়–রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কোর গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।
প্রথম ওহীর অভিজ্ঞতার পর আতঙ্কিত মুহাম্মদকে খাদিজা তাঁর খ্রিস্টান চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফল-এর কাছে নিয়ে যান; তিনি ইহুদি–খ্রিস্টান গ্রন্থ–জ্ঞান থাকা একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং অভিজ্ঞতাটিকে পূর্বের নবীদের ন্যায় “নামুস” বা জিবরাইল বলে ব্যাখ্যা করেন। কিছু সময়ের মধ্যেই ওয়ারাকার মৃত্যু ঘটে এবং পরবর্তী দীর্ঘ বিরতিতে (ফাত্রাতুল ওহী) ওহী নেমে আসা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে মুহাম্মদ তীব্র মানসিক সংকট, সন্দেহ ও ভয়ে ভোগেন। সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে—তিনি বারবার পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইতেন; প্রতিবারই কল্পিত জিবরাইলের আবির্ভাবের মাধ্যমে তা থেকে বিরত থাকেন। এই পর্ব ইসলামের আদি নবুয়ত–গল্পকে এক গভীর সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিস ও বাইবেলীয় প্রভাবে মুহাম্মদের নির্ভরতা তুলে ধরে, যা আধুনিক পাঠে “মানসিক ভাঙন থেকে নবুয়ত” প্রশ্নও উত্থাপন করে।
আবু যর আল-গিফারী ছিলেন বনি গিফার গোত্রের, যারা বাণিজ্য–রুটে ডাকাতি ও হাইওয়ে–রবিংয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল; তবু তিনি নিজে মূর্তি–পূজা ও গোত্রীয় দেবদেবীতে বিশ্বাস করতেন না এবং এক ধরনের প্রাক-ইসলামিক একেশ্বরবাদে ঝুঁকেছিলেন। মক্কায় এক নতুন “নবুয়ত দাবি” ও ভিন্ন ধর্মবাণীর কথা শুনে তিনি একাই গোপনে মক্কায় আসেন, কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের পর কাবার কাছে গিয়ে মুহাম্মদের সঙ্গে দেখা করেন এবং কিছু আয়াত শোনার পর ইসলাম গ্রহণ করেন বলে বর্ণিত আছে। এরপর তিনি প্রকাশ্যে কাবা প্রাঙ্গণে নতুন দাওয়াতের স্লোগান দিলে কুরাইশরা তাকে নির্মমভাবে প্রহার করে; আব্বাস নাকি কুরাইশদের মনে করিয়ে দেয় যে গিফার গোত্র বাণিজ্য–পথের কাছের উপজাতি, তাদের লোককে মেরে ফেললে বাণিজ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে—এরপরই প্রহার কিছুটা থামে। মুহাম্মদ তাকে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতে বলেন এবং গিফার ও আশপাশের উপজাতিদের মধ্যে দাওয়াত প্রচার করতে বলেন; কিছুদিন পর গোত্রের বড় অংশ ইসলাম গ্রহণ করে, অর্থাৎ আগের বাণিজ্য কাফেলায় ডাকাতি করা গোত্র নতুন ধর্মীয় রাষ্ট্রের সৈন্য/সমর্থকে পরিণত হয়। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণে, আবু যরের কাহিনি দেখায়—একদিকে আরবের ভেতরে মূর্তি–বিরোধী একেশ্বরবাদ আগেই ছিল, অন্যদিকে ইসলাম সেই একেশ্বরবাদী প্রবণতাকে গোত্রীয় লুট–অর্থনীতির সঙ্গে মিলিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক–ধর্মীয় প্রকল্পে টেনে নেয়।
এই পর্যায়ে প্রকাশ্য দাওয়াতের মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের দেব–দেবী ও পূর্বপুরুষ–ধর্মকে কোরআনের ভাষায় “অন্ধ অনুসরণ” ও “জাহান্নামের পথ” বলে আক্রমণ করা হয়। একইসাথে মূর্তিগুলো নিয়ে মুহাম্মদ নানা ধরণের কটূক্তি ও নিন্দা করতে শুরু করে [12]। ফলে দাস ও নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের ওপর নির্যাতন বাড়ে, আর নবীর গোত্র বানু হাসিমকে সামাজিক–অর্থনৈতিক বয়কটে ফেলা হয়। প্রথম হিজরত আবিসিনিয়ায় এই চাপ থেকে পালানোর প্রচেষ্টা হলেও, আদি ইসলামী আন্দোলনের কৌশলগত অংশ হিসেবে এটাকে দেখা যায়।
কোরআনের বিভিন্ন মক্কী আয়াতে উল্লেখ আছে যে মুহাম্মদকে পাঠানো হয়েছে মূলত “অম্মুল কুরা (মক্কা) ও তার আশপাশের এলাকাগুলোর জন্য”, যা নবুয়তের প্রথম পর্যায়ের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে। এটি সেই সময়ের বাস্তবতার প্রতিফলন, যখন ইসলামের দাওয়াত ছিল একটি ছোট স্থানীয় আন্দোলন—গোত্রীয় সমাজের সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ। পরবর্তী মদিনা পর্বের সামরিক সম্প্রসারণ, গোত্র–জয় ও দূরবর্তী অঞ্চলে কর–ব্যবস্থা আরোপের সঙ্গে এই প্রাথমিক সীমাবদ্ধ ঘোষণা তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। ক্লাসিকাল তাফসীরকাররা পরে সকল জাতির জন্য “রহমাতুল্লিল আলামিন” ধারণার মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতাকে ব্যাখ্যা বা পুনঃসংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে, ইসলামের বার্তা ক্রমান্বয়ে স্থানীয় আঞ্চলিক আন্দোলন থেকে শক্তিশালী রাজনৈতিক–সামরিক রাষ্ট্রবাদের দিকে রূপান্তরিত হয়েছে।
উমর প্রথমদিকে ইসলামের অন্যতম কট্টর বিরোধী ছিলেন; মক্কার রাজনৈতিক–সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষ নিয়ে মুহাম্মদকে হত্যার পরিকল্পনাও করেছিলেন বলেই প্রচলিত বর্ণনা আছে। তবে পরে বর্ণিত হয়, তার বোন ফাতিমা এবং দুলাভাইয়ের কাছে কোরআনের কিছু আয়াত শুনে তিনি মন পরিবর্তন করেন এবং সরাসরি দারুল আরকামে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, উমরের ইসলাম গ্রহণ কুরাইশের ভেতর একটি প্রতীকী শক্তির ভারসাম্য তৈরি করে এবং বনু আদীর মতো গুরুত্বপূর্ণ গোত্রকে আংশিকভাবে নিরপেক্ষ বা সহনশীল করে। উমর ইসলাম গ্রহণ করার ফোলে মুহাম্মদ ও অন্যান্য মুসলিমরা প্রকাশ্যেই কাবাতে প্রার্থণা করার সাহস পায়। ইসলামি আখ্যান এটিকে “ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি” হিসেবে তুলে ধরলেও, বাস্তবতা হলো—এটি মক্কার রাজনৈতিক মেরুকরণকে আরও তীব্র করে এবং সংঘাতের দিকটি দ্রুত বাড়িয়ে দেয়।
প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু হওয়ার পর মক্কার কুরাইশ নেতারা একসময় আবু তালিবের কাছে এসে অভিযোগ করে—তোমার ভাতিজা আমাদের দেবদেবীকে গালি দিচ্ছে, আমাদের ধর্মকে বিভ্রান্ত বলছে; তাকে থামাও, নইলে আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা নেব। প্রথমে আবু তালিব ভাতিজাকে ডেকে নরমভাবে সতর্ক করতে চাইলে মুহাম্মদ তার দাওয়াত থামাতে অস্বীকৃতি জানান এবং প্রচলিত বর্ণনায় আবেগী ভাষায় “সূর্য এক হাতে, চাঁদ আরেক হাতে দিলে”–ধরনের কথা বলেন। কুরাইশ এই বার্তা বুঝে যায় যে, নবীর দাবি কেবল আধ্যাত্মিক নয়, গোত্রীয় নেতৃত্ব ও সামাজিক প্রভাব কাঠামোর সাথেও সংঘাতে গেছে। ফলে এখান থেকেই ধর্মীয় মতবিরোধ ধীরে ধীরে পুরোপুরি রাজনৈতিক সংঘাতে রূপ নিতে শুরু করে, যা পরে সামাজিক বয়কট ও সরাসরি নিপীড়নে গিয়ে পৌঁছায়। শুরুর দিকে মুহাম্মদ যখন তার ধর্ম প্রচার করছিল, সেই সময়ে পৌত্তলিক কুরাইশগণ মুহাম্মদের প্রতি বিরূপ হয়নি, কিন্তু এই ঘটনার পরেই পৌত্তলিকগণ মুসলিমদের ওপর নির্যাতন শুরু করে।
একই বছরে স্ত্রী খাদিজা ও চাচা–অভিভাবক আবু তালিবের মৃত্যুতে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দু’দিক থেকেই মুহাম্মদ দুর্বল হয়ে পড়েন। আর্থিক সাপোর্ট ও গোত্র–সুরক্ষা কমে গেলে তিনি তায়েফে সমর্থন খুঁজতে যান এবং সেখানে চরম অপমানের শিকার হন। এই ব্যর্থতা পরোক্ষভাবে ইয়াসরিবের (মদিনা) দিকে রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের পথ খুলে দেয়, যা পরে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রে পরিণত হয়।
এই সময় তিনি প্রায় ৪০ বছরের বিধবা সাওদা বিনতে যাম‘আহ-কে বিয়ে করেন; তাঁর বয়স প্রায় ৪৯ বছর, অর্থাৎ ব্যবধান প্রায় ৯ বছর। একই পর্বে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকরের কন্যা আয়িশা বিনতে আবু বকর-এর সঙ্গে বিয়ে হয়; প্রথাগত হিসাব অনুসারে তখন আয়িশার বয়স ৬ বছর এবং মুহাম্মদের বয়স ৪৯ বছর—প্রায় ৪২ বছরের পার্থক্য। সহবাস তখনও হয়নি; সেটি পরে মদিনায় গিয়ে ঘটবে বলে সীরাতে বর্ণিত, যা আজকের মানদণ্ডে শিশুবিবাহ ও ক্ষমতার বৈষম্যমূলক সম্পর্ক হিসেবে স্পষ্টভাবে সমস্যা–সঙ্কুল।
সূরা আল-কাফিরুনের শেষাংশে “তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার” ঘোষণা করা হয়, যা মক্কা পর্যায়ের একটি অপেক্ষাকৃত নরম ও সহাবস্থান–ধর্মী বার্তা। এটি এমন এক সময়ের প্রতিফলন, যখন মুহাম্মদ রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন অবস্থায় ছিল এবং কুরাইশদের সামাজিক চাপ মোকাবিলা করছিলেন। পরবর্তীতে মদিনার জিহাদ–কেন্দ্রিক আয়াতগুলি আসার পর বেশিরভাগ ক্লাসিকাল তাফসীর এই মক্কী বার্তাকে “সীমাবদ্ধ” বা কার্যত রহিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। তা সত্ত্বেও এটি ইসলামী আখ্যানের প্রাথমিক নমনীয়তা ও পরবর্তী কঠোরতার মধ্যে ধারাবাহিক টোন–পরিবর্তন দেখায়।
“ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই” আয়াতটি মদিনায় নাজিল হলেও এর টোন ও দর্শন স্পষ্টতই মক্কা পর্যায়ের সহনশীল আখ্যানের ধারাবাহিকতা বহন করে। প্রাথমিক মুসলিমদের সংখ্যা কম এবং রাজনৈতিক শক্তি অনুপস্থিত থাকায় এই সময়ের বক্তব্য ছিল ব্যক্তিগত বিশ্বাস–স্বাধীনতা কেন্দ্রিক। পরবর্তীতে সূরা তাওবা–পর্বে “যুদ্ধ, জিজিয়া ও অনুগত্য”–নির্ভর বিধান আসার পর ক্লাসিকাল স্কলাররা এই আয়াতকেও আংশিক–রহিত বা শর্তাধীন বলেছেন। এটি ধর্মীয় বার্তায় প্রাথমিক নমনীয়তা থেকে কেন্দ্রীভূত সামরিক–রাষ্ট্রিক কাঠামোর দিকে রূপান্তরের একটি ভালো উদাহরণ।
এই আয়াতে স্পষ্ট স্বাধীন ইচ্ছার ঘোষণা এসেছে—“যে ইচ্ছে ঈমান আনুক, যে ইচ্ছে অস্বীকার করুক”; এটি মক্কা পর্যায়ের অন্যতম উদার ধারণা। মুহাম্মদ তখনো রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, ফলে জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ বা সামরিক জিহাদের ধারণা তখনো ব্যবহার হয়নি। পরবর্তী মদিনা পর্বের সামরিক আয়াতগুলোর সঙ্গে এই বক্তব্যের তীব্র বৈপরীত্য থাকায় ক্লাসিকাল তাফসীর এটিকে “অবস্থা–নির্ভর” বলে ব্যাখ্যা করে। এটি কোরআনের মক্কা–মদিনা টোন–পার্থক্য এবং প্রাথমিক বার্তা বনাম পরবর্তী রাষ্ট্রিক নীতির মাঝে স্পষ্ট বিভাজন প্রকাশ করে।
কোরআনে মক্কা পর্বে বারবার এসেছে—“তুমি তাদের অভিভাবক নও”, “তুমি জবরদস্তিকারী নও”, “তোমার কাজ শুধু পৌঁছে দেওয়া”—যা নবুয়তের প্রথম পর্যায়ের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন। এই সময়ে কোনো জিহাদ, রাষ্ট্র, সেনাবাহিনী বা আইনি কাঠামো না থাকায় ধর্ম প্রচার ছিল সম্পূর্ণ অহিংস ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পরবর্তী মদিনা পর্বে এসব আয়াতের বিপরীত চরিত্রের যুদ্ধ–আয়াত নাজিল হওয়ায় স্কলাররা এগুলোকে সময়–নির্ভর আয়াত হিসেবে ব্যাখ্যা করে। ধর্মীয় শিক্ষায় প্রাথমিক “স্বতঃস্ফূর্ত দাওয়াত” থেকে পরবর্তী “রাষ্ট্র–সমর্থিত প্রয়োগ”–এর দিকে পরিবর্তন এখানেও স্পষ্ট।
প্রচলিত মুসলিম বর্ণনায় এক রাতে মক্কা–জেরুজালেম–আসমানে অলৌকিক ভ্রমণ (ইসরা ও মিরাজ) এবং সেখানে নামাজের সংখ্যা কমিয়ে আনা ইত্যাদি কাহিনি পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকভাবে তারিখ নির্দিষ্ট নয় এবং নিরপেক্ষ গবেষণায় এসব আখ্যানকে পরবর্তী ধর্মীয় কল্পনার সংযোজন হিসেবে দেখার প্রবণতাও রয়েছে। ঘটনাটি মুসলিম আত্মপরিচয়ে কাবা ও জেরুজালেম—দুই কেন্দ্রকেই পবিত্র স্থান হিসেবে স্থাপন করে, যদিও পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রয়োজন মেনে কিবলা স্থায়ীভাবে মক্কার দিকে নির্দিষ্ট হয়।
মক্কার তীব্র বিরোধ ও সামাজিক বয়কটের প্রেক্ষাপটে ক্লাসিকাল সীরাতে এক বিতর্কিত ঘটনার উল্লেখ আছে, যা পরবর্তীতে “শয়তানের আয়াত” বা গারানিক নামে পরিচিত। ইবন ইসহাক, ইবন সা‘দ, তাবারী প্রমুখের বর্ণনায় দেখা যায়—সূরা আন-নাজম তিলাওয়াতের সময় শয়তান মুহাম্মদের জবানায় তিন দেবী আল-লাত, আল-উজ্জা, মানাত সম্পর্কে এমন কথা ঢুকিয়ে দেয়, যেন তাদের সুপারিশ আশা করা যায়; উপস্থিত মুশরিক কুরাইশরা এতে আনন্দিত হয়ে মুসলিমদের সঙ্গে সেজদা করে। পরে মুহাম্মদ বলেন, এই অতিরিক্ত বাক্যগুলো আল্লাহর নয়, শয়তানের হস্তক্ষেপ; ফলে সেগুলো বাতিল করা হয় এবং সূরায় কেবল মূর্তিদেবীদের নিন্দা রেখে দেওয়া হয়। কোরআনের ২২:৫২ আয়াতকে এই ঘটনার সাথে জুড়ে বলা হয়, কোনো নবী যখন তিলাওয়াত করে, শয়তান তার পাঠে কিছু নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে—পরে আল্লাহ তা বাতিল করেন। পরবর্তী যুগের অনেক মুহাদ্দিস সনদকে দুর্বল বললেও, প্রারম্ভিক ঐতিহাসিক সূত্রে এটি নবুয়তের শুরুতে এক বড় ধর্মতাত্ত্বিক ও মানসিক টালমাটাল পর্বরূপে উপস্থিত, যা “ভুল–ওহী” ও নবীর নবুয়তের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
ইয়াসরিব (মদিনা) থেকে আগত প্রতিনিধি দলগুলো রাতে গোপনে আকাবা উপত্যকায় বায়আত দেয় এবং মুহাম্মদকে শহরের রাজনৈতিক মধ্যস্থ ও বিচারক হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। গৃহযুদ্ধ–ক্লান্ত ইয়াসরিব এক বহিরাগত নেতাকে গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অভ্যন্তরীণ গোত্রীয় দ্বন্দ্ব সামলাতে চেয়েছিল। সেই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি গোত্র বসবাস করতো যারা নিজেদের মধ্যে নানা রকম যুদ্ধ ও রক্তারক্তিতে ব্যস্ত থাকতো। মুহাম্মদ যেহেতু নিজেকে ইবাহীমের ধর্মের নবী দাবী করছে, তারা মুহাম্মদকে তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করে যেহেতু ইয়াসরিব অঞ্চলে প্রচুর ইহুদি ছিল। এই বায়আতই পরবর্তী হিজরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে।
মক্কার ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ ও হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ধীরে ধীরে মদিনায় চলে যান। সেখানে তিনি শুধু ধর্মীয় নেতা নন, বরং একটি নগর–রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রধানে পরিণত হন। এখান থেকেই কোরআনি বক্তব্যে “ধর্মতত্ত্ব”–এর সঙ্গে “রাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধনীতি” জুড়ে গিয়ে ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক প্রোজেক্টে রূপ নিতে শুরু করে।
মদিনায় মুহাম্মদ, আনসার, মুহাজির, ইহুদি গোত্র ও অন্যান্যদের নিয়ে এক ধরনের সামাজিক–রাজনৈতিক চুক্তি গঠিত হয়, যা “মদিনার সনদ” নামে পরিচিত। এতে মুহাম্মদকে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর সর্বোচ্চ সালিশকারী ও সামরিক নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়; গোত্রীয় রক্ত–বদলার অংশও কেন্দ্রীভূত হয়। শুরুতে বহুধর্মীয় সহাবস্থান থাকলেও, পরবর্তী সংঘাতগুলো দেখায়—এই সনদ বাস্তবে একধরনের অস্থায়ী ট্রানজিশন, যা শেষ পর্যন্ত মুসলিম একচেটিয়া কর্তৃত্বের দিকে গিয়েই থামে।
সালমান ফারসি তার নিজ ফার্সি পরিবার ছেড়ে বহু ধর্মীয় গোষ্ঠী অতিক্রম করে অবশেষে আরবে এসে দাস হিসেবে বিক্রি হন; এরপর তিনি মদিনায় একজন ইহুদি মালিকের অধীনে দাসত্বে ছিলেন। তিনি মুহাম্মদের সাথে পরিচিত হওয়ার পর কিছুদিন পরিশ্রম করে নিজ মুক্তিপণ পরিশোধ করে স্বাধীন হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি পূর্বে কিছু সামরিক বাহিনীতে ছিলেন বলে জানা যায়। খন্দক–যুদ্ধের সময় শহর রক্ষার জন্য “পরিখা খনন”–এর ধারণা তিনিই প্রস্তাব করেছিলেন, যা ডিফেন্স কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর গল্প ইসলামি ঐতিহ্যে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান হিসেবে বর্ণিত হলেও, ঐতিহাসিকভাবে এটি অঞ্চলের বহুধর্মীয় যোগাযোগ, দাসপ্রথা এবং সাংস্কৃতিক মিশ্রণকে দেখায়।
মদিনায় হিজরতের পরপরই কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলার ওপর নজরদারি ও আক্রমণের জন্য একাধিক ছোট সামরিক দল পাঠানো হয়, যেগুলোকে সীরাতে “সারিয়া” বলা হয়। মুসলিম ঐতিহ্যে এগুলোকে প্রায়শই “প্রতিরক্ষামূলক” বলা হলেও, নিরপেক্ষ ইতিহাসে এগুলোকে কুরাইশের অর্থনীতি ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগ্রাসী অভিযাত্রা বা লুটপাট হিসেবে দেখা হয়। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাগুলো সাধারণত যোদ্ধা বা ভারী অস্ত্র বহন করতো না, তাই তাদের মেরে মালামাল লুট করা অপেক্ষকৃত সহজ ছিল। অর্থনৈতিক লুট ও রাজনৈতিক চাপ মিলিয়ে এই পর্বই পরবর্তী বড় বড় যুদ্ধের ভূমিকা তৈরি করে।
মদিনায় হিজরতের পর কুরাইশ কাফেলার ওপর প্রথম সশস্ত্র চাপ সৃষ্টির চেষ্টা হিসেবে হামজা প্রায় ত্রিশ জন সহচর নিয়ে লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে কুরাইশদের এক কাফেলার পথ রোধ করেন। দুই পক্ষ মুখোমুখি হলেও প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হয়নি; তবে এটি শক্তি–প্রদর্শন ও ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক যুদ্ধের স্পষ্ট সূচনাবিন্দু। ধর্মীয় ভাষ্য এটিকে “আল্লাহর পথে প্রথম অভিযান” বললেও, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের বাণিজ্য–রুট সামরিকভাবে হুমকির উদাহরণ। একে হামজা ইবন আবদুল মুত্তালিবের অভিযান এবং কিছু বইতে “Sīf al-Baḥr” (Sea Coast Expedition) হিসেবে নাম দেয়া আছে।
উবাইদা ইবন আল-হারিস প্রায় ৬০–৮০ জন মুসলিমকে নিয়ে কুরাইশের আরেকটি কাফেলার দিকে অগ্রসর হন, লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য–রুটে ভীতি তৈরি ও ভবিষ্যতের লুটের পথ খোলা। সীমিত তীর নিক্ষেপের পর পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ ছাড়াই উভয় পক্ষ সরে যায়, তবে এখানে প্রথম “তীরযুদ্ধ” কথাটি ইসলামী আখ্যানের অংশ হয়ে যায়। অন্যের মালামাল লুটপাট বা অর্থনৈতিক যুদ্ধকে “জিহাদ” নাম দিয়ে পবিত্র রূপ দেওয়ার প্রবণতা এখান থেকেই দেখা যায়।
সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ছোট একটি দল আল-খাররায় পাঠানো হয় কুরাইশ কাফেলা আক্রমণের উদ্দেশ্যে, তবে কাফেলাটি আগেই পথ বদলে চলে যাওয়ায় সংঘর্ষ হয়নি। তবুও এই অভিযান মক্কার বাণিজ্যের উপর ক্রমাগত সামরিক চাপ ও রুট–নিরাপত্তা ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখা যায়। একে “আল-খাররার অভিযান” বা “সারিয়াত সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস”- বলেও অভিহিত করা হয়।
এটি ছিল প্রথম অভিযান যেখানে মুহাম্মদ সরাসরি বাহিনীর নেতৃত্ব নেন এবং কুরাইশ কাফেলা বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াদ্দান/আল-আবওয়া অঞ্চলে যান। কাফেলা না পেয়ে তিনি বানু দামরা গোত্রের সাথে অনাক্রমণ ও মিত্রতা–চুক্তি করেন, যা ভবিষ্যৎ সামরিক অগ্রযাত্রার জন্য নিরাপদ রুট নিশ্চিত করার বাস্তববাদী পদক্ষেপ।
বুয়াতে মুহাম্মদ বড় একটি বাহিনী নিয়ে কুরাইশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কাফেলার গতিপথে অবস্থান নেন, উদ্দেশ্য ছিল কাফেলা আটকানো বা অন্তত আতঙ্ক সৃষ্টি করা। কাফেলাটি অন্য রুট ব্যবহার করায় কোনো যুদ্ধ হয়নি, তবে মক্কায় স্পষ্ট বার্তা চলে যায় যে, নতুন মদিনা–রাষ্ট্র অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে প্রস্তুত।
বদরের প্রথম অভিযান, সাফওয়ান অভিযান নামেও পরিচিত, ছিল কুরাইশ নেতা সাফওয়ানের কাফেলা আঘাত করার প্রচেষ্টা। মুসলিম বাহিনী বদরে পৌঁছালেও কাফেলা পালিয়ে যায়; স্থানটি পরবর্তীতে বড় বদর যুদ্ধের মঞ্চ হয়ে ওঠে। ছোট ছোট এই ব্যর্থ অভিযাত্রাগুলোই পরবর্তীতে “মহৎ বিজয়” হিসেবে নির্মিত আখ্যানের পেছনের বাস্তব সামরিক ট্রায়াল–এন্ড–এররকে আড়াল করে।
জুল আল-উশাইরা অভিযানে মুহাম্মদ আবারও কুরাইশ কাফেলার রুটে অবস্থান নেন এবং স্থানীয় বানু মুদলিজ গোত্রের সাথে চুক্তি করে। এতে মদিনা–রাষ্ট্র পশ্চিম দিকের মরুভূমি ও উপকূলীয় পথ নিয়ন্ত্রণের কৌশলগত ভিত্তি পেতে শুরু করে, যা পরবর্তী যুদ্ধের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়।
নাখলা উপত্যকায় আবদুল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে ছোট একটি দল কুরাইশ কাফেলার ওপর আকস্মিক হামলা চালায়, একজনকে হত্যা করে এবং কয়েকজনকে বন্দী করে মালামাল লুট করে আনে। এই হামলা পবিত্র মাসে হওয়ায় মুসলিমদের ভেতরেও প্রশ্ন ওঠে; কারণ পবিত্র মাসে তারা কখনো যুদ্ধ করতো না। পরে কোরআনে “পবিত্র মাসে যুদ্ধ” প্রসঙ্গে আয়াত নাজিল হয় এবং কাজটিকে বৈধতা দেয়া হয়। বাস্তবে এটি ছিল ধর্মীয় মাসের সুরক্ষাকে উপেক্ষা করে কৌশলগত আক্রমণ, যাকে পরে ওহীর মাধ্যমে নৈতিক বৈধতা দেওয়া হয়।
হিজরতের পর প্রথম প্রায় ১৬–১৭ মাস মুসলিমরা ইহুদি–খ্রিস্টান ঐতিহ্যের কেন্দ্র বায়তুল মাকদিস (জেরুজালেম)মুখী হয়ে নামাজ পড়ত; তাফসীর গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে এগুলো ছিল ইহুদিদের আকৃষ্ট করার কৌশল। কিন্তু ইহুদিরা তাতে খুব বেশী সাড়া না দেয়ায় হঠাৎ নির্দেশ আসে কিবলা মক্কার কাবা-মুখী করার। সীরাত অনুযায়ী, এক চলমান নামাজের মধ্যেই দিক বদলানো হয়, যা “সালাতুল কিবলতাইন” নামে পরিচিত। কোরআন ২:১৪২–১৫০-এ এই পরিবর্তন নিয়ে ইহুদি ও মুনাফিকদের আপত্তির উল্লেখ আছে; নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থধারার থেকে এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক–ধর্মীয় পরিচয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হিসেবেই বেশি বোধগম্য।
বদর ছিল মদিনার মুসলিম ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ, যেখানে প্রায় ৩১৩ জন মুসলিম প্রায় এক হাজার সশস্ত্র কুরাইশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়। কুরাইশের একাধিক শীর্ষ নেতা নিহত হয়, বহু বন্দী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মদিনায় আসে, এবং ইসলামী আখ্যান এটি “ফুরকান” বা মোড় ঘোরানো বিজয় হিসেবে উপস্থাপন করে। তবে যুদ্ধের পটভূমিতে বারবার কাফেলা আক্রমণ ও অর্থনৈতিক উসকানির কারণে এটিকে একেবারে “শুধু প্রতিরক্ষা যুদ্ধ” বলা যায় না।
সহিহ হাদিসের বর্ণনায় এসেছে, মদিনায় হিজরতের পর ২ হিজরির দিকে আয়িশাকে পুতুল খেলা অবস্থা থেকেই নবীর গৃহে আনা হয় এবং তখনই দাম্পত্য সহবাস শুরু হয়। প্রচলিত সংখ্যাগণনা অনুযায়ী তার বয়স ছিল প্রায় ৯ বছর, আর মুহাম্মদের বয়স প্রায় ৫২ বছর; বয়সের পার্থক্য প্রায় ৪০ বছরেরও বেশি। আজকের নৈতিক ও আইনগত মানদণ্ডে এটি স্পষ্টভাবে শিশুবিবাহ ও ক্ষমতার বৈষম্যমূলক সম্পর্ক, যদিও ইসলামী ফিকহে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটিকে আদর্শ সুন্নাহ হিসেবে প্রচার করা হয়েছে।
বনু কায়নুকা আত্মসমর্পণ করার পর মুহাম্মদ গোত্রটির প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সমষ্টিগতভাবে হত্যা করতে চেয়েছিলেন বলে সীরাত–ইবনে হিশামের বর্ণনায় স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এ সময় খাজরাজের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মুহাম্মদের জামার কলার ধরে বলেন— “চারশত (৪০০) নিরস্ত্র মানুষকে এক সকালে কেটে ফেলবেন আপনি? এরা সেই গোত্র যারা আমাকে আমার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছে।” বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদ রাগে কালো হয়ে যান, কিন্তু ইবনে উবাই প্রায় জোর করেই তাকে থামতে বাধ্য করেন। শেষ পর্যন্ত গণহত্যা বাতিল হয়; গোত্রটির পুরুষদের হত্যা না করে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নির্বাসন দেওয়া হয়। এই ঘটনা দেখায় যে সিদ্ধান্তটি কেবল ধর্মীয় নয়—মদিনার অভ্যন্তরীণ গোত্র–রাজনীতি ও স্থানীয় ক্ষমতার ভারসাম্যও মুহাম্মদের সামরিক নীতিকে প্রকটভাবে প্রভাবিত করছিল। [13]
বদরের পর প্রতিশোধ হিসেবে আবু সুফিয়ান ছোট বাহিনী নিয়ে মদিনার আশপাশের খেজুরবাগানে মাঝরাতে আগুন লাগিয়ে দ্রুত সরে যায়। মুসলিমরা তাদের পিছু নিলেও মূল বাহিনীকে ধরতে পারে না; কেবল কিছু ফেলে যাওয়া গম–সাওয়িক জিনিস লুট হয়। এ ঘটনায় সামরিক ফল খুব নগণ্য, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে মদিনার নিরাপত্তা ভেঙে পড়া ও মদিনাবাসীর মধ্যে সীমান্ত আতঙ্ক তৈরি হয়।
আল-কুদর অভিযানে বানু সুলায়ম গোত্রের ওপর আগাম হামলার উদ্দেশ্য ছিল মদিনা–বিরোধী জোট গড়ার আগেই তাদের দুর্বল করা। গোত্রটি প্রস্তুত থাকায় বড় সংঘর্ষ না হলেও, মুসলিম বাহিনী তাদের পশুপাল ও কিছু সম্পদ নিয়ে মদিনায় ফিরে আসে। ছোট–ছোট এমন আক্রমণগুলো আশপাশের গোত্রকে ভয়ে নিরপেক্ষ বা মিত্র হতে বাধ্য করার রাজনৈতিক কৌশলের অংশ।
মদিনার ইহুদি কবি ও নেতা কাব ইবন আল-আশরাফ বদরে কুরাইশদের নিহতদের জন্য শোক–কবিতা লিখে এবং মদিনায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। রাতের অন্ধকারে প্রতারণামূলক কৌশলে তাকে ডেকে নিয়ে হত্যা করা হয় এবং তার মাথা শহরে আনা হয়। মতপ্রকাশ ও রাজনৈতিক বিরোধীকে “রাষ্ট্রের শত্রু” ঘোষণার পর টার্গেটেড কিলিং–এর এটি ছিল প্রাথমিক এক দৃষ্টান্ত।
জু আমার অঞ্চলে গাজওয়া মূলত ঘাতক–গোত্র গাতাফানকে আগেই ভয় দেখিয়ে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পরিচালিত হয়। মুসলিম বাহিনী এলাকায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেও বড় ধরনের যুদ্ধ ছাড়া তারা সরে আসে; তবুও এই উপস্থিতি গোত্রগুলোর বাণিজ্য ও চলাচলের ওপর লাগাতার চাপ তৈরি করে। প্রতিরক্ষার ভাষা ব্যবহৃত হলেও, বাস্তবে এটি সীমান্ত–নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তারের এক আগ্রাসী কৌশল।
বুহরান অভিযানে মুসলিম বাহিনী বানু সুলায়ম ও আশপাশের গোত্রগুলোর ওপর আরও একটি চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে। সরাসরি সংঘর্ষ না হলেও, এই ধরনের অভিযান গোত্রসমাজকে বুঝিয়ে দেয়—মদিনা রাষ্ট্র এখন অঞ্চলটির সামরিক সুপারপাওয়ার হতে চাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক নির্ভরতা তৈরির এই ধারা পরবর্তীতে খাজনা ও জিজিয়া ব্যবস্থায় গিয়ে চূড়ান্ত রূপ পায়।
আল-কারাদা অভিযানে একটি বাণিজ্য কাফেলার ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে পণ্য ও পশু লুট করা হয়। কাফেলার লোকজনকে আংশিক বন্দী করে মদিনায় আনা হয়, আর তাদের সম্পদ “গনিমত” হিসেবে বণ্টন করা হয়। বণিক–অর্থনীতির ওপর এই ধরনের আক্রমণ ইসলামের প্রাথমিক অর্থনৈতিক মডেলকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে।
বদরের প্রতিশোধ হিসেবে কুরাইশদের পূর্ণাঙ্গ সেনাবাহিনীর সাথে উহুদের পাহাড়ঘেরা প্রান্তরে এই যুদ্ধ হয়। প্রথমে মুসলিমরা স্পষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও তীরন্দাজদের অমান্যতার ফলে পেছন দিক থেকে হামলা গিয়ে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং অনেক প্রধান সাহাবি নিহত হন। পরাজয় সত্ত্বেও কোরআনে এটিকে ঈমান–পরীক্ষা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়; কিন্তু বাস্তবে সামরিক কৌশলগত ভুল, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং গনিমতের মাল লুটের প্রতি ঝোঁক এই পরাজয়ের মূল কারণ ছিল।
উহুদের পরপরই আহত–ক্লান্ত মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে হামরা আল-আসাদ অঞ্চলে কুরাইশকে তাড়া করা হয়, যেন শত্রুপক্ষ আরেকটি আক্রমণের সাহস না পায়। বড় যুদ্ধ ছাড়াই মক্কাবাসীরা সরে যায়, ফলে এটিকে “মনস্তাত্ত্বিক প্রতিশোধযুদ্ধ” বলা যায়। প্রচার আখ্যানের দৃষ্টিতে এটি উহুদের পর “পরাজয়ের দাগ মুছতে” ব্যবহৃত হয়, যদিও সামরিক বাস্তবতায় ফল খুব সীমিত।
কাতান অঞ্চলে গাতাফান গোত্রের শক্তি–কেন্দ্রের দিকে দিকনির্দেশিত এই অভিযানে মদিনা বাহিনী তাদের বাড়িঘর ও পশুর ওপর হামলা চালায়। সরাসরি মুখোমুখি বড় যুদ্ধে না গিয়ে দ্রুত আক্রমণ–লুট–ফিরে আসার কৌশল প্রয়োগ করা হয়, যা পরে “গজওয়াতুল ফুজ্বা” ধরনের হিট–অ্যান্ড–রান অভিযানের ধারা তৈরি করে।
আবদুল্লাহ ইবন উনাইসকে একা পাঠানো হয়েছিল এক গোত্রনেতাকে গোপনে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, যিনি নাকি মদিনায় আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি আকস্মিক হামলায় ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করে তার মাথা নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন; পরে এই মাথা ব্যবহৃত হয় রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে। ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে গুপ্তহত্যা করার এই মডেল পরবর্তী খিলাফতি যুগের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও দেখা যায়।
আর-রাজি অভিযানে কিছু মুসলিমকে “কোরআন শিক্ষক” হিসেবে পাঠানো হলেও, মূল বাস্তবতা ছিল মিত্রতা ও প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা। এরা পথে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে নিহত হয়; পরে এই ঘটনাকে “শহীদের কাহিনি” হিসেবে ধর্মীয় আবেগ তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু গোড়ায় যে রাজনৈতিক–সামরিক ক্যালকুলেশন ছিল, প্রচারকথনে তা অনেকটাই আড়াল হয়ে যায়।
বীর মাউনাহ ঘটনায়ও একটি শিক্ষক–দলকে ডাক দেওয়া হলেও, পথিমধ্যে গোত্রশত্রুরা আক্রমণ করে প্রায় সবাইকে হত্যা করে। পরবর্তীতে কোরআনের কিছু আয়াত এই শহীদদের স্মরণে নাজিল হয়েছে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু মূলত এটি গোত্রীয় রাজনীতির ভুল হিসাব ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যতীত ভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশের ঝুঁকি নেয়ার ফলাফল।
মদিনার ইহুদি পণ্ডিতরা—বিশেষ করে হুয়াই ইবনে আখতাব—মুহাম্মদকে ধারাবাহিকভাবে তাওরাত–সংক্রান্ত প্রশ্ন, বংশলতিকা ও নবুয়তের যৌক্তিকতা নিয়ে চাপে ফেলতেন; অনেক ক্ষেত্রে তিনি এসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে ব্যর্থ হন বলে ইসলামী রেওয়ায়েতে বর্ণিত। পরবর্তীসময়ে বনু নাদীর গোত্র মুহাম্মদকে একটি বৈঠকে আমন্ত্রণ জানায়; তার সঙ্গে প্রায় ৩০ জন লোক যায়, কিন্তু তিনি আলোচনার শুরুতেই হঠাৎ ভয়ে বা সন্দেহে একাই স্থান ত্যাগ করে অন্যদের সেখানেই রেখে মদিনায় ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি গোত্রটির বিরুদ্ধে “হত্যাচক্রান্ত”–এর অভিযোগ তোলেন—যা ইহুদি সূত্র অনুযায়ী ভিত্তিহীন, আর মুসলিম সূত্রেও ঘটনাটি অস্পষ্ট ও বিরোধপূর্ণ রয়ে গেছে। মুহাম্মদকে নাকি জিবরাইল এসে গোপন সংবাদ দিয়ে গেছে যে, ইহুদিরা পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর ছুড়ে মুহাম্মদকে হত্যার চক্রান্ত করছিল! এরপর এই অভিযোগে মুহাম্মদ বনু নাদীরের দুর্গ অবরোধ করেন এবং কয়েকদিনের চাপের পর গোত্রটিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়; তাদের জমি, বাগান ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে গোত্রটিকে নির্বাসিত করা হয়। এই ঘটনা দেখায়, ধর্মীয় বিতর্কে পরাজয়, রাজনৈতিক সন্দেহ এবং স্থানীয় ক্ষমতার ভারসাম্য—সবই মিলে মদিনার ইহুদি গোত্রগুলোকে একে একে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
দত্তকপুত্র জায়েদ ইবন হারিসার স্ত্রী জায়নাব বিনতে জাহশকে তালাকের পর মুহাম্মদ নিজে তাকে বিয়ে করেন; কোরআনের ৩৩:৩৭ এই ঘটনাকে সরাসরি স্পর্শ করে। এর পর থেকে দত্তক–পুত্রকে আর “আসল ছেলে” বলে বিবেচনা করা হয় না এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে বৈধ বলা হয়। সমালোচকের চোখে এটি এক ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে ওহীর মাধ্যমে বৈধতা দেওয়ার উদাহরণ, যা দত্তক–প্রথার সামাজিক নিরাপত্তাও ভেঙে দেয়।
কুরাইশ ও মুসলিমরা আবারো বদর সংলগ্ন এলাকায় মুখোমুখি হওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে কুরাইশরা বড় যুদ্ধে আসেনি। মুসলিম বাহিনী কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করে “শক্তি প্রদর্শন” করে ফিরে আসে; কোনো বড় সংঘর্ষ হয়নি। যুদ্ধহীন এই অভিযানে লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়া যে বদরের পরও মদিনার সামরিক আত্মবিশ্বাস অটুট আছে।
যাত আল-রিকার অভিযানে মুসলিম বাহিনী নাজদের দিকে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটি গোত্রকে ভয় দেখায় এবং কিছু সম্পদ দখল করে। কঠিন মরুভূমি অঞ্চলে এই অভিযানে সরাসরি বড় যুদ্ধের বদলে টহল, লুট এবং ভীতি সৃষ্টিই বেশি ঘটেছে বলে বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। এই সময়ই “সালাতুল খাওফ” বা যুদ্ধাবস্থায় নামাজের হালকা রূপ নিয়ে আয়াত নাজিল হয়েছে বলে দাবি রয়েছে।
দুমাতুল জানদাল ছিল সিরিয়া–মুখী বাণিজ্য–রুটের গুরুত্বপূর্ণ জংশন, যা বাইজেন্টাইন প্রভাবাধীন অঞ্চলের কাছাকাছি। মুসলিম বাহিনী এখানে হঠাৎ হাজির হয়ে স্থানীয়দের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ও কাফেলাদের ভয় দেখায়, ফলে অনেকে সেই রুটব্যবহার কমিয়ে দেয়। এটি আরব উপদ্বীপ থেকে বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডের দিকে ইসলামী সামরিক নজর প্রসারের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে দেখা যায়।
আল-মুরাইসি অভিযানে বানু মুস্তালিক গোত্রের ওপর আক্রমণ চালানো হয়, তাদের অনেককে বন্দী করা এবং সম্পদ দখল করা হয়। এখানেই গোত্র–প্রধানের কন্যা জুয়াইরিয়া বন্দী হন এবং পরে মুহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন; ফলে বন্দীদের একাংশকে “শ্বশুরালয়”–সম্পর্কের যুক্তিতে মুক্তি দেওয়া হয়। এতে একদিকে নারী বন্দি–ব্যবস্থাকে বৈধ রাখা হয়, অন্যদিকে রাজনৈতিক বিবাহের মাধ্যমে গোত্রকে নিজের পক্ষে টেনে আনা হয়।
আল-মুরাইসি অভিযানের ফিরতি পথে আয়িশা কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়লে তার ওপর ব্যভিচারের গুজব ছড়ায়, যা মদিনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট সৃষ্টি করে। দীর্ঘ একমাস পরে কোরআনে তার নির্দোষতার ঘোষণা এসেছে বলে দাবি করা হয়, আর গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধানও প্রণীত হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত–পারিবারিক সঙ্কটকে ওহীর মাধ্যমে সমাধান করে একে আইনগত নীতি বানানোর প্রবণতা স্পষ্ট হয়।
মক্কা, গাতাফান এবং কিছু ইহুদি গোত্রের জোট তৈরি করে এবং মুহাম্মদের একের পর এক বাণিজ্য কাফেলা লুটের জবাব দিতে তারা একত্রিত হয়ে মদিনাকে ঘিরে ফেললে, সালমান আল-ফারসির পরামর্শে শহরের চারদিকে বড় পরিখা খোঁড়া হয়। পরিখা কৌশলে সরাসরি হামলা ব্যর্থ হয় এবং দীর্ঘ অবরোধ শেষে জোট ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; কোরআনে এটিকে “আহযাব” নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সামরিকভাবে এটি ছিল প্রতিরক্ষামূলক সফলতা, কিন্তু এর পরপরই মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্মম গণহত্যা সংগঠিত হয়।
খন্দক যুদ্ধ যেহেতু রক্ষণাত্মক ছিল, সেখানে তেমন কিছুই গনিমতের মাল পাওয়া যায় না। কিন্তু পরিখা খননে মুহাম্মদের সাহাবীদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সাহাবীদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ ছিল। তখনই “বিশ্বাসঘাতকতা”–র অভিযোগে মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযাকে আক্রমণের নির্দেশ আল্লাহর কাছ থেকে নাকি চলে আসে, এবং কয়েক সপ্তাহ অবরোধের পর তাদের পানই ও খাদ্য বন্ধ করে দিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। পুরুষদের সারিবদ্ধভাবে গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে শত শত মানুষকে শিরশ্ছেদ করা হয়, নারী–শিশুদের দাস হিসেবে বণ্টন করা হয় এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়। ইসলামী ঐতিহ্যে এটিকে ন্যায়বিচার বলা হলেও আধুনিক দৃষ্টিতে এটি সুস্পষ্ট গণহত্যা ও গণ–দাসত্বের উদাহরণ।
মুহাম্মদ ইবন মাসলামার নেতৃত্বে সীমান্তে এমন কিছু গোত্রের বিরুদ্ধে হামলা চালানো হয় যাদের মদিনা–বিরোধী কার্যকলাপের সন্দেহ ছিল। লক্ষ্য ছিল সম্ভাব্য জোট গঠনের আগেই তাদের ভীত ও দুর্বল করে ফেলা। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ–ঘোষণা ছাড়াই এই ধরনের শাস্তিমূলক আক্রমণাত্মক জিহাদ রাজনৈতিক মতভেদের ওপর সামরিক পদক্ষেপকে স্বাভাবিক করে তোলে।
বনু লাহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযানে পূর্বের শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ ও সীমান্ত–নিয়ন্ত্রণ দুটোই লক্ষ্য ছিল। গোত্রটি পাহাড়ি পথে পালিয়ে যাওয়ায় বড় সংঘর্ষ না হলেও, মুসলিম বাহিনী তাদের এলাকায় কিছুদিন অবস্থান করে প্রভাব ফলায়। প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের স্বাধীন সামরিক উপস্থিতি সহ্য করা হবে না—এই বার্তা ছিল স্পষ্ট।
জু কারাদ অভিযানে মুসলিম উট ও সম্পদ লুটের প্রতিশোধ নিতে শত্রু দলকে তাড়া করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর পাল্টা হামলা করা হয়। শত্রুপক্ষ কিছুটা দূরে সরে গেলেও মুসলিমরা তাদের কিছু পশুপাল ও সম্বল দখল করে মদিনায় নিয়ে আসে। এতে যুদ্ধ–লব্ধ সম্পদ আবারও মদিনার অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে।
উক্কাশা ইবন আল-মিহসান সীমান্তবর্তী একদল বেদুইন ও সম্ভাব্য দস্যু–গোত্রের ওপর আকস্মিক হামলা চালান। বর্ণনাগুলোতে ছোটখাটো সংঘর্ষ ও কিছু সম্পদ দখলের কথা থাকলেও, কোনো বড় যুদ্ধের বিবরণ নেই। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য–রুট ও তীরবর্তী অঞ্চলগুলোকে মদিনা–নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা–জোনে রূপান্তর করা।
বনু সালাবা গোত্রের বিরুদ্ধে পরপর কয়েকটি অভিযানের প্রথমটিতে মুসলিম বাহিনী তাদের অবস্থানের দিকে গিয়ে হঠাৎ আক্রমণ চালায়। গোত্রটি পালিয়ে গেলেও তাদের পশু ও কিছু সম্পত্তি দখল হয়; এভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের দুর্বল করা হয়।
প্রথম অভিযানের পরেও বনু সালাবা হুমকি হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় আবারও সামরিক দল পাঠানো হয়। এখানেও সরাসরি বড় লড়াই না হলেও উপস্থিতি ও টহলের মাধ্যমে তাদের চলাচল সীমিত করে দেওয়া হয়। এই ধারাবাহিক চাপ গোত্রটিকে রাজনৈতিকভাবে ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে পরিচালিত।
যায়েদ ইবন হারিসা আল-জুমুম অঞ্চলে একদল শত্রুবাহিনী ও তাদের মিত্র গোত্রকে আক্রমণ করেন, কিছু লোক বন্দী ও সম্পদ দখল করা হয়। সীমান্ত–টহল ও আশপাশের গোত্রগুলোর ওপর লাগাতার হামলার ফলে অনেক ছোট গোত্র মদিনার অধীন বা মিত্র হতে বাধ্য হয়েছিল।
আল-ইস অঞ্চলে যায়েদের এই অভিযানে শত্রুদের কিছু গবাদিপশু ও সামগ্রী দখল করা হয়; প্রতিপক্ষ মূলত ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। বাণিজ্যে ও খাদ্যে নির্ভর এই পশুপালগুলো জব্দ করে মুসলিম রাষ্ট্র বাস্তবে শত্রু গোত্রদের অর্থনৈতিক শ্বাসরোধ করছিল।
বনু সালাবার তৃতীয় দফা অভিযানে আবারো তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়; এ সময় গোত্রের অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। প্রচার আখ্যান এই সব অভিযানে “ইসলামবিরোধী শক্তিকে দমন” বললেও, বাস্তবে তা ছিল গোত্র–ভিত্তিক স্বাধীনতা ভেঙে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র–নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া।
হিসমা অঞ্চলে যায়েদের অভিযানে কয়েকজনকে হত্যা ও বন্দী করা হয়, গবাদিপশু ও সম্পদ দখল করা হয়। অনেক বেদুইন গোত্র মদিনা–নিয়ন্ত্রিত রুটে চলাচলের বিনিময়ে নিজেদের আনুগত্য দেখাতে শুরু করে; অর্থাৎ সামরিক চাপকে রাজনৈতিক আনুগত্যে রূপান্তরের কৌশল এখানে স্পষ্ট।
ওয়াদি আল-কুরা ছিল কৃষি–সমৃদ্ধ অঞ্চল; সেখানে অভিযানে কিছু লোক নিহত ও অনেক সম্পদ দখল করা হয়। এই অঞ্চলের ইহুদি ও অন্যান্য গোত্রের ওপর ক্রমাগত চাপ পরে খাইবার–আক্রমণ ও ফিদাক ইত্যাদিতে পরিণতি হয়।
নবী মুহাম্মদ প্রায় ১,৪০০ মুসলিমকে নিয়ে মক্কায় উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাদের কাছে যুদ্ধের অস্ত্র ছিল না, তাই যাত্রাটি ছিল শান্তিপূর্ণ। তবে কুরাইশরা সন্দেহ করে মুসলিমদের প্রবেশ আটকে দিতে সৈন্য পাঠায় এবং হুদায়বিয়ার কাছেই মুসলিম কাফেলাকে থামিয়ে দেয়।
মক্কার কুরাইশদের সাথে আলোচনার জন্য উসমান ইবনে আফ্ফানকে মক্কায় পাঠানো হলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে কুরাইশরা তাকে হত্যা করেছে। এই গুজব ওঠার পরে মুহাম্মদ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং তিনি ও অন্য মুসলিমরা হুদায়বিয়ার গাছের নিচে “বাই‘আতুর রিদওয়ান” নামে বিখ্যাত শপথ নেয়— যেখানে তারা উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নিতে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে। এই বিষয়ে কোরআনের একটি আয়াতও নাজিল হয় যেখানে আল্লাহও উসমানের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার শপথে মুসলিমদের সাথে আছেন এরকম আশ্বাস দেয়া হয়, এমনকি আল্লাহও উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার শপথে মুসলিমদের সম্মিলিত হাতের ওপর নিজের হাত রেখেছেন বলে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জানা যায়—উসমান জীবিত আছেন এবং সশরীরে তিনি ফিরে আসেন।
উসমানের ফিরে আসার পর দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে “হুদায়বিয়া চুক্তি” স্বাক্ষরিত হয়। এতে প্রথমে মনে হয় মুসলিমদের ওপর কঠোর ও অসম শর্ত আরোপিত হয়েছে, তবে বাস্তবে এটি ছিল দুই পক্ষের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধবিরতি এবং মদিনার রাষ্ট্রকে কুরাইশদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান। এই শান্তিকালীন বিরতির সুযোগে মুসলিমরা পরে খাইবারসহ পার্শ্ববর্তী বহু অঞ্চল সামরিকভাবে দখল করতে সক্ষম হয়।
বদর ও উহুদের মতো প্রধান যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামরিক কৌশলের নেতৃত্বদানকারী খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। হুদায়বিয়া চুক্তির পর কুরাইশদের ভবিষ্যৎ ক্ষমতা দুর্বল ও অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে—এ সময়ই খালিদ, আমর ইবন আল-আস এবং উসমান ইবন তালহা একসাথে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার যোগদানের পর মুসলিম বাহিনীর সামরিক সক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মক্কা বিজয় ও পরবর্তী অভিযানে তার ভূমিকা প্রায় প্রধান সেনাপতির মতো হয়ে ওঠে। খালিদের ইসলাম গ্রহণকে প্রায়ই “আধ্যাত্মিক জাগরণ” বলা হয়, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এটি ছিল যুদ্ধজোট–রাজনীতির বাস্তব মূল্যায়ন এবং ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের প্রভাব।
খাইবার ছিল উত্তর আরবের একটি শক্তিশালী ইহুদি দুর্গ–নগর, যেখানে আগের নির্বাসিত ইহুদিদেরও অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিল। খাইবারে ছিল অত্যন্ত ধনী কৃষি-অর্থনীতি, মদিনার উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে ধনী অর্থনীতির কেন্দ্র। এখানেও একই অভিযোগে আক্রমণ করা হয়, বলা হয় ইহুদিরা পালিয়ে এখানে আশ্রয় নিচ্ছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে নাকি ষড়যন্ত্র করছে। দীর্ঘ অবরোধ ও একাধিক দুর্গ পতনের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী এলাকা দখল করে; পুরুষদের একাংশ নিহত হয়, নারীরা বন্দী ও বহু সম্পদ গনিমত হিসেবে বণ্টিত হয়। এখানেই সাফিয়া বিনতে হুয়াইয়্য–সহ একাধিক নারী যুদ্ধবন্দি পরে নবী বা সাহাবিদের “মালিকানা”–তে চলে যায়, যা যুদ্ধ–ধর্ষণ ও দাসত্ব–প্রথাকে ধর্মীয় বৈধতার ছায়া দেয়।
খাইবার দখলের পর বনি নাদীরের মৃত প্রধান কিঞ্চানা ইবন আবি আল-হুকাইকের স্ত্রী জয়নাব বিনতে হারিস মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের খাবারের দাওয়াত দেন। এই মহিলা তার পরিবার পরিজন সবাইকেই হারিয়েছে মুহাম্মদের হাতে। সে একটি রোস্টেড ভেড়ার মাংস পরিবেশন করেন, যেখানে তিনি মাংসের নির্দিষ্ট অংশে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। বর্ণনা অনুযায়ী, মাংসের কাঁধের অংশ মুখে দেওয়ার পর মুহাম্মদ নাকি অস্বাভাবিক স্বাদ টের পান এবং থেমে যান, কিন্তু তার সঙ্গী বিশার ইবন বারা মাংস খাওয়ার পরেই তীব্র ব্যথায় মারা যান। জয়নাব স্বীকার করেন যে তিনি মুহাম্মদকে হত্যা করে খাইবারে সংঘটিত গণহত্যা, পরিবার পরিজন সবাইকে মেরে ফেলা ও জমি–বাগান দখলের জন্য প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন, এবং যাচাই করতে চেয়েছিলেন তিনি সত্যিই “নবী কি না”। ইসলামি সূত্রে মুহাম্মদ পরবর্তীতে তাকে ক্ষমা করেন বলে একটি রেওয়ায়েত আছে, আবার অন্য সূত্রে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়—উৎসগুলো পরস্পরবিরোধী। এই ঘটনা দেখায় যে খাইবার দখলের সহিংসতা ও সম্পদ–বাজেয়াপ্তকরণের পরে ইহুদি বেঁচে থাকা সদস্যদের মধ্যে প্রতিশোধ ও উত্তেজনা কতটাই গভীর ছিল।
খাইবারের পর ফিদাকসহ কিছু ইহুদি–অধ্যুষিত এলাকা যুদ্ধ ছাড়াই জমি–কর ও আনুগত্যের শর্তে মুসলিম রাষ্ট্রের অধীন হয়ে যায়। এসব অঞ্চল থেকে পাওয়া কৃষিজ আয়ের বড় অংশ “নবীর ব্যক্তিগত মালিকানা” বা বায়তুল মাল–এর নামে কেন্দ্রীভূত হয়, যাকে কোরআনে “ফাই” আয়ের বিধান দিয়ে বৈধতা দেওয়া হয়।
খাইবার ও আশপাশের দখলের পরপরই মিশরের শাসক মুকাওকিসের পাঠানো উপহার–দল থেকে কপ্টিক দাসী মারিয়া আল-ক্বিবতিয়্যা মদিনায় আনা হয় এবং তাকে মুহাম্মদের ব্যক্তিগত দাসী ও উপপত্নী হিসেবে রাখা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ইসলামী সূত্রে তাকে “উম্মুল মুমিনীন” উপাধি দেওয়ার চেষ্টা থাকলেও অধিকাংশ ক্লাসিকাল ফিকহ তার আইনগত মর্যাদাকে “আমাত” (দাসী) হিসেবে ধরে, অর্থাৎ তিনি অন্য স্ত্রীদের মতো সমমানের “বৈধ স্ত্রী” নন। তিনি শুরুতে ছিলেন মুহাম্মদের যৌনদাসী এবং পরবর্তীতে তার মর্যাদা উম্মু ওয়ালাদে উন্নীত হয়, যার ফলে মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে তিনি খলিফাদের থেকে কিছু ভাতা পেতেন।
হুদায়বিয়া চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুসলিমরা এক বছর পর মক্কায় ঢুকে তিন দিন অবস্থান করে উমরা আদায় করে, যাকে উমরা কজা বলা হয়। এটি মক্কা–কাবার ওপর মুসলিমদের ধর্মীয় দাবিকে স্বীকৃত ও স্বাভাবিক করে তোলে, যদিও তখনও শহরটি কুরাইশদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে ছিল।
সালামা ইবন আল-আকওয়া একটি গোত্রের দ্বারা মুসলিম উট লুট হয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে দ্রুত পিছনে তাড়া দেন। তিনি একাই তাদের ওপর তীর নিক্ষেপ করে গতি কমিয়ে দেন এবং পরে প্রধান বাহিনী পৌঁছে লুট হওয়া উটগুলো উদ্ধার করে। উদ্দেশ্য ছিল উট-বাণিজ্য রুটে মুসলিম আধিপত্য প্রদর্শন এবং ভবিষ্যতে লুটের ঘটনা নিরুৎসাহিত করা। যদিও বড় যুদ্ধ হয়নি, তবে এই অভিযান দেখায় যে নবী–রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ট্রানজিট রুটকে যেকোনো মূল্যে দখলে রাখতে চাচ্ছিল।
আবু কাতাদাকে নাজদের মরু–অঞ্চলে পাঠানো হয়েছিল এমন কিছু উপজাতির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে, যারা মুসলিম কর–ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করছিল। হাদিসে আছে, তিনি পথে প্রতিপক্ষের একজনকে হত্যা করেন এবং তাদের পশুপাল দখল করেন। অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শক্তির প্রদর্শন ও রাজনৈতিক আনুগত্য আদায় করা। যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে এটি একটি ছোট গোত্রের উপর অর্থনৈতিক–রাজনৈতিক সামরিক চাপ প্রয়োগের উদাহরণ।
আবদুল্লাহ ইবন আবি হাতিবকে পাঠানো হয়েছিল সীমান্তবর্তী উপজাতিদের কাছ থেকে কর আদায় বা শর্তে আনুগত্য আদায় করতে। তাদের মধ্যে কেউ মুসলিম রাষ্ট্রকে মেনে নিলে শান্তি, কেউ অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত হামলা চালানো হতো। কিছু মানুষ বন্দী করা হয় এবং তাদের সম্পদ গনিমত হিসেবে গণ্য হয়। এটিও ছিল আরব উপদ্বীপের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক–সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি ধাপ।
হাদিস–আখ্যান অনুযায়ী, একদিন স্ত্রী হাফসা বিনতে উমর-এর ঘরে তার অনুপস্থিতিতে মুহাম্মদ মারিয়ার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন; হাফসা হঠাৎ ফিরে এসে এটি দেখে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাকে চুপ করাতে মুহাম্মদ নাকি মারিয়াকে আর না ছোঁয়ার শপথ করেন এবং ঘটনাটি ফাঁস না করার অনুরোধ করেন; কিন্তু হাফসা আয়িশাকে জানালে গৃহের অভ্যন্তরে বড় সংকট সৃষ্টি হয়। এর পরপরই কোরআনের ৬৬:১–৫ (সূরা তাহরীম) নাজিল হয়েছে বলে দাবি করা হয়, যেখানে মুহাম্মদকে অপ্রয়োজনীয় “হারাম” না করতে বলা ও স্ত্রীদের কড়া ভাবে সতর্ক করে বলা হয়—তারা অনুতপ্ত না হলে আল্লাহ চাইলে তাদের তালাক দিয়ে নবীর জন্য “ভাল স্ত্রী” এনে দেবেন। যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে এটি একেবারে ব্যক্তিগত যৌন–কেলেঙ্কারি ও গৃহকলহকে ওহীর মাধ্যমে ম্যানেজ করে, স্ত্রীদের উপর চাপ দিয়ে এবং দাসী–উপপত্নী ব্যবস্থাকে প্রশ্নের উর্ধ্বে তুলে ধরার একটা স্পষ্ট উদাহরণ।
মু’তা ছিল বাইজেন্টাইন সীমান্তের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ, যেখানে মুসলিম বাহিনী স্থানীয় খ্রিস্টান আরব বাহিনী ও রোমান মিত্রদের মুখোমুখি হয়। প্রারম্ভিক তিন কমান্ডার মারা গেলে খালিদ ইবন ওয়ালিদ বাহিনীকে কৌশলে ফিরিয়ে আনেন বলে বর্ণনা আছে; মুসলিমদের মাঝারি মানের ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রচারে এটি “বড় বিজয়” হিসেবে দেখালেও, বাস্তবে এটি ছিল সীমান্ত–পরীক্ষা ও শক্তির ভারসাম্য যাচাইয়ের যুদ্ধ।
কুরাইশ–মিত্র এক গোত্রের আকস্মিক হামলাকে ভিত্তি করে বলা হয়, হুদায়বিয়া চুক্তি কার্যত ভেঙে গেছে। মুসলিম বাহিনী এই ঘটনাকে মক্কার বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযানের ধর্মীয় ও নৈতিক যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে।
দশ হাজারেরও বেশি সৈন্য নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার ফলে শহর প্রায় যুদ্ধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে; কাবার চারপাশের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। কিছু ব্যক্তিকে “মাফ না করার” তালিকায় রেখে হত্যা করার নির্দেশ থাকলেও, বেশিরভাগকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়—যদিও সেই ক্ষমা শর্তযুক্ত: ইসলাম গ্রহণ বা নিরাপদভাবে বেঁচে থাকার অন্য পথ খুব কমই ছিল। বিজয়ের পর কুরাইশ নেতৃত্ব ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুরোনো গোত্র–অভিজাত শ্রেণি নতুন ধর্মীয় ক্ষমতা–কাঠামোর ভেতরেই আবার কেন্দ্রে ফিরে আসে।
মক্কা বিজয়ের দিনই মুহাম্মদের কাছে উম্মে হানী আসে, যার আগে উম্মে হানীর স্বামী মুহাম্মদের ভয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে যায়। সেইদিন উম্মে হানী মুহাম্মদের সাথে দেখা করতে এসে দেখে মুহাম্মদ গোছল করছে, ফাতিমা সেখানে পর্দা করে আছে। এর কিছুক্ষণ পরেই, মুহাম্মদ উম্মে হানীর বাসায় চলে যান, সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এবং আরও একবার গোছল করেন। [7]
মক্কা বিজয়ের পরপরই হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের সঙ্গে হুনাইনে কঠোর যুদ্ধ হয়; প্রথমে মুসলিমরা হুট করে আক্রমণে হতচকিত হয়ে পিছু হটে। পরে তারা পুনর্গঠিত হয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে এবং বিপুল পরিমাণ গবাদিপশু ও নারী–পুরুষ বন্দী করে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনে কুরাইশের নতুন মুসলিম অভিজাতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যা “মুয়াল্লাফাতুল কুলুব” নামে নরম ভাষায় ঢেকে দেওয়া হয়।
হুনাইনের পর বিজিত হাওয়াজিনদের অংশ তায়েফ দুর্গে আশ্রয় নিলে সেখানে দীর্ঘ অবরোধ করা হয়, কিন্তু শহরটি তৎক্ষণাৎ পতন হয় না। পরে তায়েফবাসীরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করে; মূর্তি ভাঙা ও করব্যবস্থা মানতে রাজি হয়। ভয়ের রাজনীতি ও ধর্মীয় আনুগত্য এখানে একসাথে কাজ করেছে।
উয়াইনাহ ইবন হিসন মদিনার একদল রাখালকে হত্যা করে পশুপাল লুট করে নিলে মুসলিম বাহিনী তার বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। অভিযানে তার গোত্রের কয়েকজন নিহত হয় এবং প্রচুর গবাদিপশু দখল করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তরাজনীতিতে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জকে কঠোরভাবে দমন করা। এতে ছোট গোত্রগুলো ক্রমে স্পষ্ট বার্তা পায়—মদিনার ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বই ঝুঁকির মুখে পড়বে।
আলি একটি ছোট গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন, যারা মুসলিম রাষ্ট্রকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল। যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ছিল, তবে অভিযানের পর গোত্রটি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এখানে কিছু সম্পদ জব্দ করা হয় এবং উল্লেখযোগ্য লোকবল বন্দী করা হয়। এটি দেখায় যে নবী–রাষ্ট্র কূটনীতি ব্যর্থ হলে জোর করে আনুগত্য আদায় করতে দ্বিধা করত না।
খালিদকে পাঠানো হয়েছিল বনি জাজিমা গোত্রে, যারা আগে মুসলিমদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িত ছিল। হাদিসে আছে, তারা দাবি করে “আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি”, তবু খালিদ তাদের অনেককে হত্যা করেন। ফিরে এসে মুহাম্মদ প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেন। এই ঘটনা ইসলামী সামরিক প্রচারে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও গোত্রীয় উত্তেজনার জটিলতা দেখায়।
নবী ওমান ও বাহরাইন অঞ্চলে প্রতিনিধি পাঠান—কিছু অঞ্চল ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে, অন্যত্র সামরিক চাপ সৃষ্টি করতে হয়। খাজনা, জিজিয়া বা ইসলাম—এই তিনটির যেকোনো একটি বেছে নিতে বলা হতো। প্রতিরোধী গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে ছোট হামলা চালানো হতো, যাতে তারা নতুন রাষ্ট্র কাঠামোর অধীন হতে বাধ্য হয়। এতে আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলীয় রাজনৈতিক মানচিত্র দ্রুতই মুসলিম কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।
বিভিন্ন সাহাবিকে পাঠানো হয়েছিল বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলোতে, যাদের কেউ জিজিয়া দিতে অস্বীকার করছিল, কেউ বা ইসলাম গ্রহণের পর আবার পুরোনো ধর্মে ফিরছিল। কিছু অভিযানে হত্যা, কিছুতে দাসত্ব, আর কিছুতে সম্পূর্ণ জমি–দখলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ছোট ছোট অভিযানের ফল হিসেবে গোত্রীয় স্বায়ত্তশাসন ভেঙে মদিনা–কেন্দ্রিক রাষ্ট্রিক কাঠামো দৃঢ় হয়।
সিরিয়া সীমান্তবর্তী বেদুইন গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সারিয়া পাঠানো হয়, কারণ তারা কখনো মুসলিম পথরোধ করছিল, কখনো মদিনার প্রভাব খর্ব করছিল। এসব টহলে কিছু হত্যা, কিছু বন্দী ও পশুপাল–দখলের ঘটনা বারবার ঘটে। উদ্দেশ্য ছিল বাইজেন্টাইন–ঘেঁষা অঞ্চলগুলোকে আগেই দুর্বল করে রাখা, যা পরে তাবুক অভিযানে কাজে লাগে।
ইয়েমেনের হামদান গোত্রে আলিকে পাঠানো হয় ইসলাম প্রচার ও শাসনবিধি প্রতিষ্ঠা করতে। তিনবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও চতুর্থবার গোত্রের প্রধানরা ইসলাম গ্রহণ করে। এটি রক্তপাতছাড়া হলেও, গোত্রীয় সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক স্বার্থ যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা পরিষ্কার। হাদিস অনুযায়ী নবী আলিকে প্রশংসা করেন, কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল আলোচনাভিত্তিক রাজনৈতিক সমঝোতা।
মারিয়ার গর্ভে জন্ম নেয় মুহাম্মদের পুত্র ইব্রাহিম; মদিনায় জন্ম নেওয়া এটি তার একমাত্র ছেলে, ফলে দাসী মারিয়ার সামাজিক অবস্থান উম্মে ওয়ালাদে উন্নীত হয়। প্রায় ১৬–১৮ মাস বয়সে ইব্রাহিম মারা যায়; সহিহ হাদিস–বর্ণনায় মুহাম্মদের চোখে পানি আসা ও শোকের কথা এসেছে, এবং এ দিন সূর্যগ্রহণ হওয়ায় কিছু লোক “ইব্রাহিমের মৃত্যুর জন্য সূর্যগ্রহণ” বলে গুজব ছড়ায়—যা তিনি নিজে অস্বীকার করেন। ধর্মীয় আখ্যান এ ঘটনাকে “নবীর মানবিক আবেগ” ও “আল্লাহর পরীক্ষা” হিসেবে দেখালেও, যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে এখানে ধারাবাহিক যুদ্ধ–লুট ও দাসপ্রথার ভেতরে জন্ম নেওয়া এক শিশুর ট্র্যাজেডি ও তার মায়ের ভঙ্গুর অবস্থানটাই বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
তাবুক অভিযানের আগে উত্তর–পশ্চিম সীমান্তে বাইজেন্টাইন–ঘেঁষা আরব গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে একাধিক ছোট সারিয়া পাঠানো হয়। লক্ষ্য ছিল সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি দেখিয়ে ভীতি সৃষ্টি করা, বাণিজ্যপথের ওপর চাপ রাখা, আর মদিনা–কেন্দ্রিক নতুন রাষ্ট্রের সামরিক সক্ষমতা প্রদর্শন করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো ছিল টহল–ধরনের অভিযান— সীমিত সংঘর্ষ, দ্রুত হামলা, তারপর ফিরে আসা।
কিছু সারিয়ায় সরাসরি সেইসব আরব গোত্রকে লক্ষ্য করা হয়, যারা উত্তর দিকের খ্রিস্টান শক্তি বা বাইজেন্টাইন প্রভাববলয়ের সাথে জোটবদ্ধ ছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। ছোট ক্যাম্পে আকস্মিক হামলা, পশু–সম্পদ লুট, রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সামরিক চাপ—এসবের মাধ্যমে সীমান্তের “নিরাপত্তা হুমকি” আগে থেকেই দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ বড় যুদ্ধের বদলে এগুলো ছিল ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা ছোট আঘাত।
সীমান্তে ধারাবাহিক সামরিক উপস্থিতি ব্যবহার করে কিছু গোত্রের ওপর কর–সদৃশ অর্থনৈতিক চাপও তৈরি হয়— “নিরাপত্তা” ও “শান্তি”র বিনিময়ে অর্থ প্রদান বা আনুগত্যের অঙ্গীকার আদায় করা হয়। এই ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে মদিনা কেন্দ্র থেকে শাম–অভিমুখী বাণিজ্যপথ ও রাজনীতি উভয়ের ওপরই শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারের গ্রাউন্ডওয়ার্ক তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে বৃহৎ তাবুক অভিযানের মানসিক ও সামরিক প্রস্তুতি হিসেবেও কাজ করে।
ইয়েমেন অঞ্চলে মুহাম্মদ একাধিক প্রতিনিধি ও গভর্নর পাঠান—কখনও আলি ইবন আবি তালিবের মতো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে, কখনও বা অন্য সাহাবিদের। কেউ কেবল দাওয়াত ও কর–সংগ্রহের দায়িত্বে, আবার কোথাও স্থানীয় বিদ্রোহী গোত্র বা প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক অভিযান চালানো হয়। কিছু গোত্র চাপের মুখে ইসলাম গ্রহণে রাজি হয়, অন্যরা “কর দিয়ে থাকো, ধর্ম রাখো” ধরনের সমঝোতায় যায়। ফলে ইয়েমেন ক্রমে মদিনা–কেন্দ্রিক ধর্মীয়–রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়।
উপসাগর–ঘেঁষা বাহরাইন অঞ্চলে পাঠানো দূতেরা স্থানীয় শাসক ও আরব–অনআরব গোষ্ঠীগুলোর সাথে চিঠিপত্র ও সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে। কেউ ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়, কেউ খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মে থেকে মদিনা–কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের কাছে জিজিয়া কর দিতে রাজি হয়। অর্থাৎ, ধর্মীয় একরূপতার বদলে রাজনৈতিক আনুগত্য ও অর্থনৈতিক কর–ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অঞ্চলটি কার্যত কেন্দ্রের অধীনস্তে চলে যায়।
ওমানের স্থানীয় শাসকদের কারও প্রতি সরাসরি দাওয়াতপত্র পাঠানো হয়, কারও কাছে দূত পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিজিয়া–সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কোথাও শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ, কোথাও অংশত রাজনৈতিক সমঝোতা—এই দুই ধরনের ঘটনাই বর্ণনায় পাওয়া যায়। সামরিক শক্তির সম্ভাব্য হুমকি এবং কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সামনে রেখে অনেক স্থানীয় নেতা আপসের পথ বেছে নেয়।
ইয়েমেন, বাহরাইন, হাদ্রামাউত, ওমান–সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলে পাঠানো এসব প্রতিনিধি ও ছোট ছোট সামরিক দলের সামগ্রিক ফল হচ্ছে এক নতুন কেন্দ্রীয় এজেন্সির উত্থান—যেখানে ধর্মীয় দাওয়াত, অর্থনৈতিক কর–ব্যবস্থা, এবং প্রয়োজনে সামরিক শক্তি—এই তিনটি একসাথে কাজ করে। ফলে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশগুলোও ধীরে ধীরে “স্বাধীন স্থানীয় ক্ষমতার কেন্দ্র” থেকে সরে এসে একটি ধর্মীয়–রাজনৈতিক কেন্দ্রের অধীনস্তে পরিণত হতে থাকে।
আলি ইবন আবি তালিবকে এই সময়ে একাধিকবার দক্ষিণের দিকে পাঠানো হয়—কোথাও স্থানীয় মন্দির বা মূর্তি–কেন্দ্র ধ্বংস, কোথাও “ইসলাম গ্রহণ করো, না হলে কর ও আনুগত্যের চুক্তি করো” ধরনের আল্টিমেটাম নিয়ে। বর্ণনায় আসে, আলির কিছু অভিযানে স্থানীয় ধর্মীয় প্রতীক ধ্বংস ও গোত্রনেতাদের ওপর স্পষ্ট রাজনৈতিক–সামরিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। এতে বোঝা যায়, “ইসলামি দাওয়াত” আর “কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বিস্তার”—দুইটি প্রক্রিয়া বাস্তবে একসাথে চলছিল।
খালিদ ইবন আল–ওয়ালিদকে পাঠানো বিভিন্ন অভিযানে কখনও স্থানীয় নেতাকে হত্যা বা বন্দী করে আনুগত্য আদায়ের ঘটনা উল্লেখ আছে; কোথাও গোত্রকে কঠোর ভাষায় বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে রাজি করানো হয়। আবার কোথাও “ধর্ম রাখতে পারবে, তবে কর দিতে হবে এবং রাজনৈতিকভাবে আনুগত্য দেখাতে হবে”—এই শর্তে সমঝোতা হয়। ফলে খালিদের অভিযানগুলো কেবল ধর্মীয় প্রচারের উদাহরণ নয়, বরং নতুন ক্ষমতা–কেন্দ্র গঠনের নির্লজ্জ বাস্তব রাজনীতিও স্পষ্ট করে।
উক্কাশা ইবন আল–মিহসান ও অন্য কয়েকজনকে নিয়ে সীমান্ত ঘেঁষা ছোট ছোট সারিয়া পাঠানো হয়। এগুলোর চরিত্রও মূলত “হিট–অ্যান্ড–রান” ধরনের—ছোট গোত্র বা ক্যারাভানে আকস্মিক হামলা, সামরিক শক্তি প্রদর্শন, তারপর দ্রুত ফিরে আসা। অনেক ক্ষেত্রে কোনো বড় যুদ্ধ ছাড়াই শুধুই ভীতি–রাজনীতি ও সামরিক উপস্থিতির বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য, যা পরবর্তীতে বৃহত্তর অভিযানগুলোর পথ মসৃণ করতে সাহায্য করে।
সুরাদ ইবন আবদুল্লাহ ও অন্যদের মাধ্যমে কিছু অঞ্চলে সরাসরি সামরিক চাপ, আবার নজরানের মতো খ্রিস্টান–প্রধান এলাকায় আপাত শান্তিপূর্ণ চুক্তি—এই দুই রকম দৃশ্যই একসাথে দেখা যায়। নজরানের ক্ষেত্রে, আখ্যান বলে তারা ধর্ম রক্ষা করে জিজিয়া ও রাজনৈতিক আনুগত্যের শর্ত মেনে নেয়; কিন্তু এর পেছনে সামরিক শক্তি ও কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাবের shadow সবসময়ই কাজ করেছে। সংশয়বাদী পাঠে এসব ঘটনাকে দেখা যায়—“কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্বাধীন রাজনৈতিক/ধর্মীয় কেন্দ্র থাকবে না”—এই নীতির ধারাবাহিক বাস্তবায়ন হিসেবে।
মসজিদে দিরার ছিল এমন একটি মসজিদ, যাকে কোরআনের ভাষায় “ক্ষতি–সাধন ও কুফর প্রচার”–এর ঘাঁটি বলা হয়; পরে সেটি ধ্বংসের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাস্তবে এটি ছিল রাজনৈতিক বিরোধী ও ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর আড্ডাখানা, অর্থাৎ এক ধরনের “বিরোধী মসজিদ”। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে ধর্মীয় অবকাঠামোকেও একচেটিয়া করার উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ।
শেষ দিককার বছরগুলোতে মুহাম্মদের একাধিক বিয়ে ও “মালাকাত aimanukum” ক্যাটাগরিতে নারী–অধীকারের ঘটনা ঘটে—এর মধ্যে যুদ্ধবন্দি, বিধবা, এবং অল্পবয়সি তরুণীও ছিল। এগুলোর অনেকগুলোই রাজনৈতিক মিত্রতা, গোত্রীয় সামঞ্জস্য অথবা যুদ্ধের ট্রফি হিসেবে দেখা যায়; ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক ক্যালকুলেশন এখানে মিশে গেছে। আধুনিক নৈতিক মানদণ্ডে এগুলোকে সহজে আদর্শিক আচরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব, যদিও ক্লাসিকাল ফিকহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটিকে সুন্নাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।
নবম হিজরিতে হাজ্জ মৌসুমে প্রথমে আবু বকরকে হজদলপ্রধান করা হয়; পরে সূরা তাওবার প্রারম্ভিক আয়াত নিয়ে আলি ইবন আবি তালিবকে পাঠানো হয় মক্কায়। ঘোষণায় আরবের মুশরিকদের জন্য চার মাসের আল্টিমেটাম, এরপর কাবা–তাওয়াফে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ, আগের চুক্তিগুলো
বাতিল এবং ইসলাম গ্রহণ বা যুদ্ধ—এই দুই বিকল্পের কথা বলা হয়; “আহলে কিতাব”–দের জন্য জিজিয়া কর নির্ধারণ করা হয়।
এই ঘোষণা ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রথম বৃহৎ ধর্মীয়–রাষ্ট্রিক আল্টিমেটাম, যা আরব উপদ্বীপকে বাস্তবে এক–ধর্মীয় একচেটিয়া ভূখণ্ডে পরিণত করার মতবাদী ভিত্তি তৈরি করে।
দুমাতুল জানদালে খালিদের অভিযানে স্থানীয় খ্রিস্টান–ঘেঁষা আরব নেতা ও জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে ইসলাম গ্রহণ বা কর–ব্যবস্থা মানাতে বাধ্য করা হয়। বর্ণনাগুলোতে কিছু যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ থাকলেও, ফলাফল হিসেবে অঞ্চলটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রভাব–অঞ্চলে পরিণত হয়।
মক্কা বিজয়ের পর আবু সুফিয়ানকেও কিছু সামরিক অভিযানে অংশ নিতে দেখা যায়, যেখানে তিনি নতুন ক্ষমতা–কাঠামোর অংশ হিসেবে মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব বা সহায়তা দেন। একসময়ের প্রধান শত্রুর এই দ্রুত রূপান্তর দেখায়, কীভাবে গোত্রীয় অভিজাতরা নতুন ধর্মীয় ক্ষমতাকেও নিজেদের অবস্থান রক্ষার জন্য ব্যবহার করেছে।
দ্বিতীয়বারের অভিযানে যারা প্রথম দফায় ইসলাম গ্রহণ বা আনুগত্য দেখিয়েও গোপনে বিরোধিতা করছিল বলে সন্দেহ ছিল, তাদের ওপর আবারও সামরিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। এতে স্পষ্ট বার্তা যায়—একবারের আনুগত্যই যথেষ্ট নয়; কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের পলিসি মানা না হলে আবারও আক্রমণ আসবে।
সুরাদ ইবন আবদুল্লাহকে পাঠানো অভিযানে স্থানীয় কিছু গোত্র প্রথমে প্রতিরোধ করলেও পরে মুসলিম বাহিনীর সামনে ভেঙে পড়ে। ফলাফল হিসেবে তারা ইসলাম গ্রহণ বা কর–ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন ক্ষমতাকে মানতে বাধ্য হয়; স্বাধীন ধর্ম–রাজনীতি টেকেনি।
নজরান ছিল খ্রিস্টান–অধ্যুষিত ও তুলনামূলক সমৃদ্ধ এলাকা; আলোচনার পাশাপাশি সামরিক চাপের প্রেক্ষিতে তারা জিজিয়া করের শর্তে ধর্মীয় পরিচয় রাখা সত্ত্বেও রাজনৈতিক আনুগত্য স্বীকার করে। এতে “ধর্ম পাল্টাও অথবা কর–দাও”—এই দ্বিমুখী কাঠামো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
মুযহিজ অঞ্চলে আলির অভিযানে স্থানীয় গোত্রগুলোকে ইসলাম গ্রহণ–কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা হয়। বর্ণনায় কিছু যুদ্ধ, কিছু হত্যা ও কিছু কর–চুক্তির উল্লেখ রয়েছে; প্রচার–আখ্যান এটিকে “ইসলামের বিজয়”, যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে এটিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের ধাপ হিসেবে দেখা যায়।
ইয়েমেনের হামদান অঞ্চলে আলি এক বড় গোত্রকে ইসলাম গ্রহণে রাজি করান; বর্ণনায় এখানে তুলনামূলক কম রক্তপাতের কথা বলা হয়। তবে কর–ব্যবস্থা, আনুগত্য এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া বিদ্রোহ না করার শর্ত ছিল স্পষ্ট।
যুল খালাসা ছিল ইয়েমেন অঞ্চলের এক বিখ্যাত মূর্তিপূজার মন্দির; আলি বা জারির ইবন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে এটি আক্রমণ করে ধ্বংস করা হয়। মন্দির ভেঙে ফেলা এবং স্থানীয়দের ইসলাম গ্রহণ বা অন্তত মূর্তিপূজা ত্যাগে বাধ্য করার ঘটনা আরবের ধর্মীয় বহুত্ববাদকে শেষ করে দেয়।
নবী মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায়ই উসামা ইবন যায়েদের অধীনে বাইজেন্টাইন সীমান্তের দিকে একটি বড় বাহিনী পাঠানোর নির্দেশ দেন। অনেক সাহাবি কমবয়সি উসামার নেতৃত্ব নিয়ে আপত্তি করলেও, নবী তাকে কমান্ডার হিসেবে স্থির রাখেন; নবীর অসুস্থতা ও মৃত্যুর কারণে এই অভিযান কিছুটা বিলম্বিত হয়, পরে আবু বকরের খিলাফতের শুরুতে বাস্তবায়িত হয়।
নবুয়তের শেষ দিকে মুহাম্মদ আলি ইবন আবি তালিবকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন, সেখানে স্থানীয় গোত্রদের ইসলাম গ্রহণ, খাজনা ও আইনি বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে। হাদিসে আছে, কিছু লোক আলির বিচার–পদ্ধতি ও গনিমত বণ্টন নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল, যা মদিনায় ফিরে এসে নবীর কাছে অভিযোগ আকারে পৌঁছায়। এই সময়ে গনিমতের মাল বণ্টনের আগেই আলী একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা মেয়েকে গনিমতের মাল থেকে নিজে পছন্দ করে নিয়ে সহবাস করে [14]। ইসলামের বিধান অনুসারে খলিফার বণ্টনের পুর্বে কেউ গনিমতের মাল ভোগ করতে পারে না। মুহাম্মদ পরে আলির পক্ষে বলেন যে, আলি যেহেতু তার পরিবার, তাই ঐটা খুমুসের অংশ থেকেই আলি নিয়েছে বলে গণ্য হবে। এখানে নবী মুহাম্মদ ইসলামের প্রচলিত কঠিন বিধান আলীর জন্য পরিবর্তন করে ফেলেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, আলীকে পরিবার হিসেবে ঘোষণা দিলেও, রাজনৈতিকভাবে আলিকে সামনে রেখে কিন্তু উত্তরাধিকার প্রশ্নটি লিখিতভাবে কখনও স্পষ্ট করেননি। এই দ্বৈততা পরে সুন্নি–শিয়া বিরোধের অন্যতম ভিত্তিতে পরিণত হয়।
জীবনের শেষ হজে মুহাম্মদ বিপুল জনসমাগমের সামনে খুৎবা দেন, যেখানে শরিয়াহ–বিধান, রক্ত ও সম্পদের অক্ষততা, সুদ নিষিদ্ধকরণ এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয়গুলো পুনর্ব্যক্ত হয়। মুসলিম ঐতিহ্যে এটিকে “ইসলামী সামাজিক–রাজনৈতিক ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ ঘোষণা” বলা হলেও, যুক্তিবাদীদের চোখে এটি একটি সুসংগঠিত ক্ষমতা–ব্যবস্থাকে ধর্মীয় ভাষায় স্থায়ী করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা হিসেবে বোঝা যায়।
বিদায় হজ শেষে মদিনায় ফেরার পথে জুহফা এলাকার কাছে গাদীর খুমে একটি বড় বিরতিতে মুহাম্মদ
জনসমাগম ডেকে আলি ইবন আবি তালিব সম্পর্কে বিখ্যাত ঘোষণাটি দেন—
“যার মওলা আমি, আলি তার মওলা”। প্রচলিত বর্ণনায় আরও এসেছে—তিনি নাকি বলেছিলেন,
“হে আল্লাহ, যিনি আলিকে ভালোবাসে তাকে তুমি ভালোবাসো, যিনি আলির বিরোধিতা করে তাকে তুমি বিরোধিতা করো।”
শিয়া ইতিহাসে এই ঘোষণাকে স্পষ্ট রাজনৈতিক উত্তরসূরি–মনোনয়ন বা “নাস্” হিসেবে গণ্য করা হয়—অর্থাৎ আলিকে
ভবিষ্যৎ নেতা ও ইমাম হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে; গাদীর খুম তাই তাদের মতে ইসলামী ইতিহাসের কেন্দ্রীয় সংযোগবিন্দু।
কিন্তু সুন্নি ইতিহাসে ঘটনাটি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়—এটি নাকি ছিল কেবল আলির মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে
একটি সাময়িক বার্তা; নেতৃত্ব বা খিলাফতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সমস্যাটি হলো,
“মওলা” শব্দটির বহুমাত্রিক অর্থ—বন্ধু, অভিভাবক, সাথী, নেতা—যা পরবর্তীতে দ্ব্যর্থতার কারণে
দুই ভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা তৈরিতে সহায়ক হয়।
সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ঘটনাটি বিদায় হজের পরপরই ঘটেছে—অর্থাৎ মুহাম্মদ বৃদ্ধ, অসুস্থ,
এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি মুসলিম সমাজে তীব্র রাজনৈতিক টেনশন সৃষ্টি করছিল। ঠিক সেই সময়ে আলিকে নির্বাচন করে
“মওলা” শব্দের মাধ্যমে অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া কি উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক সংকেত ছিল? নাকি এটি শুধু আবেগী প্রশংসা?
উভয়ই সম্ভব, কিন্তু এর পর মুহাম্মদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের—বিশেষত উমর, আবু বকর, উসমান—
কারো কাছেই এটি স্পষ্ট উত্তরসূরি ঘোষণার মতো প্রতীয়মান হয়নি।
কারণ, নবীর মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে সাকিফায় যে তীব্র ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়, সেখানে
গাদীর খুমের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না; আলিও তখন তার দাবি জোর দিয়ে উপস্থাপন করেননি।
ফলে সংশয়বাদীদের মতে,
যদি গাদীর খুম নবীর সরাসরি রাজনৈতিক মনোনয়ন হতো, তবে তার তাৎক্ষণিক এবং অস্বীকার–অযোগ্য প্রভাব
সাকিফার বিতর্কে স্পষ্ট দেখা যেত—যা বাস্তবে দেখা যায় না।
ঘটনা তাই ধর্মীয় আখ্যান বনাম বাস্তব রাজনৈতিক ইতিহাস—এই দুই ভিন্ন স্তরে দাঁড়িয়ে থাকে।
আখ্যান একে আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি ঘোষণার মতো তুলে ধরে; ইতিহাস দেখায় এটি ছিল এক দ্ব্যর্থক ঘোষণা,
যা পরবর্তীতে শক্তিশালী গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী পুনর্ব্যাখ্যা করেছে।
বিদায় হজের কিছুদিন পর থেকেই মুহাম্মদ জ্বর ও শারীরিক দুর্বলতায় ভুগতে শুরু করেন; তিনি প্রথমে বিভিন্ন স্ত্রীর ঘরে পর্যায়ক্রমে থাকছিলেন। পরে স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে তিনি আয়িশার ঘরে স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত সেখানেই থাকেন—এই সিদ্ধান্তকে প্রায়ই “আয়িশার বিশেষ মর্যাদা” হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এখানে রাজনৈতিক দিকও আছে, কারণ আয়িশা ছিলেন আবু বকরের মেয়ে, যার ঘরেই শেষ দিন কাটানো পরবর্তী উত্তরাধিকারের ক্ষমতার ভারসাম্যকেও প্রভাবিত করে।
সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, অসুস্থ অবস্থায় মুহাম্মদ কোনো ওষুধ খেতে রাজি ছিলেন না, তবু আয়িশা ও অন্যান্য আত্মীয়রা জোর করে তার মুখে ওষুধ ঢেলে দেন। যখন তিনি কিছুটা সজাগ হন, তখন নাকি তিনি রাগ করে বলেন—আমার সামনে আর কেউ অসুস্থ হলে তাকেও এমন জোর করে ওষুধ খাওয়ানো হবে—এবং এই আচরণের জন্য তাদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করেন। এই ঘটনা দেখায়, শেষ সময়ে পরিবার–পরিবেশেও দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাস ছিল, যেখানে “ওহীর উৎস” বলে বিশ্বাস করা মানুষটিই নিজের চিকিৎসা সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। [15] [16]
সহিহ বুখারি ও অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে এক বৃহস্পতিবার মুহাম্মদ লিখে কিছু নির্দেশ দিতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর উম্মাহ “কখনও পথভ্রষ্ট না হয়”। উপস্থিত সাহাবিরা কলম–কাগজ আনার প্রসঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে; উমর বলেন, “নবীর অবস্থা গুরুতর, কিতাবুল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট”, ফলে কেউ কেউ তাকে সমর্থন, কেউ বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত গোলমাল ও কোলাহলের কারণে কোনো লিখিত নস–বা স্পষ্ট রাজনৈতিক উইল–না দিয়েই কথাটা বন্ধ হয়ে যায়; আহলে হাদিস এটাকে “রজিয়াতুল খামিস” বলে। যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে, এখানে স্পষ্ট দেখা যায় খিলাফতের প্রশ্নে উঁচু সাহাবীদের মধ্যেও স্বার্থ–সংঘাত ছিল এবং তা সরাসরি নবীর কথাকেই ছাপিয়ে গেছে। [17] [18]
বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর আগে মুহাম্মদের শেষ দিককার নির্দেশের মধ্যে ছিল—“আরব উপদ্বীপে দুইটি ধর্ম একসাথে থাকবে না”; অর্থাৎ ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের বের করে দিতে হবে বা বিশেষ শর্তে আনতে হবে। পরবর্তীতে খলিফারা এই নির্দেশের দোহাই দিয়ে হিজাজ অঞ্চল থেকে ইহুদি–খ্রিস্টানদের ধীরে ধীরে উচ্ছেদ বা স্থানান্তরে বাধ্য করে, কিছুকে শুধু করদ–প্রজার মর্যাদায় থাকতে দেয়। “রহমাতুল্লিল আলামিন” ধারণার বিপরীতে এই নিষেধাজ্ঞা স্পষ্টভাবেই ধর্মীয় বহুত্ববাদবিরোধী এবং আরব ভূখণ্ডকে এক–ধর্মীয় গেটোতে রূপান্তরের ঘোষণা হিসেবে কাজ করেছে।
হাদিসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর দিন মুহাম্মদের ওপর অনেকগুলো আয়াত নাজিল হয়। যেহেতু সেগুলো ছিল একদম শেষ মূহুর্তের আয়াত, তাই সেগুলো যে গুরুত্বপুর্ণ আয়াত ছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই শেষদিনের আয়াতগুলো সবই হারিয়ে গেছে। কারণ শেষদিনের আয়াত কেউই মুখস্ত করেনি, লিখে রাখেনি। এরপরেই তারা মুহাম্মদের অসুস্থতা, মৃত্যু আর খলিফা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। [19] [20]
বেশ কয়েকদিন জ্বর ও দুর্বলতার পর মুহাম্মদ আয়িশার কোলে/বুকে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেন বলে প্রচলিত বর্ণনা আছে; সেই সময় ঘরে আবু বকর, উমর সহ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আসা–যাওয়া করছিলেন। সহিহ হাদিসে এসেছে, তিনি মৃত্যুর আগে বারবার নামাজ ও দাস–গণকে নিয়ে সতর্ক করার কথা বলেছেন; আবার কিছু বর্ণনায় “আমার কবরকে ইদের জায়গা বানিও না” বা “আমাকে খ্রিস্টানদের ঈসার মতো পূজা করো না” ধরনের কথাও এসেছে। তবে কোনো বিশ্বস্ত সনদে উত্তরসূরি নির্ধারণের স্পষ্ট লিখিত বা মৌখিক একক নির্দেশ নেই—যা পরবর্তী রাজনীতিতে বড় ফাঁক তৈরি করে।
সীরাত ও ইতিহাস–গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মৃত্যুর পর নবীর লাশ তাৎক্ষণিকভাবে দাফন না করে একাধিক দিন ঘরে রাখা হয়; এ সময় বাইরে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সাকিফা বানী সাঈদায় তীব্র তর্ক–বিতর্ক চলে—কারা খলিফা হবে। আনসাররা নিজেদের নেতা চায়, মুহাজিররা কুরাইশ নেতৃত্বের দাবি তোলে; দ্রুত রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত আবু বকরকে খলিফা ঘোষণা করা হয়, অনেক সাহাবি তখন উপস্থিতই ছিলেন না। দাফন–বিলম্ব ও ক্ষমতার জন্য হুড়োহুড়ি দেখায় যে নবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই “উম্মাহ” ধারণা ভেঙে বাস্তব গোত্র–রাজনীতি ও ক্ষমতার লড়াই সামনে চলে আসে।
কিছু হাদিস–সূত্রে এসেছে, নবীর মৃত্যুর পর আয়িশার ঘরে রাখা কোরআনের কিছু লেখা ছিল, যার মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ককে দুধ পান করানোর বিধান ও পাথর নিক্ষেপে ব্যভিচারীর সাজা–সংক্রান্ত একটি আয়াতও ছিল—সেগুলো নাকি একটি ছাগল খেয়ে ফেলে। ইসলামী পণ্ডিতদের অনেকে এ ঘটনাকে দুর্বল বা ব্যাখ্যামূলক বলে পাশ কাটাতে চাইলেও, টেক্সট–সমালোচনায় এটি কোরআনের সংরক্ষণ ও পাঠ–ইতিহাস নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে। একদিকে বলা হয় “কোরআন লওহে মাহফূজে অক্ষত”, অন্যদিকে বাস্তবে দেখা যায় কাগজে লেখা কিছু অংশ ছাগল খেয়ে ফেলায় পরবর্তী মুসহাফে সেগুলো আর নেই—দুই দাবির মধ্যে স্পষ্ট টেনশন তৈরি হয়।
মুহাম্মদের যুদ্ধ ও সামরিক আক্রমণ – সারসংক্ষিপ্ত টেবিল
সারিয়া হলো যেখানে মুহাম্মদ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না,
আর গাজওয়া হলো যেখানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন
| № | তারিখ (খ্রিঃ / হিজরি) | যুদ্ধ / অভিযান | প্রতিপক্ষ / স্থান | প্রকৃতি | সংক্ষিপ্ত মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৬২৩–৬২৪ খ্রিঃ ১–২ হিজরি |
প্রাথমিক সশস্ত্র অভিযান (সারিয়া) | কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা মদিনা–শাম রুট |
আক্রমণাত্মক | হিজরতের পরপরই মক্কার কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার ওপর নজরদারি ও আক্রমণের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক ছোট ছোট বাহিনী পাঠানো হয়। মূল লক্ষ্য ছিল কুরাইশের অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বল করা এবং কাফেলা লুটের মাধ্যমে সামরিক ও আর্থিক তহবিল গঠন। [21] [22] |
| ২ | মার্চ ৬২৩ খ্রিঃ ১ হিজরি |
সিফুল-বাহর অভিযান | কুরাইশ কাফেলা লোহিত সাগর উপকূল |
আক্রমণাত্মক | হামজা ইবন আবদুল-মুত্তালিব প্রায় ৩০ জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে লোহিত সাগর উপকূলে কুরাইশ কাফেলা বাধা দিতে অগ্রসর হন। সরাসরি যুদ্ধ না ঘটলেও এটি ছিল স্পষ্ট শক্তি–প্রদর্শন এবং বাণিজ্য রুটের ওপর কৌশলগত হুমকি সৃষ্টি। [23] |
| ৩ | এপ্রিল ৬২৩ খ্রিঃ ১ হিজরি |
উবাইদা ইবন আল-হারিসের অভিযান | কুরাইশ কাফেলা বাণিজ্য–রুট |
আক্রমণাত্মক | উবাইদা ইবন আল-হারিস প্রায় ৬০–৮০ জনের দল নিয়ে কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার দিকে অগ্রসর হন; দুই পক্ষের মধ্যে তীর নিক্ষেপ হয়, যা মদিনা–মক্কা অর্থনৈতিক সংঘাতের প্রথম দিকের সশস্ত্র মুখোমুখি হওয়া হিসেবে বিবেচিত। পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ না হলেও ভবিষ্যৎ কাফেলা আক্রমণের পথ সুগম হয়। [24] |
| ৪ | মে ৬২৩ খ্রিঃ ১ হিজরি |
সারিয়াতুল খারার | আল-খারার অঞ্চল | আক্রমণাত্মক | সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ছোট একটি দল খারার অঞ্চলে কুরাইশ কাফেলা আক্রমণের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। মুহাম্মদ নিজে এই অভিযানে অংশ নেননি; এটি ছিল স্পষ্টভাবে একটি সারিয়া। কাফেলা আগেই সরে যাওয়ায় কোনো সরাসরি সংঘর্ষ ঘটেনি, তবে কাফেলা–রুট পর্যবেক্ষণ ও চাপ সৃষ্টির কৌশল অব্যাহত থাকে। [25] |
| ৫ | আগস্ট ৬২৩ খ্রিঃ ১ হিজরি |
ওয়াদ্দান / আল-আবওয়া অভিযান | ওয়াদ্দান অঞ্চল বানু দামরা গোত্র |
আক্রমণাত্মক | প্রথমবারের মতো মুহাম্মদ স্বয়ং বাহিনী নিয়ে ওয়াদ্দান অঞ্চলে অগ্রসর হন কুরাইশ কাফেলা লক্ষ্য করে। কাফেলা না পাওয়ায় বানু দামরা গোত্রের সাথে অনাক্রমণ–চুক্তি করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে মদিনা বাহিনী এ রুট দিয়ে নিরাপদে সামরিক অগ্রযাত্রা চালাতে পারে। [26] |
| ৬ | সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রিঃ ২ হিজরি |
বুয়াত অভিযান | বুয়াত অঞ্চল কুরাইশ কাফেলা |
আক্রমণাত্মক | বড় একটি বাহিনী নিয়ে বুয়াত অঞ্চলে কুরাইশ কাফেলার পথ রোধের প্রচেষ্টা চালান মুহাম্মদ। যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি, তবে মক্কায় স্পষ্ট বার্তা যায় যে, তাদের বাণিজ্য–রুট এখন সামরিকভাবে হুমকির মুখে। [27] |
| ৭ | সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রিঃ ২ হিজরি |
বদরের প্রথম অভিযান (বদর–সাফওয়ান) | বদর এলাকা সাফওয়ানের কাফেলা |
আক্রমণাত্মক | কুরাইশ নেতা সাফওয়ান ইবন উমাইয়ার কাফেলাকে লক্ষ্য করে বদর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। কাফেলা সরে যেতে সক্ষম হলেও এই অভিযান মক্কা–মদিনা উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে এবং পরবর্তী বড় বদর যুদ্ধের মঞ্চ তৈরি করে। [28] |
| ৮ | ডিসেম্বর ৬২৩ খ্রিঃ ২ হিজরি |
জুল আল-উশাইরা অভিযান | দুল উশাইরা অঞ্চল বানু মুদলিজ |
আক্রমণাত্মক | পশ্চিম দিকের কুরাইশ বাণিজ্য–রুট সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে দুল উশাইরা এলাকায় অভিযানে বের হন মুহাম্মদ। কাফেলা বাধা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও পাশের বানু মুদলিজ গোত্রের সাথে চুক্তি করে সেখানে মুসলিম বাহিনীর প্রভাব বিস্তারের ভিত্তি তৈরি করা হয়। [29] |
| ৯ | জানুয়ারি ৬২৪ খ্রিঃ ২ হিজরি |
নাখলা হামলা | নাখলা উপত্যকা কুরাইশ কাফেলা |
আক্রমণাত্মক | আবদুল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে পাঠানো ছোট দল পবিত্র মাসে নাখলা উপত্যকায় কুরাইশ কাফেলার ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে একজনকে হত্যা, কয়েকজনকে বন্দী এবং মাল–লুট করে মদিনায় নিয়ে আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোরআনের ২:২১৭ আয়াতে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, যেখানে একদিকে এ ধরনের যুদ্ধকে গুরুতর অপরাধ বলা হয়, অন্যদিকে কুরাইশের ‘বহু গুরুতর অপরাধ’কে যুক্তি হিসেবে টেনে এনে এই হামলার বৈধতার পক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। [30] [31] |
| ১০ | ১৩ মার্চ ৬২৪ খ্রিঃ ২ হিজরি |
বদর যুদ্ধ | বদর কুরাইশ বাহিনী |
আক্রমণাত্মক | কুরাইশের সিরিয়া–গামী বিশাল বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর উদ্দেশ্যে মদিনা বাহিনী বের হয়। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের পূর্ণাঙ্গ সামরিক সংঘর্ষে রূপ নেয়, যা ছিল অর্থনৈতিক যুদ্ধ থেকে সরাসরি উন্মুক্ত যুদ্ধে উত্তরণ এবং প্রাথমিক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য একটি মোড় ঘোরানো সামরিক বিজয়। [32] [33] |
| ১১ | ৬২৪ খ্রিঃ ২ হিজরি |
বনু কায়নুকা অবরোধ | মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকা | আক্রমণাত্মক | বদর যুদ্ধের অল্প কিছু পরেই মদিনার ইহুদি লৌহকার–গোত্র বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে “চুক্তিভঙ্গ” ও বাজার–ঘটনার অজুহাতে সামরিক অবরোধ আরোপ করা হয়। প্রায় পনেরো দিনের অবরোধের পর গোত্রটি আত্মসমর্পণ করলে, প্রথমে পুরুষদের গণহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়; কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর জোরালো হস্তক্ষেপের ফলে হত্যাযজ্ঞ থেকে সরে এসে পুরো গোত্রকে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মদিনা থেকে নির্বাসিত করা হয়। এতে মদিনার অর্থনৈতিক সম্পদ মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং ইহুদি উপস্থিতি ধীরে ধীরে নির্মূলের প্রক্রিয়া শুরু হয়। [34] [35] |
| ১২ | মে/জুন ৬২৪ খ্রিঃ ২ হিজরি |
সাওয়িক হানা | আবু সুফিয়ানের হানা মদিনা–সংলগ্ন অঞ্চল |
প্রতিরক্ষামূলক | বদরের পর কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান কয়েকশ’ সশস্ত্র লোক নিয়ে মদিনার আশেপাশে আকস্মিক হানা দিয়ে কিছু খেজুরবাগান পুড়িয়ে দেয় ও দু’জনকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। মুসলিমরা পিছু ধাওয়া করলেও মূল বাহিনীকে ধরতে ব্যর্থ হয়; পথে তাড়া খেয়ে আবু সুফিয়ানের ফেলে যাওয়া শস্যভর্তি বোঝা (সাওয়িক) লুট হয়, এখান থেকে অভিযানের নামকরণ। চরিত্রগতভাবে এটি কুরাইশের প্রতিশোধমূলক সীমিত আক্রমণ, মুসলিমদের ভূমিকা মূলত প্রতিরক্ষামূলক ধাওয়া–অভিযান। [36] [37] |
| ১৩ | সেপ্টেম্বর ৬২৪ খ্রিঃ ৩ হিজরি |
জু আম্মার অভিযান | জু আম্মার গাতাফান গোত্র |
আক্রমণাত্মক | গাতাফান গোত্রকে সীমান্তে শক্তি–প্রদর্শনের মাধ্যমে আগেভাগেই ভয় দেখানো এবং সম্ভাব্য জোট গঠনের আগেই তাদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে জু আম্মার অঞ্চলে অভিযান পরিচালিত হয়। ইসলামী সূত্রে একে প্রায়ই “প্রতিরক্ষা–উদ্দেশ্য” বলে বর্ণনা করা হলেও, বাস্তবে এটি ছিল স্পষ্টভাবে আগ্রাসী সীমান্ত–নিয়ন্ত্রণ এবং আশপাশের গোত্রকে আনুগত্যে বাধ্য করার কৌশল। [38] |
| ১৪ | নভেম্বর ৬২৪ খ্রিঃ ৩ হিজরি |
আল-কারাদা হামলা | আল-কারাদা কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা |
আক্রমণাত্মক | জায়েদ ইবন হারিসাহর নেতৃত্বে পাঠানো বহর আল-কারাদা অঞ্চলে কুরাইশের এক বাণিজ্য কাফেলার ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে উট, পণ্য ও সম্পদ লুট করে নিয়ে আসে। গনিমত হিসেবে এসব সম্পদ মদিনায় ভাগ করে দেওয়া হয়; যুদ্ধ–লব্ধ সম্পদের ওপর নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো কীভাবে গড়ে উঠছিল, এই অভিযান তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। [39] [40] |
| ১৫ | ২৩ মার্চ ৬২৫ খ্রিঃ ৩ হিজরি |
উহুদ যুদ্ধ | উহুদের প্রান্তর কুরাইশ সেনাবাহিনী |
প্রতিরক্ষামূলক | বদরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কুরাইশরা পূর্ণ সেনাবাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। প্রথমে শহরের ভেতরে থেকে প্রতিরক্ষা নেয়া হবে কি না তা নিয়ে মদিনার ভেতরে বিতর্ক হয়; শেষে মুসলিমদের একটি অংশ শহর থেকে বেরিয়ে উহুদের পাদদেশে খোলা ময়দানে মুখোমুখি যুদ্ধ বেছে নেয়। প্রাথমিক সাফল্যের পর পাহাড়ি তীরন্দাজ টিমের অবস্থান ভেঙে পড়ায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং মুসলিম পক্ষ কৌশলগত পরাজয়ের মুখে পড়ে। সামগ্রিকভাবে এটি ছিল কুরাইশের নেওয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ, তবে ট্যাকটিক্যাল স্তরে মদিনা বাহিনীই আক্রমণাত্মক অবস্থান বেছে নিয়েছিল। [41] [42] |
| ১৬ | ৬২৫–৬২৬ খ্রিঃ ৪ হিজরি |
বনু নাদির অবরোধ ও নির্বাসন | মদিনার ইহুদি গোত্র বনু নাদির | আক্রমণাত্মক | এক ঘটনায় “খুনের রক্তপণ (দিয়া)” নিয়ে আলোচনা করার অজুহাতে মুহাম্মদ বনু নাদিরের বসতিতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। এরপর গোত্রটির দুর্গঘেরা বসতি সামরিকভাবে অবরুদ্ধ করা হয়, আশেপাশের খেজুরবাগান কেটে–পুড়িয়ে দেওয়া হয় (যা পরবর্তীতে কোরআন ৫৯:২–এ উল্লেখিত)। শেষ পর্যন্ত গোত্রটিকে জোরপূর্বক মদিনা থেকে নির্বাসিত করা হয় এবং তাদের জমি–বাড়ি, খেজুরবাগানসহ বিপুল সম্পদ মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর অধীনে ‘ফাই’ হিসেবে চলে যায়। “বিশ্বাসঘাতকতা” অভিযোগকে ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ গোত্রের ওপর এই ধরনের সামষ্টিক শাস্তি আরোপকে ক্লাসিক্যাল ইসলামী ইতিহাসেও কঠোর সামরিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যায়। [43] [44] |
| ১৭ | ৬২৬ খ্রিঃ ৪–৫ হিজরি |
দাতুর-রিকা অভিযান | গাতাফানসহ মরু–গোত্র | আক্রমণাত্মক | গাতাফান ও আশপাশের মরু–গোত্রগুলোকে সম্ভাব্য জোট গঠনের আগেই সামরিকভাবে চাপে রাখার জন্য দাতুর-রিকা অভিযানে বের হওয়া হয়। বড় ধরনের সংঘর্ষ না হলেও এই দীর্ঘ অভিযান দূর–দূরান্তের গোত্রকে মদিনা–কেন্দ্রিক নতুন শক্তির সামরিক সামর্থ্য ও প্রভাব সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টির ভূমিকা পালন করে, যা প্রকৃত অর্থে “প্রি-এম্পটিভ” আগ্রাসী কৌশল। [45] |
| ১৮ | ৬২৬ খ্রিঃ ৫ হিজরি |
দুমাতুল-জান্দাল অভিযান | উত্তর আরব বাণিজ্য ও গোত্রসমূহ |
আক্রমণাত্মক | উত্তর আরবের কৌশলগত বাণিজ্য–কেন্দ্র দুমাতুল-জান্দাল পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সামরিক বহর নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে সেখানে সক্রিয় গোত্র ও কাফেলাদের ওপর রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা যায়। অভিযানের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয় যে মদিনা–কেন্দ্রিক নতুন শক্তি শুধু স্থানীয় নয়, দূরবর্তী বাণিজ্য–রুটেও নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তারে আগ্রহী ও সক্ষম। [46] [47] |
| ১৯ | ৬২৭ খ্রিঃ ৫ হিজরি |
খন্দক যুদ্ধ (আহযাব) | মদিনা কুরাইশ ও মিত্র জোট |
প্রতিরক্ষামূলক | কুরাইশ, গাতাফান ও আরও কয়েকটি গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ জোট–বাহিনী মদিনা অবরোধের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলে মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেওয়া হয়। দীর্ঘ অবরোধের পর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জোটের ভাঙনের ফলে আক্রমণকারী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। সরাসরি বড় আকারের খোলা যুদ্ধ খুব বেশি না হলেও, কৌশলগত দৃষ্টিতে এটি ছিল মদিনার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিরক্ষামূলক সফলতা। [48] [49] |
| ২০ | মে ৬২৭ খ্রিঃ ৫ হিজরি |
বনু কুরাইযা গণহত্যা | মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযা | আক্রমণাত্মক |
খন্দক যুদ্ধের সময় “চুক্তিভঙ্গ” ও “বিশ্বাসঘাতকতা”র অভিযোগ তুলে মদিনার ইহুদি
গোত্র বনু কুরাইযাকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলা হয়। আত্মসমর্পণের পর সিদ্ধান্ত হয়,
গোত্রটির প্রাপ্তবয়স্ক সব পুরুষকে বেছে–বেছে হত্যা করা হবে এবং নারী–শিশুদেরকে
দাস ও উপপত্নী হিসেবে বণ্টন বা বাজারে বিক্রি করা হবে। ক্লাসিক্যাল সীরাত–ইতিহাসে
উল্লেখ আছে, এই অভিযানে আনুমানিক ছয়শ’ থেকে নয়শ’ পর্যন্ত পুরুষকে গর্ত খুঁড়ে
সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে তাকরে–তাকরে শিরশ্ছেদ করা হয়; পরে নারীদের ও শিশুদের মধ্যে
অনেককে দাসী ও গৃহদাসে পরিণত করা হয়, বাকি অংশকে বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে
দেওয়া হয়।
“বিশ্বাসঘাতকতা”র অভিযোগ প্রমাণিত হোক বা না হোক, একটি গোত্রের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে আলাদা বিচার ছাড়া একই ফতোয়ায় হত্যা করা এবং নারী–শিশুদের দাসে পরিণত করা আধুনিক নৈতিক মানদণ্ডে নিখাদ সামষ্টিক শাস্তি (collective punishment) এবং কার্যত একটি জাতিগত/ধর্মীয় গণহত্যা (genocide) হিসেবে বিবেচিত হবে। এখানে ব্যক্তিগত অপরাধ–দায় বিবেচনা না করে গোত্র–পরিচয়কে অপরাধের একমাত্র মানদণ্ড করা হয়েছে—যা ন্যূনতম ন্যায়বিচার–নীতির সাথেও মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক। [50] [51] [52] |
| ২১ | আগস্ট / সেপ্টেম্বর ৬২৭ খ্রিঃ ৬ হিজরি |
বনু সালাবার প্রথম হামলা | বনু সালাবা গোত্রাঞ্চল | আক্রমণাত্মক | মরু অঞ্চলের বনু সালাবা গোত্রের ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করা হয়, কিছু মানুষ নিহত হয় এবং পশু ও সম্পদ দখল করা হয়। ইসলামী সূত্রে একে প্রায়ই “শত্রু হুমকি মোকাবিলা” হিসেবে দেখানো হলেও প্রকৃত বাস্তবতায় এটি ছিল গোত্রটিকে আগেভাগে দুর্বল ও নিরস্ত্র করে ফেলার সামরিক আগ্রাসন। [53] |
| ২২ | আগস্ট / সেপ্টেম্বর ৬২৭ খ্রিঃ ৬ হিজরি |
বনু সালাবার দ্বিতীয় হামলা | বনু সালাবা গোত্র | আক্রমণাত্মক | প্রথম অভিযানের পরও “হুমকি অব্যাহত” থাকার অজুহাতে বনু সালাবার ওপর দ্বিতীয়বার সামরিক দল পাঠানো হয়। লক্ষ্য ছিল শুধু তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা নয়, বরং গোত্রটির রাজনৈতিক ও সামরিক কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে দিয়ে তাদেরকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অনুগত ‘প্রান্তিক প্রজা’তে রূপান্তর করা। এই ধরনের পুনরাবৃত্ত অভিযান প্রমাণ করে যে, এগুলো কেবল ‘ডিফেন্সিভ স্কারমিশ’ ছিল না, বরং দীর্ঘমেয়াদি সাম্রাজ্য–বিস্তারের অংশ। [54] |
| ২৩ | ৬২৭ খ্রিঃ ৬ হিজরি |
জায়েদ ইবন হারিসার অভিযান (আল-ইস) | আল-ইস অঞ্চল | আক্রমণাত্মক | আল-ইস অঞ্চলে পরিচালিত এই অভিযানে প্রতিপক্ষের পশুপাল ও সম্পদ দখল করা হয়। পশুপাল জব্দ ও কাফেলা লুট করে প্রতিপক্ষের অর্থনীতি দুর্বল করা এবং সেই সম্পদ মদিনা–কেন্দ্রিক শাসকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত করার কৌশল এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই ধরনের অভিযান প্রমাণ করে যে যুদ্ধ শুধু ‘ধর্মীয় প্রতিরক্ষা’ নয়, বরং অর্থনৈতিক লুট ও সম্পদ পুনর্বণ্টনেরও কার্যকর হাতিয়ার ছিল। [55] |
| ২৪ | ডিসেম্বর ৬২৭ খ্রিঃ ৬ হিজরি |
জায়েদ ইবন হারিসার অভিযান (ওয়াদি আল-কুরা) | ওয়াদি আল-কুরা কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল |
আক্রমণাত্মক | ওয়াদি আল-কুরা ছিল খেজুরবাগান ও কৃষি–উৎপাদনে সমৃদ্ধ এলাকা। এই অভিযানে স্থানীয় জনবসতির সঙ্গে সংঘর্ষে কিছু মানুষ নিহত হয় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ দখল করা হয়। খাইবার ও ফিদাক আক্রমণের আগেই এই অঞ্চলে সামরিক চাপ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা হয়—অর্থাৎ পুরো উত্তরাঞ্চলকে ধীরে ধীরে মদিনা–কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অনুগত কর–অঞ্চলে পরিণত করা। [56] [57] |
| ২৫ | আগস্ট ৬২৭ খ্রিঃ ৬ হিজরি |
জু কারাদ অভিযান | জু কারাদ উট–লুটের প্রতিশোধ |
প্রতিরক্ষামূলক | মুসলিম উট ও সম্পদ লুটের প্রতিশোধ নিতে শত্রু দলকে ধাওয়া করে জু কারাদ অঞ্চলে আক্রমণ চালানো হয়; এখানেও শেষ পর্যন্ত তাদের কিছু পশুপাল ও সম্পদ দখল করা হয়। ইসলামী বর্ণনায় এটিকে “প্রতিরক্ষামূলক” প্রতিশোধ অভিযান বলা হলেও, ফলাফলের দিক থেকে এটি আরেকটি লুট–সমৃদ্ধ পাল্টা–আক্রমণ—যেখানে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের নামে নতুন করে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় শাসক পক্ষের হাতে। [58] |
| ২৬ | ৬২৮ খ্রিঃ ৭ হিজরি |
খাইবার আক্রমণ | খাইবারের ইহুদি দুর্গসমূহ | আক্রমণাত্মক | মদিনা থেকে নির্বাসিত বনু নাদিরসহ ইহুদি গোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল এবং কৃষি–সমৃদ্ধ দুর্গশহর খাইবারে মুসলিম বাহিনী ভোরবেলা আকস্মিক হানা দেয়। একের পর এক দুর্গ দখলের মধ্যে দিয়ে বহু মানুষ নিহত হয়, পুরুষদের একাংশকে হত্যা করা হয়, নারী–শিশুদের দাসী ও উপপত্নী হিসেবে বণ্টন করা হয় এবং প্রচুর সম্পদ গনিমত হিসেবে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে খাইবারের জমি ও বাগান স্থানীয় ইহুদিদের মাধ্যমে চাষ করিয়ে “অর্ধেক ফলন” কর হিসেবে আদায় করা হয়— অর্থাৎ খাইবার একটি স্থায়ী কর–সংগ্রহের উপনিবেশে পরিণত হয়, যেখানে ইহুদিরা কার্যত পরাজিত প্রজা ও করদাসে রূপান্তরিত হয়। ক্লাসিক্যাল সূত্র অনুযায়ী এখানেই সাফিয়া বিনতে হুয়াইয়ের মতো বন্দী নারীকে যুদ্ধ–লব্ধ দাসী থেকে “বিবাহ” শর্তে মুক্ত করার ঘটনাও ঘটে—যা বিজিত নারীর ওপর বিজয়ীর যৌন ও সামাজিক ক্ষমতার অনন্য উদাহরণ। [59] [60] |
| ২৭ | ৬২৮–৬২৯ খ্রিঃ ৭ হিজরি |
ফিদাক, ওয়াদি আল-কুরা সহ আশপাশের অভিযান | ইহুদি ও অন্যান্য গোত্র | আক্রমণাত্মক | খাইবার দখলের পর আশপাশের ফিদাক, ওয়াদি আল-কুরা এবং অন্যান্য কৃষি–সমৃদ্ধ ইহুদি ও গোত্রীয় বসতিগুলোর ওপর সামরিক চাপ বাড়ানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে “যুদ্ধ ছাড়া” চুক্তি স্বাক্ষর হলেও, বাস্তবে এগুলো ছিল পরাজয়–স্বীকারোক্তিমূলক কর–চুক্তি, যেখানে জমি–বাগানের একটি বড় অংশের উৎপাদন স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই ধাপে উত্তর আরবের উল্লেখযোগ্য কৃষি–সম্পদ ও কর–রাজস্ব কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে, আর স্থানীয় জনগোষ্ঠী পরিণত হয় দ্বিতীয় শ্রেণির করদাস–প্রজায়। [61] [62] |
| ২৮ | ৬২৯ খ্রিঃ ৮ হিজরি |
মু’তা যুদ্ধ | মু’তা বাইজেন্টাইন সীমান্ত |
আক্রমণাত্মক | বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ঘেঁষা আরব–খ্রিস্টান অঞ্চলের দিকে প্রথম বড় আকারের বাহিনী পাঠানো হয় মু’তা যুদ্ধের মাধ্যমে। “দূতের হত্যার প্রতিশোধ”কে অজুহাত হিসেবে দেখানো হলেও, বাস্তবে এটি ছিল রোমান প্রভাবাধীন সীমান্ত অঞ্চলে মুসলিম সামরিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ক্লাসিক্যাল সূত্র অনুযায়ী, এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী তীব্র ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পিছু হটে; অর্থাৎ সাম্রাজ্য–বিস্তারের প্রথম বড় প্রচেষ্টা এখানে সামরিক সাফল্যের বদলে কৌশলগত পরীক্ষামূলক ধাক্কাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। [63] [64] |
| ২৯ | জানুয়ারি ৬৩০ খ্রিঃ ৮ হিজরি |
ফাতহে মক্কা | মক্কা নগরী কুরাইশ |
আক্রমণাত্মক | হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গের অজুহাতে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি সৈন্য নিয়ে মুহাম্মদ মক্কা নগরী ঘেরাও করেন। ন্যূনতম সংঘর্ষে শহর দখল হয়ে গেলে কাবার ভেতরের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয় এবং কুরাইশের বহুদলীয় রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে একক কেন্দ্রীয় ইসলামী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনেককে “মাফ” দেওয়া হলেও, এ মাফ ছিল বিজিতদের প্রতি বিজয়ীর ক্ষমাশীলতার ভাষ্য—রাজনৈতিক বাস্তবতা ছিল স্পষ্ট: মক্কার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে মদিনা–কেন্দ্রিক নবী–রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। [65] [66] |
| ৩০ | ৬৩০ খ্রিঃ ৮ হিজরি |
হুনাইন যুদ্ধ | হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র | আক্রমণাত্মক | মক্কা দখলের অল্প সময় পরই আশেপাশের শক্তিশালী হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের বিরুদ্ধে বৃহৎ বাহিনী নিয়ে হুনাইনের উপত্যকায় অভিযানে বের হয় মুসলিম বাহিনী। প্রথমে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আর টেরেইন–জ্ঞানহীনতার কারণে মুসলিমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, পরে পুনর্গঠিত হয়ে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে। যুদ্ধের পর বিশাল পরিমাণ গনিমত, নারী ও শিশু বন্দী হয়; এগুলোর বড় অংশ পরবর্তীতে গনিমত হিসেবে বণ্টন করা হয়। হুনাইন–পরবর্তী গনিমত বিতরণ, বিশেষ করে নতুন মক্কী মুসলিম ও কুরাইশ অভিজাতদের মধ্যে “তালবিয়া” হিসেবে সম্পদ বিলি, রাজনৈতিক আনুগত্য কিনতে সম্পদ ব্যবহারের নগ্ন উদাহরণ। [67] [68] |
| ৩১ | ৬৩০ খ্রিঃ ৮ হিজরি |
তায়েফ অবরোধ | তায়েফ নগরী সাকিফ গোত্র |
আক্রমণাত্মক | হুনাইন যুদ্ধের পর পিছু হটা হাওয়াজিন–সাকিফ জোটের রাজনৈতিক কেন্দ্র তায়েফ নগরীকে সামরিকভাবে ঘিরে ফেলা হয়। দুর্গবেষ্টিত শহরটি দখল করতে মুসলিমরা মঞ্জনীক (catapult) ব্যবহার করে এবং আশেপাশের আঙুরবাগান ও খেজুরবাগান কাটার চেষ্টা চালায়। দীর্ঘ অবরোধের পরও শহর তাৎক্ষণিকভাবে পতিত না হলেও পরবর্তীতে ধারাবাহিক রাজনৈতিক চাপ, সামরিক শক্তির ভয় এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে সাকিফ ইসলাম গ্রহণ ও কর–চুক্তিতে রাজি হয়; অর্থাৎ তায়েফের আত্মসমর্পণ ছিল সরাসরি আস্থা নয়, বরং সামরিক অবরোধ–পরবর্তী বাস্তবতার কাছে নতি স্বীকার। [69] [70] |
| ৩২ | জুলাই/আগস্ট ৬৩০ – জুন/জুলাই ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ ৯–১০ হিজরি |
আলির অভিযানে মন্দির ধ্বংস ও কর–সংগ্রহ | দক্ষিণ ও মধ্য আরবের বিভিন্ন অঞ্চল | আক্রমণাত্মক | হাদিস ও সীরাত–বর্ণনায় পাওয়া যায়, নবী মুহাম্মদ আলি ইবন আবি তালিবসহ কিছু সাহাবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান এই নির্দেশনা দিয়ে যে, কোথাও যেন উঁচু কবর, মূর্তি বা মন্দির অক্ষত না থাকে—“কোনো ছবি যেন মুছে না রাখা হয় এবং কোনো উঁচু কবর যেন সমতল না করা হয়” টাইপের হাদিস পরবর্তীতে এই অভিযানের আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব অভিযানে স্থানীয় মন্দির, তীর্থস্থান ও গোত্র–পরিচয়ের প্রতীক ভেঙে ফেলার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের ওপর যাকাত/জিজিয়া/কর আরোপ করা হয়। ফলাফল হিসেবে আরবের বহু পুরনো ধর্মীয় বহুত্ববাদী সংস্কৃতি শারীরিকভাবে ধ্বংস হয় এবং তার জায়গায় একক ইসলামী–রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কর–নির্ভর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকাঠামো স্থাপিত হয়। [71] [72] |
| ৩৩ | অক্টোবর ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ ৯ হিজরি |
খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদের অভিযান | দুমাতুল জানদাল | আক্রমণাত্মক | বাইজেন্টাইন প্রভাবাধীন সীমান্ত–শহর দুমাতুল জানদাল অঞ্চলে খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদকে বড় বাহিনীসহ পাঠানো হয়। স্থানীয় আরব–খ্রিস্টান গোষ্ঠীর সামনে তিনটি অপশন তোলা হয়— ইসলাম গ্রহণ, কর–চুক্তি (জিজিয়া) মানা, অথবা যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের আশঙ্কা ও সামরিক শক্তির ভয়ে তারা চুক্তি–স্বাক্ষরে রাজি হয় এবং নিয়মিত কর প্রদানের বিনিময়ে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় বজায় রাখে। এই মডেল পরবর্তীকালে বৃহত্তর বাইজেন্টাইন–এলাকায় আরব–ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক অনুশীলন হিসেবে দেখা যায়। [73] [74] |
| ৩৪ | ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ ৯ হিজরি |
আবু সুফিয়ান ইবন হারবের অভিযান | তায়েফ নগরী মূর্তিপূজা কেন্দ্র আল-লাত মন্দির ধ্বংস |
আক্রমণাত্মক | তায়েফের সাকিফ গোত্র ইসলাম গ্রহণে রাজি হওয়ার পর নবী মুহাম্মদ আল-লাত নামের বিখ্যাত দেবীমূর্তি–মন্দির ধ্বংসের শর্ত চাপিয়ে দেন। বর্ণনা অনুযায়ী, আবু সুফিয়ান ইবন হারব ও মুগিরা ইবন শুওবা–সহ কয়েকজনকে পাঠানো হয় মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলতে। আল-লাত ছিল স্থানীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম প্রধান প্রতীক; তার ধ্বংস আরবের পূর্বাপর ইতিহাসে ধর্মীয় বহুত্ববাদ শেষ করে রাজনৈতিক–ধর্মীয় একচেটিয়া ইসলামী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নাটকীয় মুহূর্তগুলোর একটি। এখানে “তাওহিদ প্রতিষ্ঠা”র নামে অন্য ধর্মের প্রতীককে শারীরিকভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার সহিংস রাজনৈতিক প্রকল্প স্পষ্ট হয়ে ওঠে। [75] [76] |
| ৩৫ | ৬৩০ খ্রিঃ ৯ হিজরি |
তাবুক অভিযান | তাবুক বাইজেন্টাইন সীমান্ত |
আক্রমণাত্মক | “রোমান আক্রমণ”র গুজবকে অজুহাত করে প্রখর গরম, খরা ও দুর্ভিক্ষের মধ্যেও প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ উত্তরে তাবুক পর্যন্ত দীর্ঘ অভিযানে বের হন মুহাম্মদ। সরাসরি কোনো যুদ্ধ হয়নি; তথাকথিত বাইজেন্টাইন বাহিনীও উপস্থিত ছিল না। তবে সীমান্ত অঞ্চলের একাধিক খ্রিস্টান–আরব শাসক ও গোত্রনেতার সঙ্গে চুক্তি করে তাদের ওপর কর–ব্যবস্থা (জিজিয়া) ও রাজনৈতিক আনুগত্যের শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, বাস্তবে তাবুক ছিল এক ধরনের সামরিক শক্তি–প্রদর্শন, যার মাধ্যমে যুদ্ধ ছাড়াই সীমান্ত–অঞ্চলকে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য–বিস্তারের জন্য কর–প্রদায়ী প্রান্তিক অঞ্চলে পরিণত করা হয়। [77] [78] |
| ৩৬ | ৬৩০–৬৩১ খ্রিঃ ৯–১০ হিজরি |
সিরিয়া সীমান্তে টহল ও হামলা | বাইজেন্টাইন–ঘেঁষা বেদুইন গোত্র | আক্রমণাত্মক | তাবুকের পরবর্তী সময়ে সিরিয়া সীমান্তে বিভিন্ন বেদুইন ও আরব–খ্রিস্টান গোত্রের ওপর ছোট ছোট টহল ও হানা চালানো হয়। এসব অভিযানে কখনো হত্যা ও বন্দিত্ব, কখনো পশুপাল ও সম্পদ দখল, আবার কখনো জোরপূর্বক জিজিয়া–চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত এলাকার গোত্রগুলোর সামরিক ক্ষমতা ভেঙে দিয়ে তাদেরকে আগেভাগেই প্রান্তিক কর–প্রজায় পরিণত করা, যাতে পরবর্তীতে বৃহত্তর রোমান–অঞ্চলে সাম্রাজ্য–বিস্তারের পথ মসৃণ থাকে। [79] |
| ৩৭ | জুন/জুলাই ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ ১০ হিজরি |
খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদের অভিযান | নজরান অঞ্চল | আক্রমণাত্মক | দক্ষিণ আরবের খ্রিস্টান–প্রধান নজরান অঞ্চলের দিকে খালিদকে পাঠানো হয় প্রথমে ইসলাম গ্রহণ, না হলে যুদ্ধ—এই আলটিমেটাম নিয়ে। উল্লেখযোগ্য সশস্ত্র শক্তি সামনে দেখে স্থানীয় নেতৃত্ব যুদ্ধের বদলে চুক্তি–স্বাক্ষর ও কর–প্রদানে সম্মত হয়। পরে নজরানের প্রতিনিধিদল মদিনায় এসে আরও একটি চুক্তি করে; এর ফলে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ‘আহলে কিতাব করদাতা প্রজা’তে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে “দাওয়াত” থাকলেও এর পেছনে ছিল সামরিক চাপ, কর–ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অধীনতার মিশেল। [80] [81] |
| ৩৮ | ৬৩০–৬৩১ খ্রিঃ ৯–১০ হিজরি |
ইয়েমেন, ওমান, বাহরাইনসহ দক্ষিণ আরব অভিযান | বিভিন্ন স্থানীয় শাসক ও গোত্র | আক্রমণাত্মক | দক্ষিণ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে—ইয়েমেন, ওমান, হাজর, বাহরাইন ইত্যাদিতে—চিঠি, দূত এবং প্রয়োজনে সৈন্য পাঠিয়ে শাসক–গোত্রগুলোর সামনে তিনটি অপশন তোলা হয়ঃ ইসলাম গ্রহণ, কর–প্রদায়ী ‘মু’আহিদ’ হওয়া, অথবা যুদ্ধ। কোথাও তুলনামূলকভাবে অল্প রক্তপাতের মাধ্যমে চুক্তি হয়, কোথাও প্রতিরোধ ও যুদ্ধের পরেই এই চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে আরব উপদ্বীপের প্রায় পুরো অঞ্চলকে রাজনৈতিকভাবে একক ইসলামী কেন্দ্রের অধীনে এনে ধর্ম–দাওয়াত, কর–ব্যবস্থা এবং সামরিক শক্তিকে একসাথে সাম্রাজ্য–বিস্তারের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। [82] [83] |
| ৩৯ | ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ ১০ হিজরি |
আলি ইবন আবি তালিবের অভিযান | হামদান অঞ্চল (ইয়েমেন) | আক্রমণাত্মক | ইয়েমেনের হামদান গোত্রাঞ্চলে আলিকে পাঠানো হয় ইসলাম–দাওয়াত ও কর–সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে। সীরাত বর্ণনায় আছে, কিছুদিন অনীহা ও টানাপোড়েনের পর গোত্রটি শেষে “দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণ” করে এবং এরপর থেকে সেখানে যাকাত ও অন্যান্য কর সংগ্রহ শুরু হয়। মুসলিম সূত্রে এটিকে “বড় বিজয়” হিসেবে তুলে ধরা হলেও, রাজনৈতিক বাস্তবতায় এটি ছিল সামরিক উপস্থিতি, আদর্শিক চাপ এবং কর–ব্যবস্থার সম্মিলিত ফল—যেখানে কোনো বিকল্প ধর্ম–রাজনৈতিক প্রজেক্ট টিকে থাকার সুযোগ রাখা হয়নি। [84] [85] |
| ৪০ | ডিসেম্বর ৬৩১ খ্রিঃ ১০ হিজরি |
আলি ইবন আবি তালিবের অভিযান (মুযহিজ) | মুযহিজ অঞ্চল (ইয়েমেন) | আক্রমণাত্মক | ইয়েমেনের মুযহিজ অঞ্চলে আলির নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে স্থানীয় গোত্রগুলোর সঙ্গে কিছু সংঘর্ষ, হত্যা ও বন্দিত্ব ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত কর–চুক্তি ও আনুগত্যের শর্ত আরোপ করা হয়। এ ধরনের অভিযানে সাধারণ প্যাটার্ন ছিল—প্রথমে সামরিক চাপ ও ভীতি সৃষ্টি, এরপর ইসলাম গ্রহণ বা কর–চুক্তির মধ্যে বেছে নেওয়ার “স্বাধীনতা”। বাস্তবে এগুলো ছিল একমুখী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যেখানে গোত্রসমূহকে ইসলামী রাজনৈতিক কাঠামোর অধীনে এনে স্থানীয় ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোকে ধীরে ধীরে ভেঙে দেওয়া হয়। [86] |
| ৪১ | এপ্রিল ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ ১০ হিজরি |
যুল খালাসা মন্দির ধ্বংস | যুল খালাসা দক্ষিণ আরব |
আক্রমণাত্মক |
দক্ষিণ আরবের বিখ্যাত পৌত্তলিক মন্দির “যুল খালাসা”—যাকে “ইয়ামান ও মিহরার কাবা”
বলা হতো—এটি ধ্বংসের জন্য মুহাম্মদ জারির ইবন আবদুল্লাহকে পাঠান।
বর্ণনায় আছে, তিনি সেখানে গিয়ে মন্দির ভেঙে ফেলেন, মূর্তি পুড়িয়ে দেন এবং
প্রতিরোধকারীদের হত্যা করে এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেন।
এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল স্পষ্টঃ
আরবের ধর্মীয় বহুত্ববাদ সম্পূর্ণ নির্মূল করে ইসলামকে একমাত্র অনুমোদিত ধর্মে রূপান্তর করা।
স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই মন্দির ধ্বংস আরবের প্রাচীন সাংস্কৃতিক–ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি একটি সুস্পষ্ট আঘাত—একটি আদর্শ–প্রণোদিত “ধর্মীয় পরিশোধন অভিযান”, যেখানে ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়কে অস্তিত্বশূন্য করে দেওয়া হয়। [87] [88] |
| ৪২ | মে ৬৩২ খ্রিঃ ১০ হিজরি |
উসামা ইবন যায়েদের অভিযান | মু’তা সীমান্ত বাইজেন্টাইন ফ্রন্ট |
আক্রমণাত্মক |
নবীর মৃত্যুর ঠিক আগে মাত্র কিশোর (প্রায় ১৮–২০ বছর বয়সী) উসামা ইবন যায়েদকে
একটি বড় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে উত্তর দিকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়—
লক্ষ্য ছিল বাইজেন্টাইন–ঘেঁষা সীমান্ত অঞ্চলে আগের মু’তা যুদ্ধের প্রতিশোধ ও
ভবিষ্যৎ রোমান–অঞ্চলে সামরিক বিস্তারের ভূমি প্রস্তুত করা।
বহু প্রবীণ সাহাবী উসামার কম বয়স নিয়ে আপত্তি তুললেও নবী আদেশ পুনর্ব্যক্ত করেন।
নবীর মৃত্যুর পর মুহূর্তেই এই বাহিনী ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে আবু বকর কঠোর নির্দেশ দেন—“উসামার বাহিনী অবশ্যই যাবে”—এবং অবশেষে বাহিনী উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। এই অভিযান ছিল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম বড় পররাষ্ট্র–সামরিক উদ্যোগ, যেখানে আরব উপদ্বীপের বাইরে সাম্রাজ্য–বিস্তারের ভবিষ্যৎ রূপরেখা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। [89] [90] |
তথ্যসূত্রঃ
- Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources, Martin Lings, page 17 ↩︎
- আর রাহীকুল মাখতুম, আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা ৭৫ ↩︎
- Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources, Martin Lings, page 21 ↩︎
- Muhammad ibn Saad. Kitab al-Tabaqat al-Kabair vol. 3. Translated by Bewley, A. (2013). The Companions of Badr. London: Ta-Ha Publishers ↩︎
- নবীকে হামযার গোলাম বলে গালি ↩︎
- আর রাহীকুল মাখতুম, আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, পৃষ্ঠা ৭৬ ↩︎
- উম্মে হানী- মুহাম্মদের গোপন প্রণয় 1 2
- কাবার পাশে পঁয়ত্রিশ বছরের ন্যাংটু নবী ↩︎
- মুহাম্মদের সমসাময়িক নবীগণ ↩︎
- হেরাগুহায় পৌত্তলিক প্রার্থনা ↩︎
- হেরা গুহার ওহিঃ ইসলামের ভিত্তিমূলের বাস্তবতা ↩︎
- নবী মুহাম্মদ ছিলেন ধর্ম অবমাননাকারী ↩︎
- বনু কুরাইজার গণহত্যা ↩︎
- আলীর নাবালিকা দাসী ধর্ষণ ↩︎
- সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নম্বরঃ ৫৫৭৩ ↩︎
- সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন, হাদিস নম্বরঃ ৪৪৫৮ ↩︎
- সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিসঃ ১১৫ ↩︎
- সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, হাদিসঃ ৫৬৬৯ ↩︎
- সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী, হাদিসঃ ৭৪১৪ ↩︎
- সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৮৪, হাদিসঃ ৭২৪৩ ↩︎
- ইবনে হিশাম, সীরাতে রাসূলুল্লাহ, খণ্ড ২ ↩︎
- আল-তাবারি, তারিখ আল-রসূল ওয়াল-মুলুক, ১/১২৩–১৩১ ↩︎
- ইবনে হিশাম, সীরাত, ২/২৩২ ↩︎
- আল-তাবারি ১/১২৮ ↩︎
- ইবনে হিশাম ২/২৩৫ ↩︎
- ইবনে হিশাম ২/২৩৮ ↩︎
- তাবারি ১/১৩৪ ↩︎
- ইবনে হিশাম ২/২৪০ ↩︎
- তাবারি ১/১৩৯ ↩︎
- তাফসির আল-তাবারি, সূরা আল-বাকারাহ ২:২১৭ ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ↩︎
- ইবনে হিশাম ২/২৪৭ ↩︎
- তাবারি ১/১৪৭–১৫০ ↩︎
- ইবনে হিশাম, সীরাতে রাসূলুল্লাহ, বনু কায়নুকা অধ্যায় ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বাংলা অনুবাদ ↩︎
- ইবনে হিশাম, সীরাত, সাওয়িক গাজওয়া অধ্যায় ↩︎
- তাবারি, তারিখ, ২ হিজরি ঘটনার বর্ণনা ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, জু আম্মার ঘটনা ↩︎
- ইবনে হিশাম, সীরাত, আল-কারাদা কাফেলা অভিযান ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, গনিমত বণ্টন প্রসঙ্গ ↩︎
- ইবনে হিশাম, উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, ৩ হিজরি ঘটনা ↩︎
- ইবনে হিশাম, বনু নাদির অধ্যায় ↩︎
- তাফসির ইবনে কাথির, সূরা আল-হাশর ৫৯:২ ↩︎
- ইবনে কাথির, দাতুর-রিকা গাজওয়া বর্ণনা ↩︎
- ইবনে হিশাম, দুমাতুল-জান্দাল অভিযান ↩︎
- তাবারি, উত্তরের অভিযানের বিবরণ ↩︎
- ইবনে হিশাম, গাজওয়াতুল-খন্দক ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, আহযাব অধ্যায় ↩︎
- ইবনে হিশাম, বনু কুরাইযা অধ্যায় ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বনু কুরাইযা ঘটনা ↩︎
- মুহাম্মদ হুসাইন হাইকَل, হায়াতু মুহাম্মদ, বাংলা অনুবাদ, বনু কুরাইযা প্রসঙ্গ ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বনু সালাবা প্রসঙ্গ ↩︎
- ইবনে কাথির, একই অধ্যায় ↩︎
- ইবনে হিশাম ও ইবনে কাথির, জায়েদ ইবন হারিসা–সম্পর্কিত গাজওয়া/সারিয়ার তালিকা ↩︎
- তাবারি, ওয়াদি আল-কুরা ঘটনা ↩︎
- ইবনে কাথির, খাইবার–পূর্ব কৃষি অঞ্চলসমূহের বর্ণনা ↩︎
- ইবনে হিশাম, জু কারাদ ঘটনার বর্ণনা ↩︎
- ইবনে হিশাম, গাজওয়াতু খাইবার অধ্যায় ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খাইবার ঘটনা ↩︎
- তাবারি, ফিদাক চুক্তি বর্ণনা ↩︎
- তাফসির ইবনে কাথির, সূরা আল-হাশর ও ফাই সম্পদ প্রসঙ্গ ↩︎
- ইবনে কাথির, গাজওয়াতু মু’তা ↩︎
- তাবারি, মু’তা যুদ্ধের বর্ণনা ↩︎
- ইবনে হিশাম, ফাতহে মক্কা অধ্যায় ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, ৮ হিজরি ঘটনা ↩︎
- ইবনে হিশাম, গাজওয়াতু হুনাইন ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, হুনাইন ও গনিমত বণ্টন অধ্যায় ↩︎
- ইবনে হিশাম, গাজওয়াতু হুনাইন ও তায়েফ অবরোধ ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৮ হিজরি ঘটনা ↩︎
- মুসনাদ আহমদ, আলির মাধ্যমে কবর সমতল ও মূর্তি ধ্বংস সম্পর্কিত হাদিস ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, ইয়েমেন ও দক্ষিণ আরব অভিযানের বর্ণনা ↩︎
- তাবারি, তারিখ, দুমাতুল জানদাল চুক্তি প্রসঙ্গ ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, খালিদের অভিযানের বর্ণনা ↩︎
- ইবনে হিশাম, সাকিফের ইসলাম গ্রহণ ও আল-লাত ধ্বংস ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, আল-লাত মন্দির প্রসঙ্গ ↩︎
- তাবারি, গাজওয়াতু তাবুক বর্ণনা ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, ৯ হিজরি – তাবুক অভিযান ↩︎
- তাবারি, সিরিয়া সীমান্তের ছোট গাজওয়া ও সারিয়া–সমূহ ↩︎
- ইবনে কাথির, নজরান খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি ↩︎
- তাবারি, নজরান প্রসঙ্গ ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, দক্ষিণ আরবের ইসলাম গ্রহণ ও কর–চুক্তি ↩︎
- তাবারি, নবীর পাঠানো চিঠি ও আমিলদের তালিকা ↩︎
- ইবনে কাথির, হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ↩︎
- ইবনে হিশাম, ইয়েমেন অভিযানের বর্ণনা ↩︎
- ইবনে কাথির, ইয়েমেন ও আশপাশের গাজওয়া–সমূহ ↩︎
- সহীহ বুখারি, কিতাবুল জিহাদ, باب: بعث جرير إلى ذي الخلصة ↩︎
- ইবনে কাথির, আল-বিদায়া, যুল খালাসা ধ্বংস ↩︎
- ইবনে হিশাম, উসামা বাহিনী অধ্যায় ↩︎
- তাবারি, উসামা সেনাদল পাঠানোর নির্দেশ ↩︎