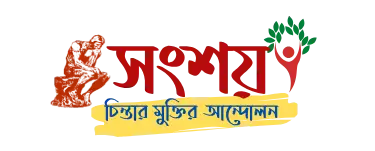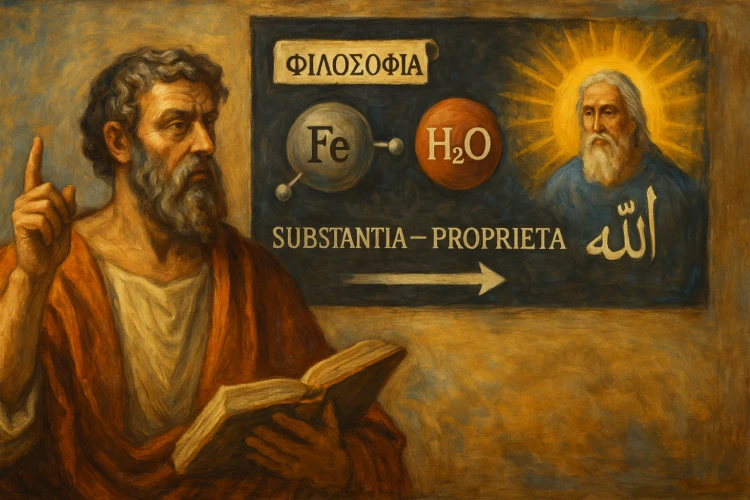
Table of Contents
- 1 ভূমিকা
- 2 বৈশিষ্ট্য ও বস্তু: অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক
- 3 অবস্তুগত সত্তার গুণ ধারণের যৌক্তিক সমস্যা
- 4 চেতনা ও গণিত: অবস্তুগত নয়, উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য
- 5 ঈশ্বরের গুণাবলি ও যৌক্তিক স্ববিরোধ
- 6 বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি: মনবাদ, দ্বৈতবাদ ও সর্বচৈতন্যবাদ
- 7 পদার্থের বৈশিষ্ট্যের আণবিক ভিত্তি: বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ
- 8 ধারণাগত ঈশ্বর বনাম অস্তিত্বশীল ঈশ্বর
- 9 উপসংহার
ভূমিকা
“বৈশিষ্ট্য” (Property) ধারণাটি দর্শনের অন্যতম প্রাচীন ও মৌলিক প্রশ্নগুলির একটি। কোনো কিছু কি—এই প্রশ্নের উত্তর যতটা তার অস্তিত্বে (Being) নিহিত, ততটাই নিহিত থাকে তার বৈশিষ্ট্যে। Plato থেকে Aristotle, Descartes থেকে Spinoza, এবং পরবর্তীতে Hume ও Kant—সব যুগের দার্শনিকরা একাধিকবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন: কোনো কিছুর বৈশিষ্ট্য কোথায় থাকে? সেটি কি বস্তু নিজেই ধারণ করে, নাকি বৈশিষ্ট্য কোনো স্বাধীন সত্তা? অর্থাৎ, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পানির যে তরল বৈশিষ্ট্য, তা কী পানির বস্তুগত অস্তিত্ব থেকে আলাদা স্বাধীন কিছু, নাকি পানির বস্তুগত অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল কিছু?
Plato তার Theory of Forms-এ বলেন, আমাদের চোখে দেখা বস্তুগুলি পরিবর্তনশীল হলেও প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের একটি “চিরন্তন আদর্শ রূপ” (Ideal Form) আছে যা বস্তুজগতের বাইরে একটি অবাস্তব জগতে বিদ্যমান থাকে। যেমন, কোনো কিছু “সুন্দর” বলার মানে হল সেটি ‘সৌন্দর্যের রূপ’-এর সাথে অংশীদার হচ্ছে [1]। অন্যদিকে Aristotle এই ধারণার বিরোধিতা করে বলেন, বৈশিষ্ট্য কখনোই বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না; বৈশিষ্ট্য মানে হলো বস্তুর নির্দিষ্ট রূপ ও কাঠামো, যা ঐ বস্তুটি ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। অর্থাৎ বস্তুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুর ওপর নির্ভরশীল, আলাদা কিছু নয় [2].
Descartes এই প্রশ্নকে নতুন মাত্রা দেন তাঁর দ্বৈতবাদে। তিনি বলেন, পদার্থ দুই রকম—চিন্তাশীল (mind) ও বিস্তৃত (matter)। চিন্তাশীল পদার্থ ধারণ করে জ্ঞান, ইচ্ছা ইত্যাদি; আর বিস্তৃত পদার্থ ধারণ করে স্থানিক গঠন ও আন্দোলন [3]. কিন্তু Spinoza এভাবে পদার্থকে ভাগ না করে বলেন, একটি মাত্র সার্বজনীন পদার্থ আছে, যার অসংখ্য বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সবকিছু তারই অবস্থা মাত্র [4].
Hume এই সমগ্র ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেন, আমরা কোনো “বস্তু” প্রত্যক্ষ করি না; আমরা কেবল বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যক্ষ করি। অতএব, “বস্তু” ধারণাটি মানসিক অভ্যাস মাত্র, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নয় [5]। Kant এর উত্তরে বলেন, বৈশিষ্ট্য ও বস্তু হল মনের গঠনগত বিভাগ—অর্থাৎ জগৎকে আমরা এইভাবে সংগঠিত করি, কিন্তু তা বস্তুজগতের বাইরের “বস্তু নিজে” সম্পর্কে কিছু বলে না [6].
এইসব তত্ত্ব আমাদের এক গভীর দার্শনিক সমস্যার মুখোমুখি করে: যে সত্তার কোনো ভৌত কাঠামো নেই—যেমন অবস্তুগত আত্মা বা ঈশ্বর—সে কি আদৌ বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে? যদি বৈশিষ্ট্য মানে হয় শক্তি, আচরণ বা ক্রিয়াশীলতা, তাহলে অবস্তুগত কোনো সত্তার গুণাবলি কিভাবে থাকবে?
এই প্রবন্ধে আমরা দেখব, বৈশিষ্ট্য ধারণ করা মানে আসলে কী, তার অন্টোলজিক্যাল ভিত্তি কোথায়, এবং পদার্থ ও বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক কতটা অবিচ্ছেদ্য। শেষে আমরা বিশ্লেষণ করব, অবস্তুগত ঈশ্বর বা আত্মার গুণাবলির ধারণা যুক্তিগতভাবে কতটা টিকে থাকতে পারে।
বৈশিষ্ট্য ও বস্তু: অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক
বৈশিষ্ট্য এবং বস্তু—এই দুই ধারণার পারস্পরিক সম্পর্কই হল অস্তিত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি। প্রাচীন দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ Aristotle তার Metaphysics-এ বলেছিলেন, [7]
Substance is that which exists in itself; properties exist in something else.
এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, বৈশিষ্ট্য কখনোই স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না—তা সর্বদা কোনো পদার্থ বা বস্তুতে নিহিত থাকে। বৈশিষ্ট্য মানে বস্তুর এমন কিছু গুণ, যা তার অন্তর্নিহিত গঠন, শক্তিবিন্যাস এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ অনুসারে কোনো বৈশিষ্ট্য যদি দেখা যায়, তাহলে সেটি কোনো না কোনো পদার্থের মধ্যেই অস্তিত্বমান।
এই বক্তব্য আধুনিক দর্শনেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। David Armstrong ২০শ শতকে বলেন, [8]
Properties are instantiated in particulars; they do not float freely in the void.
অর্থাৎ, বৈশিষ্ট্য কোনো ধোঁয়াশাপূর্ণ বিমূর্ত ধারণা নয়; এগুলো বাস্তব বস্তুর মধ্যেই দৃশ্যমানভাবে আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, চৌম্বকত্ব হলো লোহার পারমাণবিক কাঠামোর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ, যা ইলেকট্রনের স্পিন ও তাদের বিন্যাসের উপর নির্ভর করে।
প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক নিয়ে সবচেয়ে বাস্তবভিত্তিক অবস্থান নিয়েছিল চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন। এই দার্শনিকগণ বিশ্বাস করতেন যে কেবল ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থই বাস্তব—অর্থাৎ যা দেখা, ছোঁয়া বা অভিজ্ঞতা করা যায়, কেবল সেটিই অস্তিত্বশীল। বৈশিষ্ট্য কখনোই বস্তু থেকে আলাদা কোনো সত্তা নয়; বরং সেটি বস্তুর প্রকৃত গঠন ও উপাদানগত বিন্যাসের প্রকাশ। চার্বাকদের ভাষায়, [9]
যেমন আগুনে তাপ, জলে স্নিগ্ধতা এবং চিনি-তে মাধুর্য নিহিত—তেমনই বৈশিষ্ট্যও পদার্থের মধ্যেই অন্তর্নিহিত।
তাঁদের মতে, আত্মা, ঈশ্বর বা অন্য কোনো অবস্তুগত সত্তার ধারণা হলো কল্পনার ফল, কারণ কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে হলে তা কোনো উপাদানগত কাঠামোর মধ্য দিয়ে কার্যকর হতে হয়। চার্বাক দার্শনিক জয়রাশি ভট্ট তাঁর Tattvopaplava-siṁha-এ যুক্তি দেন যে “যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না; কারণ অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো সত্তা বা বৈশিষ্ট্য কল্পনা মানে শূন্যের উপর তত্ত্ব দাঁড় করানো।” এইভাবে চার্বাক দর্শন বৈশিষ্ট্য ও বস্তুর সম্পর্ককে সম্পূর্ণ ভৌত ও পরীক্ষণযোগ্য বাস্তবতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে, যা পরবর্তীকালে আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আশ্চর্যরকমভাবে মিলে যায়। [10]
বিজ্ঞান এই দর্শনের ভিত্তিকে আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। প্রতিটি পদার্থের বৈশিষ্ট্য তার গঠন ও শক্তিবিন্যাস দ্বারা নির্ধারিত। নিচের টেবিলটি কয়েকটি সাধারণ পদার্থের উদাহরণ উপস্থাপন করছে:
| Substance | Observable Property | Underlying Cause |
|---|---|---|
| Iron (Fe) | Magnetic, Solid, Heavy | Electron spin alignment, metallic crystal lattice |
| Water (H₂O) | Liquid, Cohesive, Transparent | Polar covalent bonding, hydrogen bonds |
| Sodium Chloride (NaCl) | Crystalline, Soluble, Salty | Ionic lattice structure, dissociation in polar solvent |
| Oxygen (O₂) | Gaseous, Reactive, Supports combustion | Diatomic bonding, unpaired electrons in outer shell |
এই টেবিল থেকে বোঝা যায়, পদার্থের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য আসলে তার ভেতরের গঠনগত ও শক্তিগত বাস্তবতার প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ, পানির তরলতা (fluidity) কোনো রহস্যময় গুণ নয়, বরং তার অণুর মধ্যকার হাইড্রোজেন বন্ডের ফল। প্রতিটি H2O অণুতে অক্সিজেন পরমাণুটি সামান্য ঋণাত্মক এবং হাইড্রোজেন সামান্য ধনাত্মক চার্জ বহন করে, ফলে পাশের অণুগুলোর সাথে এটি “polar covalent” আকর্ষণ তৈরি করে। এই বন্ধন এতটাই দুর্বল যে তা ভাঙে ও গঠিত হয় প্রতি মুহূর্তে, ফলে অণুগুলি একে অপরের সাথে যুক্ত থেকেও স্বাধীনভাবে সরে যেতে পারে—এ কারণেই পানি কঠিন নয়, তরল অবস্থায় প্রবাহিত হয়। যদি তাপমাত্রা কমিয়ে হাইড্রোজেন বন্ডগুলো স্থায়ী করে তোলা যায়, তবে অণুগুলো একে অপরের উপর স্থির জাল তৈরি করে বরফের স্ফটিক গঠন করে—এতে দেখা যায়, কেবল আণবিক গঠন ও তাপীয় শক্তির পরিবর্তনেই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বদলে যায় [11].
লোহার চৌম্বকত্বের ক্ষেত্রেও একই রকম আণবিক স্তরের নিয়ম কাজ করে। লোহা (Fe) পরমাণুতে চারটি অনিবদ্ধ ইলেকট্রন থাকে, যাদের স্পিন (spin) যদি একদিকে সমন্বিত থাকে, তবে অসংখ্য পরমাণুর মধ্যে একটি বৃহৎ চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এই সমন্বয়কে বলে “ferromagnetic alignment”। কিন্তু যদি ইলেকট্রনের স্পিন এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত থাকে, যেমন তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের মতো ধাতুতে দেখা যায়, তবে কোনো নেট চৌম্বক ক্ষেত্র গঠিত হয় না। এমনকি লোহা উত্তপ্ত করলে তার পরমাণুগুলোর স্পিনের সঙ্গতি নষ্ট হয় এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (Curie point, প্রায় 770°C) অতিক্রম করলে এটি চৌম্বকত্ব হারিয়ে ফেলে [12].
এটি প্রমাণ করে, বৈশিষ্ট্য মানে একটি পদার্থের গঠন ও শক্তিবিন্যাসের নিখুঁত সংহত রূপ; বৈশিষ্ট্য কখনোই বস্তুবিচ্ছিন্নভাবে বাস্তব নয়। ফলে অবস্তুগত সত্তার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ তার মধ্যে এসব গঠনতাত্ত্বিক উপাদান অনুপস্থিত।
অবস্তুগত সত্তার গুণ ধারণের যৌক্তিক সমস্যা
যদি কোনো সত্তাকে অবস্তুগত (immaterial), আকারহীন, স্থান-কালাতীত বলা হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে: তার “বৈশিষ্ট্য” কোথায় অবস্থান করে?Thomas Aquinas এবং René Descartes-এর মতে, আত্মা বা ঈশ্বর অবস্তুগত হলেও তাদের নানা “গুণ” থাকতে পারে—যেমন জ্ঞান, ইচ্ছা, ন্যায়। Descartes তাঁর Meditations-এ বলেছেন, [13]
Again, the idea that gives me my understanding of a supreme God—eternal, infinite, unchangeable, omniscient, omnipotent and the creator of everything that exists except for himself—certainly has in it more representative reality than the ideas that represent merely finite substances.
অপরদিকে Aquinas ও যুক্তি দিয়েছেন যে ঈশ্বরের গুণগুলো কোনো স্বাধীন সত্তা নয়, বরং ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গেই একীভূত। তিনি বলেন, [14]
In God, being good is not anything distinct from Him; He is His goodness.
কিন্তু Hume-এর মতে, এই দাবিগুলো একধরনের ক্যাটাগরি মিস্টেক(category mistake), [15]
We have no impression of any substance; we only perceive a bundle of qualities.
Hume-এর মূল আপত্তি হল: আমরা যে-কোনো পদার্থকে চিনি তার দৃশ্যমান/অনুভূত বৈশিষ্ট্যগুলোর সমষ্টি হিসেবে—অর্থাৎ রং, গন্ধ, আকার, তাপ, স্থিতিস্থাপকতা, ইত্যাদি। আলাদা কোনো “অধার পদার্থ” (substratum) বা “অবস্তুগত সত্তা”—যে-সত্তা নাকি গুণগুলোকে বহন করে—এমন কিছুর কোনো সরাসরি সংবেদনগত ছাপ (impression) আমাদের নেই; তাই ঐ ধরনের সত্তা কল্পনা করা মানে অভিজ্ঞতার বাইরে নতুন সত্তা বসানো, যা জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে শূন্য দাবির সমতুল্য [5]. এই আপত্তির পেছনে ধারণাটি সহজ: গুণ/বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা যে আচরণগত ক্ষমতাগুলো দেখি—যেমন টানার ক্ষমতা, তাপ পরিবহণ, আলো শোষণ/প্রতিফলন—এসব সবই কোনো নির্দিষ্ট ভৌত গঠন ও শক্তিবিন্যাসের ফল। সুতরাং গঠনহীন, শক্তিবিহীন, স্থান-কালাতীত কোনো ‘সত্তা’কে গুণসম্পন্ন বলা ভাষাগতভাবে তো বটেই, কার্যকারণগত (causal) অর্থেও ফাঁকা কথা।
এখানে যুক্তিটি ধাপে ধাপে দাঁড় করালে বিষয়টি স্বচ্ছ হয়—
- বৈশিষ্ট্য = কর্মক্ষমতা/প্রভাবক্ষমতা — কোনো কিছুর ‘বৈশিষ্ট্য’ বলতেই আমরা যা বুঝি তা হলো তার কি করতে পারে বা কিসে প্রতিক্রিয়া দেখায় (capacity to act or be affected)। উদাহরণ: লোহা চৌম্বকের আকর্ষণে সাড়া দেয়; পানি নির্দিষ্ট তাপে প্রবাহিত/বরফে রূপান্তরিত হয়—এগুলো ক্ষমতা বা আচরণ [8].
- কর্মক্ষমতা = শক্তি/তথ্য স্থানান্তর — কোনো প্রভাব ঘটতেই হলে শক্তি, ভর, চার্জ, স্পিন, বা ক্ষেত্রের মাধ্যমে ইন্টারঅ্যাকশন ঘটতে হয়—এটাই পদার্থবিজ্ঞানের মর্মবস্তু (interaction picture: বল/ক্ষেত্র/কণার মধ্যস্থতা) [16].
- ইন্টারঅ্যাকশন সর্বদা ভৌত কাঠামোর মাধ্যমে — প্রভাব ঘটানোর/গ্রহণের জন্য স্থানিক-বিন্যাস (structure), অবস্থা (state), ও গতি-বিধি (dynamics) লাগে: যেমন ইলেকট্রন স্পিনের সমাঙ্কনেই ফ্যারোম্যাগনেটিজম; H2O-এর পোলার জ্যামিতি ও হাইড্রোজেন বন্ডিং-এই তরলতার ব্যাখ্যা—সবই নির্দিষ্ট গঠনভিত্তিক [17].
- অবস্তুগত সত্তা = কাঠামো-বর্জিত — সংজ্ঞামতে অবস্তুগত সত্তার নেই ভর, চার্জ, স্পিন, স্থানিক বিস্তার, শক্তিবিন্যাস বা কোনো গুপ্ত মাইক্রো-স্ট্রাকচার।
মূলকথা: যদি বৈশিষ্ট্য মানে কর্মক্ষমতা, আর কর্মক্ষমতা মানে ভৌত কাঠামো-ভিত্তিক ইন্টারঅ্যাকশন, তবে যে সত্তায় কোনো ভৌত কাঠামো নেই, তাতে বৈশিষ্ট্য আরোপ যৌক্তিকভাবে অসঙ্গত। প্রতীকী আকারে যুক্তিটি “modus tollens” আকারে—
– যদি P হয় তবে Q। (P: বৈশিষ্ট্য থাকলে ভৌত-সাবস্ট্রেট লাগে; Q: ভৌত ইন্টারঅ্যাকশন সম্ভব)
- Q নয় (অবস্তুগত সত্তায় ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোই নেই)
- অতএব, P নয় (অবস্তুগত সত্তায় বৈশিষ্ট্য নেই)।
এই প্রথম প্রেমিস—“বৈশিষ্ট্যের জন্য সাবস্ট্রেট লাগে”—শুধু দার্শনিক অনুমান নয়; এটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হলে আমরা সর্বদা অন্তর্গঠন/অবস্থার পরিবর্তন পাই—লোহা কুরি তাপমাত্রার ওপরে (প্রায় ৭৭০°C) গেলে তার ইলেকট্রন স্পিনের সমন্বয় ভেঙে যায় এবং চৌম্বকত্ব হারিয়ে ফেলে; আবার পানির অণু-জ্যামিতি বা হাইড্রোজেন বন্ডিং সামান্য পরিবর্তিত হলে তার পর্যায়, ঘনত্ব ও পৃষ্ঠটানও পাল্টে যায়। এই গুণ-পরিবর্তন ↔ গঠন-পরিবর্তনের দৃঢ় সম্পর্ক দেখায়, যে কোনো ‘বৈশিষ্ট্য’ আসলে স্বাধীন বা মুক্ত-ভাসমান সত্তা নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেট বা কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। ফলে Hume-এর উপসংহারটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক—অবস্তুগত কোনো সত্তায় গুণ আরোপ করা মানে অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত, কারণ-বিবর্জিত, এবং শেষ পর্যন্ত অর্থহীন দাবি: it is a category mistake. [18] [19] [20].
গুণ-পরিবর্তন ↔ গঠন-পরিবর্তন : কপলিং ডায়াগ্রাম
চেতনা ও গণিত: অবস্তুগত নয়, উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য
অনেকে বলেন, “চেতনা” (consciousness) বা “গণিত” অবস্তুগত সত্তা; তাই ঈশ্বরও হতে পারেন। কিন্তু আধুনিক cognitive science অনুযায়ী, চেতনা হচ্ছে emergent property—অর্থাৎ মস্তিষ্কের জটিল নিউরোনাল প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত আচরণ।
Daniel Dennett ব্যাখ্যা করেছেন, [21]
Consciousness is not a ghost in the machine; it is the machine’s organization that gives rise to the phenomenon.
অর্থাৎ, চেতনা (consciousness) কোনো স্বতন্ত্র আত্মা বা অবস্তুগত সত্তা নয়; বরং এটি জীববিজ্ঞানের জটিল সংগঠন থেকে উদ্ভূত একটি কার্যপ্রক্রিয়া। আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের মতে, মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ৮৬ বিলিয়ন নিউরন এবং ট্রিলিয়ন সিন্যাপটিক সংযোগ একসঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকে; এই অসংখ্য নিউরোনাল সার্কিটের বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক সংকেতের সমন্বয়েই চেতনার অনুভব গঠিত হয়। প্রতিটি স্নায়ু-কোষের বৈদ্যুতিক সম্ভাবনায় (action potential) ক্ষুদ্র পরিবর্তন সারা নেটওয়ার্কে প্রভাব ফেলে, যার মাধ্যমে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি উদ্ভূত হয়। এই ধারণাকে বলা হয় emergentism—যেখানে বলা হয়, জটিল কাঠামোতে নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় যা আলাদা অংশগুলোর মধ্যে থাকে না [22]; [23]. উদাহরণস্বরূপ, পৃথক নিউরন কোনো সচেতনতা ধারণ করে না, কিন্তু তাদের জৈব নেটওয়ার্কের নির্দিষ্ট সংগঠন একটি উচ্চতর গুণ হিসেবে ‘চেতনা’ তৈরি করে—যেমন পানি অণুর সমষ্টি থেকে “তরলতা” উদ্ভূত হয়, অথচ একক H₂O অণুর নিজস্ব কোনো তরলতা নেই।
একইভাবে, “গণিত” (mathematics) বা “সংখ্যার ধারণা”ও কোনো অবস্তুগত অস্তিত্ব নয়; এটি মানব মস্তিষ্কের বিমূর্ত চিন্তাশক্তির প্রতিফলন। গণিতের প্রতীক ও সূত্রগুলো আমাদের বোধের এক প্রকার ‘মেটা-সংগঠন’, যা বাস্তব জগৎকে বর্ণনা ও পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মানসিক কাঠামো সরবরাহ করে। Kant এই বিষয়টিকে বলেছেন synthetic a priori জ্ঞান—অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পূর্বেই মানব মনের স্থান, সময়, সংখ্যা ও কারণিকতার ধারণা বিদ্যমান থাকে, যা অভিজ্ঞতাকে সাজানোর জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে [24]. উদাহরণ হিসেবে ধরা যায় জ্যামিতি বা গাণিতিক নিয়মাবলি—যা প্রকৃতির গঠন অনুসারে নয়, বরং মানব মনের স্থানিক-সংবেদী কাঠামো অনুযায়ী তৈরি। যখন আমরা বলি “ত্রিভুজের কোণসমষ্টি ১৮০°,” আমরা প্রকৃত জগতে এমন কোনো ত্রিভুজ অস্তিত্বশীল বলে বলি না; বরং মস্তিষ্কের যুক্তি-সংবেদন কাঠামোর মধ্যে এমন বিমূর্ত রূপ তৈরি করি। অতএব, গণিতের সত্যতা মননগত, পদার্থগত নয় [25].
ফলে, যেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে “অবস্তুগত” বলে মনে হয়—যেমন চেতনা, চিন্তা, নৈতিকতা, বা গণিত—তাও শেষ পর্যন্ত পদার্থিক সংগঠন ও স্নায়বিক বা মানসিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত। এগুলো স্বতন্ত্র আত্মা বা বাহ্যিক অধিবিদ্যাগত জগৎ থেকে আসে না; বরং পদার্থের নির্দিষ্ট বিন্যাস ও কার্যপ্রণালীর মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়। এ কারণেই আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বে এই ধারণাকে বলা হয় emergent physicality—অর্থাৎ পদার্থের জটিল সংগঠনেই তথাকথিত “অবস্তুগত” বৈশিষ্ট্যগুলির উৎপত্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চেতনা ও গণিত উভয়ই বাস্তব, কিন্তু তাদের বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে পদার্থের কাঠামো ও সংগঠনের উপর নির্ভরশীল।
ঈশ্বরের গুণাবলি ও যৌক্তিক স্ববিরোধ
ধর্মীয় ব্যাখ্যায় ঈশ্বরকে বলা হয় “সর্বশক্তিমান”, “সর্বজ্ঞ”, “সর্বদয়”। কিন্তু দার্শনিকভাবে এই গুণগুলো পরস্পরের সঙ্গে স্ববিরোধী।
- সর্বজ্ঞ কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন:
যদি ঈশ্বর ভবিষ্যৎ জানেন, তবে তাঁর ইচ্ছা নির্ধারিত; আর যদি তাঁর ইচ্ছা স্বাধীন হয়, তবে তিনি ভবিষ্যৎ জানেন না। এ দুটি একসঙ্গে সত্য হতে পারে না। [26] - আকারহীন অথচ “দেখেন”, “শোনেন”:
এসব ক্রিয়া সংবেদনসংক্রান্ত, যা স্থানিক মাধ্যম দাবি করে—চোখ, কান, তরঙ্গ। আকারহীন সত্তা এগুলো কীভাবে সম্পন্ন করবে? - অবস্তুগত অথচ “সৃষ্টি করেন”:
কারণসৃষ্ট (causal) ক্রিয়া মানে শক্তি বা পদার্থের পরিবর্তন। পদার্থ ছাড়া causation-এর কোনো অর্থ হয় না।
Bertrand Russell তাই বলেন, [27]
To say that a timeless, spaceless being causes the universe is to use the word ‘cause’ in a sense entirely empty.
অতএব, ঈশ্বরের গুণাবলি নিজের মধ্যেই ভাষাগত ও যুক্তিগত সংঘর্ষে জর্জরিত।
বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি: মনবাদ, দ্বৈতবাদ ও সর্বচৈতন্যবাদ
যদিও বস্তুবাদ (Physicalism) মতে অবস্তুগত সত্তার কোনো গুণ নেই, তবু কিছু বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি আছে—
| দৃষ্টিভঙ্গি | মূল ধারণা | সমস্যা |
|---|---|---|
| Dualism (Descartes) | মন ও দেহ পৃথক সত্তা; মন অবস্তুগত | Interaction problem — অবস্তু কিভাবে পদার্থে প্রভাব ফেলে? |
| Idealism (Berkeley) | সবকিছু মনের ধারণা; বস্তু মানে অনুভূতি | Empirical testability নেই |
| Panpsychism (Goff, Galen Strawson) | চেতনা সব কণাতেই মৌলিক | Overgeneralization, explanatory gap |
এই মতগুলো অবস্তুগত সত্তার বৈশিষ্ট্য ধারণের সম্ভাবনা দেখাতে চায়, কিন্তু এগুলো কোনো প্রমাণনির্ভর কাঠামো দেয় না।
পদার্থের বৈশিষ্ট্যের আণবিক ভিত্তি: বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ
বিজ্ঞান দেখিয়েছে, প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের উৎস লুকিয়ে আছে পদার্থের আণবিক গঠন ও শক্তি-বিন্যাসের মধ্যে। কোনো পদার্থের আকার, অবস্থা, দৃঢ়তা, তাপ পরিবাহিতা, চৌম্বকত্ব, এমনকি স্বাদ—সবই নির্ভর করে তার পরমাণু ও অণুর বিন্যাস এবং সেই বিন্যাসে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রকৃতির উপর। পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, বৈশিষ্ট্য হলো কণাগুলোর মধ্যে কার্যরত মৌলিক বল (electromagnetic, gravitational, nuclear) এবং সেগুলোর ফলশ্রুতি শক্তি-সমতা (energy equilibrium)-এর প্রকাশ [11].
১️ চৌম্বকত্ব (Magnetism): চৌম্বকত্ব কোনো “অদৃশ্য” বা “অলৌকিক” গুণ নয়; এটি ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম স্পিন এবং তাদের সুষম বিন্যাসের ফল। প্রতিটি ইলেকট্রন ক্ষুদ্র চৌম্বক ডাইপোলের মতো আচরণ করে। যখন অসংখ্য ইলেকট্রনের স্পিন একই দিকে সারিবদ্ধ হয় (ferromagnetic alignment), তখন একটি বৃহত্তর সম্মিলিত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, লোহার (Fe) স্ফটিক কাঠামোতে ইলেকট্রন স্পিন সমন্বিত থাকে বলে এটি স্থায়ী চুম্বক হতে পারে। কিন্তু নিকেল উত্তপ্ত করলে (Curie temperature-এর ওপরে) ইলেকট্রনের এই বিন্যাস ভেঙে যায়, ফলে পদার্থ তার চৌম্বকত্ব হারায়। অর্থাৎ গঠনগত সামান্য পরিবর্তনেই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয় [28].
২️ পানির তরলতা ও পৃষ্ঠটান (Cohesion and Surface Tension): পানি (H₂O) তরল কেন—এই প্রশ্নের উত্তর এর আণবিক জ্যামিতিতেই নিহিত। H₂O অণু একটি “বাঁকা” (bent) গঠনবিশিষ্ট, যেখানে অক্সিজেনের উচ্চ ইলেকট্রন ঋণাত্মকতা হাইড্রোজেনকে আংশিক ধনাত্মক চার্জযুক্ত করে তোলে। ফলস্বরূপ প্রতিটি অণু অন্য অণুর সাথে দুর্বল কিন্তু প্রচুর হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে। এই বন্ডগুলি অণুগুলিকে একে অপরের দিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু পুরোপুরি স্থির করে না—তাই পানি প্রবাহিত হয়। একই সঙ্গে এই হাইড্রোজেন বন্ডগুলির কারণে পানির পৃষ্ঠে অণুগুলির মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজনী বল তৈরি হয়, যা পৃষ্ঠটান নামে পরিচিত। এ কারণেই ক্ষুদ্র পোকা বা সূক্ষ্ম বস্তু পানির উপর ভাসতে পারে, এবং এটি একটি অসাধারণ উদাহরণ যে কেবল আণবিক স্তরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভারসাম্যেই তরলতার মতো বৈশিষ্ট্য জন্ম নেয় [29].
৩️ লবণের গলন ও স্বাদ (Solubility and Taste): সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) একটি আয়নিক যৌগ, যেখানে Na⁺ ধনাত্মক এবং Cl⁻ ঋণাত্মক আয়নের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল একটি স্ফটিক জালিকা (crystal lattice) গঠন করে। এই গঠন পানিতে ভাঙে কারণ পানি নিজেই একটি পোলার অণু—এর ধনাত্মক দিক (H) Cl⁻ আয়নকে এবং ঋণাত্মক দিক (O) Na⁺ আয়নকে টানে। ফলে লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়, এবং আয়নগুলো সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে—এটাই দ্রবণ (solution) গঠনের মূল প্রক্রিয়া। লবণের স্বাদও এই আয়নিক বিচ্ছিন্নতার ফল, কারণ আমাদের স্বাদগ্রাহক কোষগুলো এই বৈদ্যুতিক আয়নগুলোর সাথে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেয় [30].
এই তিনটি উদাহরণ থেকেই দেখা যায়, পদার্থের কোনো বৈশিষ্ট্যই গঠনহীন অবস্থায় কল্পনা করা যায় না। চৌম্বকত্ব, তরলতা, বা দ্রবণীয়তা—সবই আণবিক গঠন, ইলেকট্রন-বিন্যাস, এবং শক্তির সমতা থেকে উদ্ভূত আচরণগত রূপ। যদি এই গঠন ভেঙে যায়, শক্তি-বিন্যাস পাল্টে যায়, বা ইলেকট্রন স্পিনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, তবে বৈশিষ্ট্যও বিলুপ্ত হয়।
অতএব, বৈশিষ্ট্য মানে কোনো অলৌকিক বা বিমূর্ত গুণ নয়; এটি হলো শক্তি ও কাঠামোর পারস্পরিক বিন্যাসের নিয়মিত প্রকাশ—একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের ফলাফল। আর যেহেতু অবস্তুগত সত্তার মধ্যে এই গঠনগত বা শক্তিগত বিন্যাস অনুপস্থিত, তাই তারা কোনো প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে না।
ধারণাগত ঈশ্বর বনাম অস্তিত্বশীল ঈশ্বর
ঈশ্বরের ধারণাকে দুটি স্তরে ব্যাখ্যা করা যায়—ধারণাগত (conceptual) ও অস্তিত্বশীল (ontological)। যদি ঈশ্বরকে আমরা শুধুমাত্র নৈতিক বা প্রতীকী ধারণা হিসেবে দেখি, তবে তিনি “conceptually real”, অর্থাৎ চিন্তা ও সংস্কৃতির জগতে বাস্তব। কিন্তু এই বাস্তবতা কেবল মানবমনের ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ; এটি কোনো পদার্থিক বা কার্যকর (causal) অস্তিত্ব নয়। এই অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব Plato-র Theory of Forms-এর মতো—যেখানে “রূপ” (Forms) ধারণাগতভাবে বিদ্যমান, কিন্তু পদার্থিক জগতে তার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই [1].
Plato যেমন বলেছিলেন, বাস্তব জগৎ হলো আদর্শ রূপের ছায়া বা প্রতিফলন, কিন্তু সেই রূপগুলো নিজে পদার্থিক নয়—তারা মানসিক বা বিমূর্ত ধারণার স্তরে টিকে থাকে। একইভাবে, “দয়ালু ঈশ্বর”, “সর্বজ্ঞ ঈশ্বর” বা “ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর”—এসব ধারণা নৈতিক প্রতীক ও মানসিক সান্ত্বনার প্রতিফলন হতে পারে, কিন্তু এগুলোর মহাবিশ্বে কোনো causal efficacy নেই; অর্থাৎ তারা কোনো পদার্থিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম নয়। একে আধুনিক দর্শনে বলা হয় “semantic reality without ontic grounding”—অর্থাৎ নাম বা ভাবনায় বাস্তব, কিন্তু অস্তিত্বে নয় [31].
এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ধারণাগত ঈশ্বর আসলে মানব সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্বের একটি উৎপন্ন কাঠামো—নৈতিক মানদণ্ডের প্রতীকী রূপ, যা সমাজে অর্থ, শৃঙ্খলা ও আশার প্রতিফলন ঘটায়। কিন্তু এই ঈশ্বর কোনো বাস্তব পদার্থিক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান নয়; কারণ বাস্তব অস্তিত্ব মানে হলো স্থান, কাল ও কার্য-সম্পর্কের মধ্যে অবস্থান করা। ধারণাগত সত্তা যেমন সংখ্যা, ভাষা, বা গণিতের সূত্র, তারা বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, কিন্তু নিজেরা মহাবিশ্বে কোনো প্রভাব ফেলে না।
অতএব, যদি ঈশ্বরকে শুধুমাত্র ধারণা বা প্রতীক হিসেবে ধরা হয়, তাহলে তাঁর “অস্তিত্ব” কেবল চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ—তিনি “conceptually real” কিন্তু “ontologically unreal”। এই অর্থে ঈশ্বরের গুণাবলি—যেমন দয়া, জ্ঞান, বা শক্তি—কেবল ভাষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক রূপে বিদ্যমান, বাস্তব পদার্থিক জগতে নয়। [32]
উপসংহার
দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই একটি মৌলিক সত্য উদ্ভাসিত হয়—“বৈশিষ্ট্য” মানে হলো কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং আচরণগত সম্ভাবনার সমন্বিত প্রকাশ। কোনো কিছুর রং, ঘনত্ব, নমনীয়তা, কিংবা তাপ পরিবাহিতা—সবই তার গঠনগত বিন্যাস ও শক্তি-বিন্যাসের ফল। বৈশিষ্ট্য তখনই বাস্তব যখন তার সঙ্গে পদার্থিক গঠন ও শক্তির কোনো সম্পর্ক থাকে। অন্যথায়, তা কেবল বিমূর্ত ধারণা বা ভাষাগত প্রতীক মাত্র।
Aristotle-এর substance-property তত্ত্ব থেকে শুরু করে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কোয়ান্টাম-ফিল্ড তত্ত্ব পর্যন্ত, সর্বত্রই দেখা যায় যে “অস্তিত্ব” মানে হলো কোনো কাঠামোগত উপস্থিতি—যার মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টি ও গ্রহণ করা সম্ভব। একটি পরমাণুর বিন্যাস বদলালে তার গুণ বদলে যায়; একটি শক্তিবিন্যাস ভাঙলে আচরণ বদলে যায়। যেমন, পানি জমে বরফ হলে তার অণু-গঠন পাল্টে যায় এবং তরলতা হারিয়ে যায়; লোহার ইলেকট্রন-স্পিনের সামঞ্জস্য নষ্ট হলে তার চৌম্বকত্ব বিলুপ্ত হয়। ফলে, বৈশিষ্ট্য কোনো স্বাধীন সত্তা নয়, বরং কাঠামোর সংগঠিত কার্যপ্রকাশ [8]; [16].
এই দৃষ্টিকোণ থেকে অবস্তুগত ঈশ্বরের “গুণাবলি”—যেমন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদয়—বাস্তবিক অর্থে টেকসই নয়। কারণ, এই গুণাবলির অস্তিত্ব বোঝাতে গেলে কোনো না কোনো কাঠামো, স্থানিক-সম্বন্ধ, বা কার্যকারণ সম্পর্ক প্রয়োজন, যা অবস্তুগত সত্তার ক্ষেত্রে সংজ্ঞাগতভাবেই অনুপস্থিত। ফলে, এসব গুণ কেবল মানুষের মানসিক, ভাষাগত ও নৈতিক কল্পনার প্রতিফলন—এক ধরনের anthropomorphic projection—যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই।
“To be is to be something; to have properties is to have structure.”
— (Adapted from Aristotle and modern physical ontology)
অতএব, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে বলা যায়—যেখানে গঠন নেই, সেখানে বৈশিষ্ট্য নেই; যেখানে বৈশিষ্ট্য নেই, সেখানে অস্তিত্বের দাবিও অর্থহীন। পদার্থবিজ্ঞানের বাস্তবতা ও যুক্তিবাদের নির্ভুলতা একত্রে দেখায় যে বৈশিষ্ট্যই অস্তিত্বের প্রমাণ, এবং অস্তিত্বহীন কোনো অবস্তুগত সত্তা কখনোই বাস্তব গুণ ধারণ করতে পারে না।
[ai_review]
তথ্যসূত্রঃ
- Plato, Republic, Book X 1 2
- Aristotle, Categories, 1a24–25 ↩︎
- Descartes, Principles of Philosophy, 1644 ↩︎
- Spinoza, Ethics, Part I, Prop. 14 ↩︎
- Hume, A Treatise of Human Nature, 1739, Book I, Part IV 1 2
- Kant, Critique of Pure Reason, 1787, B6 ↩︎
- Aristotle, Metaphysics, Book VII, 1029a–b ↩︎
- Armstrong, A World of States of Affairs, 1997 1 2 3
- Debiprasad Chattopadhyaya, Lokayata: A Study in Ancient Indian Materialism, 1959 ↩︎
- Tattvopaplava-siṁha, ed. Sukhlalji Sanghavi, 1940 ↩︎
- Atkins & de Paula, Physical Chemistry, Oxford University Press, 2014 1 2
- Tipler & Mosca, Physics for Scientists and Engineers, 7th ed., 2008 ↩︎
- Descartes, Meditations on First Philosophy, 1641, Meditation III ↩︎
- Aquinas, Summa Contra Gentiles, Book I, Ch. 38 ↩︎
- Hume, A Treatise of Human Nature, 1739, Book I, Part IV ↩︎
- Ladyman & Ross, Every Thing Must Go, 2007 1 2
- Atkins & de Paula, Physical Chemistry; Tipler & Mosca, Physics for Scientists and Engineers ↩︎
- Hume, Treatise, 1739 ↩︎
- Kim, Mind in a Physical World, 1998 ↩︎
- Russell, Human Knowledge: Its Scope and Limits, 1948 ↩︎
- Dennett, Consciousness Explained, 1991, Little Brown ↩︎
- Dennett, Consciousness Explained, 1991 ↩︎
- Crick & Koch, Scientific American, 1992 ↩︎
- Kant, Critique of Pure Reason, 1781, Transcendental Aesthetic ↩︎
- Lakoff & Núñez, Where Mathematics Comes From, 2000 ↩︎
- Plantinga, God, Freedom, and Evil, 1974 ↩︎
- Russell, Why I Am Not a Christian, 1927 ↩︎
- Tipler & Mosca, Physics for Scientists and Engineers, 2008 ↩︎
- Ball, The Water Molecule: A Biography of the Most Mysterious Substance on Earth, 2008 ↩︎
- Pauling, General Chemistry, 1970 ↩︎
- Russell, History of Western Philosophy, 1945 ↩︎
- Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, 2006 ↩︎